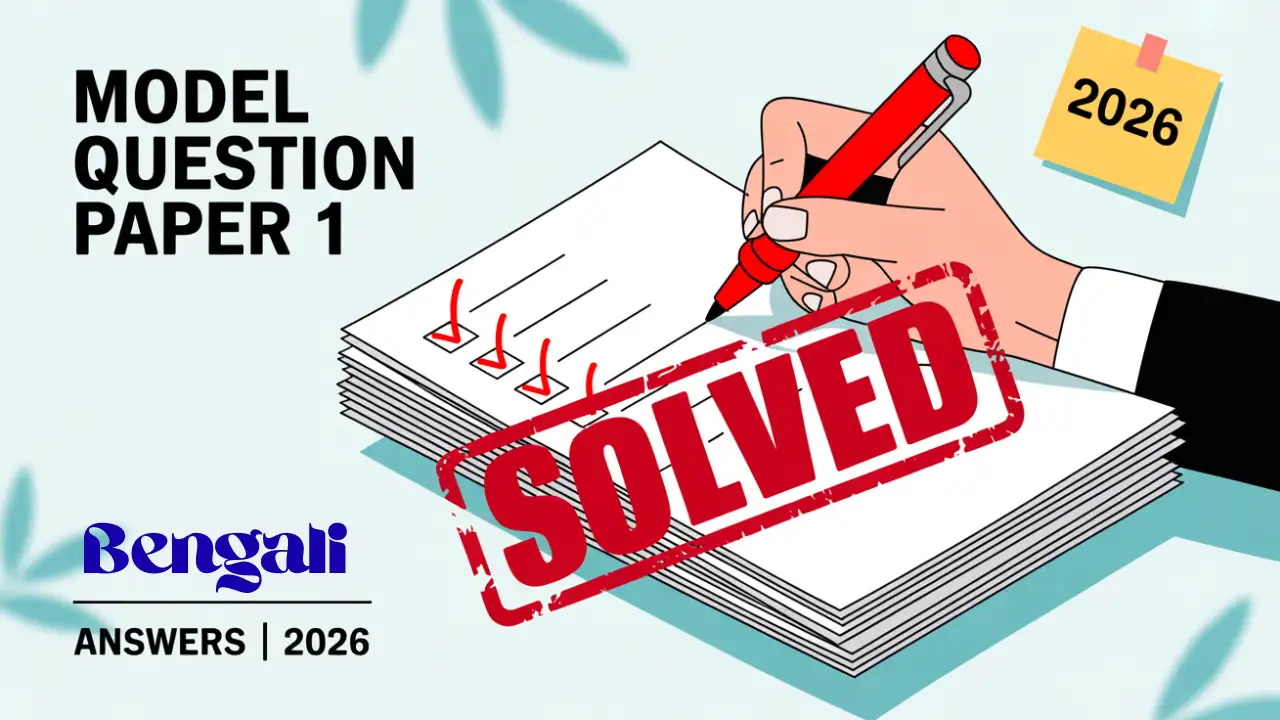আপনি কি ২০২৬ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 1 এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 1-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৫ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়া তপনের গল্পটির নাম
(ক) ইস্কুলের গল্প
(খ) একদিন
(গ) প্রথম দিন
(ঘ) রাজার কথা
উত্তর: (গ) প্রথম দিন
১.২ ‘… ছদ্মবেশে সেদিন হরিদার রোজগার মন্দ হয়নি।’ কীসের ছদ্মবেশে?-
(ক) বাইজির
(খ) পুলিশের
(গ) পাগলের
(ঘ) ভিখারির
উত্তর: (ক) বাইজির
১.৩ নদেরচাঁদকে পিষিয়া দিয়া চলিয়া গেল-
(ক) ৭ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার
(খ) ৫নং ডাউন প্যাসেঞ্জার
(গ) ৭নং আপ প্যাসেঞ্জার
(ঘ) ৫নং আপ প্যাসেঞ্জার
উত্তর: (ক) ৭ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার
১.৪ ‘ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে।’ কাছে দূরে ছড়ানো রয়েছে-
(ক) ধ্বস
(খ) আমাদের শিশুদের শব
(গ) হিমানীর বাঁধ
(ঘ) গিরিখাদ
উত্তর: (খ) আমাদের শিশুদের শব
১.৫ ‘যুগান্তের কবি’ কোথায় এসে দাঁড়াবেন?
(ক)মন্দিরে
(খ) শিশুদের কাছে
(গ) সভ্যতার প্রান্তে
(ঘ) মানহারা মানবীর দ্বারে
উত্তর: (ঘ) মানহারা মানবীর দ্বারে
১.৬ ‘হৈমবতীসুত’ হলেন
(ক) অর্জুন
(খ) লক্ষ্মণ
(গ) কার্তিকেয়
(ঘ) মেঘনাদ
উত্তর: (গ) কার্তিকেয়
১.৭ চারখন্ড রামায়ণ কপি করে একজন লেখক অষ্টাদশ শতকে কত টাকা পেয়েছিলেন?-
(ক) সাত টাকা
(খ) আট টাকা
(গ) ন’টাকা
(ঘ) দশ টাকা
উত্তর: (ক) সাত টাকা
১.৮ “তিল ত্রিফলা সিমুল ছালা” ‘ত্রিফলা’ হল
(ক) আমলকি, সুপারি, হরিতকি
(খ) সুপারি, এলাচ, জায়ফল
(গ) সুপারি,এলাচ, বহেড়া
(ঘ) আমলকি, হরিতকি, বহেড়া
উত্তর: (ঘ) আমলকি, হরিতকি, বহেড়া
১.৯ ‘Sensitized Paper’-এর অনুবাদ কী লিখলে ঠিক হয় বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন?
(ক) স্পর্শকাতর কাগজ
(খ) সুগ্রাহী কাগজ
(গ) সুবেদী কাগজ
(ঘ) ব্যথাপ্রবণ কাগজ
উত্তর: (খ) সুগ্রাহী কাগজ
১.১০ ‘বিপদে মোরে রক্ষা করো।’ রেখাঙ্কিত পদটির কারক-
(ক) অধিকরণ কারক
(খ) অপাদান কারক
(গ) করণ কারক
(ঘ) কর্মকারক
উত্তর: (খ) অপাদান কারক
১.১১ ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ককে বলে
(ক) সমাস
(খ) কারক
(গ) প্রত্যয়
(ঘ) বিভক্তি
উত্তর: (খ) কারক
১.১২ ‘গ্রামান্তর’ কোন সমাস হবে?
(ক) দ্বন্দ্ব
(খ) দ্বিগু
(গ) নিত্য
(ঘ) তৎপুরুষ
উত্তর: (গ) নিত্য
১.১৩ উপমান ও উপমেয় পদের অভেদ কল্পনা করা হয় যে সমাসে, তার নাম-
(ক) উপমিত কর্মধারয়
(খ) উপমান কর্মধারয়
(গ) রূপক কর্মধারয়
(ঘ) সম্বন্ধ তৎপুরুষ
উত্তর: (গ) রূপক কর্মধারয়
১.১৪ যে বাক্যে সাধারণত কোনো কিছুর বর্ণনা বা বিবৃতি থাকে, তাকে বলা হয়-
(ক) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য
(খ) নির্দেশক বাক্য
(গ) আবেগসূচক বাক্য
(ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্য
উত্তর: (খ) নির্দেশক বাক্য
১.১৫ আজও সে যাইল এবং সেইখানে বসিল। কোন্ ধরনের বাক্য? –
(ক) সরল বাক্য
(খ) জটিল বাক্য
(গ) যৌগিক বাক্য
(ঘ) মিশ্রবাকা
উত্তর: (গ) যৌগিক বাক্য
১.১৬ ‘নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে’ এটি কোন্ বাচ্যের উদাহরণ?-
(ক) কর্মবাচ্য
(খ) ভাববাচ্য
(গ) কর্তৃবাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (গ) কর্তৃবাচ্য
১.১৭ যে বাচ্যে কর্তার অর্থপ্রধান্য ঘটে, তাকে বলে-
(ক) কর্তৃবাচ্য
(খ) কর্মবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (ক) কর্তৃবাচ্য
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ ‘এবিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।’ কোন বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল?
উত্তর: আশাপূর্ণা দেবীর “জ্ঞানচক্ষু” গল্পে তপন প্রথমে ভাবত লেখকরা বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু তাদের দৈনন্দিন আচরণ, স্বাভাবিক চাহিদা ও দুর্বলতা দেখে তার মনে সন্দেহ জাগে যে লেখকরাও আসলে সাধারণ মানুষের মতোই।
২.১.২ ‘অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।’ হরিদার কোন্ ভুলের কথা এখানে বলা হয়েছে?
উত্তর: উক্তিটি সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। বিরাগী সাজে সজ্জিত হরিদা ধনীমানুষ জগদীশ বাবুর দেওয়া প্রণামী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এখানে তাঁর এই প্রণামী গ্রহণ না করার ঘটনাকেই হরিদার ভুল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
২.১.৩ ‘বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।’ বুড়োমানুষের কোন্ কথা শুনতে বলা হয়েছে?
উত্তর: বুড়োমানুষ অর্থাৎ নিমাইবাবু যে কথাটি গিরিশ মহাপাত্রকে শুনতে বলেছিলেন তা হল- “আর গাঁজা খেও না।
২.১.৪ “সবাই যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেল।” তাদের পালিয়ে যাওয়ার কারণ কী?
উত্তর: কালিয়া ও ইসাবের কুস্তি তামাশা থেকে গুরুতর রূপ নেয়।
ইসাব ল্যাং মারতে কালিয়া ব্যাঙের মতো হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে চ্যাঁচাতে লাগে।
তামাশা করে হলেও এখন ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে পড়েছে এবং কালিয়ার বাবা-মা এসে ওদের পিটুতে পারে বুঝতে পেরে সবাই যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়।
২.১.৫ ‘সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; কেঁদে ফেলার কারণ কী?
উত্তর: নদেরচাঁদের কাছে নদী ছিল জীবন্ত মানুষের প্রতিমূর্তি। এক অনাবৃষ্টির বছরে সে তার দেশের নদীটিকে প্রায় শুকিয়ে যেতে দেখেছে। নদীর এই প্রাণহীন রূপ তার কাছে মানুষের মৃত্যুর সমান মনে হয়েছিল। তাই ছোটবেলার সেই নদীর এমন অবস্থায় দেখে নদেরচাঁদ প্রায় কেঁদে ফেলেছিল।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ ‘তারপর যুদ্ধ এল’ যুদ্ধ কেমনভাবে এল?
উত্তর: ‘তারপর যুদ্ধ এল’ যুদ্ধ— যুদ্ধ এল রক্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের মতো।
২.২.২ ‘এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি।’ কে, কী বুঝতে পারেননি?
উত্তর: ‘এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি বক্তা মেঘনাদ।
মৃত্যুর পরেও রামচন্দ্র কীভাবে পুনরায় জীবিত হলেন—এই মায়ার ছলনা তিনি বুঝতে পারছেন না।
২.২.৩ “আসছে নবীন-“- ‘নবীন’ এসে কী করবে?
উত্তর: আসছে নবীন — ‘নবীন’ এসে জীবনহারা অ-সুন্দরে ছেদন করবে।”
অংশটি কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘ প্রলয়োল্লাস ’ কবিতা থেকে নেওয়া। কবিতায় এই ছুটন্ত জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে । নিশ্চিত জীবনহারা – অশুভের বিনাশকারী নবীনের মধ্যেই আছে সেই নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা । সেই পারে নির্জীব গতিহীন এবং জীবন ধারায় যা কিছু অ-সুন্দর তা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে । উপরের উদ্ধৃতিটিতে কবি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন
২.২.৪ “পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন।” ‘পঞ্চকন্যা’ কারা?
উত্তর: আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ আলাওল রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের অন্তর্গত ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতা থেকে প্রদত্ত অংশটি নেওয়া হয়েছে।
যে অচেতন পঞ্চকন্যার কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন সিংহল রাজকন্যা তথা চিতোর রাজ রন্তসেনের পত্নী পদ্মাবতী ও তাঁর চারজন সখী, চন্দ্রকলা, বিজয়া, রোহিনী এবং বিধুন্নলা।
২.২.৫ ‘মাথায় কত শকুন বা চিল / আমার শুধু একটা কোকিল’ চিল, শকুন ও কোকিল কীসের প্রতীক?
উত্তর: জয় গোস্বামীর ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় শকুন ও চিল প্রতীক— হিংস্রতা ও নৃশংসতার, যা যুদ্ধবাজদের স্বভাব নির্দেশ করে। আর কোকিল প্রতীক শান্তি, সৌন্দর্য ও মানবিকতার।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘নামটা রবীন্দ্রনাথের দেওয়াও হতে পারে।’ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নামটি কী?
উত্তর: ফাউন্টেন পেনের বাংলা ‘নামটা রবীন্দ্রনাথের দেওয়াও হতে পারে নামটি হলো ঝরণা কলম।
২.৩.২ ‘বাংলায় একটা কথা চালু ছিল,’ কথাটি কী?
উত্তর: ‘বাংলায় একটা কথা চালু’—- বাংলায় চালু কথাটি হলো – “কালি নেই, কলম নেই, বলে আমি মুনশি।”
২.৩.৩ ‘কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় দেখেছি’- কে, কী দেখেন?
উত্তর: প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু একটি পত্রিকায় দেখেছিলেন, জনৈক লেখক লিখেছেন— অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই; এগুলি শুধু জীবের বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য উপাদান মাত্র।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ প্রযোজক কর্তার উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।
উত্তর: প্রযোজক কর্তার সংজ্ঞা:
যে কর্তা নিজে কাজটি করে না, অন্য কর্তা দিয়ে কাজ করায়, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।
এক্ষেত্রে কর্তার কাজ সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া বা উদ্যোগ নেওয়া প্রধান কাজ।
উদাহরণ: রামুকে দিয়ে মাঠে ঘাস কাটালো।
২.৪.২ বিভক্তি ও অনুসর্গের একটি পার্থক্য লেখো।
উত্তর: বিভক্তি একটি চিহ্ন, এর নিজস্ব অর্থ নেই; অন্যদিকে অনুসর্গের একটি শব্দ, এর নিজস্ব অর্থ আছে ।
২.৪.৩ “নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?” ‘নদী’ কী পদ?
উত্তর: “নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?” বাক্যে “নদী” একটি বিশেষ্য পদ।
২.৪.৪ ‘পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?’- নিম্নরেখ পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: ব্যাসবাক্য: লৌকিক নয় যা, তাই অলৌকিক।
সমাসের নাম: নঞ্ তৎপুরুষ সমাস।
২.৪.৫ ‘গৌর অঙ্গ যাহার’ ব্যাসবাক্যটি সমাসবদ্ধ করে সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: ব্যাসবাক্য: গৌর অঙ্গ যাহার
সমাসবদ্ধ পদ: গৌরাঙ্গ
সমাসের নাম: সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস
২.৪.৬ দ্বিগু সমাস ও সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের একটি পার্থক্য লেখো।
উত্তর: পার্থক্য:
দ্বিগু সমাসে সংখ্যা-সূচক শব্দটি সমাসের প্রথমপদ হয় এবং সমাসপদটি সাধারণত বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।
উদাহরণ: ত্রিলোক (তিনটি লোক)।
সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসে সংখ্যা-সূচক শব্দ থাকলেও সমাসপদটি বিশেষণরূপে অন্য কিছুকে নির্দেশ করে।
উদাহরণ: ত্রিনয়ন (যার তিনটি নয়ন আছে)।
২.৪.৭ ‘আসত্তি’ কাকে বলে? এর অপর নাম কী?
উত্তর: যখন দুটি বা ততোধিক পদ পরস্পরের এত নিকটে থাকে যে, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা সন্নিধি বোঝা যায়, তখন সেই সম্পর্ককে আসত্তি বলে।
অপর নাম: নৈকট্য বা সন্নিধি।
২.৪.৮ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি কাব্য রচনা করেন। বাক্যটি থেকে উদ্দেশ্য সম্প্রসারক নির্ণয় করো।
উত্তর: বাক্য: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি কাব্য রচনা করেন।
এখানে “গীতাঞ্জলি কাব্য” হলো উদ্দেশ্য সম্প্রসারক।
২.৪.৯ কর্মকর্তৃবাচ্য কাকে বলে?
উত্তর: কর্মকর্তৃবাচ্য
সংজ্ঞা: যে বাক্যে ক্রিয়ার ফল বা কাজের প্রধান লক্ষ্য (কর্ম) কর্তার স্থানে এসে কর্তা রূপে ব্যবহৃত হয় এবং মূল কর্তা (যে কাজটি করে) অপাদান, কর্তৃকারক বা অন্য কোনো কারকে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে।
২.৪.১০ ‘ক্ষমা করো।’ ভাববাচ্যে রূপান্তর করো।
উত্তর: ‘ক্ষমা করো’ বাক্যটির ভাববাচ্য রূপ হবে — ক্ষমা করা হোক।
৩। প্রসজ্ঞা নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ “পারিলেও মানুষ কি তাকে রেহাই দিবে?” কার, কী পারার কথা বলা হয়েছে? মানুষ কেন তাকে রেহাই দেবে না?
উত্তর: উক্তিটি নদেরচাঁদের বক্তব্য।
তার মতে, নদী ইচ্ছা করলে মানুষের গড়া বাঁধ ভেঙে গুরিয়ে চুরমার করে দিতে পারে নদীর তীব্র জলস্রোত।
তবুও মানুষ তাকে রেহাই দেবে না, বরং আবার নতুন বাঁধ তৈরি করে জীবন্ত প্রবহমান নদীকে নিজেদের স্বার্থে বন্দি করবে। ফলে গভীর, জলপূর্ণ নদী ক্ষীণস্রোতা নদীতে পরিণত হবে।
৩.১.২ ‘হরির কান্ড।’ এখানে হরির কোন কান্ডের কথা বলা হয়েছে? এই কান্ডে হরির কত রোজগার হয়েছিল?
উত্তর: সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পে ‘হরির কাণ্ড’ বলতে বোঝানো হয়েছে শহরের পথে রূপসি বাইজির ছদ্মবেশে, লেজে ঘুঙুর বেঁধে নাচতে নাচতে চলার ঘটনাকে। এই অভিনব ছদ্মবেশ প্রদর্শনের মাধ্যমে হরিদা মোট আট টাকা দশ আনা রোজগার করেছিলেন।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “সে জানত না আমি আর কখনো ফিরে আসব না।” ‘সে’ কে? ‘আমি আর কখনো ফিরে আসব না’ বলার কারণ কী?
উত্তর: পাবলো নেরুদা রচিত, নবারুণ ভট্টাচার্য অনূদিত ‘অসুখী একজন’ কবিতায় ‘সে’ বলতে বোঝানো হয়েছে প্রতীক্ষায় থাকা মেয়েটিকে। কবি কথক কর্তব্যের টানে স্বদেশ ও আপনজনদের ছেড়ে সুদূরে পাড়ি জমিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও আর তাঁর দেশে ফেরা হয়নি। এই না ফেরা হয়ে ওঠে কবির জীবনের করুণ নিয়তি। কিন্তু মেয়েটি কিছুই জানত না, সে ভেবেছিল প্রিয়জন একদিন ফিরে আসবেন। তাই বছরের পর বছর সে দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে। কবি আসলে জানতেন তিনি আর কোনোদিন ফিরবেন না, তাই কবিতায় বলেছেন— “আমি আর কখনো ফিরে আসব না।”
৩.২.২ “হায় ছায়াবৃতা,” ‘ছায়াবৃতা’ কে? কেন সে ছায়াবৃতা?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আফ্রিকা’ কবিতায় ‘ছায়াবৃতা’ বলতে আফ্রিকা মহাদেশকে বোঝানো হয়েছে। আফ্রিকা দীর্ঘদিন আধুনিক সভ্যতা ও জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল, তার প্রকৃতি রহস্যময় অরণ্যে আবৃত ছিল। তাই কবি তাকে ‘ছায়াবৃতা’ বলেছেন।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ বিদেশি সাহেবের কাছে অপূর্বর অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার যে দুটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে,তা লেখো।
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ গল্পাংশে ইংরেজদের হাতে অপূর্বর দুটি অপমান ও লাঞ্ছনার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
ঘটনা নম্বর ১: স্টেশনে কিছু ফিরিঙ্গি ছেলে বিনা কারণে অপূর্বকে লাথি মেরে প্ল্যাটফর্ম থেকে তাড়িয়ে দেয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে সাহেব স্টেশনমাস্টার তাকে ভারতীয় বলে অপমান করে কুকুরের মতো দূর করে দেয়। নিজের দেশে এমন লাঞ্ছনার অপমান অপূর্ব আজীবন ভুলতে পারেনি।
ঘটনা নম্বর ২: রেঙ্গুন থেকে ভামো নগরে প্রথম শ্রেণির যাত্রী হিসেবে যাত্রাকালে পুলিশ বারবার তার ঘুম ভেঙে নাম-ঠিকানা নথিভুক্ত করে। বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করলে সাব-ইনস্পেকটর কটুবাক্যে জানায়, এসব তাকে সহ্য করতেই হবে কারণ সে ইউরোপীয় নয়। অপূর্বর যুক্তি ছিল, প্রথম শ্রেণির যাত্রী হিসেবে এমন আচরণ অনুচিত, কিন্তু ইনস্পেকটর জানায়, এই নিয়ম রেলের কর্মচারীদের জন্য, তার জন্য নয়। শুধুমাত্র ভারতীয় হওয়ায় তাকে এই অপমান মেনে নিতে হয়েছিল।
৪.২ ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।
উত্তর: আশাপূর্ণা দেবীর ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পে কিশোর তপনের জ্ঞানোদয়ের কাহিনী ফুটে উঠেছে। ছোটো মাসির বেড়াতে এসে মামার বাড়িতে সে প্রথমবার এক লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়—তার নতুন মেসো।
লেখক সম্পর্কে কল্পনা ভেঙে সে উপলব্ধি করে, লেখকরাও সবার মতো সাধারণ মানুষ। পৃথিবির বাইরে থেকে আসা কেউ না।
এটাই তার প্রথম জ্ঞানোদয়।
পরে তপন একটি গল্প লিখে মেসোর হাতে দেয় ছাপানোর জন্য, কিন্তু ছাপার সময় পুরো গল্পটি সংশোধনের নামে মেসো বদলে দেয়। নিজের লেখা চিনতে না পেরে তার আনন্দ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই ঘটনা থেকে দ্বিতীয়বার তার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়—সে সিদ্ধান্ত নেয়, ভবিষ্যতে নিজের লেখা নিজেই ছাপাতে দেবে, যেমন আছে তেমনই তাতে ছাপা হোক না হোক ।
গল্পে তপনের দুইবার জ্ঞানোদয় হয়। প্রথমবার লেখককে দেখে বাস্তব উপলব্ধি, দ্বিতীয়বার সৃজনের স্বাধীনতার বোধ—গল্পের নামের সঙ্গে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই ‘জ্ঞানচক্ষু’ নামকরণটি সার্থক।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।’ কাদের প্রতি কবির এই আবেদন? বেঁধে বেঁধে থাকার তাৎপর্যটি কী?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি” কবিতায় কবি সাধারণ মানুষের প্রতি এই আবেদন জানিয়েছেন। কবির মতে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ ভীষণ সংকটের মুখে পড়েছে। তাদের চারদিকে শুধু ধ্বংস আর বিপদ—ডান দিকে ধ্বস, বাঁ পাশে গভীর গিরিখাত, মাথার উপর মৃত্যুর বার্তা নিয়ে বোমারু বিমান, আবার পায়ে হিমবাহের বাঁধ। কোথাও তাদের আশ্রয় নেই; এমনকি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অর্থাৎ শিশুরাও ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে।
এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষের আর হারাবার কিছু অবশিষ্ট নেই। তারা হয় সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে, নয়তো ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়বে। তাই কবি সাধারণ মানুষকে আহ্বান করেছেন—তারা যেন ‘বেঁধে বেঁধে’ অর্থাৎ মিলিত হয়ে, একত্র থেকে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলে। কবির মতে, মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পথ হলো ঐক্য। ঐক্যের মধ্য দিয়েই তারা দুর্বার শক্তি অর্জন করতে পারে এবং অশুভ শক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।
৫.২ ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় কবি অস্ত্র ফেলতে বলেছেন কেন? অস্ত্র পায়ে রাখার মর্মার্থ কী?
উত্তর: কবি জয় গোস্বামী তাঁর ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় মানুষকে অস্ত্র ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন। কবির মতে, অস্ত্র হলো হিংসা, ধ্বংস ও অমানবিকতার প্রতীক। ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারের নেশায় মানুষ যখন হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, তখন মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কবি বলেছেন অস্ত্র ফেলে দিতে, কারণ অস্ত্র কোনো সভ্যতার শেষ কথা নয়।
অস্ত্র গানের পায়ে রাখার মর্মার্থ হলো—অস্ত্র যেন গানের সুরের নিচে চেপে থাকে, গানের মানবিক শক্তির কাছে পরাভূত হয়। অর্থাৎ গান, সুর, প্রেম ও শান্তিই হোক জীবনের পথপ্রদর্শক, অস্ত্র নয়। কবি এভাবেই মানবতাবাদী চিন্তাকে সামনে এনে অস্ত্রের পরিবর্তে গানকে জীবনযুদ্ধের আসল হাতিয়ার করতে বলেছেন।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ ‘কমপিউটারও নাকি ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু সে ছবি কতখানি যন্ত্রের, আর কতখানি শিল্পীর?’ লেখকের এই মন্তব্যের কারণ বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: কম্পিউটার একটি উন্নত যন্ত্র, যা প্রযুক্তির সহায়তায় ছবি আঁকতে সক্ষম। কিন্তু সেই ছবির সঙ্গে মনের কোনো যোগ থাকে না। ছবি আঁকা কেবল প্রযুক্তি নির্ভর নয়, এটি এক ধরনের সৃজনশীল শিল্পকর্ম। শিল্পীর আঁকা ছবির মধ্যে তার অনুভূতি, আবেগ ও ভাবনার প্রকাশ ঘটে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষর কাটাকাটি করতে গিয়েও খেয়ালি মনে সাদা-কালো ছবি এঁকে ফেলতেন, যেখানে তার মনের স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটত। কিন্তু কম্পিউটারের কোনো মন নেই, তাই তার আঁকা রেখা নিছকই যান্ত্রিক আঁকিবুঁকি মাত্র। লেখক এ কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন—যন্ত্রে তৈরি ছবির মধ্যে কতটা শিল্পীর, আর কতটা যন্ত্রের অবদান।
লেখকের মতে, মনের সৃষ্টিকে যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলে তা কৃত্রিম হয়ে যায়, কারণ আবেগহীন শিল্প জীবন্ত হতে পারে না। যখন ভাব গভীর হয়, শিল্পী রং ও তুলির মাধ্যমে তা প্রাণবন্ত করে তোলেন। তাই শিল্পীর আঁকা ছবি কম্পিউটারের তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী মনে হয়।
৬.২ “আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন” ‘শব্দের ত্রিবিধ কথা’ কী? এই ত্রিবিধ কথা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উত্তর: আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন— অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। প্রাবন্ধিক এই তিন প্রকার শব্দবৃত্তির মাধ্যমে শব্দের অর্থপ্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বোঝাতে চেয়েছেন।
প্রথমটি অভিধা—এতে শব্দ তার মুখ্য অর্থ প্রকাশ করে। এই বৃত্তিতে শব্দটি বাচক এবং অর্থটি বাচ্য বা অভিধেয় হয়। যেমন—‘পঙ্কজ’ শব্দে পদ্ম অর্থই মুখ্য। যদিও ‘পাঁকে জন্মে যা’ অর্থেও ব্যবহার হতে পারে, তবু অভিধা পদ্ম অর্থেই সীমাবদ্ধ।
দ্বিতীয়টি লক্ষণা—যখন মুখ্য অর্থের পরিবর্তে গৌণ অর্থ প্রধান হয়। যেমন—“এই রিকশা, এদিকে এসো” বাক্যে ‘রিকশা’ দ্বারা রিকশাওয়ালাকে বোঝানো হয়েছে; এখানে মুখ্য অর্থ ‘যান’-এর পরিবর্তে গৌণ অর্থ ‘মানুষ’ প্রধান হয়েছে।
তৃতীয়টি ব্যঞ্জনা—যখন অভিধা ও লক্ষণায় অর্থ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না, তখন শব্দ নতুন অর্থের ইঙ্গিত দেয়। যেমন—“সোনার হাতের সোনার কাঁকন কে কার অলংকার?”—এখানে গভীর ভাবার্থের প্রকাশ ঘটেছে।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ ‘জাতির সৌভাগ্য-সূর্য আজ অস্তাচলগামী;’ কোন্ জাতির কথা উদ্ধৃতাংশে বলা হয়েছে? তার সৌভাগ্য-সূর্য অস্তাচলগামী কেন?
উত্তর: নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত সিরাজদ্দৌল্লা নাটকে বাংলার চরম দুর্দিনে উক্ত মন্তব্য করেছেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। এখানে জাতি বলতে বাঙালি জাতিকে বোঝানো হয়েছে। নবাবের প্রধান সেনাপতি মিরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, ঘসেটি বেগম প্রমুখ ইংরেজদের সঙ্গে মিলে সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আলিবর্দি খাঁ-র মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসে সিরাজ।
সিরাজ জাতির স্বাধীনতা রক্ষা ও প্রজাদের কল্যাণে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ইংরেজদের আক্রমণ, ফরাসি বণিকদের বাণিজ্যস্থল দখল ও অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় করেন। কিন্তু ইংরেজদের ক্ষমতা ও সৈন্যসমাবেশ ক্রমে বাড়তে থাকে। নিরুপায় অবস্থায়ও নবাব শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। তখনই তাঁর বেদনাময় উপলব্ধি— “জাতির সৌভাগ্য-সূর্য আজ অস্তাচলগামী।”
৭.২ “আমার রাজ্য নাই, তাই আমার কাছে রাজনীতিও নাই আছে শুধু প্রতিহিংসা।” বক্তা কে? উদ্ধৃত উক্তিটির আলোকে বক্তার চরিত্র আলোচনা করো।
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশে সিরাজের উক্তি—”আমার রাজ্য নাই, তাই আমার কাছে রাজনীতিও নাই, আছে শুধু প্রতিহিংসা।”—কথাগুলি মাতৃস্বসা ঘসেটি বেগম নবাব সিরাজদ্দৌলার উদ্দেশ্যে বলেছেন।
উদ্ধৃত উক্তিটির আলোকে বক্তার চরিত্র আলোচনা আলীবর্দি, নিজের কোনো পুত্র না থাকায় তৃতীয় মেয়ের পুত্র সিরাজদ্দৌলাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। সেইমতো আলীবর্দির মৃত্যুর পরে সিরাজ বাংলার মসনদে বসেন। কিন্তু এই ঘটনায় সর্বাপেক্ষা বিরূপ হয়েছিলেন ঘসেটি বেগম। তিনি আর-এক বোনের পুত্র, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকতজঙ্গকে বাংলার মসনদে বসাতে চেয়েছিলেন। এজন্যে তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ফলে সিরাজ তাকে নিজ প্রাসাদে বন্দি করেন। বন্দিনী ঘসেটির প্রতিহিংসার এই ছিল মূল কারণ, যা থেকে তার প্রতিহিংসাপরায়ণ চরিত্র স্পষ্ট হয়।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ ‘ফাইট কোনি, ফাইট’ শব্দবন্ধটি সমগ্র উপন্যাসকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, আলোচনা করো।
উত্তর: মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসে ‘ফাইট কোনি, ফাইট’ শব্দবন্ধটি কেবল একটি স্লোগান নয়, বরং সমগ্র উপন্যাসের চালিকাশক্তি। শ্যামপুকুর বস্তির দরিদ্র পরিবারের মেয়ে কোনির জীবন সংগ্রামের কাহিনিই এই উপন্যাসের মূল ভিত্তি। ছোটোবেলা থেকেই তাকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। তিনবেলা খাবার জোটানোই যখন পরিবারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ, তখন সাঁতারের কস্ট্যুম বা প্রশিক্ষণের খরচ বহন করা ছিল অসম্ভব। তবুও ক্ষিতিশবাবুর সহায়তায় কোনি জলের জগতে প্রবেশ করে।
কিন্তু তার লড়াই শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং নিজের অক্ষমতা ও সামাজিক অপমানের বিরুদ্ধেও ছিল। অমিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর কটুক্তি তাকে আহত করলেও সে কখনো ভেঙে পড়েনি। নিজের দক্ষতা প্রমাণের জন্য সে নিরলস পরিশ্রম করেছে। আবার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব জুপিটারের ষড়যন্ত্র ও বঞ্চনাও তাকে আটকে রাখতে পারেনি। কখনো অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া, কখনো প্রতিযোগিতায় বসিয়ে রাখা—এসবের বিরুদ্ধে তার একমাত্র হাতিয়ার ছিল লড়াই করার মানসিকতা।
শেষপর্যন্ত, মাদ্রাজের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়ে কোনি নিজের প্রতিভার প্রমাণ দেয় এবং চ্যাম্পিয়ন হয়। তাই ‘ফাইট কোনি, ফাইট’ শব্দবন্ধটি শুধু কোনির নয়, প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের অনুপ্রেরণার প্রতীক। এটি উপন্যাসের মূল মন্ত্র, যা পাঠককে জীবনযুদ্ধে সাহসী হতে উদ্বুদ্ধ করে।
৮.২ প্রণবেন্দু বিশ্বাসের চরিত্র পাঠ্য রচনা অবলম্বনে আলোচনা করো।
উত্তর: কে প্রণবেন্দু বিশ্বাস—
মতি নন্দী রচিত ‘কোনি’ উপন্যাসে বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবের ট্রেনার প্রণবেন্দু বিশ্বাস একটি পার্শ্বচরিত্র হয়েও নিজস্বতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন।
প্রণবেন্দু বিশ্বাসের চরিত্র আলোচনা—
তিনি একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ সাঁতার প্রশিক্ষক। তার প্রশিক্ষণে হিয়া মিত্র বাংলার অন্যতম সেরা সাঁতারু হয়। একই বিচক্ষণতায় কোনির প্রতিভাও চিনতে ভুল করেননি। প্রণবেন্দুর সৎ ও নিরপেক্ষ মানসিকতার ফলেই কোনি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে সুযোগ পায়। এমন-কী প্রতিবাদী কন্ঠে বলেন “বেঙ্গলের স্বার্থেই কনকচাঁপা পালকে টিমে রাখতে হবে।”
হিয়ার ট্রেনার হয়েও কোনির পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, “ওর সমকক্ষ এখন বাংলায় কেউ নেই।” সংকীর্ণ দলাদলির ঊর্ধ্বে থেকে বাংলার স্বার্থে দৃপ্তকণ্ঠে জানান, “রমা যোশির সোনা কুড়োনো বন্ধ করা ছাড়া আমার আর কোনো স্বার্থ নেই।” তার সততা, প্রতিবাদী মনোভাব ও বিচক্ষণতা তাকে এক ব্যতিক্রমী চরিত্রে পরিণত করেছে।
৮.৩ “মেডেল তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু একটা দেশ বা জাতির কাছে মেডেলের দাম অনেক,” কোন্ প্রসঙ্গেঙ্গ এই উক্তি। এর মর্মার্থ লেখো।
উত্তর: কোন্ প্রসঙ্গে উক্তি–
মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসে আলোচ্য উক্তিটি বলেছেন সাঁতারু প্রশিক্ষক ক্ষিতীশ সিংহ। তিনি বিষ্ণুচরণ ধড়কে এই কথাগুলি বলেছিলেন।
উক্তিটির মর্মার্থ–
‘কোনি’ উপন্যাসে এক অতি সাধারণ বস্তির মেয়ে কোনির জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সমাজ, দেশ বা বিশ্বের কাছে একজন ব্যক্তির কৃতিত্ব তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন প্রতিভা ও মনোভাব। সেই প্রতিভাই তাকে শাশ্বতকাল মানুষের মনে বাঁচিয়ে রাখে, আর তার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদও বেঁচে থাকে।
একটি দেশ বা জাতির কাছে মেডেলের মূল্য অনেক হলেও একজন ট্যালেন্টেড খেলোয়াড়ের জন্য মেডেল তুচ্ছ। কারণ, তার প্রেরণা ও মনোভাব দেশ, জাতি এমনকি সারা পৃথিবীকে অনুপ্রেরণা জোগায়। ক্ষিতীশ সিংহের মতে, একজন খেলোয়াড়কে পৃথিবীর মানুষ যাতে এক নামে চিনতে পারে, সেটাই জীবনের সত্যিকারের সার্থকতা।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো:
Man is the maker of his fortune. We cannot prosper in our life if we are afraid of labour. Some people think that success in life depends on luck or chance. Remember, without hard work success is never attainable.
উত্তর: মানুষ নিজের ভাগ্যের নির্মাতা। পরিশ্রমকে ভয় পেলে জীবনে আমরা উন্নতি করতে পারব না। অনেকেই মনে করে জীবনে সাফল্য পাওয়া ভাগ্য বা সুযোগের উপর নির্ভর করে। মনে রাখবে, পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য কখনও অর্জন করা যায় না।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ মোবাইল ফোন ব্যবহারের ভালো-মন্দ নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
মোবাইল ফোন ব্যবহারের ভালো-মন্দ নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ
রাহুল: শুভ, আজকাল সবাই মোবাইল ফোনে এতটাই মগ্ন যে চারপাশের জগৎ ভুলে যাচ্ছে।
শুভ: ঠিক বলেছিস, তবে মোবাইলেরও অনেক ভালো দিক আছে। এতে তথ্য, পড়াশোনা, খবর—সব হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়।
রাহুল: হ্যাঁ, পড়াশোনার জন্য ইউটিউব, অনলাইন ক্লাস, ডিকশনারি—এসব খুব কাজে লাগে। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যবহার চোখের ক্ষতি করে, মনোযোগ নষ্ট করে।
শুভ: একদম ঠিক। তাছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় কাটালে আসল জীবনের সম্পর্কগুলো দুর্বল হয়ে যায়।
রাহুল: আবার জরুরি সময়ে মোবাইল প্রাণ বাঁচাতেও পারে—অ্যাম্বুলেন্স ডাকা, সাহায্য চাওয়া, খবর দেওয়া সহজ হয়।
শুভ: তাই তো, সবকিছুই নির্ভর করে ব্যবহারের ওপর। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে মোবাইল আশীর্বাদ, আর অপব্যবহার করলে অভিশাপ।
রাহুল: ঠিক বলেছিস। আমাদের উচিত সময় বেঁধে, প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইল ব্যবহার করা।
শুভ: একমত! তবেই মোবাইল আমাদের সত্যিকারের সহায়ক হবে।
১০.২ এলাকায় রক্তদান শিবিরের সাফল্য নিয়ে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
রক্তদান শিবিরে অভূতপূর্ব সাড়া, উপকৃত বহু রোগী
নিজেস্ব সংবাদদাতা, বীরভূম, সেপ্টেম্বর ২০২৫: গত রবিবার আমাদের এলাকার যুব সংঘের উদ্যোগে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টা থেকেই রক্তদাতাদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। শিবিরে মোট ১২০ জন রক্তদান করেন, যার মধ্যে ৩০ জন প্রথমবারের রক্তদাতা। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সুশৃঙ্খলভাবে রক্ত সংগ্রহ করেন এবং প্রতিটি দাতাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।
রক্ত সংগ্রহের পর তা নিকটবর্তী জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়, যা থেকে ইতিমধ্যেই কয়েকজন গুরুতর রোগী উপকৃত হয়েছেন। শিবির শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে রক্তদাতাদের সম্মাননা দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে এই কর্মসূচি আয়োজনের আশ্বাস দেওয়া হয়। এলাকার মানুষ এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এবং রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে পড়েছে।
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো:
১১.১ বিজ্ঞানের ভালো-মন্দ।
উত্তর:
বিজ্ঞানের ভালো-মন্দ
বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানযুগ বলা হয়। মানবসভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব স্পষ্ট। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে যেমন সহজ, আরামদায়ক ও উন্নত করেছে, তেমনি এর অপব্যবহারে মানবজীবন বিপদের মুখেও পড়েছে। তাই বিজ্ঞানের ভালো-মন্দ—উভয় দিকই আমাদের সামনে বিদ্যমান।
প্রথমে বিজ্ঞানের ভালো দিকের কথা বলা যাক। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে মানুষ আজ অনেক মারণরোগের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। অস্ত্রোপচার, ভ্যাকসিন, অ্যান্টিবায়োটিক—সবই বিজ্ঞানের দান। যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিজ্ঞান এনেছে বিপ্লব—টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয়। পরিবহন ব্যবস্থায় ট্রেন, বিমান, মোটরগাড়ি মানুষের যাত্রা দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করেছে। বিদ্যুৎ, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, কম্পিউটার ইত্যাদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরামদায়ক করেছে। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য।
তবে বিজ্ঞানের মন্দ দিকও কম নয়। বিজ্ঞান মানুষের হাতে দিয়েছে ভয়ঙ্কর অস্ত্র—আণবিক বোমা, মিসাইল, রাসায়নিক অস্ত্র ইত্যাদি, যা মুহূর্তে লাখো প্রাণ ধ্বংস করতে পারে। যন্ত্রনির্ভর জীবনে মানুষের শারীরিক শ্রম কমে গিয়ে অলসতা ও নানা রোগের জন্ম দিচ্ছে। শিল্পকারখানার ধোঁয়া ও গাড়ির কালো ধোঁয়া পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়াচ্ছে। ইন্টারনেটের অপব্যবহার কিশোরদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এবং ব্যক্তিগত তথ্য চুরির মতো অপরাধ বাড়াচ্ছে।
সবশেষে বলা যায়, বিজ্ঞান একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যার ভালো-মন্দ—দুটোই মানুষের ব্যবহার নির্ভর। সঠিক ও কল্যাণকর কাজে বিজ্ঞান মানবসভ্যতাকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে, আবার অপব্যবহারে তা ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। তাই আমাদের উচিত বিজ্ঞানের সুফলকে কাজে লাগিয়ে মঙ্গলময় সমাজ গঠন করা।
১১.২ একটি পথের আত্মকথা।
উত্তর:
একটি পথের আত্মকথা
আমি এক নির্জন গ্রামের ধূলোমাখা পথ। কত শত বছর ধরে এই গ্রামে মানুষের যাতায়াতের সাক্ষী হয়ে আছি। আমার জন্ম হয়েছিল বহু আগে, যখন গাছপালার ফাঁকে একটি সরু রেখার মতো আমাকে তৈরি করেছিল গ্রামের মানুষ। প্রথমে আমি ছিলাম কাঁচা মাটির, বর্ষায় কাদা আর শীতে ধুলোয় ভরা। তবুও আমি ছিলাম গ্রামবাসীর একমাত্র ভরসা।
ভোরবেলা কৃষকরা লাঙল কাঁধে নিয়ে আমার উপর দিয়ে মাঠে যেতেন। গরুর গাড়ির চাকার শব্দ, শিশুদের হাসি, মেয়েদের কলসি হাতে কূপের দিকে যাওয়া—সব কিছু আমার বুকের উপর দিয়েই ঘটত। উৎসবের দিনে আমি হয়ে উঠতাম আনন্দের মেলা। শোভাযাত্রা, ঢাকের শব্দ, গ্রাম্য নাটকের দল—সবই আমার বুকের উপর দিয়ে চলত।
তবে আমার জীবন সবসময় আনন্দে ভরা ছিল না। বর্ষার সময় আমি কাদা হয়ে যেতাম, কেউ আমাকে ব্যবহার করতে চাইত না। অনেকেই আমার পাশ কাটিয়ে শুকনো জমি ধরে চলত। তবুও আমি অভিমান করিনি, কারণ জানতাম—শুকনো মৌসুম এলে আবার সবাই আমার উপর ভরসা করবে।
সময়ের সাথে সাথে আমার চেহারা বদলাতে শুরু করল। আমাকে ইট-বিছানো, পরে পিচঢালা রাস্তায় পরিণত করা হল। এখন আমি শুধু গ্রামের নয়, শহরের সঙ্গেও মানুষকে যুক্ত করছি। সাইকেল, মোটরসাইকেল, বাস, ট্রাক—সবাই আমার উপর দিয়ে ছুটে যায়। আমি গর্ব অনুভব করি, কারণ আমি উন্নতির পথে সেতুবন্ধন হয়েছি।
তবুও মাঝে মাঝে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। সেই সরল গ্রামজীবন, গরুর গাড়ির টুংটাং শব্দ, শিশুরা আমার ধুলোর উপর খেলত—এসব দৃশ্য আর দেখা যায় না। এখন আমি ব্যস্ত, দ্রুতগামী যানবাহনের শব্দে ভরা।
আমার ইচ্ছা, আমি যেন যুগের পর যুগ এভাবেই মানুষের সেবা করতে পারি। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় আমি মানুষের চলার পথ হয়েই থাকব। আমি জানি, যতদিন মানুষ চলবে, ততদিন পথেরও প্রয়োজন থাকবে—আর আমি তখনও এই পৃথিবীতে মানুষের বন্ধু হয়ে বেঁচে থাকব।
১১.৩ বাংলার কুটির শিল্প।
উত্তর:
বাংলার কুটির শিল্প
বাংলার কুটির শিল্প আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম গর্ব। শত শত বছর ধরে বাংলার গ্রামীণ সমাজে এই শিল্পের বিকাশ ঘটেছে এবং আজও তা গ্রামীণ অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে রয়ে গেছে।
অর্থ ও তাৎপর্য:
‘কুটির শিল্প’ বলতে বোঝায় ছোট পরিসরে, পরিবারের সদস্যদের শ্রম ও দক্ষতায় গৃহভিত্তিকভাবে উৎপন্ন শিল্পকর্ম। এখানে বড় যন্ত্রপাতির ব্যবহার কম, মূলত হাতের কাজের ওপর নির্ভরশীল। বাংলার গ্রামীণ মানুষ তাদের অবসর সময়ে বা কৃষিকাজের ফাঁকে এই শিল্পে নিযুক্ত হয়, ফলে তা পারিবারিক আয়ের এক বড় উৎস হয়ে ওঠে।
বাংলার কুটির শিল্পের ধরন:
বাংলায় বহুবিধ কুটির শিল্প দেখা যায়। যেমন—তাঁতশিল্প, মাটির কাজ, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, পাটের জিনিসপত্র, শোলা শিল্প, নকশিকাঁথা, কাঠখোদাই, ধাতুর কাজ, পিতল-পিতলের বাসন, শাঁখ শিল্প ইত্যাদি। নদীমাতৃক বাংলায় মাটির কাজের বিশেষ প্রচলন রয়েছে; মৃৎশিল্পীরা অসাধারণ কারুকার্যময় হাঁড়ি, কলস, প্রদীপ ইত্যাদি তৈরি করে থাকেন। আবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, মুর্শিদাবাদের শোলা শিল্প, কুষ্টিয়ার নকশিকাঁথা বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছে।
অর্থনৈতিক ভূমিকা:
বাংলার কুটির শিল্প বহু মানুষের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। কৃষির পাশাপাশি এই শিল্প গ্রামীণ মানুষের জন্য বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে নারীরা ঘরে বসেই বোনা, সেলাই, কাঁথা সেলাই, শোলা কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন। ফলে এটি স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রাখে।
সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ:
তবুও কুটির শিল্প নানা সমস্যার সম্মুখীন। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর কারখানার প্রতিযোগিতা, বাজারে বিক্রির সুযোগের অভাব, পর্যাপ্ত সরকারি সহায়তার অভাব ইত্যাদি কারণে অনেক শিল্পী তাদের পেশা ত্যাগ করছেন।
উন্নয়নের উপায়:
কুটির শিল্প রক্ষায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। সহজ ঋণ, প্রশিক্ষণ, আধুনিক বিপণন পদ্ধতি, দেশি-বিদেশি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ, অনলাইন বিক্রির ব্যবস্থা—এসব কুটির শিল্পকে নতুন প্রাণ দিতে পারে।
উপসংহার:
বাংলার কুটির শিল্প কেবল অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও এক অমূল্য সম্পদ। প্রয়োজন সঠিক সহায়তা ও আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাহলেই বাংলার কুটির শিল্প বিশ্ববাজারে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করবে।
১১.৪ চন্দ্রযান অভিযান ২০২৩
উত্তর:
চন্দ্রযান অভিযান ২০২৩
২০২৩ সালের ২৩শে আগস্ট ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করে। ‘চন্দ্রযান-৩’ সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে, যা বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো দেশ এই অঞ্চলে পৌঁছাল। এই সাফল্য ভারতের মহাকাশ অভিযানের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে স্থান পেয়েছে।
উদ্দেশ্য ও প্রস্তুতি:
চন্দ্রযান-৩ মিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চাঁদের দক্ষিণ মেরুর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও উপাদান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, সেখানে বরফের উপস্থিতি খুঁজে বের করা এবং ভবিষ্যতের মহাকাশ গবেষণার পথ সুগম করা। ২০১৯ সালের চন্দ্রযান-২ আংশিক ব্যর্থ হলেও সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসরো আরও উন্নত প্রযুক্তি ও নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে চন্দ্রযান-৩ তৈরি করে।
গঠন ও যাত্রাপথ:
চন্দ্রযান-৩–এর দুটি প্রধান অংশ ছিল—ল্যান্ডার ‘বিক্রম’ এবং রোভার ‘প্রজ্ঞান’। ১৪ই জুলাই ২০২৩, শ্রীহরিকোটা থেকে জি.এস.এল.ভি.-এম.কে-৩ রকেটের মাধ্যমে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এক মাসের বেশি সময় ধরে মহাকাশে ভ্রমণ শেষে ল্যান্ডারটি নির্দিষ্ট গতিপথে চাঁদের মাটিতে নরম অবতরণ করে।
সাফল্যের তাৎপর্য:
এই সাফল্যের মাধ্যমে ভারত বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদে অবতরণ করে—রাশিয়া, আমেরিকা ও চীনের পরেই। তবে দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের ক্ষেত্রে ভারত প্রথম। এর ফলে মহাকাশ প্রযুক্তিতে ভারতের মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
বৈজ্ঞানিক অর্জন:
চন্দ্রযান-৩ চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছবি ও তথ্য পাঠায়। ‘প্রজ্ঞান’ রোভার মাটির উপাদান বিশ্লেষণ করে সেখানকার খনিজ, তাপমাত্রা ও গঠন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে। বরফের সম্ভাব্য উপস্থিতি ভবিষ্যতের মানব মহাকাশ অভিযানে জ্বালানি ও পানির উৎস হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হতে পারে।
সমাপ্তি:
চন্দ্রযান অভিযান ২০২৩ শুধু একটি বৈজ্ঞানিক সাফল্য নয়, এটি সমগ্র ভারতবাসীর গর্ব ও অনুপ্রেরণার উৎস। এই সাফল্য প্রমাণ করে, দৃঢ় সংকল্প, ধৈর্য এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনশক্তি থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। চন্দ্রযান-৩ ভারতের মহাকাশ অভিযানের স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।