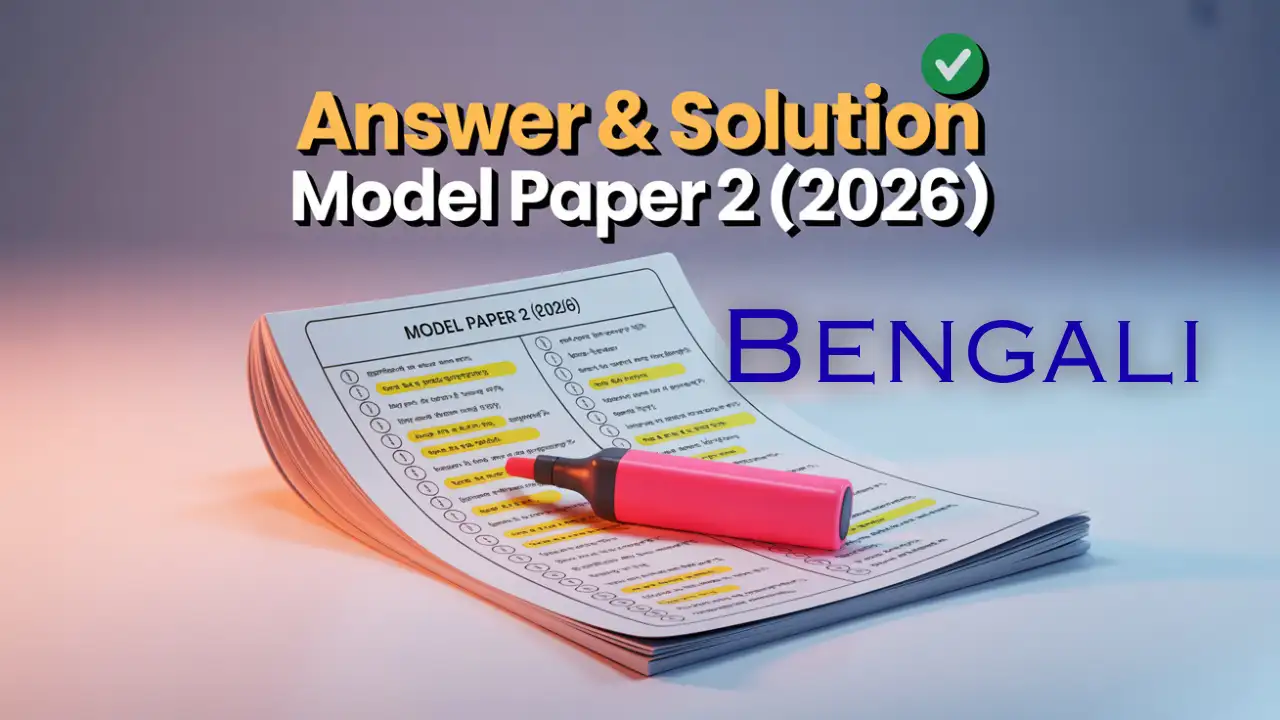আপনি কি ২০২৬ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 2 এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 2-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৫ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ ‘দয়ার সাগর! পরকে সেজে দি, নিজে খাইনে।’ বস্তা হলেন
(ক) জগদীশবাবু
(খ) নিমাইবাবু
(গ) অপূর্ব
(ঘ) গিরীশ মহাপাত্র
উত্তর: (ক) জগদীশবাবু
১.২ ইসাবের পকেট কতটা ছিড়েছিল?
(ক) দু’ইঞ্চি
(খ) ছ’ইঞ্চি
(গ) চার ইঞ্চি
(ঘ) পাঁচ ইঞ্চি
উত্তর: (খ) ছ’ইঞ্চি
১.৩ নদেরচাঁদ পেশায় ছিলেন একজন
(ক) স্কুলমাস্টার
(খ) স্টেশনমাস্টার
(গ) পোস্টমাস্টার
(ঘ) গানের মাস্টার
উত্তর: (খ) স্টেশনমাস্টার
১.৪ “সে জানত না” উদ্ধৃতাংশে ‘সে’ বলতে বোঝানো হয়েছে-
(ক) গির্জার এক সন্ন্যাসিনীকে
(খ) একটি শিশুকে
(গ) একজন সাধারণ নারীকে
(ঘ) ঈশ্বরকে
উত্তর: (গ) একজন সাধারণ নারীকে
১.৫ ‘জরায় মরা’ মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো আছে
(ক) ত্রস্ত জটায়
(খ) মহানিশায়
(গ) কালবৈশাখী ঝড়ে
(ঘ) প্রলয়ের বিনাশে
উত্তর: (ঘ) প্রলয়ের বিনাশে
১.৬ ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতাটি কবির কোন্ মূল কাব্যের অন্তর্গত?
(ক) ‘ভুতুমভগবান’
(খ) ‘ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?’
(গ) ‘পাগলী তোমার সঙ্গে’
(ঘ) ‘পাতার পোষাক’
উত্তর: (ঘ) ‘পাতার পোষাক’
১.৭ সিজার যে কলমটি দিয়ে কাসকাকে আঘাত করেছিলেন, তার পোশাকি নাম-
(ক) রিজার্ভার
(খ) স্টাইলাস
(গ) পার্কার
(ঘ) পাইলট
উত্তর: (খ) স্টাইলাস
১.৮ “হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড” উক্তিটি-
(ক) রবীন্দ্রনাথের
(খ) বঙ্কিমচন্দ্রের
(গ) কালিদাসের
(ঘ) বিদ্যাসাগরের
উত্তর: (গ) কালিদাসের
১.৯ ছোটোবেলায় রাজশেখর বসুকে যাঁর বাংলা জ্যামিতি বই পড়তে হয়েছে, তিনি হলেন-
(ক) রামমোহন রায়
(খ) ব্রজমোহন মল্লিক
(গ) কেশবচন্দ্র নাগ
(ঘ) ব্রহ্মমোহন মল্লিক
উত্তর: (ঘ) ব্রহ্মমোহন মল্লিক
১.১০ ‘কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল!’ নিম্নরেখ পদটি-
(ক) সম্বোধন পদ
(খ) কর্তৃকারক
(গ) সম্বন্ধপদ
(ঘ) নিমিত্ত কারক
উত্তর: (গ) সম্বন্ধপদ
১.১১ অনুসর্গপ্রধান কারক হল-
(ক) কর্তৃকারক
(খ) কর্মকারক
(গ) করণ কারক
(ঘ) অধিকরণ কারক
উত্তর: (গ) করণ কারক
১.১২ যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না
(ক) নিত্যসমাস
(খ) দ্বিগু সমাস
(গ) দ্বন্দু সমাস
(ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস
উত্তর: (ক) নিত্যসমাস
১.১৩ বুড়োমানুষের কথাটা শুনো। নিম্নরেখাঙ্কিত পদটি যে সমাসের উদাহরণ সেটি হল-
(ক) বহুব্রীহি সমাস
(খ) কর্মধারয় সমাস
(গ) তৎপুরুষ সমাস
(ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস
উত্তর: (খ) কর্মধারয় সমাস
১.১৪ যৌগিক বাক্যে দুটি স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয়
(ক) সংযোজক অব্যয় দ্বারা
(খ) সংকোচক অব্যয় দ্বারা
(গ) বিয়োজক অব্যয় দ্বারা
(ঘ) কোনোটিই নয়
উত্তর: (ক) সংযোজক অব্যয় দ্বারা
১.১৫ ‘তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে’ এটি কোন বাক্যের উদাহরণ?-
(ক) আবেগসূচক
(খ) প্রার্থনাবাচক
(গ) শর্তসাপেক্ষ
(ঘ) সন্দেহবাচক
উত্তর: (ঘ) সন্দেহবাচক
১.১৬ “পাঁচদিন নদীকে দেখা হয় নাই।” এটি কোন্ বাচ্যের উদাহরণ?-
(ক) কর্তৃবাচ্য
(খ) ভাববাচ্য
(গ) কর্মবাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (গ) কর্মবাচ্য
১.১৭ বাচ্যান্তর ঘটে না
(ক) কর্মবাচ্যের
(খ) কর্মকর্তৃবাচ্যের
(গ) কর্তৃবাচ্যের
(ঘ) ভাববাচ্যের
উত্তর: (খ) কর্মকর্তৃবাচ্যের
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ “শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন,” সংকল্পটি কী?
উত্তর: যদি কখনো লেখা ছাপতে দেয় তো, তপন নিজে গিয়ে দেবে। নিজের কাঁচা লেখা। ছাপা হয় হোক, না হয় না হোক। তপনকে যেন আর কখনো শুনতে না হয় ‘অমুক তপনের লেখা ছাপিয়ে দিয়েছে।’ আর তপনকে যেন নিজের গল্প পড়তে বসে অন্যের লেখা লাইন পড়তে না হয়।
২.১.২ “অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।” কী শুনে তিনি চুপ করে ছিলেন?
উত্তর: জগদীশবাবু সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য কৌশলে কাঠের খড়মে সোনার বোল লাগিয়ে ধরেছিলেন। তখন বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসী পা বাড়িয়ে দিলেন, আর জগদীশবাবু সেই সুযোগে পায়ের ধুলো নিলেন। এমনকি বিদায় দেওয়ার সময়ও তিনি সন্ন্যাসীর ঝোলার মধ্যে জোর করে একশো টাকার নোট রেখে দেন। এই অদ্ভুত কাহিনি শুনে হরিদা বিস্মিত ও ভাবুক হয়ে যান। তাই তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।
২.১.৩ “এ-সব কথা বলার দুঃখ আছে।” কোন্ কথা বলায় দুঃখ আছে বলে বক্তার ধারণা?
উত্তর: উদ্ধৃতিটির বক্তা হলেন অপূর্বর সহকর্মী তলওয়ারকার। তাঁর মতে, দুঃখের বিষয় এই যে, ইংরেজ পুলিশ অফিসার নিমাইবাবু যদিও অপূর্বর আত্মীয়, তবুও স্বাধীনতা সংগ্রামী সব্যসাচী অপূর্বর কাছে বেশি আপনজন। আত্মীয়তার চেয়ে দেশপ্রেমের বন্ধন যে অনেক গভীর ও শক্তিশালী—এই সত্য প্রকাশ করাকেই বক্তা দুঃখজনক বলে মনে করেছেন।
২.১.৪ ‘অদল বদল’ গল্পটি কে বাংলায় তরজমা করেছেন?
উত্তর: অদল বদল’ গল্পটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত
২.১.৫ ‘নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইয়া গেল।’ নদেরচাঁদ কেন স্তম্ভিত হয়ে গেল?
উত্তর: টানা পাঁচ দিনের বৃষ্টিতে নদীর জলে প্রবল স্রোত ও ভয়ঙ্কর রূপ দেখা দিয়েছিল। নদীর সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ “শিশু আর বাড়িরা খুন হলো।” ‘শিশু আর বাড়িরা’ খুন হয়েছিল কেন?
উত্তর: রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড়ের মতো’ যুদ্ধের করাল থাবার আঘাতে ‘শিশুরা আর বাড়িরা’ খুন হয়েছিল ।
২.২.২ ‘ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে।’কী ছড়ানো রয়েছে?
উত্তর: ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে শিশুদের শব
২.২.৩ “পশুরা বেরিয়ে এল-“পশুরা বেরিয়ে এসে কী করেছিল?
উত্তর: গুপ্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে পশুরা ভয়ঙ্কর ও অশুভ ধ্বনিতে দিনের অন্তিমকাল ঘোষণা করল।
২.২.৪ ‘অনুমান করে নিজ চিতে।’ কে, কী অনুমান করেছিলেন?
উত্তর: আলোচ্য উক্তিটি সৈয়দ আলাওল রচিত সিন্ধুতীরে কাব্যাংশে সমুদ্রকন্যা পদ্মার অনুমানের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। সমুদ্রদুর্যোগে ভেলায় ভেসে অচেতন অবস্থায় রানী পদ্মাবতী ও তার সখীরা পদ্মার দ্বীপে এসে পৌঁছান। ভেলায় অচেতন পদ্মাবতীর অতুলনীয় সৌন্দর্য দেখে পদ্মা মনে করেন, তিনি কোনো স্বর্গকন্যা বা অপ্সরা, যিনি দেবতার অভিশাপে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাই ‘অনুমান করে নিজ চিতে’ পদ্মার এই কল্পনারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
২.২.৫ ‘গান দাঁড়াল ঋষিবালক’ একথা বলার উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: গান দাঁড়াল ঋষিবালক” এই কথাটির উদ্দেশ্য হলো গান বা সুরের গভীরতা ও পবিত্রতা বোঝানো।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ “সমানি সম শীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।” কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: শ্রীপান্থ রচিত ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ রচনায় ব্যবহৃত “সমানি সম শীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।” কথাটির অর্থ হলো—“সব অক্ষর সমান, প্রতিটি ছত্র সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন।” এখানে লেখার সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।
২.৩.২ “কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য।”- কলম কাদের কাছে এবং কেন অস্পৃশ্য?
উত্তর: শ্রীপান্থের ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে বলা হয়েছে, আজকাল পকেটমারের কাছেও কলম অস্পৃশ্য।
কারণ– এক সময় কলম ছিল দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান, তাই চুরি করার মতো বস্তু ছিল। কিন্তু বর্তমানে কলম এতই সস্তা ও সর্বজনের হাতে পৌঁছে গেছে যে, তার আর কোনো বিশেষ দাম বা গুরুত্ব নেই। এই জন্যই পকেটমারেরাও কলমকে আর চুরি করার মতো জিনিস মনে করে না।
২.৩.৩ “বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে আর একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে।” কী দোষ নজরে পড়ে?
উত্তর: রাজশেখর বসুর ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধের উল্লিখিত অংশে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের মতে, অনেক সময় অল্পবিদ্যার কারণে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ভুল-ত্রুটি দেখা দেয়। অর্থাৎ, পর্যাপ্ত জ্ঞান ও সঠিক তথ্যের অভাবে প্রবন্ধকাররা যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক বিষয় উপস্থাপন করতে পারেন না। তাই তিনি সতর্ক করেছেন যে, বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালিখি করতে হলে গভীর জ্ঞান ও নির্ভুল তথ্যের প্রয়োজন।
২.৩.৪ “এতে রচনা উৎকট হয়।” রচনা ‘উৎকট’ হয় কীসে?
উত্তর: রাজশেখর বসুর মতে, লেখক যদি ইংরেজিতে নিজের বক্তব্য ভেবে সেটিকে যথাযথভাবে বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেন, তবে রচনা উৎকট হয়ে ওঠে। কারণ, এতে বাংলার স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশ ব্যাহত হয় এবং ভাষার স্বকীয় সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই বাংলায় লেখার সময় ইংরেজির অনুসরণ না করে সরল, স্বাভাবিক ও মৌলিক বাংলা ভাষার ব্যবহার করা উচিত।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ তির্যক বিভক্তি কাকে বলে?
উত্তর: যে বিভক্তি দ্বারা কোনো শব্দ বাক্যে কর্তা বা কর্ম ছাড়া অন্যান্য সম্পর্ক নির্দেশ করে, তাকে তির্যক বিভক্তি বলে।
২.৪.২ এই কথাটি সকল লেখকের মনে রাখা উচিত। চিহ্নিত পদটির কারক ও বিভক্তি লেখো।
উত্তর: চিহ্নিত পদ– লেখকের। “লেখকের” হলো সম্বন্ধ কারকে -এর বিভক্তিযুক্ত পদ
২.৪.৩ ‘বহুরূপী’ শব্দটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম করো।
উত্তর: ‘বহুরূপী’ শব্দটি একটি সমাস।
ব্যাসবাক্য : অনেক রূপ আছে যে – বহুরূপী
২.৪.৪ উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের একটি পার্থক্য লেখো।
উত্তর: পার্থক্য (উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাস):
উপমান কর্মধারয় সমাসে সমাসপদে উপমান অর্থে ব্যবহৃত হয়।
যেমন: সিংহনাদ (সিংহের ন্যায় নাদ) → এখানে সিংহ হলো উপমান।
উপমিত কর্মধারয় সমাসে সমাসপদে উপমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।
যেমন: চন্দ্রমুখী (চাঁদের মতো মুখ) → এখানে মুখ হলো উপমিত।
২.৪.৫ নির্দেশ অনুযায়ী বাকাটি পরিবর্তন করো — বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না। (যৌগিক বাক্যে)
উত্তর: “আশা বৃথা হলেও মরে না, আর মানুষ মরিতে মরিতেও আশা মরে না।”
২.৪.৬ ‘সে নিজের চোখে শুনেছে।’ এক্ষেত্রে বাক্য গঠনের কোন শর্তটি লঙ্ঘিত হয়েছে?
উত্তর: এখানে বাক্য গঠনের শর্ত ‘যথাযথ শব্দ-প্রয়োগ ও যুক্তি-সংগত অর্থবোধকতা’ লঙ্ঘিত হয়েছে।
২.৪.৭ শর্তসাপেক্ষ বাক্যের আর এক নাম কী?
উত্তর: শর্তসাপেক্ষ বাক্যের আর এক নাম হলো “যদি-বাক্য”
যদি পড়, তবে ভাল ফল করবে।
২.৪.৮ ঘটিত কর্তৃবাচ্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: বাক্যে কর্তার নিজের দ্বারা কাজ না হয়ে অন্যের দ্বারা বা কোনো মাধ্যমের দ্বারা কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে ঘটিত কর্তৃবাচ্য বলে।
উদাহরণ: আমি তাকে দিয়ে কাজটি করালাম।
২.৪.৯ ‘তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।’ ভাববাচ্যে পরিবর্তন করো।
উত্তর: মূল বাক্য : তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না। (কর্তৃবাচ্য)
ভাববাচ্যে হবে : স্বপ্ন আর তাদের দ্বারা দেখা গেল না।
২.৪.১০ কোন্ বাচ্যে অনুসর্গযুক্ত কর্তা বসে?
উত্তর: অনুসর্গযুক্ত কর্তা ভাববাচ্যে বসে।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ “যাঁকে খুঁজছেন তাঁর কালচরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।” ‘কালচর’ বলতে কী বোঝো? কালচরের কথা ভাবতে বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: যিনি যাঁকে খুঁজছিলেন – বাঙালি পুলিশ অফিসার নিমাইবাবু রাজবিদ্রোহী সব্যসাচী মল্লিককে খুঁজছিলেন।
কালচারের কথা ভেবে দেখতে বলার কারণ – গিরীশ মহাপাত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চেহারা ছিল খুবই হাস্যকর। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, সংসারে তাঁর মেয়াদ আর বেশি দিন নেই। একজন ডাক্তারি পড়া, উচ্চশিক্ষিত রাজবিদ্রোহী কখনও এত ক্ষীণদেহী এবং রোগগ্রস্ত হতে পারেন না। তাঁর পোশাকেও রুচির ছাপ থাকা উচিত। এই প্রসঙ্গেই গিরীশ মহাপাত্র ও সব্যসাচী মল্লিকের কালচারের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৩.১.২ “এই ভীষণ মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ, অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।’ কোন্ শব্দ? তা কেন ভীষণ এবং মধুর?
উত্তর: উদ্ধৃত অংশে যে শব্দের কথা বলা হয়েছে, তা হলো প্রবল বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে নদীর উত্তাল জলরাশির গর্জনের মিলিত ধ্বনি। এই ধ্বনি নদেরচাঁদের কানে এসে তাকে এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলে।
শব্দটি ভীষণ, কারণ নদীর উন্মত্ত ঢেউ আর আকাশভাঙা বৃষ্টির সম্মিলিত শব্দে প্রকৃতির এক ভয়ংকর রূপ প্রতিভাত হয়। জলতরঙ্গের প্রচণ্ড চাপা গর্জন নদেরচাঁদের মনে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। আবার শব্দটি মধুর, কারণ এই প্রবল গর্জন ও প্রপাতধ্বনি একত্রে মিলিত হয়ে প্রকৃতির এক অপূর্ব সঙ্গীত রচনা করে, যা নদেরচাঁদকে আমোদিত ও মুগ্ধ করে।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো পায়ে” ‘অস্ত্র’ কীসের প্রতীক? কবি অস্ত্র রাখতে বলেছেন কেন?
উত্তর: জয় গোস্বামী রচিত ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় ‘অস্ত্র’ হিংসা ও ধ্বংসের প্রতীক। যুদ্ধবাজ মানুষ ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে অস্ত্র হাতে নেয় এবং পৃথিবীকে রক্তাক্ত করে তোলে। কবির মতে, মানুষের সভ্যতায় অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ অস্ত্র দিয়ে মানবসমাজ টিকে থাকতে পারে না। তাই কবি আহ্বান জানিয়েছেন—অস্ত্রকে পরিত্যাগ করে গানের পায়ের নিচে রাখতে। অর্থাৎ, গানকেই জীবনযুদ্ধের সত্যিকার হাতিয়ার করে মানবতাকে জয়ী করতে হবে। এভাবেই কবির মানবদরদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।
৩.২.২ “বিস্মিত হইল বালা”- ‘বালা’ কে? তার বিস্ময়ের কারণ কী?
উত্তর: উল্লিখিত অংশে ‘বালা’ বলতে সমুদ্রনৃপতির কন্যা পদ্মাকে বোঝানো হয়েছে।
কবি সৈয়দ আলাওল রচিত সিন্ধুতীরে কবিতায় বর্ণিত আছে— একদিন সকালে পদ্মা তাঁর সখীদের সঙ্গে উদ্যানে ভ্রমণে বেরিয়ে সমুদ্রতীরে একটি ভেলা দেখতে পান। কৌতূহলবশত এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখেন, চার সখীর মাঝখানে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে, আর সকল সখীও সংজ্ঞাহীন। কন্যাটির রূপ স্বর্গের অপ্সরা রম্ভাকেও হার মানায়। এই দৃশ্য দেখে পদ্মা বিস্মিত হয়েছিলেন।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ “তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের।” কার সম্পর্কে এই উক্তি? কেন এই উক্তি করা হয়েছে?
উত্তর: আশাপূর্ণা দেবী রচিত ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পের নায়ক তপন সম্পর্কে এই উক্তি। কিশোর তপন যার লেখালিখির প্রতি গভীর আগ্রহ। মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সে জানতে পারে, তার মেসো একজন লেখক এবং তাঁর লেখা পত্রিকায় ছাপা হয়। উৎসাহিত হয়ে তপন নিজের লেখা গল্প মেসোর হাতে দেয় ছাপানোর জন্য।
মেসো গল্পটি পড়ে বলেন, সুন্দর হয়েছে, তবে কিছু “কারেকশন” করলে ছাপতে দেওয়া চলে। পরে ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হলে বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায় । সকলেই একবার করে চোখ বোলায় আর বলে, ‘বারে, চমৎকার লিখেছে তো।’
মেসো অবশ্য মৃদু মৃদু হাসেন, বলেন, ‘একট-আধটু ‘কারেকশান’ করতে হয়েছে অবশ্য। কিন্তু তপন বই হাতে নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখে—প্রত্যেকটি লাইন তো নতুন, আগা-গোরা তপনের অপরিচিত। মেসো তপনের গল্পটিকে আগাগোড়াই কারেকশান করেছেন। অর্থাৎ নতুন করে লিখেছেন, নিজের পাকা হাতে কলমে। তপন আর পড়তে পারে না।
তপন বইটা ফেলে রেখে চলে যায়, তপন ছাদে উঠে গিয়ে শার্টের তলাটা তুলে চোখ মোছে।
তপনের কাছে এটি আনন্দ নয়, বরং গভীর আঘাতের। নিজের সৃষ্টিকে এভাবে বদলে দেওয়া তাকে অপমানিত ও দুঃখিত করে তোলে। তপনের মনে হয় আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন।
৪.২ ” এই শহরের জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করেন বহুরূপী হরিদা।” ‘বহুরূপী’ গল্প অনুসরণে সেই চমৎকার ঘটনাগুলির পরিচয় দাও।
উত্তর: সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদা তাঁর অভিনব বেশভূষা ও বৈচিত্র্যময় আচরণের মাধ্যমে শহরের জীবনে মাঝে মাঝেই চমৎকার সব ঘটনা সৃষ্টি করতেন। তাঁর জীবন ছিল এক নাট্যশালার মতো, সেখানে এক নতুন চরিত্রে আবির্ভাব হতো।
হরিদা সপ্তাহে বড়জোর একদিন বহুরূপী সেজে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করতেন। অধিকাংশ দিন না খেয়েও তিনি একঘেয়ে পেশা গ্রহণ না করে বেছে নিয়েছিলেন রঙিন, নাটকীয় জীবনের পথ। তাঁর সৃষ্ট কিছু উল্লেখযোগ্য চমৎকার ঘটনার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:
১. পাগলের সাজে আতঙ্ক সৃষ্টি: একদিন দুপুরে হরিদা উন্মাদ পাগলের বেশে চকের বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে মুখে লালা ছিটিয়ে, হাতে ইট তুলে যাত্রীদের দিকে তেড়ে গিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন।
২. বাইজির সাজে রাজপথে আগমন: এক সন্ধ্যায় ঠোঁটে রঙ, পায়ে ঘুঙুর পরে বাইজির সাজে নেমে নৃত্যভঙ্গিতে শহরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
৩. নকল পুলিশ হয়ে শাস্তি প্রদান: একবার পুলিশ সেজে চারজন স্কুলছাত্রকে লিচু চুরির অপরাধে আটক করেন এবং পরে এক শিক্ষক ঘুষ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনেন।
৪. সন্ন্যাসীর বেশে দার্শনিক উপদেশ: হরিদা একদিন সন্ন্যাসীর সাজে জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ধর্ম ও জীবনের বিষয়ে গভীর দার্শনিক উপদেশ দেন।
৫. বিভিন্ন রূপে আবির্ভাব: কখনও কাপালিক, কখনও কাবুলিওয়ালা, কখনও ফিরিঙ্গি সাহেব, আবার কখনও বাউলের রূপ ধারণ করে পথচলতি মানুষকে চমকে দিতেন।
এইসব বিচিত্র রূপসজ্জা ও অভিনয়ের মাধ্যমে হরিদা নিছক রুজির জন্য নয়, বরং শিল্পের প্রতি ভালোবাসা ও জীবনকে আনন্দময় করে তোলার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ ‘তারপর যুদ্ধ এল’ যুদ্ধ কীসের প্রতীক? যুদ্ধের পরিণতি কী হয়েছিল, তা ‘অসুখী একজন’ কবিতা অনুসারে লেখো।
উত্তর: চিলির কবি পাবলো নেরুদা তাঁর ‘অসুখী একজন’ কবিতায় যুদ্ধকে ধ্বংস ও নৃশংসতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। কবির অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যুদ্ধ মানুষের সুখ–শান্তি কেড়ে নিয়ে আসে, সংসারের সৌন্দর্য ও জীবনের মাধুর্যকে ধ্বংস করে দেয়। কবিতায় প্রিয়তমাকে অপেক্ষায় রেখে কবি দূরে চলে যাওয়ার পর একদিন হঠাৎ আগ্নেয়গিরির পাহাড়ের মতো নেমে আসে ভয়াবহ যুদ্ধ। এর পরিণতি ছিল ভয়ংকর—মানুষ আশ্রয়হীন হয়, নিষ্পাপ শিশুরাও নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পায় না। দাবানলের মতো যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ে, দেবালয় ভস্মীভূত হয়, দেবতারাও তাদের দেবত্ব হারায়। কবির সংসারের প্রতীকী চিহ্ন—ঝুলন্ত বিছানা, গোলাপি গাছ, প্রাচীন জলতরঙ্গ—সব ধ্বংস হয় যুদ্ধের আগুনে। পুরো শহর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়; চারদিকে ছড়িয়ে থাকে কাঠকয়লা, দোমড়ানো লোহা, ভাঙা মূর্তির মাথা আর রক্তের দাগ। তবে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও অটুট থাকে এক নারীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও অবিচল ভালোবাসা, যা যুদ্ধের নৃশংসতার বিপরীতে জীবনের আশার প্রতীক হয়ে ওঠে।
৫.২ “বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর!”- এখানে কাকে, কেন ভয়ংকর বলা হয়েছে? ভয়ংকর কীভাবে আসছে?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় “বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর!” বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন নবযুগের বার্তাবহ প্রলয়রূপী বিপ্লব বা বিদ্রোহকে।
এই ‘ভয়ংকর’ ধ্বংসের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির পথ খুলে দেয়। কবি এখানে রুদ্ররূপী শিবকে সেই প্রলয় ও সৃষ্টির প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের কঠোর অত্যাচারে ভারতবাসী ছিল স্থবির, দুর্বল ও চিন্তাহীন। সমাজে ছিল কুসংস্কার, আত্মবিস্মৃতি এবং অবক্ষয়। কবির বিশ্বাস, সময়ের নিয়মে এই অচল সমাজব্যবস্থা ও দমননীতি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই ধ্বংস আসবে এক ভয়ংকর শক্তি নিয়ে, হাতে বজ্রশিখার মশাল—যা বিদ্রোহের জ্বলন্ত প্রতীক। তার আগমন হবে কালবৈশাখীর মতো প্রলয়ের ঢেউ হয়ে, যা সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের শৃঙ্খল ছিন্ন করবে।
এই ভয়ংকর ধ্বংস পুরাতনকে মুছে দিয়ে গড়ে তুলবে নতুন ও মুক্ত সমাজ, যেখানে থাকবে স্বাধীনতা, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা। এভাবেই কবি ভয়ংকরকে মুক্তির বার্তাবাহক রূপে দেখিয়েছেন।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ “মুঘল দরবারে একদিন তাঁদের কত না খাতির, কত না সম্মান!” কাদের সম্মানের কথা বলা-হয়েছে? প্রবন্ধ অনুসারে তাদের খাতির ও সম্মানের পরিচয় দাও।
উত্তর: শ্রীপান্থ রচিত ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে ‘তাঁদের’ বলতে লিপিকুশলী বা ক্যালিগ্রাফিস্টদের কথা বলা হয়েছে।
তাঁরা ছিলেন ‘ওস্তাদ কলমবাজ’
– সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন ও মুক্তোর মতো অক্ষর লেখার দক্ষতায় অনন্য। যদিও আর্থিক অবস্থা সবসময় ভালো ছিল না—আঠারো শতকে চারখণ্ড রামায়ণ নকল করে কেউ পেতেন মাত্র সাত টাকা, কিছু কাপড় ও মিঠাই—তবুও তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ছিল উঁচুতে। মুঘল দরবারে, বাংলার রাজা-জমিদারদের কাছে এমনকি সাধারণ গৃহস্থদের কাছেও তাঁরা সম্মানিত হতেন এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা পেতেন। তাঁদের তৈরি পুঁথি ছিল শিল্পসম্মত, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। এই সম্মান ও সমাদর থেকেই তাঁদের মধ্যে জন্ম নিত একধরনের আত্মমর্যাদাবোধ। পুঁথি চুরি রোধে তাঁরা সর্বদা সতর্ক থাকতেন। খ্যাতি ও মর্যাদায় তাঁরা প্রায় লেখকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।
৬.২ “বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় এখনও নানা রকম বাধা আছে।” এই বাধা দূর করতে লেখক কী পরামর্শ দিয়েছেন, তা আলোচনা করো।
উত্তর: প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু তাঁর ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে বিজ্ঞানচর্চার নানা বাধা উল্লেখ করে তা দূরীকরণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন।
প্রথমত, যতদিন উপযুক্ত বাংলা পারিভাষিক শব্দ তৈরি না হয়, ততদিন ইংরেজি শব্দ বাংলার বানানে চালানো উচিত। যেমন—অক্সিজেন, ফার্ন, মালভাসি ইত্যাদি।
দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক রচনায় স্পষ্ট, সহজ ও সাবলীল ভাষা ব্যবহার করতে হবে; আক্ষরিক অনুবাদ বা জটিল ভাষা এড়ানো দরকার।
তৃতীয়ত, ইংরেজিতে ভেবে বাংলায় অনুবাদ করলে ভাষা অপ্রাকৃত হয়, তাই সরাসরি বাংলায় ভাবা ও লেখা উচিত।
চতুর্থত, অল্প পরিচিত পরিভাষা প্রথমবার ব্যবহারের সময় তার ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।
পঞ্চমত, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় উপমা বা রূপকের সীমিত ব্যবহার করা গেলেও অন্যান্য অলংকার বর্জন জরুরি।
ষষ্ঠত, ভুল তথ্য পরিবেশন এক বড় সমস্যা; তাই অভিজ্ঞদের দ্বারা যাচাই করিয়ে লেখা প্রকাশ করা দরকার।
অতএব, ভাষার স্বচ্ছতা, যথাযথ পরিভাষার ব্যবহার এবং সত্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপন নিশ্চিত করতে পারলেই বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম হবে।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।
৭.১ “বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয় মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা।” কাদের উদ্দেশ করে একথা বলা হয়েছে? এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বক্তার কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে?
উত্তর: নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত সিরাজদ্দৌলা নাটকে নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর সভায় উপস্থিত রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, উমিচাঁদ প্রমুখ বিশিষ্ট সভ্যদের প্রতি একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেন। উক্তির মাধ্যমে নবাবের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, তা হল—তিনি একজন উদারমনের খাঁটি দেশপ্রেমিক।
নবাব সিরাজদ্দৌলা বুঝেছিলেন, বাংলা কেবল মুসলমানের বা হিন্দুর নয়—বাংলা হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত অবস্থানের মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে। বাংলার উপর ঘনিয়ে আসা দুর্দিন রোধ করতে তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আস্থা রেখেছিলেন।
তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বহিরাগত ইংরেজ শত্রুকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হলে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও ভেদাভেদ পরিহার করে হিন্দু-মুসলমান সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাঁর মতে, ধর্মের নামে বিভেদ মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তা কখনোই বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না।
এই উপলব্ধি থেকেই নবাব সিরাজদ্দৌলা কাতরভাবে সকলের প্রতি উদার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক, উদারচেতা এবং সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক শাসক।
৭.২ ‘আমরা নবাবের নিমক বৃথাই খাই না,’ নিমক খাওয়ার তাৎপর্য কী? উদ্ধৃতিটির প্রসঙ্গ উল্লেখসহ বস্তার মনোভাবের পরিচয় দাও।
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকে উক্তিটি বলেছেন নবাব সিরাজের অনুগত সেনাপতি মীরমদন। নিমক খাওয়া বলতে বোঝায় কারও বেতন বা প্রতিপালন গ্রহণ করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অবিচল আনুগত্য প্রদর্শন করা। মীরমদন নবাবের বেতনভুক সহচর হিসেবে শুধু কর্তব্যপরায়ণই নন, বরং তাঁর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততায় অটল। তিনি সৎ, চরিত্রবান ও দৃঢ়চেতা সৈনিক, যিনি রাজদরবারের দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। নম্র ও ভদ্র হলেও প্রয়োজনে কঠোর হতে দ্বিধা করেননি; যেমন, মীরজাফরের সামনে অকপটে অপ্রিয় সত্য বলা। নবাবের প্রতি দুর্ব্যবহার ও স্পর্ধা দেখে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিবাদে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা, সাহস ও আনুগত্য তাঁকে নবাবের প্রকৃত রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। ষড়যন্ত্রে অংশ না নিয়ে নবাবের সম্মান রক্ষায় দৃঢ় অবস্থানই প্রমাণ করে যে মীরমদন একজন বিশ্বস্ত, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও নির্ভীক যোদ্ধা।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ “এটা বুকের মধ্যে পুষে রাখুক।” কী পুষে রাখার কথা বলা হয়েছে? কী কারণে এই পুষে রাখা?
উত্তর: মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসে ক্ষিতীশ সিংহ একদিন কোনিকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে যান। সেখানে তারা তিন ঘণ্টা ধরে ঘোরাঘুরি করার পর বাড়ি থেকে আনা খাবার খেতে বসেন। কিন্তু খাবারের সঙ্গে জল না থাকায় কোনি তাদের পাশেই বসে থাকা একদল ছাত্রীদের কাছে জল চাইতে যায়। ছাত্রীদের একজন দিদিমণি কোনিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে জল দিতে অস্বীকার করেন। পরে, সেই দলের একজন হিয়া মিত্র নামে একটি মেয়ে কোনিকে জল দিতে এগিয়ে আসে ,কোনি সেই জলের গ্লাস ফেলে দেয়।
এই আচরণ ছিল কোনির মানসিক প্রতিক্রিয়া, কারণ সে জল চেয়ে অপমানিত হয়েছিল। সেই অপমান কোনি সহজে ভুলতে পারেনি। হিয়ার প্রতি কোনির আক্রোশের প্রকাশ ঘটে গ্লাসটি ফেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। ক্ষিতীশ সিংহ তখন কোনিকে বলেন, রাগ মনের মধ্যে পুষে রাখতে।
কোনি হিয়াকে না চিনলেও, ক্ষিতীশ সিংহ হিয়াকে চিনতেন এবং জানতেন সে সাঁতারে অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি রবীন্দ্র সরোবরে হিয়ার সাঁতার দেখেছেন এবং বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবে গিয়ে তার প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি মনে করতেন, হিয়া মিত্র কোনির তুলনায় অনেক এগিয়ে এবং হিয়া মিত্রই ভবিষ্যতে তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হবে তাই, ক্ষিতীশ সিংহ চেয়েছিলেন সেই অপমান যেন কোনির মধ্যে থেকে যায়। কারণ সেই অপমানই তাকে অনুপ্রাণিত করবে পরিশ্রম করতে এবং একদিন হিয়াকে হারিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে।
এইভাবেই ক্ষিতীশ সিংহ কোনির মনে প্রতিযোগিতার জেদ জাগিয়ে তুলে তাকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন।
৮.২ ‘অভিনন্দন আর আদরে সে ডুবে যাচ্ছে।’ কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? অভিনন্দন ও আদর প্রাপ্তির কারণ লেখো।
উত্তর: মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাস থেকে গৃহীত এই অংশে ‘অভিনন্দন আর আদরে সে ডুবে যাচ্ছে’ বলা হয়েছে প্রতিভাবান সাঁতারু কোনিকে নিয়ে।
মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় কোনি বাংলা দলের হয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বাংলার অন্যান্য সাঁতারুদের সঙ্গে সে-ও মাদ্রাজে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়েও, আগের মতোই, সে চক্রান্তের শিকার হয়।
মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের সদস্য হলেও চক্রান্তের কারণে প্রথমে কোনিকে কোনো প্রতিযোগিতায় নামানো হয়নি। শেষ মুহূর্তে বাধ্য হয়ে তাকে ৪×১০০ মিটার রিলে সাঁতারে নামানো হয়, কারণ জিততে না পারলে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না। প্রচণ্ড চাপ ও আড়ষ্টতা সত্ত্বেও কোনি দুর্দান্ত সাঁতার কাটে এবং সবার বিস্ময় জাগিয়ে পরাজিত করে বিখ্যাত সাঁতারু রমা যোশিকে।
এই জয়ে বাংলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়। কোনির সাফল্যে উত্তেজিত দর্শকরা উচ্ছ্বসিত করতালিতে ও অভিনন্দনে ভাসিয়ে দেয় তাকে। রমা যোশিও তার পিঠ চাপড়ে প্রশংসা জানায়। বাংলার অন্যান্য সাঁতারুরাও তাকে অভিনন্দন জানায়, আর দলের ধীরেন ঘোষ আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরেন। সবার ভালোবাসা, সম্মান ও গর্বে কোনি যেন সত্যিই অভিনন্দন ও আদরের সাগরে ডুবে যায়।
৮.৩ “প্রথম দিকে লীলাবতী বিদ্রোহী হয়েছিল,” লীলাবতীর পরিচয় দাও। কোন ব্যাপারে সে ‘বিদ্রোহী’?
উত্তর: মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র লীলাবতী। তিনি ক্ষিতীশের স্ত্রী—স্বল্পভাষী, কর্মপটু, বাস্তববাদী ও প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী এক নারী, যিনি যেন নিজের দৃঢ় মনোবল দিয়ে ক্ষিতীশ ও কোনিকে আগলে রেখেছেন। ক্ষিতীশের অবহেলায় প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়া দোকানকে নিজের যোগ্যতায় মাত্র চার বছরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। কোনির প্রতি ক্ষিতীশের অতিরিক্ত দায়িত্বগ্রহণে অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং সেলামির প্রসঙ্গে ব্যয়সংকোচের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি কোনিকে খাবারের বিনিময়ে দোকানে কাজ করতে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনে বেতনও দিয়েছেন। তবে কাজে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে কঠোর শাস্তি এবং জয়ের সময় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি—দুটোই দিতে কুণ্ঠা করেননি। লীলাবতী চরিত্রটির এই নিজস্বতা পাঠককে মুগ্ধ করে ।
ক্ষিতীশের মতে, বাঙালিয়ানা রান্না স্বাস্থ্যকর নয়; তাই তিনি প্রায় সব খাবার সেদ্ধ খাওয়ায় বিশ্বাসী। রান্নায় সরষে বাটা, শুকনো লঙ্কা, জিরে-ধনে বা পাঁচফোড়নের মতো উপকরণ ব্যবহার না করার বিধিনিষেধ লীলাবতীর পক্ষে মানা কঠিন ছিল। এই কারণেই প্রথমদিকে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। তবুও অন্তরে তিনি সবসময় কোনির সাফল্যের জন্য নিরবে সমর্থন ও সাহায্য জুগিয়েছেন।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো:
Education has no end. So you should keep up your studies. Many young men close their books when they have taken their degrees and learn no more. Therefore they very soon forget all they have ever learnt. If you want to continue your education, you must find time for serious reading.
উত্তর: শিক্ষার কোনো শেষ নেই। তাই তোমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। অনেক যুবক ডিগ্রি পাওয়ার পর বই বন্ধ করে দেয় এবং আর কিছু শেখে না। ফলে তারা অচিরেই যা কিছু শিখেছিল সব ভুলে যায়। তুমি যদি তোমার শিক্ষা চালিয়ে যেতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই গম্ভীরভাবে পড়াশোনার জন্য সময় বের করতে হবে।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ তোমার এলাকায় ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ
সুমন: আরে শুভ, শুনছিস? আমাদের এলাকায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নাকি অনেক বেড়ে গেছে।
শুভ: হ্যাঁ রে, আমি তো পাড়ার দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে দেখলাম। অবস্থা বেশ খারাপ।
সুমন: ডাক্তাররা বলছেন, মশা নিয়ন্ত্রণ না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে।
শুভ: ঠিক বলেছিস। মশার প্রজননস্থল নষ্ট করতে হবে—যেখানে জল জমে থাকে, সেগুলো ফেলে দিতে হবে।
সুমন: আমাদের পাড়ায় অনেকেই সাবধানতা মানছে না। বাড়ির ছাদে, টবে, এমনকি পুরোনো টায়ারে জল জমে আছে।
শুভ: আমি ভাবছি পাড়ার যুবকদের নিয়ে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করব।
সুমন: দারুণ আইডিয়া। সঙ্গে মশারি ব্যবহার আর শরীর ঢাকা কাপড় পরার ব্যাপারেও সবাইকে সচেতন করতে হবে।
শুভ: ঠিক বলেছিস। একসাথে কাজ করলে ডেঙ্গুকে হারানো সম্ভব।
সুমন: তাহলে ঠিক হলো, কাল থেকেই কাজ শুরু করব।
১০.২ বিদ্যালয়ের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
নিজেস্ব সংবাদদাতা, মালদা, সেপ্টেম্বর ২০২৫: গত ১২ই আগস্ট আমাদের বিদ্যালয়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। প্রথমেই বিদ্যালয়ের গানের দল স্বাগত সংগীত পরিবেশন করে। এরপর একে একে আবৃত্তি, নাটিকা, নৃত্য ও একক সংগীত পরিবেশিত হয়। বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকটি। অনুষ্ঠান চলাকালীন শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম ও হাতের কাজের প্রদর্শনীও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিরতিতে অতিথিদের জন্য চা ও নাস্তার ব্যবস্থা ছিল। শেষপর্যন্ত অতিথি বক্তারা শিক্ষার্থীদের প্রতিভা ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রশংসা করেন। প্রধান শিক্ষক বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং সবাইকে আগামী বছর আরও ভালো আয়োজনের জন্য উৎসাহিত করেন। আনন্দ, উৎসাহ ও সৃজনশীলতায় ভরপুর এই দিনটি বিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো:
১১.১ বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ ও মানবজাতির সংকট।
উত্তর:
বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ ও মানবজাতির সংকট
ভূমিকা
বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে সহজ, সুন্দর ও আরামদায়ক করে তুলতে আবিষ্কৃত হয়েছে। চিকিৎসা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পরিবহন—সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান আমাদের অগ্রগতির দিশা দেখিয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ মানবসভ্যতার জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে।
পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা
বিজ্ঞানের সবচেয়ে ভয়ংকর অপপ্রয়োগ হলো পারমাণবিক শক্তি। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞ মানব ইতিহাসের ভয়াল দৃষ্টান্ত। আজও বিভিন্ন রাষ্ট্রে পারমাণবিক অস্ত্র মজুত রয়েছে, যা সামান্য যুদ্ধ বা সংঘাতেই সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখে ফেলতে পারে। পাশাপাশি রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্রও সভ্যতার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
প্রযুক্তির অপব্যবহার
আধুনিক প্রযুক্তি যেমন আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনি এর অপপ্রয়োগ নানা সংকট তৈরি করছে। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে ভুয়ো সংবাদ, সাইবার অপরাধ ও আসক্তি। রোবট ও যান্ত্রিকীকরণের ফলে কর্মসংস্থানের সংকট দেখা দিচ্ছে, যা সমাজে বৈষম্য বাড়াচ্ছে।
পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু সংকট
শিল্পোন্নতি ও জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার পৃথিবীর পরিবেশকে বিপন্ন করছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, হিমবাহ গলন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি মানবসভ্যতার টিকে থাকার ওপর প্রশ্ন তুলছে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দিন দিন বাড়ছে—যা বিজ্ঞানের অযাচিত অপপ্রয়োগের ফল।
উপসংহার
বিজ্ঞান কখনও নিজে অভিশাপ নয়; এর ভুল ব্যবহারই সর্বনাশ ডেকে আনে। বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করলে মানবজাতি শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ, লোভ ও প্রতিযোগিতার বশবর্তী হয়ে যদি আমরা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ করি, তবে একদিন মানবসভ্যতা বিলীন হয়ে যাবে। তাই বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা মানবজাতির অন্যতম কর্তব্য।
১১.২ তোমার দেখা একটি গ্রাম্য মেলা।
উত্তর:
আমার দেখা একটি গ্রাম্য মেলা
ভূমিকা
বাংলার গ্রামজীবন সরল অথচ আনন্দঘন। এখানে উৎসব-অনুষ্ঠান মানুষের প্রাণে প্রাণ সঞ্চার করে। গ্রামীণ জীবনের অন্যতম আকর্ষণ হলো গ্রাম্য মেলা। সম্প্রতি আমি আমাদের গ্রামে অনুষ্ঠিত একটি পৌষসংক্রান্তির মেলা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই মেলার অভিজ্ঞতা আজও আমার মনে অম্লান হয়ে আছে।
মূল বক্তব্য
মেলা বসেছিল গ্রামের বিশাল মাঠে। মেলার চারপাশ সেজে উঠেছিল রঙিন কাগজ, পতাকা ও আলোকসজ্জায়। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসছিল দল বেঁধে। মাঠের চারদিকে বসেছিল নানারকম দোকানপাট—মাটির হাঁড়ি, কলসি, খেলনা, বাঁশি, কাঠের পুতুল, কাপড়চোপড় ও অলঙ্কার। মিষ্টির দোকানে ছিল নানান আয়োজন—সন্দেশ, জিলিপি, মোয়া, লাড্ডু, পাটিসাপটা প্রভৃতি। শিশুদের ভিড় ছিল খেলনা আর মিষ্টির দোকানে।
বিনোদনের ব্যবস্থাও ছিল চমৎকার। নাগরদোলা, ঝুলনা, ঘোড়ার গাড়ি শিশুদের আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিল। বিকেলে যাত্রাপালার আসর বসে, স্থানীয় শিল্পীরা অভিনয় করেন আর দর্শকেরা মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করেন। এছাড়া কবিগান, বাউলগান, ঢোলের তালে নাচ-গান, এমনকি দড়ি টানাটানির মতো খেলা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। মেলায় গ্রামের মানুষ যেমন এসেছিল, তেমনি দূরের লোকও কেনাকাটা ও আনন্দ উপভোগে যোগ দিয়েছিল। মেলাকে ঘিরে গ্রাম যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।
উপসংহার
দিন শেষে যখন সূর্য অস্ত গেল, তখনও মেলার কোলাহল থামেনি। বিদায় নেওয়ার সময় মনে হলো, গ্রাম্য মেলা শুধু বিনোদনের আসর নয়, বরং মানুষের সামাজিক মিলনক্ষেত্রও বটে। এখানে মানুষ অস্থায়ীভাবে দুঃখ-দুর্দশা ভুলে গিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। আমার দেখা এই গ্রাম্য মেলা তাই আজও মনে রঙিন স্মৃতির মতো ভেসে ওঠে।
১১.৩ মনীষীদের জীবনী পাঠের উপযোগিতা।
উত্তর:
মনীষীদের জীবনী পাঠের উপযোগিতা
ভূমিকা
মানুষের জীবন সবসময় সরল পথে চলে না। জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে নানা বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট ও সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়। জীবনের এই কঠিন পথে আমাদের অনুপ্রেরণা যোগান মনীষীরা। তাঁদের জীবন আমাদের কাছে শিক্ষণীয় উদাহরণ হয়ে ওঠে। তাই মনীষীদের জীবনী পাঠের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে।
মূল বক্তব্য
প্রথমত, মনীষীদের জীবনী পাঠ আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁরা নানাবিধ প্রতিকূলতা জয় করে নিজের কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যেমন— মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যসাধনা কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণামূলক বাণী আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের শিক্ষা দেয়।
দ্বিতীয়ত, তাঁদের জীবনী নৈতিক শিক্ষা দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দয়া, করুণা ও মানবপ্রেম কিংবা বুদ্ধের করুণাবাণী আমাদের মনে সৎ, দয়ালু ও আদর্শবান হওয়ার অনুপ্রেরণা জাগায়।
তৃতীয়ত, জীবনী পাঠ চিন্তাশক্তি প্রসারিত করে। বৈজ্ঞানিক যেমন জগদীশচন্দ্র বসু, নিউটন বা আইনস্টাইনের জীবনী আমাদের কৌতূহল, গবেষণা ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব শেখায়। আবার সমাজসংস্কারক বা দার্শনিকদের জীবনী সমাজ পরিবর্তনের শক্তি জোগায়।
চতুর্থত, মনীষীদের জীবনী আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। তাঁদের জীবনে ব্যর্থতা ও প্রতিবন্ধকতা এসেছিল, কিন্তু তাঁরা হাল ছাড়েননি। তাই আমরা ব্যর্থতাকে ভয় না পেয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে শিখি।
উপসংহার
সব মিলিয়ে বলা যায়, মনীষীদের জীবনী শুধু ইতিহাস নয়, এগুলি আমাদের জীবনের দিশারি। এগুলি আমাদের নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক শিক্ষা দেয়। তাই জীবনে সৎ, আদর্শবান ও সফল মানুষ হতে হলে মনীষীদের জীবনী পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।
১১.৪ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
উত্তর:
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
ভাষা মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও সত্তার প্রধান প্রকাশভঙ্গি। প্রতিটি জাতির নিজস্ব মাতৃভাষা তাদের পরিচয়ের ভিত্তি। বিশ্বব্যাপী ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান জানাতে এবং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। এই দিনটি বাংলা দেশের জনগণের আত্মত্যাগের স্মৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।
১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নিলে বাংলা ভাষীরা প্রবল আপত্তি জানায়। বাংলাভাষী মানুষের দাবি ছিল—তাদের মাতৃভাষা বাংলা যেন রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। দীর্ঘ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে আসে। পুলিশ গুলি চালালে সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ অনেকেই প্রাণ হারান। তাদের এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। ইতিহাসে এটি ভাষার জন্য রক্তদানের অনন্য ঘটনা।
১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো বাংলাদেশের উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে সারা বিশ্বে দিনটি পালিত হচ্ছে। এ ঘোষণার ফলে শুধু বাংলাভাষী জনগণই নয়, পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষ তাদের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ছয়-সাত হাজার ভাষা প্রচলিত। কিন্তু বিশ্বায়নের চাপে বহু ভাষা বিলুপ্তির পথে। তাই এই দিবস মানুষকে তার ভাষা রক্ষায় সচেতন করে তোলে।
বাংলাদেশে এই দিনটি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। কবিতা পাঠ, গান, প্রবন্ধ রচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে সর্বত্র দিবসটি পালিত হয়। এ দিনটি কেবল অতীতের আত্মত্যাগের স্মরণ নয়, বরং মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার ও বিকাশের প্রতিজ্ঞার দিন।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের শেখায়—ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অস্তিত্বের প্রতীক। তাই মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। মাতৃভাষাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, তার শুদ্ধ উচ্চারণ ও লিখন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। একই সঙ্গে অন্য জাতির ভাষা ও সংস্কৃতিকেও সম্মান জানানো উচিত।
পরিশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কেবল বাংলাভাষীদের গৌরব নয়, সমগ্র বিশ্বের ভাষাভাষী মানুষের অধিকার রক্ষার প্রতীক। ভাষাশহীদদের আত্মত্যাগ আমাদের চিরকাল অনুপ্রেরণা জোগাবে, আর এই দিবস আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা ও বিকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ করবে।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।