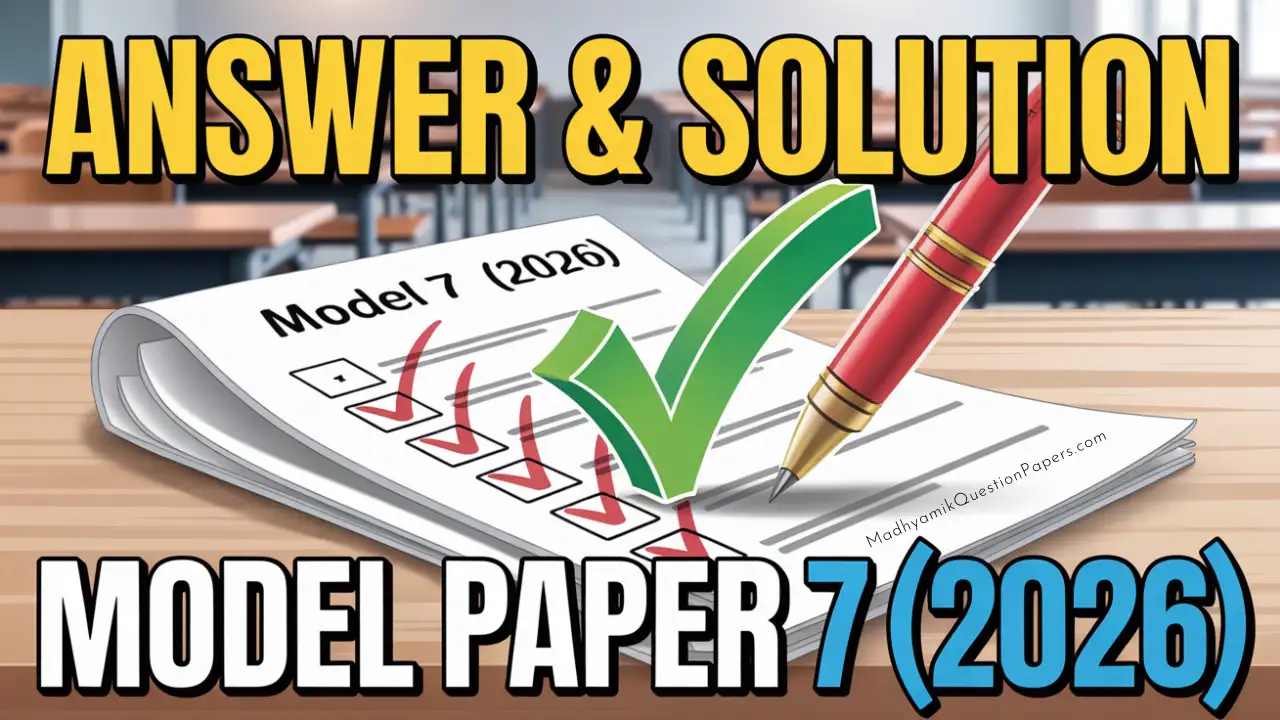আপনি কি মাধ্যমিকের বাংলা Model Question Paper 7 প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন? দেখে নিন 2026 WBBSE বাংলা Model Paper 7-এর সঠিক উত্তর ও বিশ্লেষণ। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 7-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৬ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ ‘শুধু এইটাই জানা ছিল না,’ অজানা বিষয়টি হল
(ক) মেসো একজন লেখক
(খ) তার গল্প ছাপা হবে
(গ) মানুষই গল্প লেখে
(ঘ) সে গল্প লিখতে পারে
উত্তর: (গ) মানুষই গল্প লেখে
১.২ নকল পুলিশ সেজে হরিদা মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে কত ঘুষ নিয়েছিলেন?
(ক) চারআনা,
(খ) আটআনা,
(গ) এক টাকা,
(ঘ) দু’টাকা
উত্তর: (খ) আটআনা
১.৩ নদেরচাঁদ কত বছর স্টেশন মাস্টারি করেছে? –
(ক) পাঁচ বছর,
(খ) চার বছর,
(গ) তিন বছর,
(ঘ) দু’বছর
উত্তর: (খ) চার বছর
১.৪ ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।’ বাক্যাংশটি কবিতায় ক’বার ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) একবার,
(খ) দু’বার,
(গ) তিনবার,
(ঘ) চারবার
উত্তর: (খ) দু’বার
১.৫ আদিম যুগের স্রষ্টার কার প্রতি অসন্তোষ ছিল?
(ক) দয়াময় দেবতার প্রতি,
(খ) কবির সংগীতের প্রতি,
(গ) নিজের প্রতি,
(ঘ) ধরিত্রীর প্রতি
উত্তর: (গ) নিজের প্রতি
১.৬ ‘অভিষেক’ শীর্ষক কাব্যাংশটি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর কোন্ সর্গ থেকে নেওয়া হয়েছে?-
(ক) প্রথম সর্গ,
(খ) তৃতীয় সর্গ,
(গ) নবম সর্গ,
(ঘ) পঞ্চম সর্গ
উত্তর: (ক) প্রথম সর্গ
১.৭ পন্ডিতদের মতে, কলমের দুনিয়ায় সত্যিকারের বিপ্লব ঘটিয়েছিল-
(ক) পার্কার পেন,
(খ) ফাউন্টেন পেন,
(গ) রিজার্ভার পেন,
(ঘ) সোনার কলম
উত্তর: (খ) ফাউন্টেন পেন
১.৮ ‘শ্রীপান্থ’ ছদ্মনামে লিখেছেন-
(ক) অন্নদাশঙ্কর রায়,
(খ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়,
(গ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
(ঘ) নিখিল সরকার
উত্তর: (ঘ) নিখিল সরকার
১.৯ পিতলের চেয়ে হালকা ধাতু হল
(ক) অ্যালুমিনিয়াম,
(খ) পারদ,
(গ) লোহা,
(ঘ) তামা
উত্তর: (ক) অ্যালুমিনিয়াম
১.১০ ‘ইসাবের মেজাজ চড়ে গেল।’ নিম্নরেখ পদটি কোন কারকের উদাহরণ? –
(ক) কর্মকারক,
(খ) করণ কারক,
(গ) কর্তৃকারক,
(ঘ) অপাদান কারক
উত্তর: (ক) কর্মকারক
১.১১ যাকে দিয়ে কাজ করানো হয়, সেটি কী কর্তা? –
(ক) প্রযোজক কর্তা,
(খ) প্রযোজ্য কর্তা,
(গ) সমধাতুজ কর্তা,
(ঘ) নিরপেক্ষ কর্তা
উত্তর: (খ) প্রযোজ্য কর্তা
১.১২ ‘সমাস’ শব্দের অর্থ
(ক) সংক্ষেপ,
(খ) বিদ্বান,
(গ) বিস্তৃত,
(ঘ) প্রকাশভঙ্গি
উত্তর: (ক) সংক্ষেপ
১.১৩ ‘ফেলাইলা কনক-বলয় দূরে;’ নিম্নরেখ পদটি যে সমাসের উদাহরণ তা হল-
(ক ) তৎপুরুষ,
(খ) অব্যয়ীভাব,
(গ) বহুব্রীহি,
(ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
উত্তর: (ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
১.১৪ ‘আজকের দিনটা বেশ কাটল’- গঠনগত দিক থেকে বাক্যটি হল-
(ক) সরল বাক্য,
(খ) জটিল বাক্য,
(গ) মিশ্রবাক্য,
(ঘ) যৌগিক বাক্য
উত্তর: (ক) সরল বাক্য
১.১৫ ‘আগামীকাল আমি গিয়েছিলাম’ এখানে বাক্য নির্মাণের কোন্ শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে? –
(ক) যোগ্যতা,
(খ) আকাঙ্ক্ষা,
(গ) আসত্তি,
(ঘ) কোনোটিই নয়
উত্তর: (ক) যোগ্যতা
১.১৬ “বৃষ্টির দ্বারা আমার পায়ের দাগ ধৌত হল” কোন্ বাচ্যের উদাহরণ? –
(ক) কর্তৃবাচ্য,
(খ) কর্মকর্তৃবাচ্য,
(গ) কর্মবাচ্য,
(ঘ) ভাববাচ্য
উত্তর: (গ) কর্মবাচ্য
১.১৭ যে বাচ্যের বাচ্য পরিবর্তন অসম্ভব, তা হল-
(ক) কর্মকর্তৃবাচ্য,
(খ) কর্তৃবাচ্য,
(গ) কর্মবাচ্য,
(ঘ) ভাববাচ্য
উত্তর: (ক) কর্মকর্তৃবাচ্য
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ তপনের গল্প পড়ে ছোটোমাসি কী বলেছিল?
উত্তর: তপনের গল্প পড়ে ছোটোমাসি যদিও প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু সন্দেহ করে জিজ্ঞেস করলেন যে গল্পটা সে নিজে লিখেছে, না কারও কাছ থেকে নকল করেছে।
২.১.২ “বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন বিরাগী।” কী বলতে বলতে বিরাগী সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন?
উত্তর: ‘আমি যেমন সহজে ধুলো মাড়িয়ে চলে যাই, তেমনই সহজে সোনাকেও মাড়িয়ে যেতে পারি’— এই কথা বলতে বলতেই বিরাগী সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।
২.১.৩ ‘লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল।’ লোকটির পরিচয় দাও।
উত্তর: লোকটি ‘পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট’ গিরীশ মহাপাত্র। তার গায়ের রং খুব ফরসা, কিন্তু রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। বয়স বেশি হবে না, ত্রিশ-বত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু শরীর খুবই রোগা। একটু কাশির চেষ্টাতেই সে হাঁপিয়ে উঠল। হঠাৎই মনে হয়, তার আয়ু বেশি দিনের নয়। মনে হচ্ছে ভেতরে কোনো এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে তার সমস্ত শরীর দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য শুধু তার সেই রোগা মুখের জোড়া চোখের দৃষ্টি। চোখ দুটি ছোট না বড়, টানা না গোল, উজ্জ্বল না নিষ্প্রভ—বোঝা যায় না। কিন্তু অত্যন্ত গভীর একটি জলাশয়ের মতো তাদের ভিতর কী যে লুকিয়ে আছে! ভয় হয়, সেখানে খেলা করা চলবে না, দূরে সাবধানে দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো। এই চোখেরই কোনো এক অতল তলায় তার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকিয়ে আছে, যেখানে মৃত্যুরও প্রবেশ করার সাহস হয় না। আর এই জন্যই হয়তো সে আজও বেঁচে আছে।
২.১.৪ “অমৃত ফতোয়া জারি করে দিল,” অমৃত কী ‘ফতোয়া’ জারি করেছিল?
উত্তর: অমৃতের জারি করা ‘ফতোয়া’ ছিল— ঠিক ইসবের মতো জামাটি না পেলে সে স্কুলে যাবে না ।
২.১.৫ ‘সেই ক্ষীণস্রোতা নির্জীব নদীটি’ কোন্ নদীর কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নদীর বিদ্রোহ গল্প থেকে নেওয়া আলোচ্য অংশটিতে ‘সেই ক্ষীণস্রোতা নির্জীব নদীটি’ বলতে নদেরচাঁদের দেশের নদীটির কথা বলা হয়েছে।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ ‘নেমে এল তার মাথার ওপর।’ কী নেমে আসে?
উত্তর: পাবলো নেরুদা রচিত অসুখী একজন কবিতায় কবির জন্য অপেক্ষারত মেয়েটির মাথার উপর একটার পর একটা পাথরের মতো বছরগুলো নেমে এলো।
২.২.২ “এ অদ্ভুত বারতা,” কোন্ ‘বারতা’-র কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর ‘অভিষেক’ কাব্যাংশে, প্রভাষা রাক্ষসীর ছদ্মবেশে দেবী লক্ষ্মী প্রমোদকাননে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্রজিতকে যে সংবাদটি শোনান, সেটিই হল ‘বারতা’। সেই বারতাটি ছিল রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর নিহত হওয়ার সংবাদ।
২.২.৩ ‘ওই আসে সুন্দর।’ সুন্দর কীভাবে আসে?
উত্তর: কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কাব্যে সৌন্দর্য আবির্ভূত হয়েছে এক ভয়ংকর কালরূপ ধারণ করে।
২.২.৪ “সখী সবে আজ্ঞা দিল” বক্তা তার সখীদের কী আজ্ঞা দিয়েছিলেন?
উত্তর: তিনি আদেশ দিলেন যে, চার সখীর সাহায্যে অচেতন পদ্মাবতীকে বস্ত্রাবৃত করে উদ্যানের ভিতর নিয়ে যেতে হবে।
২.২.৫ “মাথায় কত শকুন বা চিল” শকুন ও চিল বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: “অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতায় শকুন ও চিল—এ দুটি মাংসাশী পাখিকে যুদ্ধপ্রিয়, ক্ষমতাধর ও সুবিধাবাদী মানুষের চরিত্রের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। এদের সংখ্যা খুবই কম, তবু মানব সভ্যতার ইতিহাসে এদের অস্তিত্ব চিরকালীন এবং অত্যন্ত গুরুত্ববহ।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘তাই নিয়ে আমাদের প্রথম লেখালেখি।’ কী নিয়ে লেখকদের প্রথম লেখালেখি?
উত্তর: লেখকদের শুরুর দিনগুলোর লেখালেখির সরঞ্জাম ছিল বাঁশের কলম, মাটির দোয়াত, ঘরের তৈরি কালি আর কলাপাতা।
২.৩.২ ফাউন্টেন পেনের আবিষ্কর্তা কে?
উত্তর: ফাউন্টেন পেনের আবিষ্কর্তা হলেন লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যান। আসল কথা হলো, ফাউন্টেন পেনের আবিষ্কারের পেছনে একটি সত্যিকারের ঘটনা জড়িত। ‘রিজার্ভার পেন’ নামক একটি কলমই ছিল এর আদি রূপ। আমেরিকান ব্যবসায়ী লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যান সেই নকশাকে আরও পরিশীলিত করে ফাউন্টেন পেনের রূপ দেন।
২.৩.৩ ‘অভিধা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: শব্দের প্রাথমিক ও আভিধানিক অর্থই হলো তার অভিধা। যেমন- ‘অরণ্য’ শব্দের ক্ষেত্রের অভিধা হচ্ছে ‘বন’। এটি শব্দের গভীর বা প্রাসঙ্গিক কোনো অর্থ বহন করে না।
২.৩.৪ ‘এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়।’ কোন্ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়?
উত্তর: রাজশেখর বসুর অভিমত হলো, সমস্ত টেকনিক্যাল বা পারিভাষিক শব্দ বাদ দিলেই যে লেখা সহজবোধ্য হয়ে যায়, এই ধারণাটি একদম ঠিক নয়।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ নিরপেক্ষ কর্তা কাকে বলে?
উত্তর: নিরপেক্ষ কর্তা বলতে বোঝায় যখন একটি জটিল বাক্যে মূল ক্রিয়া (সমাপিকা) এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা একই ব্যক্তি বা বস্তু না হয়। সেক্ষেত্রে, অসমাপিকা ক্রিয়ার যে কর্তা থাকে, তাকেই নিরপেক্ষ কর্তা বলে। একটি নিরপেক্ষ কর্তার একটি উদাহরণ হল – বৃষ্টি পড়ছে। এখানে ‘বৃষ্টি’ হল নিরপেক্ষ কর্তা। এটি কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী নয়, একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। কর্তা হিসেবে এটি নিরপেক্ষ বা ইম্পার্সোনাল।
২.৪.২ বিশেষ্যখন্ডের উদাহরণ দাও।
উত্তর: বিশেষ্যখন্ডের একটি উদাহরণ হল – আমার ভাই একজন ডাক্তার। এখানে ‘আমার’ ও ‘ভাই’ মিলে একটি বিশেষ্যখন্ড গঠন করেছে যা বাক্যের কর্তা।
২.৪.৩ সম্বন্ধপদ কারক নয় কেন?
উত্তর: সম্বন্ধপদ কারক নয়, কারণ এটি একটি বিভক্তি বা পদ যা বিশেষ্যের সাথে বিশেষ্যের সম্বন্ধ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
২.৪.৪ ‘মেঘে ঢাকা’ শব্দটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম উল্লেখ করো।
উত্তর: ‘মেঘে ঢাকা’ শব্দটির ব্যাসবাক্য হল – মেঘ দ্বারা ঢাকা এবং সমাসের নাম হল – তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।
২.৪.৫ বাক্যাশ্রয়ী সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে সমাসে সমস্ত পদ একটি বাক্য বা বাক্যাংশকে ভিত্তি হিসেবে ধরে গঠিত হয়, তাকেই বাক্যাশ্রয়ী সমাস বলা হয়। বাক্যাশ্রয়ী সমাসের একটি উদাহরণ হল – নীলকমল।
২.৪.৬ বাক্যে ব্যবহার করে সহার্থক বহুব্রীহির একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: বাক্যে ব্যবহার করে সহার্থক বহুব্রীহির একটি উদাহরণ হল – তিনি একহাত হয়ে গেছেন।
২.৪.৭ নির্দেশক বাক্য কাকে বলে?
উত্তর: বাক্য দ্বারা যদি কোনো ব্যক্তি, বস্তুর অবস্থান, দিক, সংখ্যা বা পরিচয় নির্দেশিত হয়, তবে তাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয়। একটি নির্দেশ বাক্যের উদাহরণ হল – দরজাটা বন্ধ করে দাও।
২.৪.৮ ‘কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য।’ প্রশ্নসূচক বাক্যে পরিবর্তন করো।
উত্তর: ‘কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য।’ প্রশ্নসূচক বাক্যে পরিবর্তন করলে হবে – কলম কি তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য?
২.৪.৯ কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের অন্তত একটি পদ্ধতি উল্লেখ করো।
উত্তর: কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের একটি প্রধান পদ্ধতি হলো কর্তা -কে ‘দ্বারা’/’যোগে’/’কর্তৃক’ ইত্যাদি বিভক্তি দ্বারা চিহ্নিত করে বাক্যের শেষে স্থানান্তর করা এবং কর্ম -কে কর্তার স্থানে বসানো। কর্তৃবাচ্যে উদাহরণ – ছাত্রটি বইটি পড়ে। কর্মবাচ্যে উদাহরণ – বইটি পড়া হয় ছাত্রটির দ্বারা। (অথবা, বইটি ছাত্রটি দ্বারা পড়া হয়)।
২.৪.১০ ‘ঠিক আছে, আমাকে বেঁধে রাখো।’ ভাববাচ্যে রূপান্তর করো।
উত্তর: ‘ঠিক আছে, আমাকে বেঁধে রাখো।’ ভাববাচ্যে রূপান্তর করলে হবে – আমার বন্ধন যেন ঘটে।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ “কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল।”- কোন্ কথা শুনে, কেন তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল? ‘মার্বেল হয়ে গেল’ কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর: ছোটোমেসোমশাই যে একজন লেখক—এই কথা শুনেই তপনের চোখ মার্বেলের মতো গোল হয়ে গেল। তপনের ধারণা ছিল, লেখকেরা কোনো সাধারণ মানুষ নন, তাঁরা যেন অন্য এক জগতের মানুষ। তাই নিজের ছোটোমেসোমশাই যে গল্প লেখেন এবং সেগুলো ছাপাও হয়, তা শুনে তপনের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তার মনে হলো, সে যেন একেবারে অবিশ্বাস্য কোনো ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। এখানে ‘চোখ মার্বেল হয়ে গেল’ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তপনের প্রবল বিস্ময় ও অবাক হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিকে প্রকাশ করার জন্য।
৩.১.২ হরিদা পুলিশ সেজে কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন? তিনি কীভাবে মাস্টারমশাইকে বোকা বানিয়েছিলেন?
উত্তর: “বহুরূপী” গল্পের রচয়িতা সুবোধ ঘোষ। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদা একবার পুলিশের ছদ্মবেশে দয়ালবাবুর লিচু বাগানে উপস্থিত হন। পুলিশ সেজে তিনি চার স্কুলছাত্রকে আটক করেন, যারা বিনা অনুমতিতে লিচু বাগানে প্রবেশ করেছিল। ছাত্ররা ভয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ক্ষমা চাইতে থাকে। ঘটনাক্রমে স্কুলের মাস্টারমশায় সেখানে উপস্থিত হন এবং হরিদার ছদ্মবেশ না চিনতে পেরে, তিনি ছাত্রদের মুক্তির অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত আট আনা অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে ছাড়পত্র নেন হরিদা। এভাবে তাঁর পোশাক, সাজসজ্জা ও অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে হরিদা মাস্টারমশায়কে বোকা বানাতে সক্ষম হন।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।” ‘তারা’ কারা? কেন স্বপ্ন দেখতে পারল না?
উত্তর: পাবলো নেরুদার ‘অসুখী একজন’ কবিতায় দেবতাদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারে না। কবির বর্ণনায়, শান্ত ও হলুদ বর্ণের দেবতারা হাজার হাজার বছর ধরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। মানুষের মধ্যে বিবাদ লাগলেও দেবতারা সর্বদা নির্বিরোধ ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন। তাই তারা নিয়ত স্বপ্নের জগতে মগ্ন থাকতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সমগ্র শহরজুড়ে যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠল। সেই সর্বগ্রাসী যুদ্ধে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটল, ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হল এবং দেবতারাও তাদের অবস্থান থেকে নিপতিত হলেন। এর ফলেই তারা আর স্বপ্ন দেখতে সক্ষম হলেন না।
৩.২.২ ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।’ কাদের, কেন এই আহ্বান করা হয়েছে?
উত্তর: কাদের এই আহ্বান করা হয়েছে?
শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতা ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের উদ্দেশে এই আহ্বান করেছেন।
কেন এই আহ্বান করা হয়েছে?
এক অস্থির সময়ে সমাজ রাজনৈতিক আদর্শহীনতা, সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মান্ধতা ও হানাহানিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মানুষ অস্তিত্বের সংকটে দিশাহারা। এই পরিস্থিতিতে কবির বিশ্বাস, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একত্র হয়ে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। তাই মুক্তির আশায় কবি সবাইকে দৃঢ়ভাবে হাত ধরে বেঁধে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ ‘পথের দাবী’ উপন্যাসের যে অংশ তোমাদের পাঠ্য, তা অনুসরণে অপূর্ব চরিত্রটি আলোচনা করো।
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ উপন্যাসের উদ্ধৃত অংশে অপূর্বর অনুভূতিই কাহিনির মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। তার চরিত্রে যে গুণাবলি ফুটে উঠেছে তা হলো –
দেশপ্রেম – অপূর্ব একজন বাঙালি যুবক এবং স্বদেশী ভাবধারায় বিশ্বাসী। নিমাইবাবুর কাছ থেকে সব্যসাচীর বীরত্বগাথা শুনে তার মনে এই দেশপ্রেমিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির জন্ম হয়। অন্যদিকে, নিমাইবাবুর প্রতি তার রাগের কারণ এই যে, তিনি বাঙালি হয়েও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গ্রেফতার করতে উদ্যত। সব্যসাচী সন্দেহে আটক গিরীশ মহাপাত্রই যে আসল সব্যসাচী, তা অপূর্বর বুঝতে দেরি হয়নি। তাই সে নিমাইবাবুকে বলে— “এ লোকটিকে কোনো কথা জিজ্ঞেস না করেই ছেড়ে দিন, যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।” পুলিশের মুখে এমন স্পষ্টবাদিতা অপূর্বর চরিত্রের দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমেরই পরিচয় বহন করে।
সাহসী ও প্রতিবাদী মনোভাব – শান্ত ও শিষ্ট স্বভাবের অধিকারী হলেও অপূর্বর মধ্যে রয়েছে দৃঢ় প্রতিবাদী সত্তা। রামদাসের কাছে পুলিশের সমালোচনা করতে গিয়ে সে নিজেই রাজদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তি পাওয়ার ঝুঁকি নেয়। বর্মা সাব-ইনস্পেক্টরের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেও সে সামান্যতম দ্বিধা করেনি। সবদিক বিচার করে বলা যায়, ‘Doing and Suffering’-এর ভিত্তিতে অপূর্বর চরিত্রই এই কাহিনি অংশের কেন্দ্রীয় চরিত্র।
৪.২ “নদীকে এভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত নদেরচাঁদ দিতে পারে।”- কৈফিয়তটি কী? কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল, কেন?
উত্তর: কৈফিয়তটি >কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন
নদীকে এভাবে ভালোবাসার একটি যুক্তি শুধুমাত্র নদেরচাঁদ-ই দিতে পারে। তার সেই যুক্তিটি হলো— নদেরচাঁদের জন্ম এই নদীর তীরেই, নদীর ধারেই তিনি বড় হয়েছেন এবং সারাজীবন ধরে নদীকে ভালোবেসেছেন। তার দেশের নদীটি হয়তো আকারে খুব বড় ছিল না, কিন্তু শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের শুরুতে কেউ তো বড় বা ছোট নদীর মাপকাঠি নিয়ে ভাবে না। দেশের সেই স্বল্পস্রোতা, নিস্তেজ নদীটি তার কাছে ছিল ঠিক একজন অসুস্থ ও দুর্বল আত্মীয়ার মতোই, যে মমতা পেয়েছে। একবার অনাবৃষ্টির বছর যখন নদীটি প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছিল, তখন নদেরচাঁদ দুঃখে কেঁদেই ফেলেছিলেন— যেমন কেউ তার খুব কাছের কোনো আত্মীয়ের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে কাঁদে। এটাই ছিল ‘নদীকে এভাবে ভালোবাসার’ নদেরচাঁদের যুক্তি।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতা অবলম্বনে সমুদ্রকন্যা পদ্মার চরিত্রবৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
উত্তর: সৈয়দ আলাওলের অনূদিত পদ্মাবতী কাব্যের ‘পদ্মাসমুদ্রখণ্ড’ অংশ থেকে সংকলিত ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতায় পদ্মাই সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত চরিত্র। কবিতায় তার যে পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে, তা লক্ষণীয়।
পদ্মার পরিচয় – পদ্মা ছিলেন সমুদ্রকন্যা। সখীদের নিয়ে হাসি-খেলায় মত্ত, প্রাণবন্ত এক রূপে কবিতায় তিনি উপস্থাপিত হয়েছেন। সমুদ্রতীরে তার সুরম্য উদ্যান ও সোনা দিয়ে মোড়ানো প্রাসাদ তার সৌন্দর্যপ্রিয়তারই স্বাক্ষর বহন করে।
সৌন্দর্যপ্রিয়তা – পদ্মার সৌন্দর্যচেতনা ছিল সুগভীর। তিনি যে উদ্যান তৈরি করেছিলেন, সেখানে নানা মনোরম ফুলের সুগন্ধি ও ফলে ভরা গাছ তার এই বৈশিষ্ট্যেরই ইঙ্গিত দেয়। সোনা ও নানা রত্নে খচিত তার প্রাসাদ তার রুচিশীলতার আরেক অনন্য নিদর্শন।
মানবিক গুণ – পদ্মার চরিত্রকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে তার অন্তর্নিহিত মানবিকতা। সমুদ্রতীরে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা অপরিচিতা পদ্মাবতীকে দেখে তার মনের উৎকণ্ঠা, ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা— সব মিলিয়ে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধনেই জড়িয়ে পড়ে। পদ্মার নির্দেশে তার সখীরা তন্ত্র-মন্ত্র ও মহৌষধি দিয়ে পদ্মাবতীর চৈতন্য ফিরিয়ে আনে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আলাওলের সৃষ্ট এই চরিত্রে মানবিকতাবোধ একটি অসাধারণ গুণ হিসেবে বিবেচিত। এভাবেই সমুদ্রকন্যা পদ্মা হয়ে ওঠেন এক অনন্য চরিত্র।
প্রাণচঞ্চলতা – সখীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। রাত্রি শেষে সকালেই সখীদের সঙ্গে হাসি-আনন্দে মেতে উঠতে দেখা যায় তাকে, যা তার প্রাণবন্ত ও চঞ্চল স্বভাবেরই প্রতিচ্ছবি।
৫.২ “তোরা সব জয়ধ্বনি কর।” কবির এই কথা বলার কারণ সংক্ষেপে লেখো।
উত্তর: প্রদত্ত কবিতায় কবি ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে বিপন্ন ভারতবাসীর দুঃখ দূর করতে এমন এক ব্যক্তির আবাহন জানিয়েছেন, যিনি ইতিপূর্বে কখনও আসেননি। সেই ‘অনাগত’ হলেন ‘প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল’। প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়ের মতো তিনিও এক তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করবেন। তাঁর এই তাণ্ডবের মধ্য দিয়েই কবি এক নতুন যুগের আগমনী বার্তা লক্ষ্য করেছেন। কালবৈশাখী ঝড় যেমন ধ্বংসের মাধ্যমেই নতুন সৃষ্টির সূচনা করে, তেমনই এই প্রলয়ঙ্করী পুরুষও একটি নতুন সমাজের ভিত্তি রচনা করবেন। এই কারণে কবি সকলকে জয়ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। যিনি আসবেন তিনি ভয়াবহ, তিনি সংহাররূপী। সমগ্র জগৎজুড়ে তিনি ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালাবেন। কিন্তু সেই ধ্বংসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ‘জরায়-মরা, মুমূর্ষুদের প্রাণ’। তিনি পুরাতন সমাজব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়েই নতুন এক যুগের সূচনা করবেন। তিনি ভারতবাসীকে দাসত্বের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন আলোর পথ দেখাবেন। এই জন্যই কবি সকলকে জয়ধ্বনি করতে বলেছেন।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ কালি কলমের প্রতি ভালোবাসা ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।
উত্তর: “হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” প্রবন্ধে লেখক কলম, দোয়াত ও কালিকে ঘিরে তার স্মৃতিবহ ভালোবাসা এবং সময়ের পরিবর্তনে এগুলির বিলুপ্তির মর্মবেদনা মূর্ত করে তুলেছেন। শৈশবে তার লেখাপড়ার নিত্যসঙ্গী ছিল বাঁশের তৈরি কলম আর কলাপাতার কাগজ। বাড়ির কাঠের চুলায় বসানো কড়াইয়ের তলায় জমা কালি লাউপাতা দিয়ে ঘষে পাথরের বাটিতে জলে মিশিয়ে তৈরি করা হত কালি। সময়ের স্রোতে বাঁশের কলমের স্থান দখল করে নেয় খাগের কলম ও পরে পালকের কলম। এরপর ফাউন্টেন পেন নিয়ে আসে লেখালেখির জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কলম হয়ে ওঠে সস্তা ও সহজলভ্য। ফাউন্টেন পেনকে ঘিরে গড়ে ওঠে বিলাসিতার এক সংস্কৃতি। বাজারে ছড়িয়ে পড়ে কাজল কালি, সুলেখা কালির দোয়াত ও বোতল। পরবর্তীতে বলপেনের আগমন ঘটে। সবশেষে কম্পিউটার এসে কলমের স্থানই দখল করে নেয়। বাজার থেকে যখন নানা ধরনের কলম ও কালি লোপ পেতে থাকে, তখন লেখকের মতো ‘কালি-কলম-ভক্ত’ মানুষের হৃদয় ব্যথায় ভেসে ওঠে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে কম্পিউটারের আধিপত্য মেনে নিলেও, কলমের সাথে জড়িয়ে থাকা শৈশবের স্মৃতিগুলি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা লেখকের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।
৬.২ ‘প্রীতির সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয়। ‘তাঁর এই মন্তব্যের কারণ বুঝিয়ে দাও। কোন্ শ্রেণির পাঠক সম্পর্কে লেখকের এই মন্তব্য?
উত্তর: রাজশেখর বসু তাঁর ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ রচনায় বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা সম্পর্কে সেই সব পাঠকের আলোচনা করেছেন, যারা ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান রাখেন।
মন্তব্যের কারণ – প্রবন্ধকারের মতে, বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার পাঠক মূলত দুই ধরনের। প্রথম শ্রেণির পাঠক হলেন তারা যারা ইংরেজি জানেন না বা খুব কম জানেন। তাদের বিজ্ঞান বিষয়ে পূর্ববর্তী কোনো জ্ঞান নেই। এই পাঠকদের ক্ষেত্রে বিষয়গত জ্ঞানের স্বল্পতা সমস্যার সৃষ্টি করলেও ভাষা কখনোই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না, কারণ তারা বাংলা ভাষায় স্বচ্ছন্দ। তাদের কেবল বৈজ্ঞানিক বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু যেসব পাঠক ইংরেজি ভাষায় দক্ষ এবং ইংরেজিতে বিজ্ঞান চর্চা করেছেন, তাদের সমস্যা ভিন্ন প্রকৃতির। তারা যখন বাংলায় কোনো বৈজ্ঞানিক রচনা পড়েন, তখন তাদের পূর্বধারণা ও ইংরেজির প্রতি পক্ষপাত ত্যাগ করতে হয়। প্রথমে তাদের বাংলা ভাষাকে আন্তরিকভাবে রপ্ত করতে হয়। লেখক একটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন যে, ব্রহ্মমোহন মল্লিকের বাংলা জ্যামিতির বই তাঁর বাল্যকালে সম্পূর্ণ বোধগম্য হলেও, যারা ইংরেজিতে জ্যামিতি শিখেছে তাদের পক্ষে একই বই বুঝতে অসুবিধা হয়। এই ভাষাগত দূরত্ব অতিক্রম করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “দরবার ত্যাগ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি জাঁহাপনা।” বক্তা কে? তাঁরা কেন দরবার ত্যাগ করতে চান?
উত্তর: বক্তা: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের একটি অংশে মীরজাফর এই কথা বলেছেন।
কেন দরবার ত্যাগ করতে চান: ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্ররোচনায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার একদল সভাসদ রাজদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগতশেঠ প্রমুখ ছিলেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে ‘আমরা’ বলতে এই রাজদ্রোহী সভাসদদেরই বোঝানো হয়েছে। তারা নবাবের দরবার ছেড়ে চলে যেতে চাইছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, নবাব-বিরোধী এই সভাসদদের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন ওয়াটস নামক এক ইংরেজ কর্মচারী। এই ওয়াটস ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে নবাবের দরবারে নিযুক্ত একজন প্রতিনিধি। রাজদ্রোহের অপরাধে সিরাজউদ্দৌলা তাকে দরবার থেকে বের করে দেন। রাজা রাজবল্লভ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে, নবাব রাজদ্রোহী সভাসদদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, প্রত্যেকের কুকাজের খবর তিনি রাখেন। এই প্রসঙ্গে নবাবের অনুগত মোহনলাল ও মীরমদন নবাবের প্রতি তাদের অটল আনুগত্যের কথা প্রকাশ করে। তারা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে, “আমরা নবাবের নিমক বৃথাই খাই না”। তাদের এই কথায় নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। আর এই কারণেই তিনি নিজের সমর্থক সভাসদদের নিয়ে দরবার ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হন।
৭.২ ‘আমার রাজ্য নাই, তাই আমার কাছে রাজনীতিও নাই আছে শুধু প্রতিহিংসা।’ বক্তা কে? তার প্রতিহিংসার পরিচয় দাও।
উত্তর: বক্তা: ঘসেটি বেগম ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।
তার প্রতিহিংসার পরিচয়: নবাব আলিবর্দি খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশেই বাংলার সিংহাসনের দাবিদার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আলিবর্দির মনোনীত উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হলে ঘসেটি বেগম তা মেনে নিতে পারেননি। তিনি আলিবর্দির অপর দৌহিত্র শওকত জঙ্গকে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে সংঘর্ষের জন্য প্ররোচিত করতে চান। এভাবেই ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ পরিণত হয় সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রের আখড়ায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিস্থিতির জটিলতা বুঝতে পেরে মতিঝিল প্রাসাদ দখল করে নেন এবং ঘসেটি বেগমকে তাঁর মুরশিদাবাদ প্রাসাদে নজরবন্দি করে রাখেন। এর ফলে ঘসেটি বেগম সিরাজের প্রত্যক্ষ শত্রুতে পরিণত হন। ইংরেজরা যখন কাশিমবাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই খবর পেয়ে ঘসেটি বেগম আশা করেছিলেন যে তারা মুরশিদাবাদেও আসবে এবং বাংলার ভাগ্য পরিবর্তন হবে—”ঘসেটির বন্ধন মোচন হবে, সিরাজের পতন হবে…”। ঘসেটি বেগম অভিযোগ করতেন যে, সিরাজই তাঁকে গৃহহারা করেছেন, তাঁর সম্পদ লুট করেছেন এবং তাঁকে একজন দাসীতে পরিণত করেছেন। সিরাজউদ্দৌলা এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিলেন যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কারণেই তাঁকে মতিঝিল প্রাসাদে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। আর এই প্রেক্ষিতেই ঘসেটি বেগম ওই উক্তি করেছিলেন।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ ‘কোনি’ উপন্যাস অবলম্বনে কোনির চরিত্র বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: মতি নন্দীর এই উপন্যাসটি কোনি নামের মেয়েটির জীবনসংগ্রামের কাহিনি বলে চলে। শ্যামপুকুর বস্তিতে মা ও সাত ভাই-বোনের সঙ্গে তার দিনকাল কাটে। স্বভাবে সে একদম ডানপিটে, আর চেহারায় ফুটে ওঠে একরকম পুরুষালি ভাব। চুল ছাঁটা আছে ঘাড় পর্যন্ত। কালো আর হিলহিলে তার শরীরটা কেউটে সাপের মতোই। গঙ্গাবক্ষে আম সংগ্রহ, বিশ ঘণ্টার হাঁটা প্রতিযোগিতা, বাংলার চ্যাম্পিয়ন অমিয়াকে হারানো এবং সবশেষে মাদ্রাজে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া—এসবই তার লড়াকু মানসিকতার প্রমাণ দেয়। পুরো উপন্যাসজুড়ে কোনির এই সংগ্রামী সত্তাটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মাদ্রাজে হিয়া যখন তাকে বলে, “কোনি, তুমি আনস্পোর্টিং,” তখনই সে তার জবাব দিয়ে দেয়। কোনিদের বসবাস চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। তার বিশ্বাস, “বড়লোকরা গরিবদের ঘেন্না করে।” সেই দারিদ্র্য আর ক্ষুধাকে জয় করেই সে নিজেকে অনুশীলনে নিয়োজিত রাখে। লীলাবতীর ‘প্রজাপতি’ দোকানের যাবতীয় ফরমাশ সে খাটে। কোনির সমস্ত অভিমান জড়িয়ে ছিল ক্ষিতীশ সিংহকে ঘিরে। মাদ্রাজ যাওয়ার পথে এবং সেখানে পৌঁছে ক্ষিতীশ ছাড়া অসহায় কোনির মনে প্রবল অভিমান জেগে ওঠে। যখন তাকে বাংলাকে না ভালোবাসার অপবাদ দেওয়া হয়, তখন তার সমস্ত অপমান আর বঞ্চনা গিয়ে জমা হয় অভিমানে। সেই জন্যই হিয়া বা অমিয়াকে হারিয়ে সে তার উত্তর দিতে চেয়েছিল, আর বাংলাকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে সবারই জবাব দিয়েছে। কোনির নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সংগ্রামী ও পরিশ্রমী মানসিকতা এই চরিত্রটিকে করে তুলেছে অনবদ্য।
৮.২ “না। আমি নামব না।” বক্তার এমন অভিমানের কারণ কী? শেষপর্যন্ত কী ঘটল?
উত্তর: মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র কোনির এই উক্তিতে তার প্রতি হওয়া অন্যায়ের জন্যই অভিমান প্রকাশ পেয়েছে, একইসঙ্গে জীবনযুদ্ধে তার দৃঢ়তারও পরিচয় মেলে। কোনি একজন দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাঁতারু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার কোচ ক্ষিতীশ সিংহ এর নির্দেশনায় সে প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করেছিল। অথচ প্রতিযোগিতার সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনে তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে পিছনের সারিতে নামিয়ে দেওয়া হলো। এটি ছিল তার কঠোর পরিশ্রম ও মেধার প্রতি এক চরম অবমাননা। এই অন্যায় আচরণ তার আত্মবিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত হানে। গভীর ক্ষোভ ও অভিমানে আত্মসম্মান প্রকাশ করতে গিয়ে কনি ঘোষণা করে, “না, আমি আর সাঁতার কাটব না।”
শেষমেশ কোচ ক্ষিতীশবাবুর কঠোর কিন্তু অনুপ্রেরণাদায়ী কথায় কোনির মধ্যে হারানো সাহস ফিরে আসে। ক্ষিতীশবাবু তাকে বলেন, হাল ছেড়ে দেওয়া কোনও বিকল্প নয়; বরং নিজের দক্ষতা প্রমাণ করাই হল আসল লক্ষ্য। কোনি সেই রাগ বা অভিমান ভুলে গিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে এবং তার সেরা পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। তার এই জয় প্রমাণ করে যে কঠিন পরিস্থিতিতেও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে যেকোনো বাধা জয় করা সম্ভব। কোনির এই অদম্য মনোবল ও সাফল্য কেবল তার ব্যক্তিগত সংগ্রামেরই প্রতীক নয়, এটি সমাজের সকল সংগ্রামী মানুষের জন্য এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা।
৮.৩ “কম্পিটিশনে পড়লে মেয়েটা তো আমার পা ধোয়া জল খাবে।” বক্তা কে? কী প্রসঙ্গে তার এই উক্তি? এই উক্তিতে বক্তার কীরূপ মনোভাব ফুটে উঠেছে?
উত্তর: মতি নন্দীর ‘কনি’ উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে সাঁতারু অমিয়া বেলাকে এই কথা বলে।
উক্তি: কমলদিঘির পানিতে ক্ষিতীশ সিংহ-এর কাছে সাঁতার শিখছিল কোনি। সেই মুহূর্তে অ্যাপোলো ক্লাব থেকে বেরোল অমিয়া আর বেলা। দুইজনই এককালে ক্ষিতীশের ছাত্রী ছিল, কিন্তু এখন তার প্রতি তাদের মনে শুধুই বিরূপতা। ক্ষিতীশের নতুন শিষ্যা কোনির সাঁতারের কায়দা দেখে তারা শুরু করল উপহাস। আর তখনই অহমিকায় ভরা অমিয়া করল তার সেই উক্তি।
মনোভাব: দীর্ঘদিনের সাঁতারু অমিয়া বঙ্গীয় চ্যাম্পিয়ন। অন্যদিকে, কোনি এইমাত্র সাঁতার শিখতে শুরু করেছে। স্বাভাবিকভাবেই, দুজনের তুলনা করলে অমিয়ার দক্ষতা অনেকটাই বেশি। কিন্তু একজন সাঁতারুর দক্ষতা নিয়ে এমন মন্তব্য করা অমিয়ার ঔদ্ধত্য ও অহংকারকেই প্রকাশ করে। অহংকারই যে পতনের মূল, এই সত্যটি অমিয়া সম্ভবত জানত না। গল্পের শেষে আমরা তারই পতন দেখতে পাব। হরিচরণবাবুর মাধ্যমে তাদের কাছে খবর এসেছিল— ‘ক্ষিদ্দা নাকি জুপিটারকে হারাতে চলেছে ওই মেয়েটির মাধ্যমে।’ একজন অখেলোয়াড় কোনিকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে অমিয়া তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে চেয়েছে। তার এই আচরণ মোটেও খেলোয়াড়সুলভ নয়। এই উক্তির মধ্য দিয়ে অমিয়ার গর্ব ও অহংকার চরমভাবে ফুটে উঠেছে।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো:
The teachers are regarded as the backbone of the society. They build the future citizens of country. They love students as their children. The teachers always encourage and inspire us to be good and great in life.
উত্তর: শিক্ষকদের সমাজের মেরুদণ্ড বলা হয়। তাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলেন। শিক্ষকেরা ছাত্রদের আপন সন্তান হিসেবে ভালোবাসেন। তাঁরা সবসময় আমাদের জীবনে ভালো ও মহান মানুষ হতে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগান।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ কুসংস্কার প্রতিরোধে বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
কুসংস্কার প্রতিরোধে বিজ্ঞানমনস্কতা
রাহুল : শোন অনি, আজকে দেখলাম কেউ অসুস্থ হলে গ্রামের কিছু মানুষ ঝাড়ফুঁক করাচ্ছে। সত্যিই অবাক লাগল।
অনি : হ্যাঁ, এসবই কুসংস্কার। অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত, ঝাড়ফুঁকে কিছুই হয় না।
রাহুল : কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করে এসব করলে নাকি রোগ সেরে যায়।
অনি : আসলে অজ্ঞতার কারণে মানুষ এগুলো মানে। বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে রোগের কারণ জীবাণু, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া। তাই সঠিক ওষুধ ছাড়া রোগ সারবে না।
রাহুল : একদম ঠিক। কুসংস্কারের কারণে অনেক সময় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
অনি : তাই তো বলি, আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে। পড়াশোনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করলে কুসংস্কারের জায়গা থাকবে না।
রাহুল : ঠিকই বলেছ। আমাদের উচিত সচেতনতা ছড়িয়ে অন্যদেরও বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করা।
১০.২ ‘হকার দৌরাত্ম্যে হারিয়ে যাচ্ছে শহরের ফুটপাথ’-এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো
উত্তর:
হকার দৌরাত্ম্যে হারিয়ে যাচ্ছে শহরের ফুটপাথ
নিজেস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৫: আমাদের শহরে দিন দিন হকারদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলেছে। শহরের প্রধান রাস্তা ও ফুটপাথজুড়ে এখন হকারদের অবাধ দখলদারি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফুটপাথে দোকান বসিয়ে তাঁরা নানা পণ্য বিক্রি করছেন। এতে সাধারণ পথচারীরা হেঁটে চলার জায়গা পাচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে অনেকেই রাস্তার গায়ে হাঁটছেন, ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। বিশেষ করে স্কুলগামী শিশু ও বৃদ্ধদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। ট্রাফিক ব্যবস্থাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যদিও প্রশাসন মাঝে মাঝে উচ্ছেদ অভিযান চালায়, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই হকাররা আবার আগের জায়গায় বসে পড়ে। শহরের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। হকারদের জীবিকার সমস্যাকে অস্বীকার করা যায় না, তবে ফুটপাথ মূলত পথচারীদের জন্য। তাই সরকার ও প্রশাসনের উচিত বিকল্প জায়গায় হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, যাতে পথচারীরাও স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারেন এবং শহরের শৃঙ্খলা বজায় থাকে।
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবস্থ রচনা করো:
১১.১ পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার।
উত্তর:
পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার
মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শুদ্ধ বাতাস, বিশুদ্ধ জল, উর্বর মাটি আর শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আজ পরিবেশ ভয়াবহভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে। এই পরিবেশ দূষণ আমাদের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলেছে।
প্রথমত, বায়ুদূষণ পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান রূপ। কলকারখানা, যানবাহনের ধোঁয়া এবং ফসিল জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বাতাসে ক্ষতিকারক গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে। এতে মানুষের ফুসফুসের রোগ, অ্যাজমা, ক্যান্সার ইত্যাদি দেখা দিচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, জলদূষণও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শিল্পকারখানার বর্জ্য, পলিথিন, প্লাস্টিক এবং রাসায়নিক সার-ওষুধ নদী ও পুকুরে পড়ায় জলাশয় বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে মাছসহ জলজ প্রাণীর সংখ্যা কমছে এবং পানীয় জলও অনিরাপদ হয়ে উঠছে।
তৃতীয়ত, ভূমিদূষণও সমান ক্ষতিকর। কৃষিতে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার এবং প্লাস্টিক বর্জ্য জমা হওয়ার কারণে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। বনভূমি ধ্বংসের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা বাড়ছে।
এ ছাড়া শব্দদূষণ ও তেজস্ক্রিয় দূষণও মানুষের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে।
প্রতিকার: পরিবেশ দূষণ রোধে আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রথমত, শিল্পকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্লাস্টিকের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব জিনিস ব্যবহার করা উচিত। তৃতীয়ত, বনভূমি রক্ষা ও ব্যাপক বৃক্ষরোপণ জরুরি। চতুর্থত, নদী-নালা ও জলাশয়ে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে মানুষের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। আইন করে দূষণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
পরিবেশ দূষণ আজ বৈশ্বিক সমস্যা। নিজের স্বার্থে নয়, আগামী প্রজন্মের নিরাপত্তার জন্যও আমাদের পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে পারলেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুষম সহাবস্থান নিশ্চিত হবে।
১১.২ একটি ছেঁড়া জামার আত্মকাহিনি।
উত্তর:
একটি ছেঁড়া জামার আত্মকাহিনি
আমি এক সময় একদম নতুন ছিলাম—রঙিন, ঝকঝকে আর সুন্দর। আমার নরম কাপড়ের গায়ে ফুলের নকশা, চকচকে বোতাম—দেখে যারই চোখে পড়ত, সে বলত, “কি সুন্দর জামা!” আমি ছিলাম এক ছোট্ট ছেলের প্রিয় পোশাক। প্রতি উৎসবে, বিশেষ দিনে সে আমাকে গায়ে দিত ভালোবাসা দিয়ে, আর আমি গর্বে ভরে উঠতাম।
দিন কেটে গেল। একসময় আমার উজ্জ্বলতা ম্লান হতে শুরু করল। বারবার ধোয়ার কারণে রঙ ফিকে হয়ে গেল, আর সেলাইয়ের জায়গাগুলো ঢিলে হয়ে এলো। তারপর একদিন খেলার মাঠে ছেলেটা পড়ে গেল, আমার হাঁটুর পাশে ফেটে গেল এক জায়গা। আমি কেঁদে উঠলাম মনে মনে—জানি, এখন আর আমাকে কেউ আগের মতো ভালোবাসবে না।
মা আমাকে সেলাই করে জোড়া লাগালেও, আগের মতো রূপ আর ফিরল না। ধীরে ধীরে আমি আলমারির কোণে পড়ে রইলাম, নতুন জামাগুলোর ভিড়ে হারিয়ে গেলাম। একদিন মা বললেন, “এই জামাটা এখন খুব পুরনো, এটা ঘর মোছার কাজে লাগবে।” শুনে আমার বুকটা হু-হু করে উঠল। আমি যে একদিন সবার প্রিয় ছিলাম, আজ আমাকে তুচ্ছ মনে হচ্ছে!
কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি পুরোপুরি কঠোর হলো না। একদিন বাড়িতে এক দরিদ্র ভিক্ষুক এল। ছেলেটার মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই জামাটা এখনো পরে চলবে, ওকে দিই।” আমি নতুন করে প্রাণ পেলাম! ওই ভিক্ষুক যখন আমাকে গায়ে দিল, আমি তার মুখে একটুখানি হাসি দেখলাম। বুঝলাম, আমার জীবন শেষ হয়নি—আমি এখন অন্য এক জীবনে নতুন সুখ দিচ্ছি।
আমি শিখলাম—কোনো কিছুই চিরকাল নতুন থাকে না, কিন্তু প্রতিটি জিনিসেরই মূল্য আছে, যদি তা সঠিক কাজে ব্যবহার করা যায়। আমি এখন গর্বিত, কারণ আমি আজও কারও উপকারে আসছি।
১১.৩ বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য।
উত্তর:
বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য
বাংলা প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার ঋতুবৈচিত্র্য। পৃথিবীর অল্প কয়েকটি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ, বিশেষত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ, এমন এক দেশ যেখানে বছরে ছয়টি ঋতু স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই ঋতুগুলো একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং প্রতিটি ঋতু প্রকৃতিকে এক বিশেষ রূপে সাজিয়ে তোলে।
বাংলা বছরের প্রথমে আসে গ্রীষ্ম ঋতু। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড রোদে মাটি ফেটে যায়, নদী শুকিয়ে যায়, চারিদিকে তাপের দাহে ক্লান্তি নেমে আসে। তারপর আসে বর্ষা ঋতু। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আকাশে মেঘ জমে, ধরণি সজীব হয়ে ওঠে, নদী-নালা, পুকুর-ডোবা জলে পূর্ণ হয়। কৃষক এই সময় চাষাবাদে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।
বর্ষার পরে আসে শরৎ ঋতু। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে আকাশ হয় নীল, সাদা মেঘে ভরে ওঠে। ধান পাকে, কাশফুলে মাঠ ভরে যায়। তারপর আসে হেমন্ত ঋতু। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের সুবাসে চারিদিক ভরে ওঠে, পাকা ধানে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে।
এরপর আসে শীত ঋতু। পৌষ-মাঘ মাসে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপে মানুষ, গায়ে চাদর-কম্বল জড়ায়। ভোরের কুয়াশা আর শিশিরবিন্দু প্রকৃতিকে দেয় নতুন রূপ। অবশেষে আসে বসন্ত ঋতু, ফাগুন-চৈত্র মাসে। এ সময় গাছপালা নতুন পল্লবে সেজে ওঠে, ফুলে ফুলে রঙিন হয় বনভূমি। প্রকৃতি যেন হাসির উৎসবে মেতে ওঠে।
বাংলার এই ঋতুচক্র কেবল প্রকৃতির নয়, মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষি, উৎসব, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস—সব কিছুর উপর প্রভাব ফেলে। পয়লা বৈশাখ, পিতৃপক্ষ, নবনীৎ উৎসব, পৌষপার্বণ, হোলি—সবই ঋতুভিত্তিক।
বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য প্রকৃতির এক অপূর্ব দান। এই পরিবর্তনশীল রূপ আমাদের জীবনে আনন্দ, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য এনে দেয়। তাই বলা যায়— “বারো মাসে তেরো পার্বণ, এই বাংলারই গর্ব।”
১১.৪ একটি বীভৎস ট্রেন দুর্ঘটনা।
উত্তর:
একটি বীভৎস ট্রেন দুর্ঘটনা
জীবনের পথে দুর্ঘটনা অনিবার্য হলেও কিছু দুর্ঘটনা মানুষের মনে চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়। তেমনই এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হলো একটি ট্রেন দুর্ঘটনা, যা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।
গত বছর আমি আমার কাকুর বাড়ি যাচ্ছিলাম শালিমার এক্সপ্রেসে। সকালবেলায় ট্রেন ছাড়ার পর সবাই আনন্দে মেতে ছিল। হঠাৎ দুপুরবেলায় ট্রেন যখন একটি রেলক্রসিং অতিক্রম করছিল, তখনই হঠাৎ একটি ট্রাক গেট ভেঙে ট্র্যাকে উঠে আসে। চালক ব্রেক কষলেও সময়মতো থামাতে পারেননি। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনটি ট্রাকের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তীব্র শব্দে চারপাশ কেঁপে ওঠে। কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে উল্টে যায়। ভেতরে চিৎকার, কান্না, আহাজারিতে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে।
আমি ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। চারপাশে আহত যাত্রীদের রক্তাক্ত দেহ, কেউ কেউ বগির ভেতরে আটকে ছিল। স্থানীয় মানুষ ও রেলকর্মীরা ছুটে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। কিছু সময় পর পুলিশ ও দমকল বাহিনী এসে আহতদের হাসপাতালে পাঠায়। আমি নিজেও সামান্য আহত হয়েছিলাম, কিন্তু আশেপাশের ভয়াবহ দৃশ্য আমাকে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাত্রীদের মধ্যে অনেকের অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। সন্ধ্যার খবরের কাগজে দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়—দশজনের মৃত্যু ও বহু আহত। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দেখে বুঝেছিলাম, জীবনের কত বড় অনিশ্চয়তা লুকিয়ে আছে প্রতিটি মুহূর্তে।
এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ ছিল মানবীয় অবহেলা। গেটম্যান তার দায়িত্বে ছিলেন না, আর ট্রাকচালকও অসতর্কভাবে আচরণ করেছিলেন। যদি তারা সামান্য সচেতন হতেন, তবে এত প্রাণহানি ঘটত না।
এই ঘটনার পর থেকে আমি উপলব্ধি করেছি যে, দুর্ঘটনা এড়াতে আমাদের সকলের সচেতন হওয়া জরুরি। রেলক্রসিংয়ে নিয়ম মেনে চলা, সিগন্যাল মানা এবং দায়িত্বশীলভাবে আচরণ করাই পারে এ ধরনের বিপদ রোধ করতে।
এই বীভৎস ট্রেন দুর্ঘটনা আমার মনে গভীর দুঃখ ও ভয় রেখে গেছে। প্রতিটি মানুষ যদি সতর্ক থাকে এবং নিয়ম মেনে চলে, তবে এ ধরনের দুর্ঘটনা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।