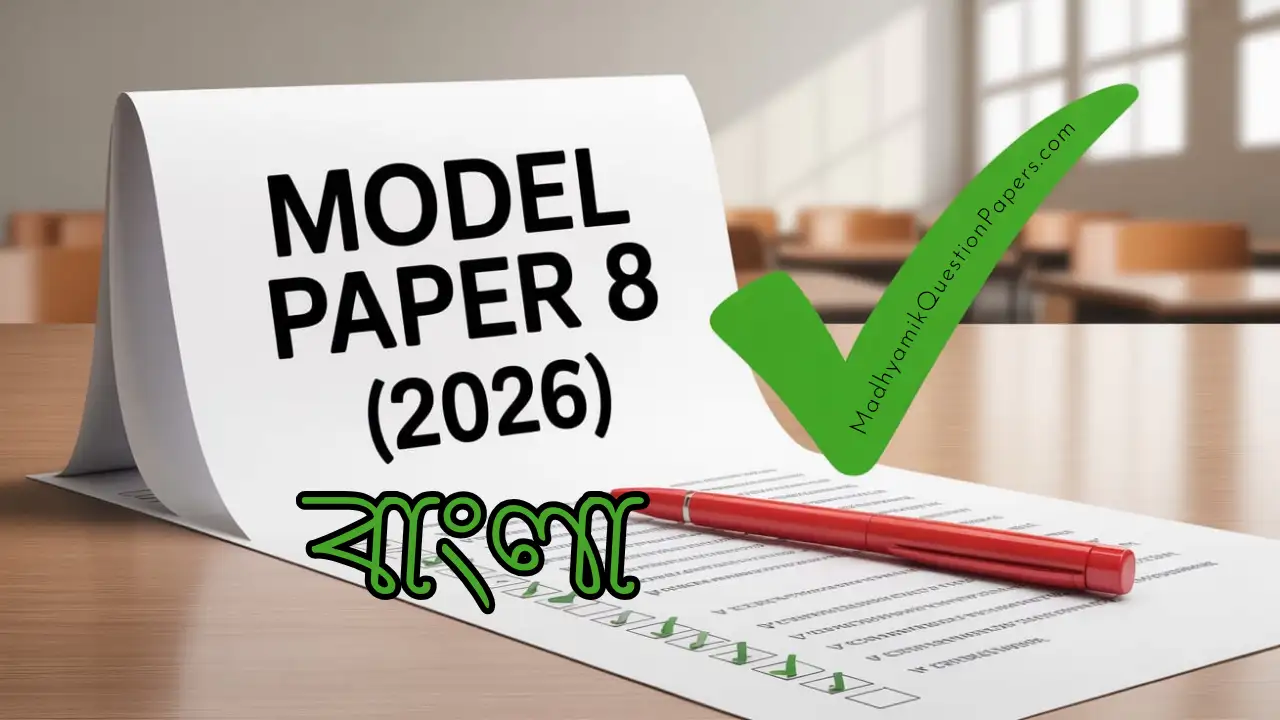আপনি কি ২০২৬ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 8 এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 8-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৬ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ “বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।” বুড়োমানুষ কে?-
(ক) জগদীশবাবু
(খ) রামদাস তলওয়ারকর
(গ) নিমাইবাবু
(ঘ) তেওয়ারি
উত্তর: (গ) নিমাইবাবু
১.২ “শোনা মাত্র অমৃত ফতোয়া জারি করে দিল,” ‘ফতোয়া’ শব্দের অর্থ হল-
(ক) প্রতিবাদ
(খ) চিৎকার
(গ) রায়
(ঘ) দাবি
উত্তর: (গ) রায়
১.৩ নদীর বিদ্রোহের কারণ কী? –
(ক) অতিবৃষ্টি
(খ) নদীতে বাঁধ দেওয়া
(গ) না পাওয়ার বেদনা
(ঘ) উপর দিয়ে ট্রেন চলা
উত্তর: (খ) নদীতে বাঁধ দেওয়া
১.৪ ‘তারপর যুদ্ধ এল’
(ক) পাহাড়ের আগুনের মতো
(খ) রক্তের সমুদ্রের মতো
(গ) আগ্নেয়পাহাড়ের মতো
(ঘ) রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড়ের মতো
উত্তর: (ঘ) রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড়ের মতো
১.৫ বিশ্বমায়ের আসন পাতা আছে-
(ক) জগতের ওপর
(খ) মহাবিশ্বের ওপর
(গ) মহাসমুদ্রের ওপর
(ঘ) বাহুর ওপর
উত্তর: (ঘ) বাহুর ওপর
১.৬ ঋষিবালকের মাথায় গোঁজা
(ক) ফুল
(খ) পাগড়ি
(গ) হাঁসের পালক
(ঘ) ময়ূর পালক
উত্তর: (ঘ) ময়ূর পালক
১.৭ ‘কঙ্কাবতী’ ও ‘ডমরুধর’-এর স্বনামধন্য লেখকের নাম-
(ক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
(খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
(ঘ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তর: (গ) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
১.৮ ‘বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে আর একটি দোষ’ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক কোন্ প্রবাদের উল্লেখ করেছেন?-
(ক) অরণ্যে রোদন
(খ) অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী
(গ) হাতের পাঁচ
(ঘ) হযবরল
উত্তর: (খ) অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী
১.৯ ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে উল্লিখিত নবাগত রাসায়নিক বস্তু—
(ক) টাইফয়েড
(খ) জিওমেট্রি
(গ) প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন
(ঘ) ম্যালভাসি
উত্তর: (গ) প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন
১.১০ বাংলা ব্যাকরণে অ-কারক পদের সংখ্যা
(ক) একটি
(খ) দুটি
(গ) তিনটি
(ঘ) চারটি
উত্তর: (খ) দুটি
১.১১ ‘বিভক্তি’ শব্দের অর্থ কী?
(ক) বিভাজন
(খ) সংকোচন
(গ) প্রসারণ
(ঘ) সংযোজন
উত্তর: (ক) বিভাজন
১.১২ ‘এত বেশি মায়া একটু অস্বাভাবিক।’ নিম্নরেখ পদটি হল
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস
(খ) নঞ্চ তৎপুরুষ
(গ) উপপদ তৎপুরুষ
(ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস
উত্তর: (খ) নঞ্চ তৎপুরুষ
১.১৩ উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে বলে
(ক) একদেশী তৎপুরুষ
(খ) অলোপ তৎপুরুষ
(গ) উপপদ তৎপুরুষ
(ঘ) ব্যাপ্তি তৎপুরুষ
উত্তর: (গ) উপপদ তৎপুরুষ
১.১৪ ‘হরিদার কাছে আমরাই গল্প করে বললাম,’- এই বাক্যের উদ্দেশ্য হল-
(ক) হরিদা
(খ) আমরাই
(গ) বললাম
(ঘ) গল্প করে
উত্তর: (খ) আমরাই
১.১৫ বাক্যের অর্থের পূর্ণতা প্রকাশ করে-
(ক) নামপদ
(খ) ক্রিয়া
(গ) সমাপিকা ক্রিয়া
(ঘ) অব্যয়
উত্তর: (গ) সমাপিকা ক্রিয়া
১.১৬ মহাশয়ের কী করা হয়? এটি কোন্ বাচ্যের দৃষ্টান্ত?
(ক) কর্তৃবাচ্য
(খ) কর্মবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (গ) ভাববাচ্য
১.১৭ ‘হ’ ধাতুজাত ক্রিয়া বসে কোন্ বাচ্যে?
(ক) কর্তৃবাচ্যে
(খ) কর্মবাচ্যে
(গ) ভাববাচ্যে
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্যে
উত্তর: (গ) ভাববাচ্যে
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ “আর সেই সুযোগেই দেখতে পাচ্ছে তপন,” কোন্ সুযোগে, তপন কী দেখতে পাচ্ছে?
উত্তর: নিজের ছোট মেসো একজন লেখক হওয়ায় তপন উপলব্ধি করল যে, লেখক মানেই কোনো দেবদূত বা আকাশ থেকে পড়া অলৌকিক সত্তা নন; বরং তিনি তার মতোই একজন সাধারণ মানুষ।
২.১.২ ‘একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল।’ কোথায়, কেন আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল?
উত্তর: একদিন দুপুরে চকের বাসস্ট্যান্ডে হঠাৎ একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল।
সেখানে এক ভয়ংকর পাগলের দেখা মেলে, যার চোখ লাল, মুখ দিয়ে লালা ঝরছে, পরনে ছেঁড়া কম্বল আর গলায় টিনের কৌটোর মালা। সে ইট হাতে বাসের যাত্রীদের দিকে তেড়ে গেলে সবাই চিৎকার করে ওঠে। কেউ কেউ ভয়ে তাকে পয়সাও দিতে থাকে। এভাবেই সেদিন আতঙ্কের সূত্রপাত হয়। কিন্তু বাস ড্রাইভার কাশীনাথ বুঝে ফেলেছিল যে লোকটি আসলে বহুরূপী হরিদা।
২.১.৩ ভামো যাত্রায় ট্রেনে অপূর্বের কে কে সঙ্গী হয়েছিল?
উত্তর: ভামো নগর অভিমুখে যাত্রাকালে অপূর্বর সঙ্গে ছিলেন আরদালি ও অফিসের একজন হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ পেয়াদা।
২.১.৪ ‘অদল-বদলের গল্প’ গ্রাম-প্রধানের কানে গেলে তিনি কী ঘোষণা করেছিলেন?
উত্তর: “অদল-বদলের গল্প” গ্রামপ্রধানের কানে পৌঁছতেই তিনি একটি ঘোষণা দিলেন। তাঁর নির্দেশ ছিল, সেদিন থেকে সবাই অমৃতকে ‘অদল’ এবং ইসাবকে ‘বদল’ নামে ডাকবে।
২.১.৫ “লোভটা সে সামলাইতে পারিল না,” কোন্ লোভের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: এখানে ‘লোভ’ শব্দটি দিয়ে নদেরচাঁদের উন্মত্ত নদীর সাথে খেলার যে অপরিসীম টান, সেটিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ ‘আমি তাকে ছেড়ে দিলাম’ কথক কাকে ছেড়ে দিলেন?
উত্তর: পাবলো নেরুদার ‘অসুখী একজন’ কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়তমাকে ত্যাগ করে চলে যান।
২.২.২ “আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।” একথা বলার কারণ কী?
উত্তর: বেঁধে বেঁধে থাকার উদ্দেশ্য বিপদকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করার শক্তি সংগ্রহ করা।
২.২.৩ ‘সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই’ সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তে কী ঘটেছিল?
উত্তর: আফ্রিকা যখন অত্যাচার ও অপমানের শিকার হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সমুদ্রপারের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে মন্দিরে মন্দিরে পূজার ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল। শিশুরা তখন মায়ের আদরে খেলায় মগ্ন, আর কবিগণ নিবেদিত ছিলেন সুন্দরের সাধনায়।
২.২.৪ “তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ।” কন্যা কোথায় থাকে?
উত্তর: ‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশে সমুদ্ররাজকন্যা পদ্মার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি এক পাহাড়ের পাশে অবস্থিত ফুল-ফলে সুশোভিত ও বিচিত্র প্রাসাদময় এক বাগানে বাস করতেন।
২.২.৫ “গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে” ‘গানের বর্ম’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতার আলোচিত অংশটিতে কবি বলতে চেয়েছেন, অস্ত্রের আতঙ্ক ও পেশিশক্তির দম্ভের বিরুদ্ধে মানুষের শুভবোধ ও শুভচেতনাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা। গানের বর্ম’ বলতে কবি এই কথা বুঝিয়েছেন।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘সোনার দোয়াত কলম যে সত্যই হতো;’ – বক্তা সোনার দোয়াত কলমের কথা কীভাবে জেনেছিলেন?
উত্তর: হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ রচনাটি থেকে প্রমাণ মেলে, সুভো ঠাকুরের দোয়াতের সংগ্রহ দেখার পরই লেখকের নিশ্চয়তা হয় যে সোনার দোয়াতকলমের অস্ত্বিত্ব বাস্তবিকই ছিল।
২.৩.২ “একজন বিদেশি সাংবাদিক লিখেছিলেন…”- কী লিখেছিলেন?
উত্তর: সম্প্রতি এক বিদেশি সাংবাদিকের লেখা থেকে জানা যায়, কলকাতার চৌরঙ্গি এলাকায় প্রতিটি তিনজন ফেরিওয়ালার মধ্যে একজনকে কলম বিক্রি করতে দেখা যায়।
২.৩.৩ লক্ষণা বলতে কী বোঝো?
উত্তর: লক্ষণা হলো এমন একটি অর্থপ্রকাশের প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো শব্দ তার মুখ্য বা প্রাথমিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে একটি গৌণ বা সম্পৃক্ত অর্থে প্রযুক্ত হয়। এটি তখনই ঘটে যখন সেই গৌণ অর্থই ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুখ্য অর্থের চেয়ে বেশি প্রচলিত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।
২.৩.৪ ‘এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত।’ কোন্ কথা সকল লেখককে মনে রাখতে বলেছেন প্রাবন্ধিক?
উত্তর: বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষা যেন সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল হয়, বাংলায় এমন রচনা লিখতে গেলে এই মূলনীতিটি লেখকদের সর্বদা স্মরণে রাখা একান্ত প্রয়োজন।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ শূন্য বিভক্তি কাকে বলে?
উত্তর: যে বিভক্তি শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে তাকে পদে পরিণত করে, কিন্তু নিজে দৃশ্যমান রূপে প্রকাশ পায় না এবং শব্দটির মূল রূপেরও কোনো পরিবর্তন ঘটায় না, তাকেই শূন্য বিভক্তি বলে।
শূন্য বিভক্তির একটি উদাহরণ হল – বাবা অফিসে গেছেন।
২.৪.২ শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে। নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
উত্তর: শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে এখানে ‘মায়ের কোলে’ পদটির কারক হল – অধিকরণ কারক এবং বিভক্তি হল – সপ্তমী বিভক্তি।
২.৪.৩ একশেষ দ্বন্দু সমাসের একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: উদাহরণ: রাম-লক্ষ্মণ
এখানে “রাম-লক্ষ্মণ” বলতে মূলত রামকেই বোঝানো হয়েছে। লক্ষ্মণ গৌণ।
অর্থাৎ, এই সমাসে একটিমাত্র (রাম) পদই মুখ্য, তাই এটি একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস।
২.৪.৪ ‘পীতাম্বর’ কথাটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: ‘পীতাম্বর’ কথাটির ব্যাসবাক্য হল – পীত যে অম্বর (বস্ত্র) এবং সমাসের নাম হল – কর্মধারয় সমাস।
২.৪.৫ আর কোনো ভয় নেই। প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিবর্তন করো।
উত্তর: আর কোনো ভয় নেই এটিকে প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিবর্তন করলে হবে – আর কোনো ভয় নেই কি?
২.৪.৬ একটি জটিল বাক্যের উদাহরণ দাও।
উত্তর: একটি জটিল বাক্যের উদাহরণ হল – যেহেতু আজ বৃষ্টি হচ্ছিল, সেহেতু আমি বাইরে যাইনি।
২.৪.৭ ‘মাছ আকাশে ওড়ে’ বাক্য নির্মাণের কোন্ শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে?
উত্তর: “মাছ আকাশে ওড়ে” – এই বাক্যটি আমাদের সাধারণ বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠিকে লঙ্ঘন করে। ভাষার একটি মূলনীতি হলো, তা প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যৌক্তিক হবে। আমাদের জানামতে, মাছের বাস জলেই এবং তা উড়তে অক্ষম। তাই এই উক্তিটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক বলে প্রতিভাত হয়। তবে কবিতা, রূপকথা বা সাহিত্যের মতো শিল্পমাধ্যমে, রূপক বা কাল্পনিক অভিব্যক্তি হিসাবে এ ধরনের বাক্য ব্যবহৃত হতে পারে; কিন্তু সাধারণ বা সরল কথোপকথনে এটি একটি ত্রুটিসূচক বাক্য হিসেবে গণ্য হয়।
২.৪.৮ ‘এসো যুগান্তের কবি,’ ভাববাচ্যে পরিণত করো।
উত্তর: ‘এসো যুগান্তের কবি,’ এটিকে ভাববাচ্যে পরিণত করলে হবে – যুগান্তের কবির প্রতি আহ্বান জানানো হলো।
২.৪.৯ কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের মধ্যে একটি পার্থক্য দেখাও।
উত্তর:
| কর্তৃবাচ্য | কর্মবাচ্য |
|---|---|
| বাক্যটি কর্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়। কর্তাই এখানে মুখ্য। | বাক্যটি কর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়। কর্মই এখানে প্রধান। |
২.৪.১০ গল্পটা সবার জানা। কর্মবাচ্যে রূপান্তর করো।
উত্তর: গল্পটা সবার জানা এটিকে কর্মবাচ্যে রূপান্তর করলে হবে – সবার দ্বারা গল্পটা জানা।
৩। প্রসজ্ঞা নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ “অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল,” অপূর্ব কীসে সম্মত হয়েছিল? সম্মতি জানানোর কারণ কী?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর লেখা ‘পথের দাবী’ গল্পে অফিসের বড়োসাহেবের নির্দেশে অপূর্ব ভামো শহর যেতে সম্মত হয়েছিল।
অফিসের বড়োসাহেব অপূর্বকে জানিয়েছিলেন যে ভামো অফিসে কোনো শৃঙ্খলা নেই। এর পাশাপাশি ম্যান্ডালে, শোএবো ও মিথিলার অফিসেও অনিয়মের কথা শোনা গেছে। তাই বড়োসাহেব অপূর্বকে সমস্ত শাখা অফিস পরিদর্শনের নির্দেশ দেন, কারণ তার অনুপস্থিতিতে অপূর্বকেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। নানা কারণে রেঙ্গুনে অপূর্বর মনেও একরকম অস্বস্তি কাজ করছিল। তাই তিনিও রেঙ্গুনের বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। বড়োসাহেবের আদেশ পেয়ে অপূর্ব ভামো নগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।
৩.১.২ “একটা উন্মাদ পাগল;” ‘পাগল’-টি কে? তার পাগলামির বিবরণ দাও।
উত্তর: সুবোধ ঘোষ এর লেখা বহুরূপী গল্পে পাগলটি হল বহুরূপী বেশধারী হরিদা।
একদিন দুপুরবেলা চকের বাসস্ট্যান্ডে এক অভূতপূর্ব আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে হঠাৎই আবির্ভূত হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর চেহারার পাগল। তার চোখ দুটো ছিল টকটকে লাল, আর মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরছিল। কোমড়ে জড়ানো ছিল ছেঁড়া একটি কম্বল, আর গলায় পরেছিল টিনের কৌটোর মালা। হাতে একটি ভারী ইট তুলে নিয়ে সে বাসের যাত্রীদের দিকে তেড়ে যাচ্ছিল। দৃশ্য দেখে যাত্রীরা চিৎকার করে উঠছিল, কেউ কেউ ভয়ে তার দিকে দুই-এক পয়সাও ছুঁড়ে মারছিল। এইভাবেই বাসস্ট্যান্ডে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে বাস ড্রাইভার কাশীনাথ ধন্দে পড়েননি; সে তাকে চিনতে পেরেছিল – লোকটা কিন্তু আসলে বহুরূপী হরিদা ছাড়া আর কেউ নয়।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “এল মানুষ-ধরার দল”- ‘মানুষ-ধরার দল’ কোথায় এল? তাদের ‘মানুষ-ধরার দল’ বলার কারণ কী?
উত্তর: মানুষ-ধরার দল আফ্রিকায় আসার কথা বলা হয়েছে।
আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে উক্ত মন্তব্যটি করা হয়েছে ইউরোপীয় উপনিবেশকারী দেশগুলোর প্রসঙ্গে। আফ্রিকা মহাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ে, উন্নত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো এই বিশাল ভূখণ্ডটিকে অরণ্যাবৃত ও অনুন্নত মনে করে বিশেষ গুরুত্ব দিত না; তারা এই নবগঠিত মহাদেশকে উপেক্ষাই করত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিপুল মানবসম্পদের প্রতি তাদের আগ্রহ জন্মায়। সর্বপ্রথম তারা আফ্রিকাকে চিহ্নিত করে একটি ক্রীতদাস সংগ্রহের বিশাল ক্ষেত্র হিসেবে। ‘লোহার হাতকড়ি’ নিয়ে এসে তারা আফ্রিকাবাসীদের বন্দি করে নিয়ে যেত। সেজন্যই তাদের ‘মানুষ ধরার দল’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।
৩.২.২ “ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।” ‘রিপুকুল’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? এখানে কোন অপবাদের কথা বলা হয়েছে, তা কবিতা অবলম্বনে লেখো।
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর লেখা ‘অভিষেক’ কবিতায় ‘রিপুকুল’ বলতে রামচন্দ্রের সৈনদলকে বোঝানো হয়েছে।
“মেঘনাদবধ কাব্য”-এর প্রথম সর্গ ‘অভিষেক’-এ দেখা যায়, ইন্দ্রজিৎ প্রমোদকাননে বিলাসে মগ্ন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হন লক্ষ্মী এবং তাকে তাঁর পিতা বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শোনান। এই সংবাদ শুনে ইন্দ্রজিতের মনে হয়, রামচন্দ্রের সৈন্যরা লঙ্কা অবরোধ করে রাক্ষসবংশের গৌরব নষ্ট করছে – এমন সময় তার এই বিলাসিতায় মত্ত থাকা নিন্দনীয়। লক্ষ্মীর কাছ থেকে তিনি আরও জানতে পারেন যে, তিনি প্রমোদকাননে আত্মহারা থাকায়, তার বৃদ্ধ পিতা রাবণ নিজেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইন্দ্রজিৎ ভাবেন, তিনি মতো সক্ষম পুত্র বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি রাজা রাবণকে যুদ্ধে যেতে হয়, সেটা তার জন্য চরম অপমান। পিতার এই অবস্থার জন্য তিনি নিজেকেই দায়ী করেন এবং তার এই আচরণকে লঙ্কার রাজবংশের জন্য ‘অপবাদ’ বলে মনে করেন।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্প অনুসরণে তপনের জ্ঞানচক্ষু কীভাবে উন্মীলিত হয়েছিল, তা আলোচনা করো।
উত্তর: তপনের ধারণা ছিল, লেখকেরা অন্য জগতের মানুষ। কিন্তু তার ছোটোমেসোর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর আচার-আচরণ দেখে সে বুঝতে পারে যে লেখকেরাও সাধারণ মানুষের মতোই। সেই মুহূর্তেই যেন তার চোখ খুলে যায়; যদিও আসলে সত্যিকারের দৃষ্টি খুলেছিল অনেক পরে। তপন সারাদিনে যা লিখেছিল, তার ছোটোমাসি সেটি একরকম জোর করেই তার মেসোমশাইকে দেখান। ছোটোমেসো গল্পটির প্রশংসা করেন, কিন্তু মত দেন যে এটিতে কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন। তিনি গল্পটি ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেবেন বলেও আশ্বাস দেন। নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখার জন্য তপন উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুদিন পর ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় সত্যিই তার গল্পটি বের হয়। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখে তপন এক অদ্ভুত আনন্দে ভেসে যায়। কিন্তু যখনই সে সবার কাছে গল্পটি পড়ে শোনায়, তখনই আবিষ্কার করে যে ছাপা গল্পটির সঙ্গে তার আসল লেখার কোনও মিলই নেই। পুরো লেখাটাই তার মেসোমশাই বদলে দিয়েছেন। লজ্জা, অপমান ও দুঃখে তপন ভেঙে পড়ে। এবারই যেন তার সত্যিকারের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। নিজের সৃষ্টির ওপর তার মালিকানাবোধ জন্ম নেয়। সে দৃঢ় সংকল্প করে যে শুধুমাত্র নিজের লেখাই সে ছাপাবে, অন্যের দয়া বা অনুগ্রহ সে গ্রহণ করবে না।
৪.২ “খাঁটি মানুষ তো নয়, এই বহুরুপীর জীবন এর বেশি কী আশা করতে পারে?” বক্তা কে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, বক্তার এই আক্ষেপ কতখানি যথার্থ তা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পের ওই অংশে বক্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন হরিদা।
পেশায় বহুরূপী হরিদা বিরাগী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে জগদীশবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন প্রচুর অর্থলাভের আশায়। তাঁর সেই বেশভূষা ও কথাবার্তার ভঙ্গি জগদীশবাবুকে মুগ্ধ করেছিল; তিনি হরিদার ছদ্মবেশ টেরই পাননি। তাই, প্রণামি স্বরূপ তিনি হরিদাকে অর্থ দিতে চাইলে, হরিদা তখন সন্ন্যাসীর ভূমিকায় সম্পূর্ণরূপে ডুবে থাকায়, একপ্রকার উদাসীনভাবেই সেই টাকা ফেলে আসেন। কথক ও তাঁর বন্ধুরা হরিদার এই ব্যবহার মেনে নিতে পারলেন না। তখন হরিদা ব্যাখ্যা করেন যে, টাকা নিলে তাঁর ‘ঢং’ অর্থাৎ অভিনয় নষ্ট হয়ে যেত। আরও বলেন, বকশিশ নেওয়ার জন্য তিনি পরে আলাদা করে জগদীশবাবুর কাছে যাবেন। একজন বহুরূপী হিসেবে, তিনি মাত্র আট-দশ আনা অর্থই নিজের প্রাপ্য বলে মনে করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, একজন ‘খাঁটি মানুষ’, যে তার জীবন ও দর্শনে একনিষ্ঠ, তার জীবনের দাবি-দাওয়া অনেক বেশি হতে পারে। কিন্তু হরিদা নিজেকে শুধুই একজন বহুরূপী মনে করেন, যার কাজ নকল করা। এই পেশার আড়ালে তাঁর ভিতরের সত্যিকারের মানুষটি সমাজের চোখে হারিয়ে গিয়েছে—এই গভীর বেদনাই ফুটে উঠেছিল হরিদার কথায়। ‘আমি খাঁটি মানুষ নই’—এই স্বীকারোক্তিটাই যেন একজন সারাজীবন খাঁটি মানুষের করুণ বিলাপ।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ “আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায়।” অপেক্ষায় থাকা এই নারীর মধ্যে দিয়ে কবি যে মানবীয় ভালোবাসার অনির্বাণ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলে ধরেছিলেন, তা পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: পাবলো নেরুদার ‘অসুখী একজন’ কবিতায় কবি যুদ্ধের পরবর্তীতে প্রেমের বিস্তারকে চিত্রিত করেছেন।
কবির প্রস্থান – মুক্তির ডাকে সাড়া দিয়ে একজন বিপ্লবীর যেমন তার সংসার, পরিবার-পরিজনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হয়।
প্রিয়তমা – কবির অতি আপনজন এই বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারেন না। তিনি অপেক্ষায় থাকেন। সপ্তাহ শেষ হয়ে বছর পেরিয়ে যায়, তবুও তার প্রতীক্ষার অবসান হয় না।
যুদ্ধের বিভীষিকা – যুদ্ধ শুরু হয়। সাজানো-গোছানো শহর পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। মানুষ গৃহহারা হয়, শিশুহত্যার মতো নৃশংস ঘটনা ঘটে। ভেঙে পড়ে মন্দিরের দেবমূর্তি।
ধ্বংসের চিত্র – যে বিপ্লবী যুদ্ধে গিয়েছিল, তার স্মৃতিচিহ্নগুলিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কথকের সুন্দর বাড়ি, বারান্দার ঝুলন্ত খাট— সবকিছুই ধ্বংস হয়। শহর পরিণত হয় কয়লা, বাঁকা লোহার ফ্রেম আর পাথরের টুকরোয় ভরা এক বিরান ভূমিতে। রক্তের শুকনো দাগ ধ্বংসের উন্মত্ত রূপকে আরও প্রকট করে তোলে।
অম্লান প্রেম – কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও পাথরের গায়ে আঁকা ফুলের মতোই অক্ষয় থাকে প্রেম। কবির প্রিয়তমার প্রতীক্ষার কোনো শেষ নেই। কারণ যুদ্ধ সম্পদ ধ্বংস করতে পারে, প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে না।
৫.২ “অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো পায়ে” কার উদ্দেশে এই আবেদন? আবেদনটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতার মাধ্যমে জয় গোস্বামী যুদ্ধপিপাসু মানুষদের উদ্দেশে শান্তির জন্য এক মর্মস্পর্শী আবেদন রেখেছেন।
ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি জয় গোস্বামী সৃষ্টিশীলতাকেই প্রতিরোধের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সঙ্গীতের সুরে মিলে যায় সহস্র কণ্ঠস্বর। কখনো তা হৃদয় শুদ্ধির মাধ্যম, কখনো বা প্রতিবাদের ধারালো অস্ত্র। প্রতিকূল শক্তির মুখোমুখি হলে গানই মানুষকে দেয় অফুরন্ত সাহস, দেয় একসাথে জোট বাঁধার প্রেরণা। অস্ত্রের বিরুদ্ধে এই গানকেই আঁকড়ে ধরে কবি অনায়াসে তাড়িয়ে দিতে পারেন বুলেট। গানই সেই নিরাপদ আশ্রয়, যা হিংসার পরিসমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম। নানান হিংসার মোকাবিলায় একটি গানই হয়ে ওঠে কবি ও শিল্পীর ব্যক্তিগত জবাব। কবির কাছে গান এক সুরক্ষা-বর্ম, যা পরে তিনি প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকানোর শক্তি অর্জন করেন। রক্তপাতের পথে না গিয়ে অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করাই তাঁর লক্ষ্য; বরং তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন এক শৈল্পিক ও নান্দনিক প্রতিরোধ। হিংসা আর সংঘাতের এই বিশ্বে গানের অমিত শক্তিই মানুষকে এক সূত্রে বাঁধে, তাদের আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত করে। এই শক্তিই কবিকে নতজানু হতে শিখিয়েছে গানের কাছে। তাই তিনি গানের বর্ম পরেই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে চেয়েছেন।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে লেখক কলমের যে অতীত ও বর্তমান রূপের কথা বলেছেন, তার সম্পর্কে লেখো।
উত্তর: “হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ দেশ-বিদেশে কলমের বিবর্তনের এক চিত্র পাঠকের সামনে এঁকেছেন। যিশুখ্রিষ্টের জন্মেরও আগে প্রাচীন মিশরে নলখাগড়া ভেঙে, তাকে ভোঁতা করে তুলি বানিয়ে লেখার কথা তাঁর বর্ণনায় উঠে এসেছে। ফিনিশিয়ায় তৈরি হত হাড়ের কলম। প্রাচীন রোমানরা ব্যবহার করত ব্রোঞ্জের একটি শলাকা, যার নাম ছিল ‘স্টাইলাস’। চীনে লেখার কাজে ব্যবহৃত হত তুলি। আমাদের এখানে, এই বাংলায়, চালু ছিল বাঁশের কঞ্চি, খাগের কলম আর পাখির পালকের কলম। রোগা বাঁশের কঞ্চি কেটে তার মুখ চিরে তৈরি করা হত বাঁশের কলম। এখন এমন কলমের ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না। খাগের কলম এখন শুধু সরস্বতী পূজোর সময়ই দৃষ্টিগোচর হয়। ব্রিটিশ আমলে জনপ্রিয় ছিল পাখির পালকের কলম, যাকে ডাকা হত ‘কুইল পেন’ নামে। এরপরের পর্যায় হলো ফাউন্টেন পেনের উদ্ভব। লুইস এডসন ওয়াটারম্যানের হাতে আবিষ্কৃত ফাউন্টেন পেন অন্যান্য সব কলমকে পিছনে ফেলে নিজের স্থান করে নেয়। পার্কার, শেফার, সোয়ান-এর মতো নামকরা ব্র্যান্ডের ফাউন্টেন পেন বাজারে আসতে থাকে। কিন্তু ফাউন্টেন পেনকেও একদিন পথ ছাড়তে হয় বলপেন বা ডটপেনের কাছে। আর সেই বলপেন বা ডটপেনও আজ কম্পিউটার ও ডিজিটাল যুগের আবির্ভাবে বিলুপ্তির পথে।
৬.২ ‘পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য।’ লেখকের এমন মন্তব্যের কারণ কী?
উত্তর: বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের পাঠকদের মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণির পাঠক হলেন যাঁরা ইংরেজি জানেন না কিংবা সামান্য জানেন; দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন যাঁরা ইংরেজিতে দক্ষ এবং ইংরেজি ভাষায় লেখা কিছু বিজ্ঞানগ্রন্থও তাঁরা পড়েছেন। লেখকের মতে, পাশ্চাত্যের মানুষের তুলনায় এ দেশের মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণাগুলোর সঙ্গে পরিচয় ছাড়া কোনো বৈজ্ঞানিক রচনা বোঝা দুষ্কর। ইউরোপ-আমেরিকায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখা সহজ, কারণ সেখানকার সাধারণ মানুষ তা সহজেই বুঝতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট তেমন সহজ নয়। এখানে বড়দের জন্যও বিজ্ঞান লিখতে হলে প্রাথমিক ধারণা দিয়েই শুরু করতে হয়, তবেই সেটি বোধগম্য হয়। বাংলায় বিজ্ঞান লিখতে চাইলে এবং পাঠকের কাছে তা জনপ্রিয় করতে হলে এই সত্য মেনে চলতে হবে। বিজ্ঞানশিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতেই প্রাবন্ধিক এই মতামত দিয়েছেন। এ কথা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বিজ্ঞানশিক্ষা সঠিকভাবে ছড়িয়ে না পড়লে বিজ্ঞানসাহিত্যেরও উন্নতি সম্ভব নয়।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “মুন্সিজি, এই পত্রের মর্ম সভাসদদের বুঝিয়ে দিন।”- কে, কাকে পত্র লিখেছিলেন? এই পত্রে কী লেখা ছিল?
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের উদ্ধৃতিতে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের একটি পত্রের কথা বলা হয়েছে, যা তিনি সিরাজের দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটস-এর কাছে লিখেছিলেন।
নবাব সিরাজউদ্দৌলা মন্তব্য করেন যে, ইংরেজদের অপকর্ম সভ্যতা ও শিষ্টাচারের সকল সীমানা অতিক্রম করেছে। তিনি এই প্রসঙ্গে ওয়াটসন কর্তৃক প্রেরিত এক পত্রের কথা উল্লেখ করেন। নবাব তার মুনশীকে উক্ত পত্রটি আনার নির্দেশ দিলে, মুনশী তা ওয়াটসনের হাতে তুলে দেন। প্রথমে ওয়াটসনকে দিয়ে পত্রটির সমাপনী অংশ পড়ানোর পর, দরবারের সকলের বোঝার সুবিধার্থে মুনশীকে এর বাংলা অনুবাদ করতে বলা হয়। অনুবাদে পত্রের মূল প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, কর্নেল ক্লাইভের প্রত্যাশা অনুযায়ী সেনাবাহিনী শীঘ্রই কলকাতায় পৌঁছাবে। তিনি দ্রুত মাদ্রাজে আরেকটি জাহাজ পাঠিয়ে এই সংবাদ প্রদান করবেন যে, বাংলায় অতিরিক্ত সৈন্য ও জাহাজের প্রয়োজন। পরিশেষে, একপ্রকার হুমকির সুরে ওয়াটসন বলেছেন, তিনি বাংলায় এমন এক অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করবেন, যা গঙ্গার সমস্ত জল দিয়েও নেভানো সম্ভব হবে না।
৭.২ ‘সিরাজদ্দৌলা’ রচনা অনুসরণে সিরাজের দেশপ্রেমের পরিচয় দাও।
উত্তর: “সিরাজদ্দৌলা” নাট্যাংশের সূচনাতে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে একজন রূঢ় শাসকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে নাটক যত এগিয়েছে, তার চরিত্র ততই পরিপূর্ণতা পেয়েছে; পাঠক আবিষ্কার করেছেন তাঁর রুক্ষ বহিরঙ্গের আড়ালে এক গভীর দেশপ্রেমিক হৃদয়। ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের বাংলায় অগ্নিসংযোগের হুমকিপূর্ণ চিঠি পড়ে তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ওয়াটসনকে দরবার থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করেন। অন্যদিকে, রাজবল্লভ, দুর্লভরাম, মীরজাফর প্রমুখ দেশীয় সভাসদের চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জেনেও, এবং তাদের কাছ থেকে চরম অপমান সত্ত্বেও, মাতৃভূমির নিরাপত্তার কথা ভেবেই তিনি আবার তাদের সাথে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেন। “বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা” – তাঁর এমন উক্তি থেকেই সেই দেশপ্রেমেরই পরিচয় মেলে। ঘসেটি বেগমের নিরন্তর অভিশাপের প্রতিও তিনি কঠোর প্রতিক্রিয়া দেননি, কিন্তু বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কাই তাকে বেশি বেদনা দিয়েছে। দেশপ্রেম প্রতিটি মানুষের মনেই থাকে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার চরিত্রে এই গুণটি তাঁকে বিশেষ মাহাত্ম্য দান করেছে। সিংহাসনের দায়িত্বে থেকে তিনি দেশ ও জনগণের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বাংলার আকাশে নেমে আসা সংকটের ছায়াই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আহত করেছে। তবুও, মাতৃভূমির প্রতি তাঁর এই আন্তরিক টান ও দায়িত্ববোধই তাঁর চরিত্রে দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ দারিদ্র্য আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনির যে লড়াই, তা সংক্ষেপে লেখো।
উত্তর: মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কনকচাঁপা পাল, সংক্ষেপে যাকে ডাকা হয় কোনি নামে। তার সংগ্রাম ছিল দ্বিমুখী—একদিকে পরিবারের চরম দারিদ্র্য, অন্যদিকে জলের প্রতিদ্বন্দ্বী। দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে দাদার মৃত্যুর পর কোনির মনে কেবল একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খেত, “এবার আমরা কী খাব?” এই ক্ষুধার যন্ত্রণাই তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় সবসময়—কখনও বেঁচে থাকার তাগিদে, কখনও বা জয়ের তীব্র লালসায়। দরিদ্র পরিবারে জন্মের সংকোচ ও জড়তা কোনিকেও গ্রাস করে ফেলেছিল। তাই অমিয়া বা হিয়ার মতো মেয়েদের আচরণ ও কথার ছলে সে প্রায়ই নিজেকে অপদস্থ মনে করত। কিন্তু হিয়ার ‘আনস্পোর্টিং’ কথাটাই তার জয়ের স্পৃহাকে আরও শান দেয়। কোনি একরোখা, জেদি, পরিশ্রমী ও অদম্য। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে—জলে আর ডাঙায়—সে লড়াই চালিয়ে যায় এবং চূড়ান্তভাবে জয়ী হয়। অসংখ্য বঞ্চনা ও অপমানের পরও সাফল্যের পদক শোভা পায় তার গলেই। ক্লাবের রাজনীতি, চরম অপমান ও অবহেলাকে পেছনে ফেলে সে নিরলস অনুশীলন করে চলে। এই লড়াকু ও পরিশ্রমী মনোভাবই তাকে এনে দেয় চূড়ান্ত সাফল্য।
৮.২ “চার বছরের মধ্যেই ‘প্রজাপতি’ ডানা মেলে দিয়েছে।” ‘প্রজাপতি’ কী? কথাটির তাৎপর্য লেখো।
উত্তর: ‘কোনি’ উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক মতী নন্দী ‘প্রজাপতি’ নামের একটি দোকানের কথা বর্ণনা করেছেন। এই দোকানটি শুরুতে ছিল ক্ষিতীশ সিংহ ও লীলাবতীর সেলাইয়ের দোকান, ‘সিনহা টেলারিং’ নামে। লীলাবতী যখন দোকানটির হাল ধরেন, তখন তিনি এটি পুনর সংগঠিত করেন। তিনি দোকানটিকে কন্যাশিশু ও ছোট্ট শিশুদের জন্যই বিশেষভাবে তৈরি পোশাকের দোকান বানান এবং এর নতুন নাম দেন ‘প্রজাপতি’।
জুপিটার ক্লাব এবং সাঁকার প্রতি গভীর অনুরাগী ক্ষিতীশ সিংহ সংসার-বদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁর দোকান থাকলেও দিনে দু-ঘণ্টার বেশি তিনি সেখানে থাকতেন না। দু’জন দর্জি জামাকাপড় সেলাই করতেন। এভাবে দিন কাটতে থাকলে একদিন দেখা গেল, দোকানের আলমারির অর্ধেকেরও বেশি কাপড় উধাও হয়ে গেছে এবং দোকানের ভাড়া বাকি পড়েছে চার মাসের। ঠিক যখন দোকান লাভের বদলে লোকসানের মুখে, তখন লীলাবতী দোকানের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। নিজের গহনা বন্ধক রেখে দু’জন মহিলার সহায়তায় তিনি শুধুমাত্র মেয়েদের ও শিশুদের জামা তৈরি শুরু করেন। ধীরে ধীরে ব্যবসায় সমৃদ্ধি ফিরে আসে। লীলাবতী তাঁর বন্ধক দেওয়া গহনার অর্ধেক ফেরত পান। কাজের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং ব্যবসা সফল হওয়ায় লীলাবতী একটি বড় দোকানের খোঁজ শুরু করেন। তাঁর বিচক্ষণতা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গৃহস্থালি-বান্ধব দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে লীলাবতী দোকানটিকে আবারও সাফল্যের পথে এগিয়ে নেন।
৮.৩ “বিষ্টু ধরের বিরক্তির কারণ হাত পনেরো দূরের একটা লোক।” বিষ্টু ধরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে, তার বিরক্তির কারণ উল্লেখ করো।
উত্তর: মতি নন্দী, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ক্রীড়া-সাহিত্যিক, তাঁর যুগান্তকারী ‘কোনি’ উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন বিষ্টুচরণ ধর নামের এক অসাধারণ চরিত্র। লেখকের বর্ণনায়, “বিষ্টু ধর (পাড়ার ডাকে বেষ্টাদা) আই.এ. পাস, এক অত্যন্ত বনেদি পরিবারের সন্তান। তাদের পরিবারের মালিকানায় রয়েছে ঝাড়ন-মশলার প্রতিষ্ঠিত কারবার। কিন্তু তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সাড়ে তিন মণ ওজনের এক বিরাট দেহ।” তার এই ভারী দেহটিকে সর্বত্র বহন করে বয়ে নিয়ে চলে চল্লিশ বছরের এক পুরনো কিন্তু বিশ্বস্ত অস্টিন গাড়ি। বিষ্টুর একান্ত আনন্দ হলো তানপুরা, তবলা, সারেগামার মিশ্র সুরের তালে তার দেহ মালিশ করানো। বর্তমানে তার মন জুড়ে রয়েছে ভোটে দাঁড়ানোর এক সুপ্ত বাসনা। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের তাগিদেই সে পাড়ার বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আর্থিক অনুদান দেয় এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করে। সংক্ষেপে, বিষ্টু ধর এর চরিত্রটি হল এক হাস্যকর, পরোপকারী, কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী।
হাত পনেরো দূরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল, যাকে দেখে বিস্টুর বিরক্তি হচ্ছিল। সাদা লুঙ্গি ও গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে রঙিন ঝোলা ঝুলানো সেই লোকটি বিস্টুর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মুচকি হাসছিল – এই দৃশ্যই তার বিরক্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো:
The peacock is first seen on the funeral urns of Harappa. The dead man’s spirit or ‘Suksma Sarira’ is depicted horizontally placed in the belly of the peacock which these birds are supposed to transport to the other world.
উত্তর: ময়ূরকে প্রথম দেখা যায় হরপ্পার মৃতদেহের পাত্রে। মৃত ব্যক্তির আত্মা বা ‘সূক্ষ্ম শরীর’কে ময়ূরের পেটের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে শায়িত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। বিশ্বাস করা হয়, এই পাখিরাই সেই আত্মাকে অন্য জগতে পৌঁছে দেয়।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ অনলাইন ক্লাসের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
বিষয়ঃ
অনলাইন ক্লাসের সুবিধা ও অসুবিধা
নীল: সোহম! আজকাল অনলাইন ক্লাস কেমন লাগছে তোমার?
সোহম: মোটামুটি ভালো। বাড়িতে বসেই ক্লাস করা যায়, যাতায়াতের ঝামেলা নেই — এটা বড় সুবিধা।
নীল: হ্যাঁ, আর সময়ও বাঁচে। নেট থাকলেই মোবাইল বা কম্পিউটার থেকে সহজে ক্লাস করা যায়।
সোহম: ঠিক বলেছো। কিন্তু কিছু অসুবিধাও তো আছে। অনেক সময় নেটওয়ার্ক সমস্যা হয়, ক্লাস ঠিকমতো বোঝা যায় না।
নীল: সত্যি। আর শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকায় প্রশ্ন করলে তৎক্ষণাৎ উত্তরও মেলে না।
সোহম: বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয় না, দলগত আলোচনা বা খেলাধুলার সুযোগও থাকে না।
নীল: একদম ঠিক। তাই মনে হয়, অনলাইন ক্লাস যেমন সুবিধাজনক, তেমনি সরাসরি স্কুলে গিয়ে পড়াশোনার মজাটাও আলাদা।
সোহম: হ্যাঁ, আমি চাই আবার যেন নিয়মিত অফলাইন ক্লাস শুরু হয়।
রাহুল: আমিও তাই চাই।
১০.২ ‘জলা বুজিয়ে সবুজ ধ্বংস করে আবাসন নয়’ এই বিষয় অবলম্বনে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
জলা বুজিয়ে সবুজ ধ্বংস করে আবাসন নয়
নিজেস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫: বর্তমান সময়ে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসবাসের জায়গার চাহিদা বেড়েছে। এই চাহিদা পূরণের জন্য বহু জায়গায় নির্বিচারে জলা ও সবুজ জমি বুজিয়ে আবাসন তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, জলধারার পথ রুদ্ধ হচ্ছে এবং বন্যা ও জলাবদ্ধতার সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, জলা ও সবুজ জমি প্রাকৃতিক জলাধার হিসেবে কাজ করে এবং পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এগুলো ধ্বংস হলে পরিবেশের ক্ষতি অনিবার্য।
পরিবেশপ্রেমীরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, যেন অবিলম্বে এই ধরনের অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করা হয় এবং বিকল্প জায়গায় পরিকল্পিতভাবে আবাসন তৈরি করা হয়।
উপসংহার:
উন্নয়ন প্রয়োজন, কিন্তু তা যেন পরিবেশের ক্ষতি না করে। তাই আবাসন হোক পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিতভাবে।
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবস্ত রচনা করো:
১১.১ মহাকাশ গবেষণায় ভারতের জয়যাত্রা।
উত্তর:
মহাকাশ গবেষণায় ভারতের জয়যাত্রা
আজকের যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। এই যুগে মহাকাশ গবেষণায় ভারত যে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে, তা গোটা বিশ্বের কাছে গর্বের বিষয়। স্বাধীনতার পর ভারত নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও মহাকাশ গবেষণায় এক অসাধারণ সাফল্যের ইতিহাস রচনা করেছে।
ভারতের মহাকাশ গবেষণার সূচনা হয় ১৯৬৯ সালে, যখন প্রতিষ্ঠিত হয় ইসরো (ISRO – Indian Space Research Organisation)। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. বিক্রম সারাভাই-এর নেতৃত্বে ভারত মহাকাশে প্রথম পদক্ষেপ নেয়। ১৯৭৫ সালে ভারত তার প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্ট মহাকাশে প্রেরণ করে, যা ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।
এরপর ধাপে ধাপে ভারত আরও অনেক সাফল্য অর্জন করে। ২০০৮ সালে ভারতের প্রথম চন্দ্র অভিযান চন্দ্রযান-১ চাঁদের মাটিতে জলের অস্তিত্বের সন্ধান দেয়, যা বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তোলে। ২০১৩ সালে ভারত প্রেরণ করে মঙ্গলযান, যা প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছে ইতিহাস গড়ে। এই সাফল্যের জন্য ভারতকে বলা হয় “সস্তায় মহাকাশ জয় করা দেশ”।
২০২৩ সালে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয় চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের মাধ্যমে। এটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে অবতরণ করে, যা এর আগে কোনো দেশ পারেনি। এই সাফল্যে ভারত বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদে অবতরণের গৌরব অর্জন করে।
এছাড়াও আদিত্য-এল১ সূর্য পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে ভারতের লক্ষ্য গগনযান মিশন, যার মাধ্যমে ভারতীয় মহাকাশচারীরা নিজস্ব যান নিয়ে মহাকাশে যাবে।
এই সব অর্জন প্রমাণ করে যে, ভারতের বিজ্ঞানীরা অদম্য পরিশ্রম, মেধা ও দৃঢ় মনোবল দিয়ে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মহাকাশ গবেষণায় ভারতের জয়যাত্রা কেবল দেশের গর্বই নয়, ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণার উৎস।
ভারত আজ মহাকাশ গবেষণায় এক শক্তিশালী দেশ হিসেবে বিশ্বে নিজের অবস্থান গড়ে তুলেছে। এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে ভারত মহাকাশ জয়ের আরও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
১১.২ তোমার প্রিয় সাহিত্যিক।
উত্তর:
আমার প্রিয় সাহিত্যিক
ভূমিকা:
সাহিত্য মানুষের মনের খাদ্য। সাহিত্য মানুষের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতির প্রকাশ। আমাদের দেশে অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজ ও মানুষের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছেন। তাঁদের মধ্যে আমার প্রিয় সাহিত্যিক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
জীবনপরিচয়:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং মাতা ছিলেন শারদাসুন্দরী দেবী। ছোটবেলা থেকেই তিনি সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি প্রথাগত শিক্ষায় না পড়ে নিজের আগ্রহ ও প্রতিভা দিয়ে জ্ঞানার্জন করেন।
সাহিত্যজগতে অবদান:
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। তিনি কবি, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, চিত্রকর ও সংগীতকার—সর্বত্রই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতিমাল্য’, ‘বলাকা’, ‘সোনার তরী’ প্রভৃতি।
তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে—‘গোরা’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘চতুরঙ্গ’, ‘যোগাযোগ’ ইত্যাদি।
গল্পের জগতে তিনি লিখেছেন—‘গল্পগুচ্ছ’, ‘ছিন্নপত্র’, ‘সমাপ্তি’ প্রভৃতি।
তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা করেন।
১৯১৩ সালে তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এটি ছিল ভারতীয়দের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।
তাঁর সাহিত্যধারা:
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য গভীর মানবতাবোধে পরিপূর্ণ। তিনি প্রকৃতি, প্রেম, সমাজ, মানবতা ও আত্মার মুক্তি নিয়ে লিখেছেন। তাঁর ভাষা মাধুর্যপূর্ণ, সহজবোধ্য ও সংগীতধর্মী। তাঁর রচনায় একদিকে যেমন আছে রোমান্টিকতা, অন্যদিকে আছে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন।
ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব:
রবীন্দ্রনাথ কেবল সাহিত্যিক নন, তিনি একজন দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ। তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর রচনা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।
উপসংহার:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জাতীয় গর্ব। তাঁর সাহিত্য আমাদের মনে আলো জ্বেলে দেয়, জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলে। তাই তিনি আমার প্রিয় সাহিত্যিক এবং চিরকাল আমার হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন।
১১.৩ দেশভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ।
উত্তর:
দেশভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ
ভূমিকা:
শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল বইয়ের জ্ঞান অর্জন নয়, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যবই আমাদের তথ্য দেয়, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা দেয় দেশভ্রমণ। তাই বলা হয়— “দেশভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ”।
দেশভ্রমণের অর্থ:
দেশভ্রমণ বলতে নিজের দেশ বা দেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করা বোঝায়। এর মাধ্যমে আমরা দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক স্থান, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সরাসরি জ্ঞান লাভ করি।
দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা:
শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করতে দেশভ্রমণের গুরুত্ব অপরিসীম। বই থেকে যে তথ্য জানা যায়, দেশভ্রমণ সেই তথ্যকে বাস্তবে চোখে দেখার সুযোগ দেয়। যেমন— আমরা ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের কথা পড়ি, কিন্তু পলাশীর প্রান্তর দেখে সেই যুদ্ধের বাস্তব চিত্র অনুভব করা যায়। ভূগোলের পাঠে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্রের নাম জানি, কিন্তু দেশভ্রমণ আমাদের তা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ দেয়।
দেশভ্রমণের শিক্ষামূলক উপকারিতা:
দেশভ্রমণ শিক্ষার্থীদের কৌতূহল বৃদ্ধি করে, দেশপ্রেম জাগায় এবং বাস্তব জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে। এর মাধ্যমে সামাজিক মেলামেশা বাড়ে, সহনশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব জন্মায়। ভ্রমণ মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে এবং নতুন উদ্যম জোগায়।
দেশভ্রমণ ও জাতীয় একতা:
দেশের বিভিন্ন প্রদেশ, ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থীরা জাতীয় ঐক্যের মূল্য বুঝতে শেখে। এটি দেশের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে।
উপসংহার:
শিক্ষা যদি জীবনের প্রস্তুতি হয়, তবে দেশভ্রমণ সেই শিক্ষার এক অপরিহার্য অংশ। শ্রেণিকক্ষের পাঠের সঙ্গে দেশভ্রমণের সমন্বয় ঘটলে শিক্ষার পূর্ণতা আসে। তাই আমাদের উচিত বিদ্যালয় পর্যায়ে দেশভ্রমণকে শিক্ষার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা।
সত্যিই, দেশভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ।
১১.৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং বিশ্বকবির আসনে অধিষ্ঠিত এক মহামানব। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা, চিন্তা-ভাবনা, মানবতাবোধ ও সৃষ্টিশীলতা শুধু বাংলাকেই নয়, গোটা বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা শারদাসুন্দরী দেবী। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যচর্চার আগ্রহ দেখা যায়। বাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁকে সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।
তাঁর সাহিত্যজীবন বহুমুখী। তিনি ছিলেন কবি, গল্পকার, উপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সংগীতকার ও চিত্রশিল্পী। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘কবি কাহিনী’ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। এরপর ‘সোনার তরী’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘বলাকা’ প্রভৃতি কাব্যে তিনি মানবজীবনের সৌন্দর্য, প্রকৃতি ও ঈশ্বরচেতনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের জন্য ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, যা কোনো ভারতীয়ের প্রথম নোবেল প্রাপ্তি।
গল্পকার হিসেবেও তিনি অসাধারণ। ‘গল্পগুচ্ছ’ গ্রন্থে তাঁর মানবজীবনের গভীর পর্যবেক্ষণ ফুটে উঠেছে। ‘চোখের বালি’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘গোরা’ প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি সমাজ, ধর্ম ও নারীমনের জটিলতা তুলে ধরেছেন। নাটক ও সংগীতে তাঁর অবদানও অনস্বীকার্য। তাঁর রচিত দুইটি গান— “জন গণ মন” ও “আমার সোনার বাংলা” যথাক্রমে ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃত।
রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শান্তিনিকেতনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে বিশ্বমানবতার আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হয়।
তিনি মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম ও স্বাধীনতার কবি। তাঁর রচনায় জীবনের আনন্দ, দুঃখ, প্রকৃতি ও মানবতার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে।
১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট তিনি পরলোকগমন করেন। তবে তাঁর সাহিত্য ও ভাবনা আজও বাঙালির জীবনে আলোকবর্তিকা হয়ে আছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু একজন কবি নন, তিনি ছিলেন যুগস্রষ্টা। তাঁর রচনা ও চিন্তাধারা আমাদের চিরকাল অনুপ্রেরণা জোগাবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাঁকে কখনো ভুলবে না।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।