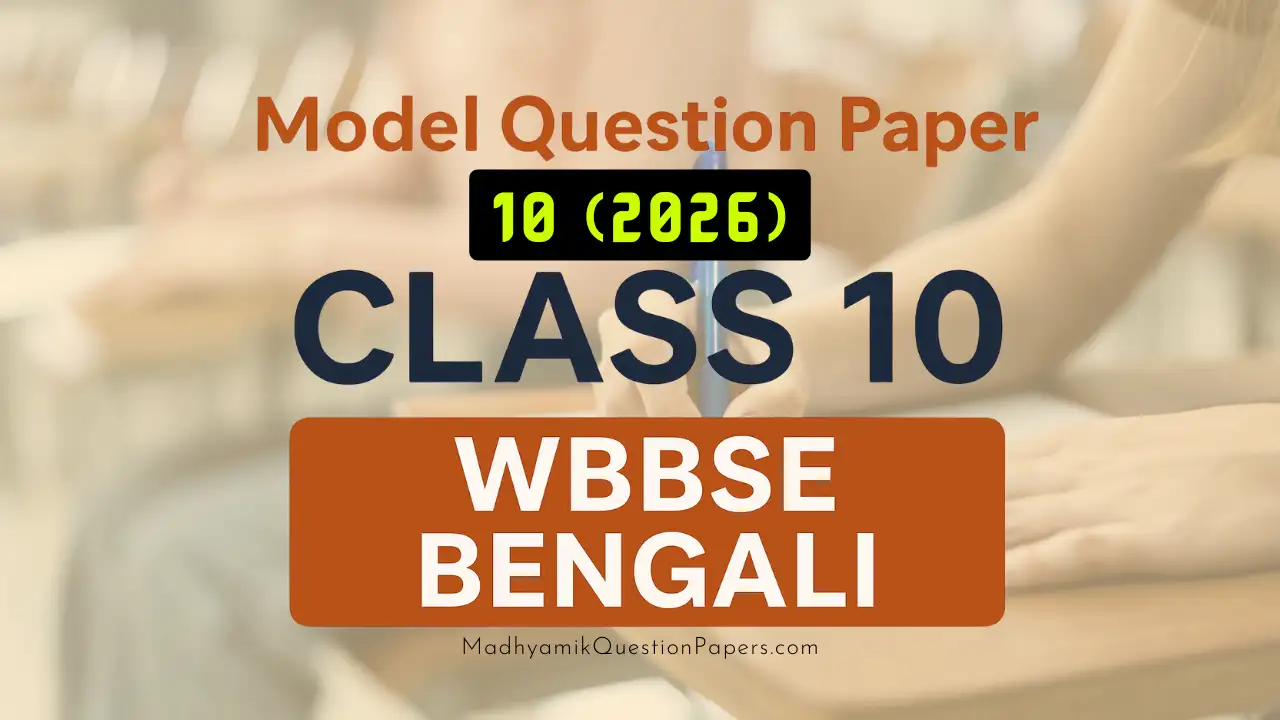আপনি কি ২০২৬ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 10 এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 10-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৬ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ ‘খুব হয়েছে হরি, এই বার সরে পড়ো। অন্যদিকে যাও।’ একথা বলেছে-
(ক) ভবতোষ
(খ) অনাদি
(গ) কাশীনাথ
(ঘ) জনৈক বাসযাত্রী
উত্তর: (গ) কাশীনাথ
১.২ ‘আমি বাবু ভারী ধর্মভীরু মানুষ।’ কথাটি বলেছে
(ক) গিরীশ মহাপাত্র
(খ) নিমাইবাবু
(গ) অপূর্ব
(ঘ) রামদাস
উত্তর: (ক) গিরীশ মহাপাত্র
১.৩ স্ত্রীকে লেখা নদেরচাঁদের চিঠির পত্রসংখ্যা ছিল
(ক) এক
(খ) তিন
(গ) চার
(ঘ) পাঁচ
উত্তর: (ঘ) পাঁচ
১.৪ ‘আমাদের মাথায় বোমারু / পায়ে পায়ে -‘- শূন্যস্থানে বসবে।
(ক) পথচলা
(খ) ঘোর অবসাদ
(গ) গিরিখাদ
(ঘ) হিমানীর বাঁধ
উত্তর: (ঘ) হিমানীর বাঁধ
১.৫ “ওই নূতনের কেতন ওড়ে”- ‘কেতন’ শব্দটির অর্থ-
(ক) শিখা
(খ) পতাকা
(গ) ঝড়
(ঘ) জয়টিকা
উত্তর: (খ) পতাকা
১.৬ “হাত নাড়িয়ে সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো-
(ক) মাছি তাড়াই
(খ) বুলেট তাড়াই
(গ) শত্রু তাড়াই
(ঘ) বিদায় জানাই
উত্তর: (খ) বুলেট তাড়াই
১.৭ শেষ পর্যন্ত নিবের কলমের মান মর্যাদা কে একমাত্র বাঁচিয়ে রেখেছিলেন?-
(ক) অন্নদাশঙ্কর রায়
(খ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
(গ) নিখিল সরকার
(ঘ) সত্যজিৎ রায়
উত্তর: (ঘ) সত্যজিৎ রায়
১.৮ ‘International’ শব্দটির যে পরিভাষা আলোচ্য প্রবন্ধে দেওয়া আছে, তা হল-
(ক) সার্বজাতিক
(খ) সর্বজনীন
(গ) আন্তর্জাতিক
(ঘ) আন্তর্দেশীয়
উত্তর: (ক) সার্বজাতিক
১.৯ বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্বপরিচয় নেই যে শ্রেণির পাঠকের-
(ক) প্রথম শ্রেণির
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণির
(গ) তৃতীয় শ্রেণির
(ঘ) মধ্যম শ্রেণির
উত্তর: (ক) প্রথম শ্রেণির
১.১০ “গঙ্গার জল পবিত্র” ‘গঙ্গার’ কী সম্বন্ধ? –
(ক) অঙ্গ সম্বন্ধ
(খ) আধার-আধেয় সম্বন্ধ
(গ) অবলম্বন সম্বন্ধ
(ঘ) উপাদান সম্বন্ধ
উত্তর: (খ) আধার-আধেয় সম্বন্ধ
১.১১ অনুসর্গের দৃষ্টান্ত কোন্টি?
(ক) জন্য
(খ) খানা
(গ) টি
(ঘ) গাছা
উত্তর: (ক) জন্য
১.১২ ‘সিংহাসন’ শব্দের ব্যাসবাক্যটি হল-
(ক) সিংহ চিহ্নিত আসন
(খ) সিংহ লাঞ্ছিত আসন
(গ) সিংহের আসন
(ঘ) সিংহ বাঞ্ছিত আসন
উত্তর: (ক) সিংহ চিহ্নিত আসন
১.১৩ সমাস হতে গেলে কমপক্ষে ক’-টি পদ দরকার?
(ক) তিনটি
(খ) দুটি
(গ) চারটি
(ঘ) পাঁচটি
উত্তর: (খ) দুটি
১.১৪ ক্রিয়াখন্ডের প্রধান উপাদান হল
(ক) অসমাপিকা ক্রিয়া
(খ) সমাপিকা ক্রিয়া
(গ) ক্রিয়াবাচক বিশেষণ
(ঘ) কালবাচক বিশেষণ
উত্তর: (খ) সমাপিকা ক্রিয়া
১.১৫ বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? অর্থগত দিক থেকে এটি
(ক) না-সূচক বাক্য
(খ) সন্দেহবাচক বাক্য
(গ) প্রশ্নবাচক বাক্য
(ঘ) প্রার্থনাসূচক বাক্য
উত্তর: (গ) প্রশ্নবাচক বাক্য
১.১৬ আজ কি তুমি বাজারে যাও নি? এটি কোন্ বাচ্যের উদাহরণ? –
(ক) ভাববাচ্য
(খ) কর্মবাচ্য
(গ) কর্মকর্তৃবাচ্য
(ঘ) কর্তৃবাচ্য
উত্তর: (ঘ) কর্তৃবাচ্য
১.১৭ কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি অকর্মক হলে, তাকে রূপান্তরিত করা হয়-
(ক) কর্তৃবাচ্যে
(খ) কর্মবাচ্যে
(গ) ভাববাচ্যে
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্যে
উত্তর: (গ) ভাববাচ্যে
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ “গল্প ছাপা হলে যে ভয়ংকর আহ্লাদটি হবার কথা, সে আহ্লাদ খুঁজে পায় না।” উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আহ্লাদিত হতে না পারার কারণ কী?
উত্তর: তপনের প্রথম গল্প ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় ছাপা হওয়ায় যতটা না তার নিজের, তার চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেওয়া হয় তার মেসোমশাইকে। এই কারণে তপন আহ্লাদিত হতে পারে না।
২.১.২ ‘বাঃ, এ তো বেশ মজার ব্যাপার!’ মজার ব্যাপারটি কী ছিল?
উত্তর: মজার বিষয় হলো, যদিও সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ, তবুও যখন কাঠের খড়মে সোনার বোল লাগিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ধরা হলো, তিনি তখনই পা বাড়িয়ে দিলেন। সেই সুযোগে জগদীশবাবু সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো সংগ্রহ করে নিলেন।
২.১.৩ ‘বড়োবাবু হাসিতে লাগিলেন।’ বড়োবাবুর হাসার কারণ কী ছিল?
উত্তর: গিরীশ মহাপাত্রের মাথায় লেবুর তেলের গন্ধে থানার সবাইরই মাথা ধরার উপক্রম হয়েছিল। জগদীশবাবু বড়োবাবুকে যখন এই কথা বললেন, তখন বড়োবাবু হেসে উঠলেন।
২.১.৪ ‘কী খাঁটি কথা!’ খাঁটি কথাটি কী?
উত্তর: পান্নালাল প্যাটেল রচিত গল্পে ইসাব অমৃতকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোর বাবা যদি তোকে মারে কী হবে? অমৃত জবাব দিয়েছিল ” আমার তো মা রয়েছে।” – অমৃতের এই কথাটিকেই খাঁটি কথা বলা হয়েছে।
২.১.৫ “আরও বেশি অপরিচিত মনে হইল।” উদ্দিষ্টকে ‘বেশি অপরিচিত’ মনে হওয়ার কারণ কী?
উত্তর: প্রদত্ত উদ্ধৃতিতে, নদেরচাঁদের স্টেশনমাস্টারের দায়িত্ব নিয়ে আসার পর বাঁধা হয়ে থাকা নদীটির সাথে তার পরিচয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। নদীটি এক সময় ছিল গভীর, প্রশস্ত ও জলসমৃদ্ধ। কিন্তু তীব্র বর্ষণের কারণে পাঁচ দিন ধরে তিনি নদীটিকে দেখতে যেতে পারেননি। পাঁচ দিন পর গিয়ে নদেরচাঁদ দেখতে পেলেন, নদীটি যেন তার বন্দিদশা থেকে মুক্তির জন্য বিদ্রোহ করেছে। নদীর গাঢ় কাদাযুক্ত জল ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। নদীর এই ভয়ঙ্কর রূপ নদেরচাঁদ এর আগে কখনো দেখেননি। তাই নদীটিকে তার কাছে অপরিচিত বলে মনে হয়েছিল।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ ‘সব চূর্ণ হয়ে গেল, জ্বলে গেল আগুনে।’ সব কী কী?
উত্তর: “অসুখী একজন” কবিতার উল্লেখিত অংশে, কবি যে বাড়িতে বাস করতেন – তার বারান্দার ঝুলন্ত বিছানা যেখানে তিনি নিদ্রা যেতেন, তাঁর প্রিয় গোলাপি রঙের সেই গাছ যার পাতা হাতের তালুর মতো ছড়ানো, চিমনি ও প্রাচীন জলতরঙ্গ – এগুলোর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।
২.২.২ ‘আমাদের ইতিহাস নেই’ একথা বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: ইতিহাস হল জাতির আত্মবিকাশের গৌরবগাথা ও তার ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার। কিন্তু যখন কোনো ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় বা রাজনীতি দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে। ক্ষমতাধররা তাদের স্বার্থে ইতিহাসকে নিজেদের মতো করে বানিয়ে নেয়। মানুষ ধীরে ধীরে তার প্রকৃত ইতিহাস ভুলে যায়, আর চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাসকেই সত্য বলে মেনে নেয়। এই প্রেক্ষাপটকেই উদ্ভাসিত করতেই কবি বলেছেন আমাদের ইতিহাস নেই।
২.২.৩ “ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা” কে, কাকে, কোথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?
উত্তর: সভ্যতার সূচনালগ্নে, স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সদ্য-সৃষ্টিকে বারবার ধ্বংস করছিলেন, তখনই এক রুদ্র সমুদ্র তার বিশাল বাহু প্রসারিত করে পৃথিবীর পূর্বাঞ্চল – সেই আদি প্রাচীন ভূখণ্ড – থেকে আফ্রিকাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল।
২.২.৪ “বেথানিত হৈছে কেশ বেশ।”- ‘বেথানিত’ শব্দের অর্থ কী? কার এ অবস্থার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: কবি সৈয়দ আলাওল রচিত ‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশের উদ্ধৃত অংশে ‘বেথানিত’ শব্দের অর্থ হলো — অসংবৃত, বিশৃঙ্খল বা এলোমেলো।
সৈয়দ আলাওল রচিত ‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশে এরকম অবস্থা হয়েছিল পদ্মাবতীর।
২.২.৫ ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় ঋষিবালকের মধ্যে কার ছায়াপাত ঘটেছে?
উত্তর: অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় কবি ঋষিবালকের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেই রাখাল বালক সুলভ রূপটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘অবাক হয়ে সেদিন মনে মনে ভাবছিলাম,’ কে, কী ভাবছিলেন?
উত্তর: সুভো ঠাকুরের বিখ্যাত দোয়াতের সংগ্রহ দেখে লেখক শ্রীপাদ ভেবেছিলেন
এই সব দোয়াতের কালি দিয়েই না শেক্সপিয়ার, দাত্তে, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র সব অমর রচনা লিখে গেছেন। হায়, কোথায় গেল সে সব দিন।
২.৩.২ ‘কালগুণে বুঝিবা আজ আমরাও তা-ই।”- কালগুণে আমাদের অবস্থা কেমন হয়ে উঠেছে বলে লেখকের অভিমত?
উত্তর: বাংলায় চিরচেনা একটি প্রবাদ হচ্ছে – ‘কালি নেই, কলম নেই, বলে আমি মুনশি’। লেখকের মতে, কম্পিউটারের বিস্তারের যুগে এই কালি-কলমহীন অবস্থায় এখন সবাই-ই যেন মুনশি বা লেখক হয়ে গেছেন।
২.৩.৩ কোন্ কথাটি কাব্যের উপযুক্ত হলেও, ভূগোলের উপযুক্ত নয়?
উত্তর: “হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড”— কালিদাসের এই উক্তিকে প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু বলেছেন, এটি কাব্যের পক্ষে যথোপযুক্ত হলেও ভূগোলের পক্ষে সঠিক নয়।
২.৩.৪ অবিখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকশের আগে কী সতর্কতা নেওয়া উচিত?
উত্তর: অবিখ্যাত কোনো লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশ করার আগে অবশ্যই সেই রচনাটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে যথাযথভাবে পর্যালোচনা ও যাচাই করে নেওয়া উচিত।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ প্রযোজ্য কর্তা কাকে বলে?
উত্তর: প্রযোজক কর্তা সেই, যে কর্তা অন্যের দ্বারা কোনো কাজ সম্পন্ন করান, তাকেই প্রযোজক কর্তা বলে।
২.৪.২ “বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের।” রেখাঙ্কিত পদটি কোন কারকের উদাহরণ?
উত্তর:
২.৪.৩ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য লেখো।
উত্তর:
| মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস | মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস |
| যে কর্মধারয় সমাসে সমস্তপদের মধ্যপদ (মধ্যের পদ) লুপ্ত হয়ে যায় এবং পূর্বপদ ও পরপদের মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণ বিদ্যমান থাকে, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। | যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদের মধ্যপদ লুপ্ত হয়ে যায় এবং সমস্তপদটি বিধেয় (কোনো কিছুর সংস্করণ/অন্য অর্থ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে। |
২.৪.৪ ‘ক্ষুদ্র গ্রহ’ ব্যাসবাক্যটিকে সমাসবদ্ধ করে সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: ‘ক্ষুদ্র গ্রহ’ ব্যাসবাক্যটিকে সমাসবদ্ধ পদ হল “ক্ষুদ্র যে গ্রহ” এবং সমাসের নাম হল কর্মধারয় সমাস।
২.৪.৫ ‘বৃষ্টিতে ধুয়ে দিল আমার পায়ের দাগ’ জটিল বাক্যে পরিবর্তন করো।
উত্তর: ‘বৃষ্টিতে ধুয়ে দিল আমার পায়ের দাগ’ জটিল বাক্যে পরিবর্তন করলে হবে বৃষ্টি যখন পড়ল, তখন তা আমার পায়ের দাগ ধুয়ে দিল।
২.৪.৬ সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়। বাক্য নির্মাণের কোন শর্ত এখানে লঙ্ঘন করা হয়েছে?
উত্তর: সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়। এখানে বাক্য নির্মাণের বাস্তবতা বা যৌক্তিকতা-র শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে। কারণ, বাস্তবে সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়, পশ্চিমে নয়।
২.৪.৭ পিকু বিকেলে খেলা করে। বাক্যটির উদ্দেশ্য অংশ চিহ্নিত করে তা সম্প্রসারিত করো।
উত্তর: পিকু বিকেলে খেলা করে বাক্যটির উদ্দেশ্য অংশ হল পিকু এবং বাক্যটির সম্প্রসারিত রূপ হল ‘সদা প্রফুল্ল ও ফুরফুরে মেজাজের ছোট্ট ছেলে পিকু তার প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে প্রতি বিকেলে বাড়ির পাশের মাঠে ক্রিকেট খেলা করে।’
২.৪.৮ আজ কি তোমার বাজার যাওয়া হয়নি। (কর্তৃবাচ্যে পরিণত করো)
উত্তর: আজ কি তোমার বাজার যাওয়া হয়নি বাক্যটিকে কর্তৃবাচ্যে পরিণত করলে হবে আজ কি তুমি বাজার যাওনি?
২.৪.৯ কর্মবাচ্য এবং ভাববাচ্যের প্রধান পার্থক্য কী?
উত্তর:
| কর্মবাচ্য | ভাববাচ্য |
| কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার রূপ কর্ম কে নির্দেশ করে। | ভাববাচ্যে কর্ম উল্লেখ থাকে না, ক্রিয়ার কাজটি সাধারণভাবে প্রকাশ পায়। |
২.৪.১০ কর্মবাচ্যের একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: কর্মবাচ্যের একটি উদাহরণ হল ‘বইটি ছাত্রের দ্বারা পড়া হয়।’
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ “তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।” ‘ঢং’ বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে? কীসে ঢং নষ্ট হয়ে যাবে?
উত্তর: এখানে ‘ঢং’ বলতে শিল্পীর অভিনয়কৌশল বা অভিনয়ের ধরনকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।
হরিদা জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন টাকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে একজন সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তিনি নিজেই ওই সন্ন্যাসীর চরিত্রে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যান। ফলস্বরূপ, তিনি কেবল বৈরাগ্য ও লোভহীন জীবনের বাণীই প্রচার করতেন না, বরং প্রণামি হিসেবে পাওয়া টাকার প্রতি উদাসীনভাবে আচরণ করে ব্যবহারিক জীবনেও তার প্রতিফলন দেখান। হরিদার বক্তব্য ছিল যে, একজন বিরাগী সন্ন্যাসী হিসেবে টাকা স্পর্শ করলে তাঁর আসল ভাব বা ‘ঢং’ নষ্ট হয়ে যাবে।
৩.১.২ ‘আমি ভীরু, কিন্তু তাই বলে অবিচারে দণ্ডভোগ করার অপমান আমাকে কম বাজে না’ বক্তা কাকে একথা বলেছিলেন? কোন্ অবিচারের দণ্ডভোগ তাঁকে ব্যথিত করেছিল?
উত্তর: রামদাসকেই বক্তা অপূর্ব ওই উদ্ধৃতিটি বলেছিলেন।
নির্দোষ অপূর্বকে কয়েকজন ইংরেজ যুবক লাথি মেরে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বের করে দিয়েছিল। অপূর্ব অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও কোনো লাভ হয়নি। দেশি মানুষ হওয়ায় সাহেব স্টেশনমাস্টার তার কোনো কথা না শুনেই তাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেন। শুধুমাত্র ভারতীয় হওয়ার কারণে এই লাঞ্ছনা অপূর্বর মনে গভীর যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। এই অবিচারের অভিজ্ঞতা তাকে গভীরভাবে পীড়া দিয়েছিল।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ ‘সেই মেয়েটির মৃত্যু হলো না।’ কোন্ মেয়েটির কথা বলা হয়েছে? তার মৃত্যু না হওয়ার কারণ কী?
উত্তর: এই অংশে বর্ণিত হয়েছে সেই নারীর কথা, যে দরজায় দাঁড়িয়ে কবির জন্য অপেক্ষা করেছিল, যখন তিনি বিদ্রোহ অথবা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা দিয়েছিলেন।
বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষ সংসার ও প্রিয়জনকে পিছনে ফেলে যুদ্ধের পথে পা রাখে। কিন্তু এই কঠোর সত্য স্বীকার করতে পারেনি তার প্রিয়তমা মেয়েটি। সে অপেক্ষা করতে থাকে প্রিয় মানুষের জন্য। যুদ্ধে অসংখ্য মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যেও মেয়েটির মৃত্যু হয় না। সে বেঁচে থাকে চিরজীবী ভালোবাসার এক প্রতীক হয়ে।
৩.২.২ ‘আমাদের পথ নেই কোনো’ এই পথ না থাকার তাৎপর্য কী?
উত্তর: প্রদত্ত উদ্ধৃতিটি শঙ্খ ঘোষ রচিত ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতা থেকে সংগৃহীত। বর্তমানের হিংসাদীর্ণ বিশ্বপরিসরে সাধারণ মানুষ তার অস্তিত্বেরই সংকট অনুভব করছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা তাকে কোনো দিকেই স্থির হতে দিচ্ছে না। আদর্শিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে ফাটল ধরেছে, তা দিনে দিনে এমনই গভীর হয়ে উঠছে যে মানুষের চেতনার গন্তব্য কী তা অস্পষ্ট থেকে আরও অস্পষ্টতর হয়ে পড়ছে। ডানদিক দেখছে সে ধ্বংসের মত্ততা, বামদিকেও দেখছে মৃত্যুর ফাঁদ। সেইসঙ্গে মাথার উপর দিয়ে বোমাবর্ষণরত বিমানের ভয়াবহতা, আর এগিয়ে চলার পথে পদে পদে অন্তরায়। এইভাবেই মানুষের চলার পথ ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। সার্বিক অন্ধকার ও আদর্শহীনতা আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছে।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।
উত্তর: আশাপূর্ণা দেবীর ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পের নামটি যথার্থ ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পে ‘জ্ঞানচক্ষু’ বলতে বোঝানো হয়েছে এমন এক অন্তর্দৃষ্টি, যা বাহ্যিক চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সত্য-মিথ্যা, আসল-নকল, মৌলিকতা ও অনুকরণের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।
তপন নামের এক কিশোর চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখিকা বুনেছেন তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের গল্প। তপনের লেখক মেসোমশাই তার লেখাটি আমূল পাল্টে দিয়ে সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় ছাপার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু এই ঘটনায় তপনের লেখকসত্তা গভীরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। শুধু নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখার আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং তার সৃজনশীলতার স্বীকৃতি না পাওয়ার বেদনাই তপন চরিত্রটিকে দেয় বিশেষ মাত্রা। গল্পের পরিণতি যতই গম্ভীর হোক, লেখিকা তা তুলে ধরেছেন অপূর্ব দক্ষতায়। গল্পে তপনের লেখক মেসোমশাইয়ের চরিত্রটি বর্ণনার নিপুণতায় হয়ে ওঠে চিত্তাকর্ষক—“ঠিক ছোটো মামাদের মতোই খবরের কাগজের সব কথা নিয়ে প্রবলভাবে গল্প করেন, তর্ক করেন, আর শেষ পর্যন্ত ‘এ দেশের কিছু হবে না’ বলে সিনেমা দেখতে চলে যান…।”—এই অনবদ্য রচনাশৈলী গল্পটিকে দিয়েছে গতিময়তা। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পটি তার পরিণতিতেই পেয়েছে প্রকৃত সার্থকতা। মৌলিকতায় বিশ্বাসী এক আত্মমর্যাদাবান কিশোর লেখকের যন্ত্রণা শুধু চরিত্রটিকেই নয়, গল্পটিকেও দিয়েছে অসাধারণত্ব।
সুতরাং, ‘জ্ঞানচক্ষু’ নামটি তপনের আত্মজাগরণের প্রতীক। এই গল্পে ‘জ্ঞানচক্ষু’ই তাকে শেখায় সত্যিকারের সৃষ্টিশীলতার মানে কী। তাই বলা যায়, গল্পের ভাব, ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশের সঙ্গে ‘জ্ঞানচক্ষু’ নামটি সম্পূর্ণ সার্থক।
৪.২ “নিজের এই পাগলামিতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।” কার ‘পাগলামি’-র কথা বলা হয়েছে? তার পাগলামির পরিচয় দাও।
উত্তর: কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে ত্রিশ বছর বয়সেও নদীর প্রতি নদেরচাঁদের অসীম মমত্ববোধকে কিছুটা অস্বাভাবিকই মনে হতো। নদেরচাঁদের এই নদী-স্নেহকেই গল্পে ‘পাগলামি’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।
নদীর ধারেই নদেরচাঁদের বসবাস। নদী ছিল তার চিরসঙ্গী। বর্ষার জলে নদীর ধারেই নদেরচাঁদের বসবাস। এই নদীটিও খুব শীঘ্রই তার আপনজন হয়ে ওঠে। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সে এই নদীর কথা ভেবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। বর্ষার জলে নদীটি যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, তখন তার উত্তাল স্রোতের অস্থিরতা দেখে নদেরচাঁদ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। নদেরচাঁদের মনে হত, নদীর এই অস্থিরতা যেন তারই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। সারাদিন ও রাত জুড়ে যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনের দ্রুত গতি নিয়ন্ত্রণ করা—এই একাগ্র কাজের মানুষটির নদীর জন্য এতটা আবেগপ্রবণ হওয়া কি ঠিক?—এই প্রশ্ন প্রায়ই তার মনে উঠত। নদেরচাঁদ নিজেও এই সত্য বুঝত, কিন্তু তার মনকে কোনোভাবেই এটা বোঝাতে পারত না। আসলে, মানসিকভাবে সে নদীর সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। নদীর সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে পেরে সে নিজেকে সত্যিকারের সার্থক মনে করত। নদীর প্রতি এই গভীর মোহ ও পাগলামির মধ্যে দিয়ে নদেরচাঁদ এক অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ করত, যা ছিল শুধুমাত্র তারই একান্ত নিজস্ব।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ “পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন।” ‘পঞ্চকন্যা’ কারা? এদের অচৈতন্য হওয়ার কারণ কী? তারা কীভাবে চেতনা ফিরে পেয়েছিল?
উত্তর: সৈয়দ আলাওল রচিত পদ্মাবতী কাব্যের ‘সিন্ধুতীরে’ অংশে ‘পঞ্চকন্যা’-দের চেতনা ফিরে পাওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ—
পঞ্চকন্যা কারা: পঞ্চকন্যার মধ্যে মধ্যমণি হলেন সিংহলরাজকন্যা পদ্মাবতী, আর তাঁর চার সখী হলেন—চন্দ্রকলা, বিজয়া, রোহিণী ও বিধুন্নলা।
অচৈতন্য হওয়ার কারণ: স্বামী রত্নসেনের সঙ্গে চিতোরে ফেরার পথে সমুদ্রে প্রবল ঝড় ওঠে। ঝড়ে তাদের জাহাজ ভেঙে যায়। পদ্মাবতী ও তাঁর সখীরা একটি ভাঙা ভেলায় (মান্দাসে) আশ্রয় নেন। হঠাৎ ভেলাটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে তারা রত্নসেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দীর্ঘ ভেসে থাকা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তারা অচৈতন্য হয়ে পড়েন।
চেতনা ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়া: তাদের এই শোচনীয় অবস্থায় দেবী সমুদ্রকন্যা পদ্মা করুণায় উদ্বেল হয়ে নিরঞ্জনকে তাঁদের প্রাণরক্ষার নির্দেশ দেন। দেবীর আদেশে নিরঞ্জন শুষ্ক বস্ত্র দিয়ে তাদের দেহ আবৃত করেন, অগ্নি প্রজ্বলিত করে দেহে তাপ দেন, তান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন। নিরবচ্ছিন্ন চার দণ্ডকালব্যাপী সেবা-শুশ্রূষার ফলে রাজকন্যা পদ্মাবতী ও তাঁর চার সখী ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পান। দেবী পদ্মার করুণা ও নিরঞ্জনের অনেকক্ষণ সেবা ও যত্নের পরে রাজকন্যা পদ্মাবতী ও তাঁর সখীরা চেতনা ফিরে পান।
৫.২ “ভেঙে আবার গড়তে জানে” এখানে কার কথা বলা হয়েছে? ভেঙে আবার গড়তে জানে কেন বলেছেন কবি?
উত্তর: প্রদত্ত অনুচ্ছেদটিতে প্রাথমিকভাবে মহাদেবকে নির্দেশ করা হলেও ভেঙে আবার গড়তে জানে এর মাধ্যমে দেশের যুব বিপ্লবীদেরই ইঙ্গিত করা হয়েছে।
“প্রলয়োল্লাস” কবিতায় কবি নজরুল চিরবিদ্রোহী নবযৌবনের বন্দনা করেছেন। এই বিপ্লবী শক্তির আবির্ভাব ঘটে ভয়ংকরের রূপ ধারণ করে। ‘মহাকালের চণ্ডরূপে’ অর্থাৎ শিবের প্রলয়ংকর মূর্তির মধ্য দিয়ে যেন তাদের আগমন। ‘জয় প্রলয়ঙ্কর’ ধ্বনি তুলে তারা জরাগ্রস্ত, মৃতপ্রায় সমাজের অবসান ঘটায়। তাদের শক্তির প্রচণ্ডতায় চারদিক দিশেহারা হয়ে পড়ে। রক্তাক্ততা, বিশৃঙ্খলতা ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে তাদের আবির্ভাবে যে ধ্বংসের উন্মাদনা দেখা দেয়, তা মানুষকে শঙ্কিত করে তোলে। সৃষ্টির প্রলয়ের দেবতা শিব যেমন ধ্বংসের মাধ্যমেই নতুন সৃষ্টিকে নিশ্চিত করেন, তেমনি বিপ্লবী শক্তিও আপাত নৈরাজ্যের আড়ালে গড়ে তোলে সুস্থ ও সুন্দর সমাজের স্বপ্ন। কবির দৃষ্টিতে এই প্রলয় জড়ত্বেরও অবসান ঘটায়। ধ্বংসের এই তীব্রতা আসলে নতুন সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য। কালরাত্রির শেষেই রয়েছে উষার সূর্যোদয়। অন্ধকার কারাগারের হাড়িকাঠে বন্দী যে দেবতা, তাকে মুক্ত করে মানবতার প্রতিষ্ঠাই এই তরুণদের লক্ষ্য। তাই এই প্রলয় হল ‘নূতন সৃজন-বেদনা’। জীবনহীন ও অসুন্দরকে ধ্বংস করতেই যার আবির্ভাব। তাই ভাঙনের পিছনেই লুকিয়ে থাকে গড়ার বাসনা। স্বাধীনতা, সাম্য ও সম্প্রীতির বীজমন্ত্রেই নিহিত রয়েছে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। এজন্যই কবি মন্তব্য করেছেন ভেঙে আবার গড়তে জানে।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ ‘সোনার দোয়াত কলম যে সত্যই হতো; তা জেনেছিলাম সুভো ঠাকুরের বিখ্যাত দোয়াত সংগ্রহ দেখতে গিয়ে।’ সুভো ঠাকুর কে? সোনার দোয়াত কলমের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে? এছাড়া আর কীসের দোয়াত হত? দোয়াতের সঙ্গে সাহিত্য ও ইতিহাসের বিভিন্ন চরিত্রের যোগসূত্র কী?
উত্তর: সুভো ঠাকুরের পুরো নাম সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর জন্ম ৩রা জানুয়ারি, ১৯১২ এবং মৃত্যু ১৭ই জুলাই, ১৯৮৫ তারিখে। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপ্রৌত্র ছিলেন। চিত্রশিল্পী, কবি, পত্রিকা সম্পাদক ও শিল্পসংগ্রাহক—এই নানা পরিচয়েই তিনি সাত দশক জুড়ে সক্রিয় ছিলেন।
শ্রীপান্থ লিখেছেন, সুভো ঠাকুরের বিখ্যাত দোয়াত সংগ্রহের দেখা পেয়েই তিনি প্রথম জানতে পারেন যে সোনার দোয়াত-কলম বলে সত্যিই কিছু থাকতে পারে। তিনি আরও জানান, গ্রামাঞ্চলে তখন কেউ পরীক্ষায় পাস করলে বুড়োবুড়িরা আশীর্বাদ করে বলতেন, “বেঁচে থাকো বাছা, তোমার সোনার দোয়াত-কলম হোক!”
সোনার তৈরি দোয়াত ছাড়াও লেখক এখানে বিভিন্ন ধরনের দোয়াত ও কলমের বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলি হল – কাচ, কাট-গ্লাস, পোর্সেলিন, সাদা পাথর, জেড পাথর, পিতল এমনকি গোরুর শিং দিয়ে তৈরি দোয়াতের কথাও প্রবন্ধে রয়েছে।
শ্রীপান্থের ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ রচনায় তিনি কালির দোয়াতের সঙ্গে সাহিত্য ও ইতিহাসের বহু ব্যক্তিত্বের সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন। লেখক বিস্ময় নিয়ে ভেবেছেন যে, শেকসপিয়র, দান্তে, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র—সকলেই এই সমস্ত দোয়াতের কালি দিয়েই তাদের চিরস্মরণীয় সৃষ্টিকর্ম রচনা করে গেছেন।
৬.২ ‘বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে আর একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে।’ কোন্ দোষের কথা বলা হয়েছে? কীভাবে এই দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে?
উত্তর: রাজশেখর বসুর ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধের উল্লিখিত অংশে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের মতে, অনেক সময় অল্পবিদ্যার কারণে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ভুল-ত্রুটি দেখা দেয়। অর্থাৎ, পর্যাপ্ত জ্ঞান ও সঠিক তথ্যের অভাবে প্রবন্ধকাররা যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক বিষয় উপস্থাপন করতে পারেন না। তাই তিনি সতর্ক করেছেন যে, বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালিখি করতে হলে গভীর জ্ঞান ও নির্ভুল তথ্যের প্রয়োজন।
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা রচনার ক্ষেত্রে পাঠক যেমন সচেতন, লেখককেও তেমনি আরও বেশি সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে। শুধু সঠিক রচনাপদ্ধতি অনুসরণ বা ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদ পরিহার করাই যথেষ্ট নয়, বরং বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও গভীর জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক লেখকই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করেই লিখতে বসেন। বিভিন্ন সাময়িকীতে এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়। যেমন, একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল – “অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর বলে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এগুলো কেবল জীবের বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু ওজোন গ্যাস স্বাস্থ্যকর।” এ ধরনের ভুল তথ্যপূর্ণ লেখা সাধারণ পাঠকের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য পত্রিকার সম্পাদককেও বিশেষ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। অপরিচিত বা নবীন লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও যাচাই করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবেই এই ত্রুটি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। লেখকের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও সম্পাদকের সজাগ দৃষ্টি – এই দুয়ের সমন্বয়েই কেবল বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা সার্থক ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “I know we shall never meet.” কে, কাকে একথা বলেছেন? এই বক্তব্যের পূর্বপ্রসঙ্গ কী ছিল?
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের একটি অংশে, ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উদ্দেশ করে এই মন্তব্যটি করেছিলেন।
ইংরেজরা যখন বাংলায় ফরাসিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সূচনা করে, তখন ফরাসিদের পক্ষে তা প্রতিহত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর আগে ফরাসিরা ইংরেজ আক্রমণ মোকাবিলায় দুর্গ নির্মাণের উদ্যোগ নিলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাতে বাধা দেন। নবাবের আদেশ ফরাসিরা মেনে নিলেও ইংরেজরা তা অমান্য করে। তারা ফরাসিদের চন্দননগর কুঠি দখল করে নেয় এবং সমস্ত বাণিজ্যকুঠির উপর কর্তৃত্ব দাবি করে। সংকটগ্রস্ত ফরাসি পক্ষের প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা সামরিক সহায়তার আশায় নবাবের শরণাপন্ন হন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে সেই মুহূর্তে তাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, কলকাতা দখল এবং পূর্ণিয়ার যুদ্ধে তার সৈন্যবল ও অর্থভাণ্ডার মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। ফলত, নবাবের কাছ থেকে কোনো সাহায্য না পেয়ে ফরাসিদের বাংলা ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। এই বিদায়মুহূর্তে মর্মাহত মঁসিয়ে লা তাই তাঁর বক্তব্যে এই অনুভূতিই প্রকাশ করেন।
৭.২ “জানি না, আজ কার রক্ত সে চায়।” বক্তা কে? বক্তার এমন মন্তব্যের কারণ কী?
উত্তর: নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের আলোচ্য উক্তিটির বক্তা হলেন স্বয়ং নবাব সিরাজউদ্দৌলা।
বক্তার অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলার এমন মন্তব্যের কারণ হল – কোনো যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি কখনোই আগাম অনুমান করা যায় না, বিশেষ করে পলাশির যুদ্ধের মতো একটি জটিল সংঘাতের ক্ষেত্রে। কারণ এতে একাধিক পক্ষ জড়িত ছিল, যাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ ছিল ভিন্ন। ব্যক্তিগত লাভ, পারিবারিক প্রতিশোধ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য—এসব নানা জটিল বিষয় এতে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। তাই এই সংঘাত কেবল সিরাজ বনাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা নবাব নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন। মীরজাফর ও রাজবল্লভের মতো অনুচররা তাঁর পক্ষে থাকার অঙ্গীকার করলেও যে চূড়ান্ত লড়াইয়ে তারা তাঁকে ছেড়ে দেবেন—এই কঠিন সত্যটি বুঝতে সিরাজের বিলম্ব হয়নি। পলাশির রণক্ষেত্রে সংঘটিত এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিনাশের ছবি যেন আগাম দেখতে পেয়েছিলেন সংবেদনশীল নবাব। আর তাই তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এক গভীর হাহাকারে, যা প্রশ্নোক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ ‘কোনি’ উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী রূপে লীলাবতীর পরিচয় দাও।
উত্তর: মতি নন্দী রচিত ‘কোনি’ উপন্যাসে ক্ষিতীশ সিংহের স্ত্রী লীলাবতী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্র।
পুরো সংসারই মূলত চলে লীলাবতীর অক্লান্ত পরিশ্রমে। ‘সিনহা টেলারিং’ যখন লোকসানের সম্মুখীন, তখন তিনি নিজের গয়না বন্ধক রেখে নতুনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। দোকানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন ‘প্রজাপতি’ এবং অসম্ভব পরিশ্রম ও দক্ষতার সাথে চার বছরের মধ্যেই তিনি ‘প্রজাপতি’-কে নিয়ে যান উন্নতির শিখরে। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না লীলাবতী পুরুষদের পোশাক তৈরি বন্ধ করে শুধুমাত্র মেয়ে ও শিশুদের পোশাক তৈরির সিদ্ধান্ত নেন এবং দুজন মহিলা কর্মচারী নিয়োগ করেন। তাঁরই দক্ষ নেতৃত্বে ব্যবসা দ্রুত বিকশিত হতে থাকে এবং এর জন্য আরও বড় জায়গার প্রয়োজন পড়ে। গম্ভীর প্রকৃতির হলেও লীলাবতী স্বামীর প্রতি ছিলেন অগাধ শ্রদ্ধাশীলা। স্বামীর সাঁতারপ্রীতির কথা জেনেই তিনি সংসারের সব দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন, যাতে স্বামী নিশ্চিন্তে তাঁর শখ চর্চা করতে পারেন। এই শ্রদ্ধাবশতই তিনি কোনির সাঁতার প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি কোনিকে সাফল্যের জন্য ফ্রক উপহার দেবেন বলেছেন, এমনকি ইন্ডিয়া রেকর্ড করলে সিল্কের শাড়ি দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এসব ঘটনায় তাঁর গম্ভীর স্বভাবের আড়ালে যেন মাতৃসুলভ একটি আবেগ উঁকি দেয়। স্বল্প পরিসরে হলেও এই উপন্যাসে লীলাবতীর কর্মবিমুখতাহীন, সংসারনিষ্ঠা এবং পরোক্ষে স্বামী-অনুরাগিণী চরিত্রটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।
৮.২ “হঠাৎ কোনির দু’চোখ জলে ভরে এল।” কোনির দু’চোখ জলে ভরে এল কেন? এরপর কী হয়েছিল?
উত্তর: মতি নন্দীর কোনি উপন্যাসে রবীন্দ্র সরোবরের এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় কোনি সবশেষে গন্তব্যে পৌঁছায়। এর জন্য তাকে “পরের বছরের প্রতিযোগিতায় প্রথম হত যদি আরও একটু দেরি করে পৌঁছাতো”- এরকম বিদ্রূপের মন্তব্যও সহ্য করতে হয়। বোনের জন্য এতক্ষণ ধরে চিৎকার করে যাওয়া কমল এই কারণে অপমানিত বোধ করে। এই মুহুর্তেই ক্ষিতীশ কোনিকে দ্বিতীয়বারের মতো সাঁতার শেখার প্রস্তাব দেন। সাঁতার শিখলেই যে সাফল্য পাওয়া সম্ভব, ক্ষিতীশ সেটা বুঝিয়ে দেন। ক্ষিতীশের কথায় কোনির ভেতরের জমে থাকা অপমানই চোখের জলে পরিণত হয়ে বেরিয়ে আসে।
ক্ষিতীশ জানতে পারেন, নীল শার্ট-পরা লোকটি, যে এতক্ষণ কোনির জন্য চিৎকার করছিল, সে হচ্ছে কোনির দাদা কমল। ক্ষিতীশ কমলকে প্রস্তাব দেন যে তিনি কোনিকে সাঁতার শেখাতে চান। কমল ক্ষিতীশকে সাঁতারের প্রতি তার নিজের ভালোবাসার কথা জানান, কিন্তু একই সাথে এ-ও স্পষ্ট করে দেন যে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তিনি কোনিকে সাঁতার শেখানোর সামর্থ্য রাখেন না। তিনি একটি মোটর গ্যারাজে কাজ করেন। আর্থিক সংকটের কারণেই তাকে নিজের নামকরা সাঁতারু হওয়ার স্বপ্ন ত্যাগ করতে হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, সংসার চালানোর পাশাপাশি কোনির সাঁতার প্রশিক্ষণের খরচ বহন করা তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানান কমল। কোনির মাঝে সাফল্যের সম্ভাবনা দেখে পেয়ে ক্ষিতীশ ঘোষণা দেন যে, কোনির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করবেন।
৮.৩ “চার বছরের মধ্যেই ‘প্রজাপতি’ ডানা মেলে দিয়েছে।” ‘প্রজাপতি’ কী? কার তত্ত্বাবধানে, কীভাবে ‘প্রজাপতি’ ডানা মেলে দিয়েছে?
উত্তর: মতি নন্দী রচিত ‘কোনি’ উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ‘প্রজাপতি’ দোকানটির পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষিতীশ সিংহ ও লীলাবতীর একটি সেলাইয়ের দোকান ছিল, যার প্রাথমিক নাম ছিল ‘সিনহা টেলারিং’। পরবর্তীতে লীলাবতী দোকানটির দায়িত্ব নিয়ে এটিকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্বিন্যাস করেন। তিনি এটিকে মেয়েদের ও শিশুদের পোশাক তৈরির বিশেষায়িত দোকানে রূপান্তরিত করেন এবং এর নতুন নামকরণ করেন ‘প্রজাপতি’।
দোকানে যখন লাভ না হয়ে লোকসান হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় লীলাবতী দোকানের দায়িত্ব নেন। তিনি নিজের গহনা বন্ধক রেখে দুজন মহিলাকে নিয়ে শুধুমাত্র মেয়ে ও শিশুদের জামাকাপড় তৈরি করার কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে ব্যবসায় সমৃদ্ধি আসে। লীলাবতী তাঁর বন্ধক রাখা গহনার অর্ধেক ফেরত পান। কাজের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং ব্যবসা ভালো চলার কারণে, লীলাবতী একটি বড় দোকানের সন্ধান শুরু করেন। তাঁর বিচক্ষণতা, কঠোর পরিশ্রম এবং গৃহস্থালি কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি দোকানটিকে আবারও সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যান।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো:
The most important things for a citizen is simply to be a good man. He must try to be honest, just and merciful in his private life. This is his primary duty. The reason should not be difficult to understand. The well-being of a state or city ultimately depends on the moral character of its citizens.
উত্তর: একজন নাগরিকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভালো মানুষ হওয়া। তাকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এটাই তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। কোনো রাষ্ট্র বা নগরের মঙ্গল শেষ পর্যন্ত তার নাগরিকদের নৈতিক চরিত্রের উপরই নির্ভর করে।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ ‘সাবধানে চালাও জীবন বাঁচাও / সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ এ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও
মামন: শুভ, আজকাল রাস্তায় কত দুর্ঘটনা হচ্ছে দেখছো?
শুভ: হ্যাঁ রে! প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে দুর্ঘটনার খবর থাকে। বেশিরভাগই অসাবধানতার কারণে।
মামন: ঠিক বলেছো। কেউ হেলমেট পরে না, কেউ আবার সিগন্যাল মানে না।
শুভ: তাই তো সরকার “সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ” প্রচার চালাচ্ছে। আমাদেরও সচেতন হতে হবে।
মামন: অবশ্যই। ট্রাফিক নিয়ম মানলে এবং সাবধানে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে।
শুভ: আমি তো এখন বাইক চালানোর সময় সবসময় হেলমেট পরি আর মোবাইল ব্যবহার করি না।
মামন: খুব ভালো করছো। আমিও মনে করি, জীবন একটাই, তাই একটু সাবধান থাকলেই জীবন বাঁচানো যায়।
শুভ: ঠিক বলেছো। আমরা নিজেরা সচেতন হলে অন্যদেরও উৎসাহ দিতে পারি।
মামন: চল, সবাইকে বলি – “সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও।”
সচেতনতা ও নিয়ম মেনে চলাই পারে দুর্ঘটনামুক্ত সমাজ গড়তে।
১০.২ বিশ্ব নারী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
বিশ্ব নারী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো
নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৮ই মার্চ ২০২৫, আজ আমাদের বিদ্যালয়ে বিশ্ব নারী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য ছিল— “নারীর ক্ষমতায়নেই সমাজের উন্নয়ন”। সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রধান শিক্ষক শুভ সূচনা ভাষণ দেন এবং সমাজে নারীর ভূমিকা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরপর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বক্তৃতা, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা নারী শিক্ষার প্রসার ও আত্মনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় নারী সমাজকর্মী, যিনি নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানের শেষে সেরা বক্তৃতার জন্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
সার্বিকভাবে দিনটি ছিল উৎসবমুখর ও শিক্ষণীয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা নারীর মর্যাদা ও সমাজে তাদের অবদানের গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে সচেতন হয়।
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো:
১১.১ উন্নায়ন বনাম পরিবেশ।
উত্তর:
বিষয়:
উন্নয়ন বনাম পরিবেশ (Development vs Environment)
ভূমিকা:
আজকের পৃথিবী দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। শিল্পায়ন, নগরায়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আধুনিক সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই উন্নয়নের পেছনে লুকিয়ে আছে এক গভীর সংকট—পরিবেশের অবনতি। তাই আজকের যুগে “উন্নয়ন বনাম পরিবেশ” এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।
উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা:
একটি দেশের অগ্রগতির মাপকাঠি হলো তার উন্নয়নের হার। নতুন নতুন শিল্প স্থাপন, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রযুক্তির প্রসার—এসবই জনগণের জীবনমান উন্নত করার জন্য জরুরি। উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ে, শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর হয়।
পরিবেশের গুরুত্ব:
অন্যদিকে, মানবজীবনের মূল ভিত্তি হলো পরিবেশ। শুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ জল, সবুজ গাছপালা এবং প্রাণীকুল—সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে প্রকৃতির এক অনন্য ভারসাম্য। এই ভারসাম্য নষ্ট হলে জীবনধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
সংঘাতের কারণ:
উন্নয়নের তাগিদে মানুষ বেপরোয়া ভাবে বন ধ্বংস করছে, নদী দূষিত করছে, মাটি ও বায়ু দূষণ বাড়াচ্ছে। শিল্পকারখানার ধোঁয়া, যানবাহনের ধোঁয়া, প্লাস্টিকের ব্যবহার ইত্যাদি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। ফলস্বরূপ গ্লোবাল ওয়ার্মিং, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি সমস্যা ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে।
সমন্বয়ের প্রয়োজন:
উন্নয়ন ও পরিবেশ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। তাই টেকসই উন্নয়নের ধারণা আজকের যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ, শিল্পে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যের ব্যবহার, এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।
উপসংহার:
পরিবেশ নষ্ট করে উন্নয়ন কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন তা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তোলা হয়। তাই আমাদের অঙ্গীকার হোক—”পরিবেশ রক্ষা করেই উন্নয়নের পথে এগোবো”।
১১.২ একটি নির্জন দুপুরের অভিজ্ঞতা।
উত্তর:
বিষয়:
একটি নির্জন দুপুরের অভিজ্ঞতা
একটি নির্জন দুপুর মানেই এক অন্যরকম অনুভূতি। যখন চারপাশে নিস্তব্ধতা নেমে আসে, গরম রোদে পথ জনশূন্য হয়ে পড়ে, তখন মন এক অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে ডুবে যায়। আমার এমন এক নির্জন দুপুরের অভিজ্ঞতা আজও ভুলতে পারি না।
সেদিন ছিল গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়। স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছিল। সকালের পর পরিবারের সবাই নিজেদের ঘরে দুপুরের বিশ্রামে গিয়েছে। ঘরজুড়ে শুধু একটা ফ্যানের আওয়াজ আর বাইরের গাছের পাতায় হালকা বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। আমি বই হাতে নিয়ে বসেছিলাম, কিন্তু পড়ায় মন বসছিল না। তখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি রাস্তাটা ফাঁকা, কোনো মানুষের দেখা নেই। দূরের কুয়োর পাশে একটা বুড়ো গাছ দাঁড়িয়ে আছে একা, তার ছায়ায় একটা কুকুর ঘুমোচ্ছে।
এই নির্জন দুপুরে চারপাশের নিস্তব্ধতা যেন আমাকে গভীর চিন্তায় ডুবিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি আজ যেন কথা বলতে ভুলে গেছে। পাখিরাও নীরব, গাছে গাছে বাতাসের হালকা ছোঁয়া, আর আমার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত শান্তি। এই একাকিত্বে হঠাৎ নিজের জীবন, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ—সব কিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম।
একটু পরে উঠোনে গিয়ে দেখি গরমে মাটি ফেটে যাচ্ছে, পিঁপড়ের সারি খাবারের খোঁজে চলছে। দূরে খেতের মাঝে একটা রাখাল তার গরু নিয়ে ছায়ায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। সেই সুর ভেসে এল আমার কানে, আর মনে হল, এই নীরবতার মধ্যেই প্রকৃতির এক অন্য সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে।
সেদিনের সেই নির্জন দুপুর আমাকে শিখিয়েছিল একা থাকার মানে। কখনও কখনও একা থাকা আমাদের মনকে স্বচ্ছ করে, ভাবনাকে গভীর করে তোলে। জীবনের ব্যস্ততার মাঝে এমন নীরব দুপুর আমাদের আত্মার বিশ্রাম এনে দেয়।
একটি নির্জন দুপুর হয়তো নিস্তব্ধ, কিন্তু তার ভেতরে লুকিয়ে থাকে গভীর শান্তি ও আত্ম-অনুসন্ধানের সুযোগ। আজও যখন দুপুরে চারপাশ চুপচাপ থাকে, তখন সেই দিনের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে যায়, আর মনে হয়—নীরবতাও একপ্রকার সঙ্গ।
১১.৩ বই পড়া।
উত্তর:
বিষয়:
বই পড়া
ভূমিকা:
মানুষের জ্ঞানার্জনের প্রধান মাধ্যম হলো বই। বই আমাদের চিন্তাকে প্রসারিত করে, মনকে আলোকিত করে এবং জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলে। তাই বলা হয়— “বই হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।” বই পড়া কেবল বিনোদনের জন্য নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দিশা দেয়।
বই পড়ার গুরুত্ব:
বই পড়ার মাধ্যমে আমরা অজানা জগতকে জানতে পারি। ইতিহাসের বই পড়ে অতীতের গৌরবময় ঘটনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বই আমাদের আধুনিক জগতের সঙ্গে পরিচিত করে, সাহিত্য বই আমাদের মননশীলতা ও রুচিবোধ গঠন করে। একটি ভালো বই আমাদের মনের অন্ধকার দূর করে আলো এনে দেয়।
বই পড়ার উপকারিতা:
বই পড়ার অভ্যাস আমাদের ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ করে, চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ায় এবং মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বই আমাদের মানসিক শান্তি দেয় ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, জীবনী বা প্রবন্ধ— প্রতিটি বই-ই কোনো না কোনোভাবে জীবনের শিক্ষা দেয়। ভালো বই পড়লে আমরা নৈতিক মূল্যবোধ, মানবতা ও সহমর্মিতার পাঠ শিখি।
বর্তমান যুগে বই পড়া:
আজকের যুগ হলো প্রযুক্তির যুগ। মোবাইল, ইন্টারনেট, টেলিভিশনের প্রভাবে বই পড়ার আগ্রহ কিছুটা কমে যাচ্ছে। তবে এখন অনেক বই ই-বুক আকারে সহজলভ্য হওয়ায় বই পড়া আবারও সহজ হয়েছে। তাই সময় কাটানোর সঠিক উপায় হিসেবে বই পড়া এখনো এক অমূল্য অভ্যাস।
বই নির্বাচন:
সব বই পড়া উচিত নয়; ভালো ও শিক্ষণীয় বই বেছে নেওয়া জরুরি। মহান লেখকদের রচিত বই পড়লে আমরা অনুপ্রেরণা পাই। যেমন— রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখের রচনা আমাদের জীবনবোধকে গভীর করে তোলে।
উপসংহার:
বই পড়া মানুষের মানসিক বিকাশের অন্যতম উপায়। একজন বইপ্রেমী মানুষ কখনো একা থাকে না, কারণ তার সঙ্গী থাকে অসংখ্য জ্ঞানের আলোয় ভরা বই। তাই আমাদের সবারই উচিত প্রতিদিন কিছুটা সময় বই পড়ার জন্য রাখা। বই-ই আমাদের সত্যিকারের বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং জীবনের আলো।
মূল শিক্ষা: ভালো বই পড়ো, ভালো মানুষ হও।
১১.৪ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা।
উত্তর:
বিষয়:
মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা
ভূমিকা:
ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, জ্ঞানেরও বাহন। মাতৃভাষা আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও জ্ঞানচর্চার প্রধান ভিত্তি। তাই বিজ্ঞান নামক যুক্তি ও অনুসন্ধাননির্ভর বিষয়টির চর্চাও মাতৃভাষায় হওয়া অত্যন্ত জরুরি। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করলে সাধারণ মানুষও বিজ্ঞানের প্রকৃত জ্ঞান ও প্রয়োগ বুঝতে পারে।
বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা:
বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার মূল ভিত্তি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন, যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প—বিজ্ঞানের ব্যবহার অপরিসীম। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চা যদি কেবল বিদেশি ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সাধারণ মানুষ তার আসল তাৎপর্য বুঝতে পারে না। তাই বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হলে মাতৃভাষায় তার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সুফল:
১. মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়টি বুঝতে পারে।
২. জটিল বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোও মাতৃভাষায় প্রকাশ করলে তা মনে রাখা ও প্রয়োগ করা সহজ হয়।
৩. সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হয়।
৪. মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বই, প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র তৈরি হলে দেশীয় জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।
বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস:
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সূচনা নবজাগরণের যুগে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষীরা মাতৃভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আধুনিক যুগে সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এবং পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।
বর্তমান প্রেক্ষাপট:
বর্তমানে স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষায় তৈরি হচ্ছে। ইউটিউব, পডকাস্ট, ও অনলাইন ক্লাসেও বাংলায় বিজ্ঞান শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তবে এখনও উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় ইংরেজির প্রভাব অনেক বেশি। তাই মাতৃভাষায় উচ্চস্তরের বিজ্ঞানচর্চা বাড়াতে আরও উদ্যোগ দরকার।
সমাধান ও প্রস্তাবনা:
- বাংলায় মানসম্মত বিজ্ঞান বই প্রকাশ করতে হবে।
- মাতৃভাষায় বিজ্ঞান গবেষণাকে উৎসাহ দিতে হবে।
- বিজ্ঞান শিক্ষকদের বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।
- প্রযুক্তির সাহায্যে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চাকে জনপ্রিয় করতে হবে।
উপসংহার:
মাতৃভাষা আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক, আর বিজ্ঞান আমাদের অগ্রগতির চাবিকাঠি। তাই মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা মানে জাতির অগ্রগতি। বিজ্ঞানের আলোকে সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে হলে মাতৃভাষাকেই হতে হবে সেই আলোর বাহক।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।