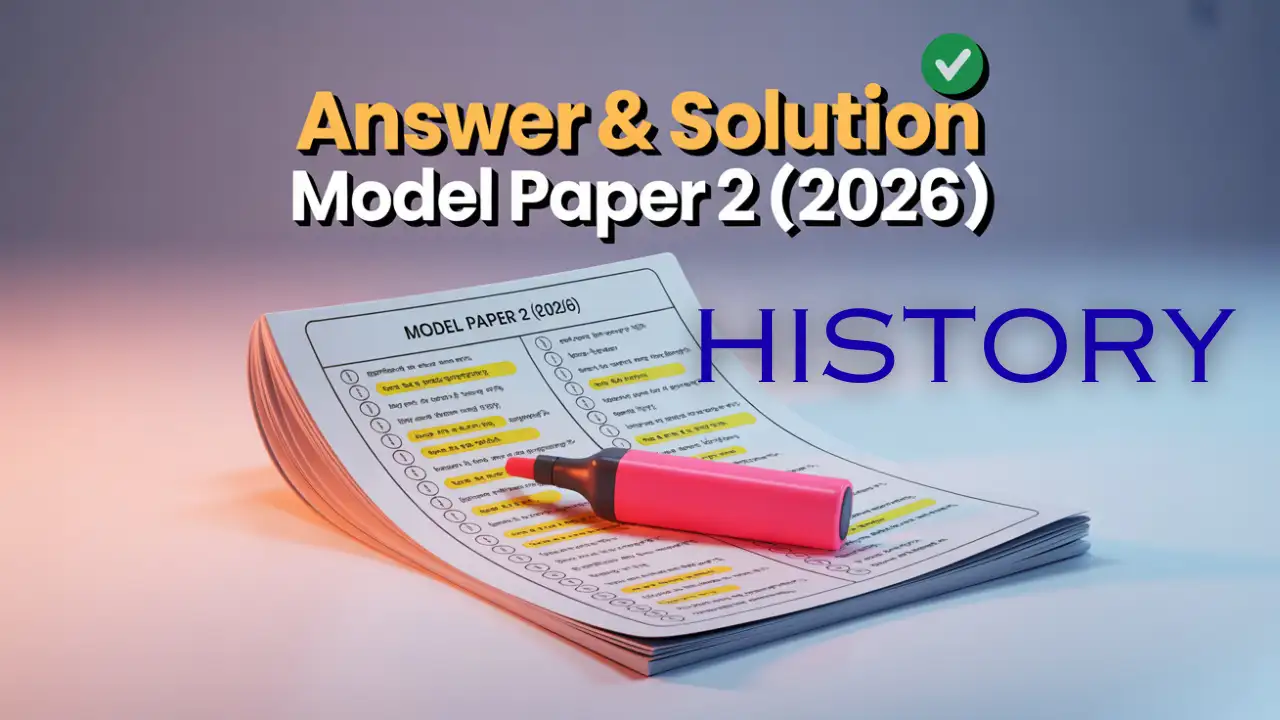আপনি কি মাধ্যমিকের ইতিহাস Model Question Paper 2 প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন? দেখে নিন 2026 WBBSE ইতিহাস Model Question Paper 2-এর সঠিক উত্তর ও বিশ্লেষণ। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর ইতিহাস ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 2-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। ইতিহাস মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৬ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggleবিভাগ-ক
১.১ সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:
১.১ ‘নিষিদ্ধ শহর’ বলা হয় –
(ক) লাসাকে,
(খ) বেইজিংকে,
(গ) রোমকে,
(ঘ) কনস্ট্যান্টিনোপলকে
উত্তর: (ক) লাসাকে
১.২ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়-
(ক) ৫ জুন,
(খ) ৪ মার্চ,
(গ) ৪ এপ্রিল,
(ঘ) ৮ জানুয়ারি
উত্তর: (ক) ৫ জুন
১.৩ প্রথম সরকারি শিক্ষা কমিশন (হান্টার কমিশন) গঠিত হয় –
(ক) ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে,
(খ) ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে,
(গ) ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে,
(ঘ) ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে
উত্তর: (গ) ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে,
১.৪ ভারতে সপ্তদশ আইনের দ্বারা যে প্রথার অবসান ঘটে-
(ক) বাল্যবিবাহ,
(খ) বহুবিবাহ,
(গ) সতীদাহপ্রথা,
(ঘ) অসবর্ণ বিবাহ
উত্তর: (গ) সতীদাহপ্রথা,
১.৫ ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন-
(ক) রামতনু লাহিড়ী,
(খ) কিশোরীচাঁদ মিত্র,
(গ) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়,
(ঘ) কেউই নন
উত্তর: (গ) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১.৬ তিতুমিরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন-
(ক) মৈনুদ্দিন,
(খ) গোলাম মাসুম,
(গ) মুসা শাহ,
(ঘ) দুদু মিঞা
উত্তর: (ক) মৈনুদ্দিন
১.৭ হাজি শরিয়ৎউল্লাহ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন-
(ক) সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহে,
(খ) ওয়াহাবি আন্দোলনে,
(গ) নীল বিদ্রোহে,
(ঘ) ফরাজি আন্দোলনে
উত্তর: (ঘ) ফরাজি আন্দোলনে
১.৮ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলেছেন-
(ক) রমেশচন্দ্র মজুমদার,
(খ) সুরেন্দ্রনাথ সেন,
(গ) বিনায়ক দামোদর সাভারকর,
(ঘ) দাদাভাই নৌরজি
উত্তর: (গ) বিনায়ক দামোদর সাভারকর
১.৯ ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি রচনা করেন-
(ক) অক্ষয়কুমার দত্ত,
(খ) রাজনারায়ণ বসু,
(গ) স্বামী বিবেকানন্দ,
(ঘ) রমেশচন্দ্র মজুমদার
উত্তর: (গ) স্বামী বিবেকানন্দ,
১.১০ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন-
(ক) সংগীত শিল্পী,
(খ) নাট্যকার,
(গ) ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী,
(ঘ) কবি
উত্তর: (গ) ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী
১.১১ ‘বর্ণপরিচয়’ প্রকাশিত হয়েছিল-
(ক) ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে,
(খ) ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে,
(গ) ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে,
(ঘ) ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে
উত্তর: (গ) ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে
১.১২ ‘History of Hindu Chemistry’ বা ‘হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস’ গ্রন্থের লেখক হলেন-
(ক) জগদীশচন্দ্র বসু,
(খ) মেঘনাদ সাহা,
(গ) সি ভি রমন,
(ঘ) প্রফুল্লচন্দ্র রায়
উত্তর: (ঘ) প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১.১৩ রম্পা উপজাতীয় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়-
(ক) মালাবার অঞ্চলে,
(খ) কোঙ্কণ উপকূলে,
(গ) ওড়িশায়,
(ঘ) গোদাবরী উপত্যকায়
উত্তর: (ঘ) গোদাবরী উপত্যকায়
১.১৪ নিখিল ভারত শ্রমিক সংঘের প্রথম সম্পাদক ছিলেন-
(ক) লালা লাজপত রায়,
(খ) বি পি ওয়াদিয়া,
(গ) পি সি যোশি,
(ঘ) দেওয়ান চমনলাল
উত্তর: (ঘ) দেওয়ান চমনলাল
১.১৫ ভারতে মহাত্মা গান্ধির প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছিল-
(ক) খেদা,
(খ) চম্পারন,
(গ) আহমেদাবাদ,
(ঘ) রাওলাট
উত্তর: (খ) চম্পারন
১.১৬ দলিতদের ‘হরিজন’ আখ্যা দিয়েছিলেন-
(ক) জ্যোতিরাও ফুলে,
(খ) নারায়ণ গুরু,
(গ) গান্ধিজি,
(ঘ) ড. আম্বেদকর
উত্তর: (গ) গান্ধিজি
১.১৭ বাংলায় ‘প্রতাপাদিত্য উৎসব’ শুরু করেন-
(ক) শ্রীমতী অবলা বসু,
(খ) হিরণ্ময়ী দেবী,
(গ) সরলাদেবী চৌধুরানি,
(ঘ) স্বর্ণকুমারী দেবী
উত্তর: (গ) সরলাদেবী চৌধুরানি
১.১৮ যুগান্তর দল গঠন করেন-
(ক) প্রমথনাথ মিত্র,
(খ) সতীশচন্দ্র বসু,
(গ) পুলিনবিহারী দাস,
(ঘ) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
উত্তর: (ঘ) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
১.১৯ ‘Train to Pakistan’ গ্রন্থটি লিখেছিলেন-
(ক) জওহরলাল নেহরু,
(খ) ভি পি মেনন,
(গ) খুশবন্ত সিং,
(ঘ) সলমন রুশদি
উত্তর: (গ) খুশবন্ত সিং
১.২০ স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল-
(ক) ৬০১টি,
(খ) ৬০২টি,
(গ) ৬০৫টি,
(ঘ) ৬১০টি
উত্তর: (ক) ৬০১টি
বিভাগ-খ
২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও)
উপবিভাগ ২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও:
২.১.১ সরকারি নথিপত্র কোথায় সংরক্ষিত হয়? ME-24, ’17
উত্তর: সরকারি নথিপত্র আর্কাইভ বা সংরক্ষণাগার কেন্দ্রে সংরক্ষিত হয়।
২.১.২ ‘দামিন-ই-কোহ’ কথার অর্থ কী?
উত্তর: ‘দামিন-ই-কোহ’ কথার অর্থ হল পাহাড়ের প্রান্তদেশ।
২.১.৩ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) সময় দিল্লির মোগল বাদশাহ কে ছিলেন? ME-10
উত্তর: মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) সময় দিল্লির মোগল বাদশাহ ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফর।
২.১.৪ বারদৌলি সত্যাগ্রহে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
উত্তর: বারদৌলি সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।
উপবিভাগ ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো:
২.২.১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -এর প্রথম মহিলা এম এ ছিলেন কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলি)। ME-19
উত্তর: ঠিক।
২.২.২ ফরাজি একটি প্রাচীন উপজাতির নাম। ME-18
উত্তর: ভুল।
২.২.৩ বাংলায় প্রথম কালার প্রিন্টিং প্রবর্তন করেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
উত্তর: ঠিক।
২.২.৪ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দল প্রতিষ্ঠা করেন সুভাষচন্দ্র বসু।
উত্তর: ঠিক।
উপবিভাগ ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও:
| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |
| ২.৩.১ রামমোহন রায় | (১) হিন্দুমেলা ΜΕ -’19, ’17 |
| ২.৩.২ নবগোপাল মিত্র | (২) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) |
| ২.৩.৩ তারকনাথ পালিত | (৩) অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ΜΕ -’22 |
| ২.৩.৪ জয়প্রকাশ নারায়ণ | (৪) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট ΜΕ -’24, ’22, ’17 |
উত্তর:
| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |
| ২.৩.১ রামমোহন রায় | (৩) অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল |
| ২.৩.২ নবগোপাল মিত্র | (১) হিন্দুমেলা |
| ২.৩.৩ তারকনাথ পালিত | (৪) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট |
| ২.৩.৪ জয়প্রকাশ নারায়ণ | (২) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল |
উপবিভাগ ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নামাঙ্কিত করো:
২.৪.১ মাদ্রাজ, ME-15, ’12,’10
২.৪.২ চুয়াড় বিদ্রোহের (১৭৯৮-১৭৯৯) এলাকা, ME-24, ’18
২.৪.৩ শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র- বোম্বাই,
২.৪.৪ পুনে। ME-’16, ’14, ’12, ’10
উত্তর:
২.৫ উপবিভাগ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো:
২.৫.১ বিবৃতি: হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
ব্যাখ্যা ১: এই পত্রিকা ছাত্রসমাজকে ব্রিটিশবিরোধী করে।
ব্যাখ্যা ২: এই পত্রিকা কৃষকসমাজকে ব্রিটিশবিরোধী করে।
ব্যাখ্যা ৩: এই পত্রিকা সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন ও নীলকরদের অত্যাচারের সমালোচনা করে।
উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: এই পত্রিকা সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন ও নীলকরদের অত্যাচারের সমালোচনা করে।
২.৫.২ বিবৃতি: শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একটি বড়ো অংশ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি।
ব্যাখ্যা ১: বিদ্রোহীরা বহু মানুষকে হত্যা করেছিল।
ব্যাখ্যা ২: বিদ্রোহীরা মোগল সম্রাটকে দিল্লির সিংহাসনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল।
ব্যাখ্যা ৩: শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর মনে করত।
উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর মনে করত।
২.৫.৩ বিবৃতি: সরলাদেবী চৌধুরানি ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ME-’18
ব্যাখ্যা ১: বিদেশি পণ্য বিক্রির জন্য।
ব্যাখ্যা ২: আন্দোলনকারী মহিলাদের সাহায্যের জন্য।
ব্যাখ্যা ৩: স্বদেশি পণ্য বিক্রির জন্য।
উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: স্বদেশি পণ্য বিক্রির জন্য।
২.৫.৪ বিবৃতি: দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি ভারতের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ছিল।
ব্যাখ্যা ১: ভারতকে রাজনৈতিক অনৈক্য ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
ব্যাখ্যা ২ : ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
ব্যাখ্যা ৩: ভারতকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে নিরাপত্তা দান করার জন্য।
উত্তর: ব্যাখ্যা ১: ভারতকে রাজনৈতিক অনৈক্য ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
বিভাগ-গ
৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে-কোনো ১১টি)
৩.১ পরিবেশের ইতিহাস বলতে কী বোঝায়? ΜΕ – ’24
উত্তর: পরিবেশের ইতিহাস হল ইতিহাসচর্চার একটি শাখা, যা অতীত কালে প্রকৃতি বা পরিবেশের সাথে মানুষের আন্তঃসম্পর্কের গতিপ্রকৃতি অধ্যয়ন করে। এটি কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশের বিবর্তনের ইতিহাসই নয়, বরং মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ কীভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে এবং পরিবর্তিত পরিবেশ আবার কীভাবে মানব সমাজ ও ইতিহাসকে রূপ দিয়েছে, তারই অনুসন্ধান করে।
৩.২ ইকোফেমিনিজম বলতে কী বোঝো?
উত্তর: ইকোফেমিনিজম (Ecofeminism) হলো এমন এক দার্শনিক ও সামাজিক ভাবধারা, যা নারীবাদ (Feminism) ও পরিবেশবাদ (Ecology)-এর ধারণাকে একত্র করে। এই মতবাদ অনুযায়ী, প্রকৃতির প্রতি শোষণ ও নারীর প্রতি নিপীড়ন—দুটির উৎস একই, অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক ও ভোগবাদী সামাজিক কাঠামো। ইকোফেমিনিস্টরা মনে করেন, যেমনভাবে সমাজে নারীকে অবদমিত করা হয়েছে, তেমনি প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ করা হয়েছে মানুষের ক্ষমতালিপ্সার কারণে।
তারা বিশ্বাস করেন, প্রকৃতি ও নারী উভয়েই সৃজনশীল, পোষণশীল ও জীবনের ধারক, তাই তাদের সম্মান ও রক্ষা করা মানবসভ্যতার নৈতিক দায়িত্ব। ইকোফেমিনিজম পরিবেশ সংরক্ষণ, সমতা ও সহাবস্থানের মাধ্যমে সমাজে এক মানবিক ও টেকসই ভারসাম্য গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।
৩.৩ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হল কেন? ME-’17
উত্তর: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিভেদ প্রথার বিরোধী হলেও অসবর্ণ বিবাহ ও উপবীত বর্জনের দাবি মানতে পারেননি। ফলে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ বাধে। ফলে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্থাপিত হয় আদি ব্রাহ্মসমাজ।
৩.৪. বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার নারীদের, বিশেষত গৃহবধূদের মধ্যে শিক্ষা, সচেতনতা ও নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানো। এর মুখ্য লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ –
নারীশিক্ষার প্রসার – তখনকার সমাজে নারীশিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল। বামাবোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে নারীদের জ্ঞানার্জন ও স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি – নারীদের তাদের সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সমাজে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করা ছিল এই পত্রিকার একটি বড় উদ্দেশ্য।
কুসংস্কার দূরীকরণ – নারীসমাজের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটানো।
৩.৫ ফরাজি আন্দোলন কি নিছক ধর্মীয় আন্দোলন ছিল? ME-’20
উত্তর: ফরাজি আন্দোলন নিছক একটি ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, যদিও এই আন্দোলনের সূচনা এবং শক্তির উৎস ছিল ধর্মীয় (ইসলামের ফরাজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য পালন এবং ধর্মীয় সংস্কার), কিন্তু এর প্রকৃতি ছিল বহুমাত্রিক। এটি একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনেও রূপ নেয়। জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার এবং কৃষকদের ওপর চাপানো অতিরিক্ত কর (আবওয়াব) এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই আন্দোলনের একটি প্রধান কারণ ও লক্ষ্যে পরিণত হয়। এই অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক ও কারিগরদের সংঘবদ্ধ করাই ছিল এর একটি বড় অভিষ্ট। ফরাজি আন্দোলন ছিল একটি ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আন্দোলনের পাশাপাশি একটি কৃষক-প্রতিবাদ ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন। একে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আন্দোলন বলে সীমাবদ্ধ করে দেখা যায় না।
৩.৬ দিকু কারা?
উত্তর: দিকু হল বহিরাগত সেই সব মধ্যস্বত্বভোগী (যেমন – জমিদার, জোতদার, মহাজন) যারা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করে আদিবাসীদের শোষণ ও নিপীড়ন করত। ‘দিকু’ শব্দটি একটি সাঁওতালি শব্দ, যার অর্থ ‘প্রতারক’।
৩.৭ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভাসমিতির যুগ’ বলা হয় কেন? ME-’17
উত্তর: উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভাসমিতির যুগ’ বলা হয় কারণ এই সময়কালে বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, সামাজিক-রাজনৈতিক আলোচনা এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অসংখ্য সভা, সমিতি ও সংগঠনের উদ্ভব ঘটে।
৩.৮ ইলবার্ট বিল কী?
উত্তর: ইলবার্ট বিল ছিল ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রস্তাবিত আইন, যা ১৮৮৩ সালে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপনের আইনসচিব স্যার কোর্টনি পার্শি ইলবার্ট প্রস্তুত করেছিলেন। এই বিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিচার ব্যবস্থায় বিদ্যমান জাতিগত বৈষম্য দূর করা। এটির মাধ্যমে ইউরোপীয় বা শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের বিচার করার ক্ষমতা ভারতীয় বিচারকদের দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল, যা শুধুমাত্র ইউরোপীয় বিচারকদেরই ছিল। এই বিলটি ব্রিটিশ ভারতের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি করে, যারা এই আইনের মাধ্যমে তাদের বিশেষ অধিকার হারানোর আশঙ্কা করেছিল। অবশেষে, বিরোধিতার মুখে একটি সমঝোতা হিসেবে এই বিল পাস হয়, তবে শর্তারোপ করা হয় যে, ইউরোপীয় অভিযুক্তদের বিচারের সময় জুরি বক্সে অর্ধেক সদস্য ইউরোপীয় হতে হবে।
৩.৯ মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিখ্যাত কেন?
উত্তর: মদনমোহন তর্কালঙ্কার মূলত নিম্নলিখিত কারণে বিখ্যাত –
বাংলা গদ্যের বিকাশ ও শিশুশিক্ষা – তিনি বাংলা ভাষায় শিশুদের জন্য ‘শিশুশিক্ষা’ (১৮৪৯) সহ একাধিক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন, যা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’-এর আগে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনা লিখিত বাংলা ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
সমাজ সংস্কার – তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন এবং ১৮৫৭ সালে প্রথম বিধবা বিবাহ সংঘটিত করতে সাহায্য করেন।
নারী শিক্ষার প্রসার – তিনি জোন বেথুন প্রতিষ্ঠিত বেথুন স্কুলে তাঁর দুই কন্যাকে ভর্তি করেন ও বিনা বেতনে মেয়েদের পড়াতেন। এছাড়া তিনি ‘সর্বশুভকরী’ পত্রিকায় স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে লেখালেখি করেন।
বাংলা নবজাগরণের অগ্রদূত – সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও তিনি বাংলা ভাষা ও শিক্ষার প্রসারে কাজ করে বাংলা নবজাগরণে ভূমিকা রাখেন।
৩.১০ কে, কেন ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড’ প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি যুবকদের মধ্যে উদ্যোগী মনোভাব গড়ে তোলা এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে চাকরির বিকল্প হিসেবে একটি দেশীয় শিল্প গড়ে তোলা। এছাড়াও, ভারতবর্ষে প্রথম রাসায়নিক ও ঔষধ শিল্পের সূচনা করাও তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল।
৩.১১ ‘উজালিপরাজ’ ও ‘কালিপরাজ’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: উজালিপরাজ – গান্ধিপন্থী কর্মীরা কালিপরাজদের নাম দেন রানিপরাজ বা উজালিপরাজ (১৯২১ খ্রি.)। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তারা কালিপরাজদের (কালো মানুষ) নাম বদল করে রানিপরাজ (অরণ্যবাসী) বা উজালিপরাজ (উজ্জ্বল মানুষ) নাম রাখেন।
কালিপরাজ – কালিপরাজ কথাটির মানে হল কালো মানুষ। তারা দুবলা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং বারদৌলির জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ। তারা বংশপরম্পরায় ঋণদান হিসেবে পাতিদার কৃষকদের জমি চাষ করত।
৩.১২ কী উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠিত হয়? ΜΕ-’20
উত্তর: জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখের উদ্যোগে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মূল উদ্দেশ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ –
১. জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার ও বাস্তবায়ন করা।
২. কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া।
৩. জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে অবস্থানরত বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের নেতা-কর্মীদের একত্রিত করা।
৪. কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করার মাধ্যমে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
৩.১৩ সাইমন কমিশনবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল কেন?
উত্তর: সাইমন কমিশনবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল নিম্নলিখিত প্রধান কারণগুলোর জন্য –
ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের সম্পূর্ণ অভাব – ১৯২৭ সালে গঠিত এই কমিশনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ৭ জন সদস্য থাকলেও একজনও ভারতীয় সদস্য ছিলেন না। ভারতীয়রা তাদের নিজেদের ভবিষ্যত সংবিধান ও শাসনসংস্কার বিষয়ে মতামত দিতে পারেনি, যা ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অবজ্ঞাকেই নির্দেশ করে।
‘শ্বেতাঙ্গ কমিশন’ হিসেবে পরিচয় – কমিশনটিকে একটি ‘অল-হোয়াইট কমিশন’ (All-White Commission) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতীয়দের বাদ দিয়ে তাদেরই ভবিষ্যৎ নির্ধারণের চেষ্টাকে ভারতীয় জনগণ তাদের মর্যাদা ও অধিকারের উপর চরম আঘাত হিসেবে দেখে।
স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে উপেক্ষা – ভারতীয়রা মনে করেছিল, তাদের ভবিষ্যতের সাংবিধানিক কাঠামো নির্ধারণে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ থাকা উচিত। কমিশনে ভারতীয় প্রতিনিধি না থাকায় এটি ভারতের স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।
৩.১৪ পুনা চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ কেন?
উত্তর: পুনা চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত কারণে –
১৯৩২ সালের পুনা চুক্তি একটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এর গুরুত্ব নিম্নরূপ –
গান্ধিজির জীবন রক্ষা – এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে মহাত্মা গান্ধি তাঁর আমরণ অনশন প্রত্যাহার করেন, যা তাঁর জীবনের সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।
সম্প্রীতির প্রতীক – এটি হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ একটি বড় বিভাজন (দলিত ও অ-দলিত Hindus) রোধ করে। গান্ধিজি একে হিন্দু সমাজের বিভাজনের হাত থেকে রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।
দলিতদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি – চুক্তির মাধ্যমে দলিতদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ব্রিটিশ প্রস্তাবিত ৭১ টি থেকে বেড়ে ১৪৭ টিতে পৌঁছায়। এটি দলিতদের জন্য প্রাদেশিক আইনসভায় উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্বের পথ খুলে দেয়।
যৌথ নির্বাচন প্রচার বজায় রাখা – ড. আম্বেদকর পৃথক নির্বাচনের দাবি ত্যাগ করে যৌথ নির্বাচনের নীতি মেনে নেন। গান্ধিজির মতে, এটি হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার পক্ষে অপরিহার্য ছিল।
ভারতীয় রাজনীতিতে দলিতদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা – এই চুক্তি দলিতদের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি মাইলফলক ছিল এবং ড. আম্বেদকরকে জাতীয় স্তরের একজন প্রধান নেতা হিসেবে উপস্থাপিত করে।
ভবিষ্যতের ভিত্তি – পুনা চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংরক্ষণের নীতি পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার একটি ভিত্তি তৈরি করে।
৩.১৫ পোত্তি শ্রীরামালু কে ছিলেন? ME-’19
উত্তর: পত্তি শ্রীরামালু ছিলেন একজন গান্ধীবাদী নেতা এবং সমাজসেবী। তিনি তেলুগু ভাষাভাষীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য (অন্ধ্রপ্রদেশ) গঠনের দাবিতে ১৯৫২ সালের ১৯ অক্টোবর আমরণ অনশন শুরু করেন। ৫৮ দিন অনশন চালানোর পর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ ভারত সরকার একটি স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হয়। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের আন্দোলনে তাঁর এই অবিস্মরণীয় ত্যাগের জন্য তাঁকে ‘অমরজীবী’ উপাধি দেওয়া হয়।
৩.১৬ দেশভাগের পর ‘পুনর্বাসনের যুগ’ বলতে কী বোঝো?
উত্তর: দেশভাগের পর ‘পুনর্বাসনের যুগ’ বলতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত সরকার কর্তৃক উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান ও তাদের পুনর্বাসনের উপর গুরুত্ত্ব প্রদানের সময়কালকে বোঝায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল ভারতের প্রধান জাতীয় সমস্যা। ভারত বিভাজন ও পাঞ্জাব ও বঙ্গবিভাজনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ শিখ ও হিন্দু নিরাপত্তা, জীবন ও জীবিকার সন্ধানে ভারতে চলে আসেন। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার প্রথম পাঁচ বছর অর্থাৎ, ১৯৪৭-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে ও পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্ব দেয়, তাই এই সময়কালকে “পুনর্বাসনের যুগ” বলে অভিহিত করা হয়।
বিভাগ-ঘ
৪. সাত বা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)
উপবিভাগ ঘ.১
৪.১ আধুনিক ইতিহাসচর্চায় পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব লেখো।
উত্তর:
ভূমিকা – খাদ্যাভ্যাসের মতো মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদও তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আধুনিক ইতিহাসচর্চায় কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ঘটনাই নয়, দৈনন্দিন জীবনের বস্তুগত দিকও গুরুত্ব পেয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এটি শুধু ভৌগোলিক পরিবেশই নয়, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক আদর্শ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ও প্রতিফলিত করে।
পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাসচর্চার বিকাশ –
আধুনিক ইতিহাসচর্চায় পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে গবেষণা একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে ইংল্যান্ডে দি অ্যাসোসিয়েশন অফ ড্রেস হিস্টোরিয়ানস প্রতিষ্ঠা এই ক্ষেত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। ষোড়শ শতকে ম্যাথেউস সোয়ার্জের পোশাকের ছবিসংবলিত বই ফ্যাশনের ইতিহাস বোঝার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এছাড়া, কর্নেল ডালটনের ভারতীয় পোশাকের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, মলয় রায়ের ‘বাঙালির বেশবাস, বিবর্তনের রূপরেখা’ এবং এমা টারলোর ‘ক্লোথিং ম্যাটারস: ড্রেস অ্যান্ড আইডেনটিটি ইন ইন্ডিয়া’ গ্রন্থ পোশাকের ইতিহাসচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে।
পোশাক-পরিচ্ছদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব –
অর্থনৈতিক অবস্থার নির্দেশক – পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা প্রকাশ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজা, জমিদার ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা বিলাসী পোশাক পরতেন, অন্যদিকে দরিদ্রদের পোশাক ছিল সাদামাটা।
ভৌগোলিক প্রভাব – শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষ গরম পোশাক ব্যবহার করে, আর গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ হালকা পোশাক পরে—এটি ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব নির্দেশ করে।
সামাজিক মূল্যবোধ ও লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য – নারী-পুরুষের পোশাকের বৈচিত্র্য থেকে সমাজের রক্ষণশীলতা বা প্রগতিশীলতা বোঝা যায়। নারীর পোশাকের স্বাধীনতা সমাজে নারীর অবস্থানেরই ইঙ্গিত দেয়।
ঔপনিবেশিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন – ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য পোশাকের অনুপ্রবেশ ঘটে। কোট-প্যান্টের ব্যবহার তখন শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে নতুন পরিচয়ের সামগ্রি হয়ে ওঠে।
রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী প্রকাশ – ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর খাদি আন্দোলন ও গান্ধী টুপি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠে। কংগ্রেস নেতাদের ‘জহর কোট’ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রকাশ ছিল।
উপসংহার – বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পোশাক-পরিচ্ছদও বিশ্বজনীন হয়েছে, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী পোশাক এখনও সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচয়ের অংশ। আধুনিক ইতিহাসচর্চায় পোশাক-পরিচ্ছদ কেবল বাহ্যিক সাজ নয়, এটি মানুষের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির গতিপথ বুঝতে অপরিহার্য উপাদান।
৪.২ আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় নারী ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা – ঐতিহাসিক গবেষণার মূলধারায় দীর্ঘকাল যাবৎ নারীদের ভূমিকা ও অভিজ্ঞতা উপেক্ষিত বা প্রান্তিকভাবে স্থান পেয়েছে। আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় নারী ইতিহাসচর্চার প্রবেশ একটি মৌলিক ও প্রয়োজনীয় রূপান্তর এনেছে, যা কেবল একটি নতুন বিষয়ই সংযোজন করেনি, বরং ঐতিহাসিক বোঝাপড়ার পুনর্গঠন করেছে। এটি ভারতীয় সমাজের জটিল ও বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে আরও সঠিকভাবে উপস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে।
আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় নারী ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব –
ঐতিহাসিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা – প্রচলিত ইতিহাসচর্চা প্রধানত রাষ্ট্রনায়ক, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রশাসনিক সংস্কার ইত্যাদি ‘পুরুষকেন্দ্রিক’ বিষয়বস্তু নিয়ে গড়ে উঠেছিল, যেখানে নারীদের অবদান ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় অনুপস্থিত ছিল। নারী ইতিহাসচর্চা এই অসমতা দূর করে ইতিহাসকে আরও সামগ্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। এটি প্রমাণ করে যে নারীরা কেবল ইতিহাসের নির্মাতাই নন, তার সক্রিয় অংশগ্রহণকারীও বটে।
সামাজিক কাঠামো ও লিঙ্গবৈষম্যের বিশ্লেষণ – নারী ইতিহাসচর্চা শুধু নারী ‘নায়িকা’দের গল্পই বলে না, বরং সেইসব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনি কাঠামোকেও বিশ্লেষণ করে যেগুলো নারীর জীবন, শ্রম ও পরিচয়কে রূপ দিয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করেছে। এটি জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, ধর্মের সাথে লিঙ্গের আন্তঃসম্পর্ক কীভাবে নিপীড়নের বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করে, তা বুঝতে সহায়তা করে।
রাজনৈতিক আন্দোলনের পুনর্মূল্যায়ন – ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসচর্চায় নারী ইতিহাস একটি গুণগত পরিবর্তন এনেছে। এটি শুধু সরোজিনী নাইডু বা অরুণা আসফ আলির মতো বিশিষ্ট নেত্রীদের ভূমিকাই নয়, বরং লক্ষাধিক সাধারণ নারীর অংশগ্রহণ, তাদের রাজনৈতিককরণের প্রক্রিয়া, এবং এই অংশগ্রহণ কীভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করেছিল, তা তুলে ধরে। এটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে একটি কেবলমাত্র পুরুষতান্ত্রিক প্রকল্প হিসেবে না দেখে একটি জেন্ডার্ড (gendered) প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণের সুযোগ করে দেয়।
সংস্কার আন্দোলন ও নারী এজেন্সি (Agency) – সতীদাহ প্রথা রদ, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি সংস্কার আন্দোলনের প্রচলিত বর্ণনায় প্রায়শই পুরুষ সংস্কারকদের ভূমিকাই মুখ্য হয়ে উঠত। নারী ইতিহাসচর্চা রাসসুন্দরী দেবী, পণ্ডিতা রমাবাই, বেগম রোকেয়ার মতো নারীদের লেখনী ও সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের ‘এজেন্সি’ বা সক্রিয় ভূমিকাকে সামনে নিয়ে আসে। এটি দেখায় যে নারীরা কীভাবে তাদের অধিকারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে লড়েছেন এবং সংস্কারের ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছেন বা পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন।
অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুনর্লিখন – নারী ইতিহাস শিল্পায়ন, নগরায়ন ও অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব শুধুমাত্র জাতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বরং নারীর গৃহস্থালি শ্রম, কৃষি শ্রম, এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কাজের উপর তার প্রভাবের আলোকে বিশ্লেষণ করে। এটি দেখায় কীভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তন নারী শ্রমকে অদৃশ্য করে, মূল্যায়নহীন রাখে বা নতুন রূপ দেয়।
ব্যক্তিগতকে রাজনৈতিক হিসেবে চিহ্নিতকরণ – নারী ইতিহাসচর্চার একটি বড় অবদান হল এটি প্রমাণ করে যে ‘ব্যক্তিগত’ ক্ষেত্রটি (যেমন- পরিবার, বৈবাহিক সম্পর্ক, প্রজনন অধিকার, যৌনতা) গভীরভাবে রাজনৈতিক। দাম্পত্য নির্যাতন, যৌতুক, উত্তরাধিকারের অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে নারী ইতিহাসের হাত ধরেই।
উপসংহার – সামগ্রিকভাবে, আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় নারী ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ইতিহাসকে একটি সমতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাস্ত্রে রূপান্তরের দাবিদার। নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামকে কেন্দ্রে রেখে এটি ভারতের আধুনিকীকরণ, জাতীয়তাবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের জটিল গতিপথকে নতুন ও সমৃদ্ধতর দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে সাহায্য করে। এটি শুধু অতীতের একটি শূন্যতা পূরণই করেনি, বরং ভবিষ্যতের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমতাপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিও সরবরাহ করে।
উপবিভাগ ঘ.২
৪.৩ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল কেন? ME-’17
উত্তর:
ভূমিকা – সাঁওতালরা ছিলেন একটি শান্তিপ্রিয় ও পরিশ্রমী কৃষিজীবী আদিবাসী সম্প্রদায়। ব্রিটিশ শাসনামলে মহাজন, জমিদার, ব্যবসায়ী ও ব্রিটিশ কর্মচারীদের তারা “দিকু” (বহিরাগত শোষক) হিসাবে চিহ্নিত করত। ১৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে দামিন-ই-কোহ অঞ্চলে সাঁওতালরা এই দিকুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যা ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
বিদ্রোহের মূল কারণসমূহ –
অত্যধিক ভূমিরাজস্ব আদায় – ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জমিদাররা সাঁওতালদের কাছ থেকে অত্যধিক হারে ভূমিরাজস্ব আদায় করত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাত্র ১৮ বছরে খাজনা ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা সাঁওতালদের জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে।
মহাজনদের শোষণ – নগদ অর্থে খাজনা পরিশোধের চাপে সাঁওতালরা মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হত। মহাজনরা ৫০% থেকে ১০০% হারে সুদ আদায় করত এবং বিভিন্ন কৌশলে তাদের জমি দখল করত।
ইংরেজ কর্মচারী ও ঠিকাদারদের অত্যাচার – রেললাইন নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ঠিকাদার ও ব্রিটিশ কর্মচারীরা সাঁওতালদের নামমাত্র মজুরিতে কাজ করাত, তাদের সম্পদ লুট করত এবং নারীদের প্রতি অশালীন আচরণ করত।
ব্রিটিশ আইনের প্রভাব – সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও বিচারব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সরকার তাদের উপর ব্রিটিশ আইন চাপিয়ে দেয়, যা তাদের রীতিনীতির পরিপন্থী ছিল।
ব্যবসায়ীদের শোষণ – ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের কাছ থেকে কম দামে ফসল কিনতেন এবং বাটখারার কারচুপি করে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করতেন।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবমাননা – দিকুদের দ্বারা সাঁওতাল নারীদের প্রতি অসন্মানজনক আচরণ এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরের চেষ্টা সাঁওতালদের ক্ষুব্ধ করে তোলে।
উপসংহার – সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শাসন, জমিদারি শোষণ ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত প্রতিবাদ। এই বিদ্রোহ সাঁওতালদের স্বায়ত্তশাসন, ন্যায়বিচার ও মর্যাদার দাবিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।
৪.৪ কোল বিদ্রোহের গুরুত্ব লেখো।
উত্তর: ১৮৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত কোল বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ ভারতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদিবাসী প্রতিরোধ আন্দোলন। ছোটোনাগপুর অঞ্চলের কোল উপজাতি দ্বারা সংগঠিত এই বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিম্নরূপ –
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত আদিবাসী প্রতিরোধ – কোল বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, তাদের ভূমি রাজস্ব নীতি এবং বহিরাগত শোষকদের (জমিদার, মহাজন) বিরুদ্ধে কোল সম্প্রদায়ের একটি সুসংগঠিত ও ব্যাপক প্রতিরোধ। এটি দেখিয়ে দেয় যে আদিবাসীরা তাদের অধিকার রক্ষায় কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।
ব্রিটিশ নীতিতে পরিবর্তন – বিদ্রোহটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে ব্রিটিশ সরকারকে তাদের নীতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। এর ফলশ্রুতিতে, ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ‘দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি’ গঠন করা হয়। এই প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল কোলদের এলাকায় সরাসরি ব্রিটিশ আইন চাপিয়ে না দিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি পরিচালনায় একটি পৃথক ব্যবস্থা করা।
আদিবাসী অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি – ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করে নেয় যে কোলদের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি ও আইন-কানুনে হস্তক্ষেপ করাই ছিল বিদ্রোহের একটি বড় কারণ। তাই তারা কোলদের তাদের স্বীয় প্রথাগত আইন ও রীতিনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার অধিকার দেয়। ব্রিটিশ আইন কোল অধ্যুষিত এলাকায় প্রয়োগ বন্ধ করা হয়।
বহিরাগত শোষণ রোধ – বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার কোল অঞ্চলে বহিরাগত জমিদার, মহাজন ও ‘দিকু’দের অবাধ প্রবেশ ও শোষণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এর লক্ষ্য ছিল কোলদের জমি ও সম্পদ থেকে বহিরাগতদের দূরে রাখা এবং শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা।
উপসংহার – সামগ্রিকভাবে, কোল বিদ্রোহ কেবল একটি সামরিক সংঘাতই ছিল না, বরং এটি একটি অত্যন্ত সফল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এই বিদ্রোহের ফলেই ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মতো ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির জন্য একটি পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করতে বাধ্য হয় এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও ভূমি-সংক্রান্ত অধিকারগুলিকে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দেয়। এটি পরবর্তীকালে অন্যান্য আদিবাসী আন্দোলনকেও প্রেরণা যুগিয়েছিল।
উপবিভাগ ঘ.৩
৪.৫ বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার বিকাশে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের কীরূপ অবদান ছিল? ΜΕ-’19
উত্তর:
ভূমিকা – ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় পাশ্চাত্য ভিত্তিক আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা প্রসারে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন একজন অগ্রদূত ও সংগঠক। একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতির প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন অন্ধকারবাদ ও কুসংস্কারের পরিবর্তে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটবে।
বিজ্ঞানচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন – ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী অবদান হলো ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স (IACS) প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি ছিল ভারতের প্রথম মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান। লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের আদর্শে তিনি এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যার মতো মৌলিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণাকে উৎসাহিত করা।
গবেষণা ও জ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থা – বিজ্ঞানচর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার পাশাপাশি তিনি এর বিস্তারেরও ব্যবস্থা করেন। তিনি ‘ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স’ নামে একটি গবেষণা পত্রিকা চালু করেন, যা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশের একটি নিজস্ব মাধ্যম দিয়েছিল। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হত, যা বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য সৃষ্টি ও নোবেল প্রাপ্তিতে ভূমিকা – ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত IACS শুধু একটি গবেষণাগারই ছিল না, এটি একটি বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের সূচনা করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীকালে সিভি রমন, জগদীশ চন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, কে. এস. কৃষ্ণান-এর মতো খ্যাতনামা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের জন্য একটি সক্রিয় গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠানেই স্যার সিভি রমন তাঁর যুগান্তকারী ‘রমন ইফেক্ট’ আবিষ্কার করেছিলেন, যার জন্য তিনি ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এভাবে মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই ভারতীয় বিজ্ঞান বিশ্ব দরবারে মর্যাদার স্থান অধিকার করে।
মূল্যায়ন – উপসংহারে বলা যায়, ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার কেবল একজন চিকিৎসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রকৃত পথিকৃৎ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতির দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির জন্য চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা অপরিহার্য। একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং একটি টেকসই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি বাংলা তথা ভারতের বিজ্ঞান আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, যার সুফল পরবর্তী প্রজন্ম পেয়েছে।
৪.৬ বাংলায় ছাপাখানা বিস্তারে উইলিয়ম কেরি সাহেবের কী ভূমিকা ছিল?
উত্তর: উইলিয়ম কেরি বাংলায় ছাপাখানা বিস্তারের অগ্রদূতদের অন্যতম, যিনি উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলা ভাষা ও মুদ্রণ সংস্কৃতির বিকাশে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮০০ সালে সেরাম্পুরে মিশন প্রেস (Serampore Mission Press) প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল বাংলার প্রথম দিকের আধুনিক ছাপাখানাগুলির একটি। এই প্রেস থেকেই বাংলা, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বিপুল পরিমাণ বই, ধর্মগ্রন্থ, শব্দকোষ ও শিক্ষাপাঠ প্রকাশিত হয়।
কেরি বাংলা ভাষা শিখে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন এবং বাংলা ভাষাকে মুদ্রণযোগ্য ও শিক্ষার উপযোগী রূপ দিতে সহায়তা করেন। তাঁর প্রেসে স্বল্পমূল্যে পাঠ্যবই, বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ ও ধর্মীয় সাহিত্য ছাপা হতো, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটায়।
তিনি বাংলা বই ছাপানোর জন্য স্থানীয় টাইপফেস ও অক্ষরছাঁচ উন্নত করেন, যা বাংলা মুদ্রণশিল্পের অগ্রগতির ভিত্তি তৈরি করে। কেরি ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় সেরাম্পুর প্রেস একসময় ভারতের সবচেয়ে বড় ও আধুনিক প্রকাশনা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়।
এছাড়া, কেরি বাংলায় সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার প্রচেষ্টায় ছাপাখানাকে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি বাংলায় নবজাগরণের সূচনায় বৌদ্ধিক জাগরণ সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীকালে সংবাদপত্র, সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার পথ সুগম করে।
সুতরাং, বলা যায় যে উইলিয়ম কেরি বাংলায় ছাপাখানা বিস্তারের জনকস্বরূপ, যাঁর উদ্যোগে বাংলায় আধুনিক মুদ্রণ, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং বাংলা ভাষা নতুন যুগে প্রবেশের সুযোগ পায়।
উপবিভাগ ঘ.৪
৪.৭ দলিত আন্দোলন বিষয়ে গান্ধি-আম্বেদকর বিতর্ক নিয়ে একটি টীকা লেখো। ME-’17
উত্তর:
ভূমিকা – ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দলিতদের রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধী ও ড. ভীমরাও আম্বেদকরের মধ্যে একটি মৌলিক মতপার্থক্য দেখা দেয়। এই বিতর্ক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গভীর প্রভাব ফেলে।
বিতর্কের কেন্দ্রীয় বিষয় – বিতর্কের মূল বিষয় ছিল দলিতদের (যাদের তখন ‘অস্পৃশ্য’ বলা হত) জন্য পৃথক নির্বাচকক্ষেত্রের দাবি। আম্বেদকরের অবস্থান ছিল যে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বর্ণভিত্তিক নিপীড়ন ও বর্জনের কারণে দলিতদের নিজেদের জন্য আলাদা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বতা আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল থাকলে দলিতদের স্বার্থ কখনোই সুরক্ষিত হবে না। অন্যদিকে, গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। তিনি দলিতদের ‘হরিজন’ (ঈশ্বরের মানুষ) আখ্যা দিয়ে তাদের হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ বলে মনে করতেন। তার মতে, পৃথক নির্বাচকক্ষেত্র ভারতের হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করে দেবে এবং অস্পৃশ্যতা দূর করার তার আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবে। তিনি এই দাবির বিরোধিতা করেন।
ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ও পুনা চুক্তি (১৯৩২) – এই বিতর্ক চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ডের ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’ (Communal Award) ঘোষণার মাধ্যমে। এই সিদ্ধান্তে দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকক্ষেত্র মঞ্জুর করা হয়। এটির তীব্র প্রতিবাদে গান্ধীজি ১৯৩২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ইয়েরওয়াদা কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করেন। তিনি এটিকে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে একটি ‘আত্মঘাতী ফাটল’ হিসেবে দেখেন। গান্ধীজির জীবনসংশয় দেখা দিলে আম্বেদকর চাপের মুখে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর গান্ধীজি ও আম্বেদকরের মধ্যে ঐতিহাসিক পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
পুনা চুক্তির শর্তাবলি – দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকক্ষেত্রের দাবি প্রত্যাহার করা হয়। এর বদলে, সাধারণ নির্বাচকক্ষেত্রেই দলিত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতে ১৪৮টি নির্ধারিত হয়, যা পরে বৃদ্ধি পায়। এই আসনগুলোর জন্য ভোট দেবেন সবাই, কিন্তু শুধুমাত্র দলিত ভোটাররাই প্রার্থী বাছাই করতে পারবেন। গান্ধী-আম্বেদকর বিতর্ক ও পুনা চুক্তি ছিল ভারতের দলিত রাজনীতির একটি টার্নিং পয়েন্ট।
আম্বেদকরের জন্য আপোষ – আম্বেদকরকে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি—পৃথক নির্বাচকক্ষেত্র—ত্যাগ করতে হয়েছিল। তিনি এটিকে একটি বড় ত্যাগ বলে মনে করতেন, কিন্তু গান্ধীজির জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি এই আপোষ মেনে নেন।
গান্ধীজির নৈতিক বিজয় – গান্ধীজি তাঁর অনশনের মাধ্যমে হিন্দু সমাজে এক বড় ধরনের নৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের ঐক্য রক্ষা করেন।
দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব – পুনা চুক্তির মাধ্যমে চালু হওয়া সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থাই স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও গৃহীত হয় এবং এটি ভারতের রাজনীতিতে দলিতদের অংশগ্রহণের ভিত্তি হয়ে ওঠে।
মতপার্থক্যের ধারা – এই বিতর্ক দুটি ভিন্ন দর্শনকে চিহ্নিত করে: আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংবিধান ও আইনের মাধ্যমে দলিতদের ক্ষমতায়নের, অন্যদিকে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমাজ সংস্কার ও নৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে।
উপসংহার – গান্ধী ও আম্বেদকরের এই বিতর্ক কেবল একটি রাজনৈতিক ইস্যুই ছিল না, বরং এটি ছিল সামাজিক ন্যায়, সমতা এবং একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের পথনিয়ে দুটি ভিন্ন কিন্তু গভীর চিন্তার সংঘাত। পুনা চুক্তি একটি তাৎক্ষণিক সংকটের সমাধান করলেও দলিতদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নটি ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে থেকে যায়।
৪.৮ অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা – ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাথে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করা। গান্ধীজীর আহ্বানে নারীরা ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিকাকে একটি নতুন মাত্রা দেয়।
নারীদের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত – ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নারীদের এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
আন্দোলনে নারীদের কর্মসূচি ও ভূমিকা – প্রাথমিকভাবে নারীদের জন্য কর্মসূচি সীমিত ছিল—স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশি পণ্য বর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু নারীরা কেবল এই সীমিত কর্মসূচির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি; তারা আরও সক্রিয় ও সাহসী ভূমিকা পালন করে –
বিক্ষোভ ও মিছিল – সারা দেশে নারীরা সভা, মিছিল ও পিকেটিং-এ অংশ নেয়। ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর ইংল্যান্ডের যুবরাজ (প্রিন্স অফ ওয়েলস) এর ভারত আগমন উপলক্ষে বোম্বাইয়ে হাজার হাজার নারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।
নেতৃত্ব ও কারাবরণ – ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কলকাতায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নারীরা সক্রিয় অংশ নেয়। এই বিক্ষোভে চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী, বোন উর্মিলা দেবী ও ভাইঝি সুনীতি দেবী গ্রেফতার হন।
সংগঠন গঠন – উর্মিলা দেবী চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘নারী কর্মমন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ সরকার কলকাতায় সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করলে এই সংগঠনের সদস্যরা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেয়।
শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ – ১৯২২ সালে স্টিমার কোম্পানির ধর্মঘটে নেলী সেনগুপ্তার নেতৃত্বে নারীরা ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।
আর্থিক সহায়তা – জাতীয় কংগ্রেসের তিলক স্বরাজ তহবিলে লক্ষ্য টাকা সংগ্রহে বাংলার নারীরা তাদের গহনা ও অর্থ দান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
মূল্যায়ন – অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের যোগদান ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তাদের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে একটি প্রকৃত গণআন্দোলনে পরিণত করেছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, “এই আন্দোলনে সারা দেশ জুড়ে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়।” নারীরা তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শুধু আন্দোলনকেই শক্তিশালী করেনি, বরং সমাজে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানও পুনর্ব্যাখ্যা করেছিলেন।
বিভাগ-ঙ
৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ ঔপনিবেশিক শাসনে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহগুলির কারণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা – অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই দেশের কৃষক ও উপজাতি সম্প্রদায়গুলির উপর চেপে বসে একের পর এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়ন। এই শোষণমূলক নীতির প্রতিক্রিয়ায় ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতজুড়ে একের পর এক কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন প্রভৃতি এইসব বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। বিদ্রোহগুলির মূল কারণগুলি নিম্নরূপ –
ঔপনিবেশিক ভূমিরাজস্ব নীতি ও অত্যধিক রাজস্ব আদায় – ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ‘দেওয়ানি’ লাভ করে, তখন থেকেই তারা কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের হার ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেয়। স্থায়ী বন্দোবস্ত, র্যয়টওয়ারি, মহারাঠা ব্যবস্থা প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্যই ছিল কোম্পানির কোষাগার পূরণ করা। কৃষকদের আর্থিক সামর্থ্যের প্রতি কোনো মনোযোগ না দিয়ে খাজনা ধার্য করা হত। খাজনা না দিতে পারলে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত, যা তাদের চরম দারিদ্র্য ও ঋণের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ করে ফেলে।
জমিদার ও মহাজন শ্রেণির দ্বৈত শোষণ – ঔপনিবেশিক ভূমি ব্যবস্থা জমিদার ও মহাজনদের একটি শক্তিশালী শোষক শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। জমিদাররা কোম্পানিকে খাজনা দিত এবং সেই খাজনার চাপ কৃষকের উপর চলে যেত। তারা কর না দিলে জমি থেকে উচ্ছেদ হতেন। অন্যদিকে, খাজনা ও জীবনধারণের খরচ মেটানোর জন্য কৃষকদের মহাজনের কাছ থেকে উচ্চসুদে ঋণ নিতে হত। ঋণ শোধ করতে না পারলে তাদের জমি দখল করা হত, তাদেরকে বেগার শ্রম দিতে বাধ্য করা হত। এই দ্বৈত শোষণ কৃষক ও উপজাতিদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল।
সরকারি কর্মচারী ও পুলিশের নির্যাতন – সরকারি কর্মচারী, রাজস্ব সংগ্রাহক এবং পুলিশ বাহিনী কৃষক ও আদিবাসীদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাত। ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় সেই সময় ১৮ প্রকারের অত্যাচারের উল্লেখ রয়েছে। এই অত্যাচারের মধ্যে ছিল মিথ্যা মামলা, বেআইনি জরিমানা, প্রহার, জবরদস্তি শ্রম দান ইত্যাদি। এই নিপীড়নমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করে।
বাণিজ্যিক ফসল চাষে বাধ্যকতা ও নীল চাষ – ইংরেজ শাসন ভারতকে তাদের শিল্পের কাঁচামালের উৎসে পরিণত করে। তারা কৃষকদের খাদ্য শস্যের জমিতে জোরপূর্বক নীল, তুলা, পাট, আফিমের মতো বাণিজ্যিক ফসল চাষ করতে বাধ্য করে। বিশেষ করে নীল চাষের সাথে জড়িত ছিল চরম শোষণ। নীলকর সাহেবরা কৃষকদের অগ্রিম টাকা দিয়ে ফসলের দাম ধার্য করে দিত, যা বাজার দরের চেয়ে অনেক কম হত। নীল চাষ করতে অস্বীকার করলে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হত। এই জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০) সহ একাধিক বিদ্রোহের জন্ম দেয়।
আদিবাসী অঞ্চলে ঔপনিবেশিক আইন ও প্রশাসনের প্রসার – ইংরেজরা তাদের রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলে তাদের প্রশাসন ও আইন কানুন চালু করে। এটি আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির স্বায়ত্তশাসন, ঐতিহ্যবাহী ‘খুনকাটি’ ব্যবস্থা এবং তাদের ভূমি ও বনাঞ্চলের অধিকারের উপর সরাসরি আঘাত হানে। তাদের আইন ও প্রথাকে অগ্রাহ্য করা হয়। বনাঞ্চলকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ঘোষণা করে তাদের বনজ সম্পদ ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এই হস্তক্ষেপ আদিবাসী বিদ্রোহগুলির (যেমন: কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ) একটি মুখ্য কারণ ছিল।
দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ও কৃষির উপর চাপ – ইংরেজ শাসনের একটি গভীর প্রভাব ছিল ভারতের গৃহশিল্প ও কারুশিল্পের ধ্বংসসাধন। ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে দেশীয় তাঁতশিল্প, লৌহশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে লক্ষ লক্ষ শিল্পী ও কারিগর বেকার হয়ে পড়ে এবং জীবিকার তাগিদে তাদের কৃষির উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এই অতিরিক্ত জনশক্তি কৃষি জমির উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং কৃষকদের দারিদ্র্য আরও বাড়িয়ে তোলে। এই বেকার শিল্পীরা অনেকক্ষেত্রে কৃষক বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
উপসংহার – সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ভারতের কৃষক ও উপজাতি সমাজ এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নীতি, শোষণমূলক ভূমিব্যবস্থা, প্রশাসনিক নিপীড়ন এবং তাদের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপই ছিল এই সকল বিদ্রোহের মৌলিক কারণ। যদিও এই বিদ্রোহগুলি ব্যর্থ হয়, তবুও এগুলি ছিল ভারতের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রারম্ভিক প্রকাশ এবং পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছিল।
৫.২ মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার সমন্বয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ME-’20
উত্তর:
ভূমিকা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ব্যক্তির সার্বিক ও সুষম বিকাশ। তাঁর মতে, প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ, যা কেবলমাত্র মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার গভীর ও সৌন্দর্য্যময় সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই অর্জন সম্ভব। এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিনিকেতন।
প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার সমন্বয় –
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতি হল মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু। প্রকৃতির মাঝে মুক্ত ও সক্রিয় জীবনযাপনের মাধ্যমে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। শহুরে জীবনের কৃত্রিমতা ও চারদেয়ালের আবদ্ধ শিক্ষাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি চেয়েছিলেন একটি এমন শিক্ষাব্যবস্থা যা হবে প্রাকৃতিক, স্বাধীন ও আনন্দময়। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পিছনে এই ধারণাই কাজ করেছিল—যেখানে আকাশ, আলো, বনানী ও মুক্ত প্রান্তরের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠবে।
প্রকৃতির সাথে সখ্যতা – শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে তার নিয়ম ও সৌন্দর্য সরাসরি উপলব্ধি করতে পারে।
গুরু-শিষ্যের আত্মিক বন্ধন – প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুলের আদর্শে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।
সৃজনশীলতার বিকাশ – পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানকেও গুরুত্ব দেওয়া হলেও সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্য ও নাটকের মতো সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটানো।
কর্মমুখী শিক্ষা – শুধু তত্ত্বীয় জ্ঞান নয়, হস্তশিল্প ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবন-উপযোগী ও উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তোলা।
বিশ্বভারতী –
শান্তিনিকেতনের ভিত্তিকে আরও বিস্তৃত করে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী। এটি ছিল তার শিক্ষাচিন্তার চূড়ান্ত রূপ। বিশ্বভারতীর মাধ্যমে তিনি –
ভারতীয় আদর্শের বিশ্বায়ন – ভারতের বৈদিক, উপনিষদিক, বৌদ্ধ, জৈন ও সুফি সহ সমগ্র আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা।
পূর্ব-পশ্চিমের মিলন – বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে একটি সার্বজনীন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা, যেখানে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটবে।
বিদ্যা চর্চার কেন্দ্র – বিশ্বভারতীকে কেবল বিদ্যা বিতরণের স্থান নয়, বরং বিদ্যা সৃষ্টি ও চর্চার একটি পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন।
উপসংহার – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তায় প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার সমন্বয় ছিল একটি জীবনদর্শন। এটি ছিল আধুনিকতার সাথে ঐতিহ্যের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতার এবং জাতীয়তাবোধের সাথে বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক অনন্য মেলবন্ধন। শিক্ষাকে জীবনের সাথে এক ও অভিন্ন করে তোলার এই মহান প্রয়াস তাকে শিক্ষাদর্শনের ইতিহাসে এক অনন্য ও অগ্রগামী চিন্তাবিদের মর্যাদা দিয়েছে।
৫.৩ বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ΜΕ -’24, ’20
উত্তর: বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগ্রাম, যা মূলত ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক কাঠামো থেকে সৃষ্ট অমানবিক অস্পৃশ্যতা, চরম অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি লাভ করা।
আন্দোলনের পটভূমি ও কারণ –
সামাজিক বৈষম্য – নমঃশূদ্ররা হিন্দু সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করত। তাদের ওপর চাপানো ছিল নানান সামাজিক নিষেধাজ্ঞা; মন্দিরে প্রবেশ, সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষা, গ্রহণ করতেও তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হত।
অর্থনৈতিক শোষণ – তারা প্রধানত কৃষিজীবী, ভূমিহীন প্রজা বা কৃষি শ্রমিক ছিল। জমিদার ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে তারা চরম শোষণের শিকার হত।
ধর্মীয় পুনরুত্থান – এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন ধর্মগুরু শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) এবং তার পুত্র শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬-১৯৩৭)। হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্ম প্রচার করেন, যা ছিল একটি সাম্যের ধর্ম, যেখানে সকল বর্ণ-জাতির মানুষ সমান এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য পুরোহিততন্ত্রের প্রয়োজন নেই। তাঁর শিক্ষা নমঃশূদ্র সমাজে আত্মসম্মানবোধ ও সংহতি গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
আন্দোলনের বিবরণ –
সংগঠন গঠন – গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে আন্দোলনটি সুসংগঠিত রূপ নেয়। ১৯১২ সালে বেঙ্গল নমঃশূদ্র অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা তাদের দাবি-দাওয়া উপস্থাপনের জন্য একটি শক্তিশালী মঞ্চ হিসেবে কাজ করে।
শিক্ষা আন্দোলন – গুরুচাঁদ ঠাকুর “শিক্ষা ছাড়া মুক্তি নেই” এই motto গ্রহণ করেন। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য অসংখ্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করেন, যাতে তারা সরকারি চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে।
রাজনৈতিক দাবি – ব্রিটিশ শাসনামলে সংস্কার (প্রস্তাব) যেমন মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার (১৯১৯) এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১৯৩২) এর সময় নমঃশূদ্র নেতারা তাদের সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনী আসন ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরেন।
সম্পর্ক ব্রিটিশ ও জাতীয় কংগ্রেসের সাথে – তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা প্রায়শই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, কারণ তারা আশঙ্কা করত যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আধিপত্যযুক্ত জাতীয় কংগ্রেস তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে না। পরবর্তীতে তারা ড. বি. আর. আম্বেদকরের সর্বভারতীয় দলিত আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেদের যুক্ত করে।
আন্দোলনের ফলাফল ও গুরুত্ব –
এই আন্দোলন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী সামাজিক সচেতনতা ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে। শিক্ষার প্রসার তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে। এটি বাংলার দলিত রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করে এবং উপনিবেশিক ভারতে একটি নিপীড়িত গোষ্ঠীর সংগঠিত সংগ্রামের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। নমঃশূদ্র আন্দোলন ছিল বাংলার দলিত সমাজের ইতিহাসে স্বমর্যাদায় জীবনের জন্য একটি বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি যুগান্তকারী অধ্যায়।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।