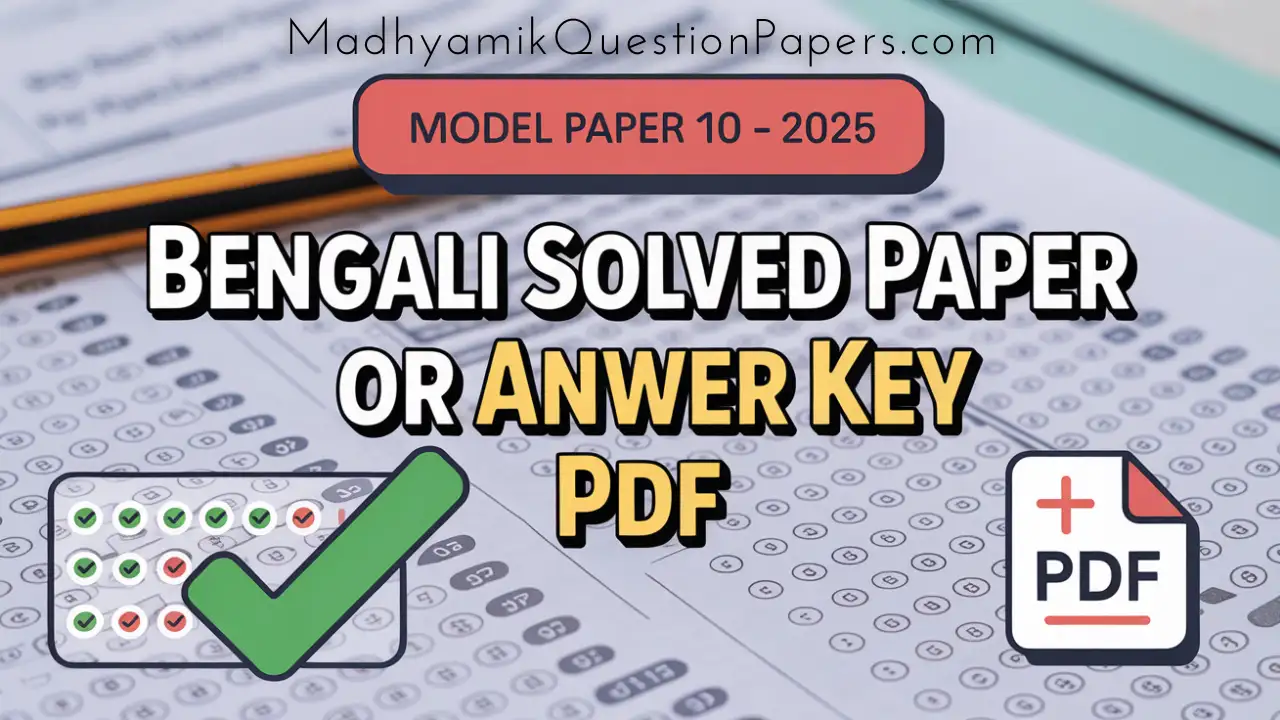আপনি কি ২০২৫ সালের মাধ্যমিক বাংলা Model Question Paper 10 (2025)-এর সঠিক উত্তর খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই প্রতিবেদনে আমরা WBBSE এর বাংলা Model Question Paper 10 (2025)-এর প্রতিটি প্রশ্নের নিখুঁত ও বিস্তারিত উত্তর তুলে ধরেছি।
নিচে প্রশ্নোত্তরগুলো পরপর সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং প্রস্তুতিতে কাজে লাগাতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার উত্তর মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ।
MadhyamikQuestionPapers.com ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তর একেবারে বিনামূল্যে সরবরাহ করে আসছে। ২০২৫ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান এখানেই সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে সম্পূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তরগুলো এখনই দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ “যেন নেশায় পেয়েছে।” কোন্ নেশায়?
(ক) গল্প বলার
(খ) গল্প শোনার
(গ) গল্প লেখার
(ঘ) গল্প পড়ার
উত্তর: (গ) গল্প লেখার
১.২ চকের বাস স্ট্যান্ডের কাছে হরি কী সেজে আতঙ্কের হল্লা তুলেছিল?
(ক) ভূত,
(খ) পাগল,
(গ) পুলিশ,
(ঘ) বাইজি।
উত্তর: (খ) পাগল
১.৩ নদীর বিদ্রোহের কারণ কী?
(ক) অতিবৃষ্টি,
(খ) নদীতে বাঁধ দেওয়া,
(গ) না পাওয়ার বেদনা,
(ঘ) উপর দিয়ে ট্রেন চলা।
উত্তর: (খ) নদীতে বাঁধ দেওয়া
১.৪ ‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশটি কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
(ক) ‘লোরচন্দ্রাণী’,
(খ) ‘পদ্মাবতী’,
(গ) ‘সতীময়না’,
(ঘ) ‘তোহফা’।
উত্তর: (খ) ‘পদ্মাবতী’
১.৫ “কাল-ভয়ংকরের বেশে এবার ওই আসে” যে আসে, সে হল
(ক) সুন্দর,
(খ) অসুন্দর,
(গ) ভূতের দল,
(ঘ) অসুর
উত্তর: (ক) সুন্দর
১.৬ ‘হৈমবতীসুত’ হলেন
(ক) অর্জুন,
(খ) লক্ষ্মণ,
(গ) কার্তিকেয়,
(ঘ) মেঘনাদ।
উত্তর: (গ) কার্তিকেয়
১.৭ বিখ্যাত লেখক শৈলজানন্দের ফাউন্টেন পেনের সংগ্রহ ছিল
(ক) এক ডজন,
(খ) দু’ডজন,
(গ) তিন ডজন,
(ঘ) চার ডজন।
উত্তর: (খ) দু’ডজন
১.৮ ‘লক্ষণা’ যে অর্থ প্রকাশ করে, তা হল-
(ক) বোধমূলক,
(খ) আভিধানিক,
(গ) বিস্তৃত,
(ঘ) সংক্ষিপ্ত।
উত্তর: (ক) বোধমূলক
১.৯ বল-পেনের আর এক নাম
(ক) কুইল,
(খ) ডট পেন,
(গ) ফাউন্টেন পেন,
(ঘ) রিজার্ভার পেন।
উত্তর: (খ) ডট পেন
১.১০ বিপদে মোরে রক্ষা করো রেখাঙ্ক্ষিত পদটির কারক হল
(ক) অধিকরণ কারক,
(খ) অপাদান কারক,
(গ) করণ কারক,
(ঘ) কর্মকারক।
উত্তর: (খ) অপাদান কারক
১.১১ “গায়ক গান করেন” বাক্যের ‘গায়ক’ কর্তাটি হল-
(ক) নিরপেক্ষ কর্তা,
(খ) ব্যতিহার কর্তা,
(গ) প্রযোজ্য কর্তা,
(ঘ) সমধাতুজ কর্তা।
উত্তর: (ঘ) সমধাতুজ কর্তা
১-১২ যাকে তুলনা করা হয়, তাকে বলে
(ক) উপমান,
(খ) উপমিত,
(গ) উপমা,
(ঘ) উপমেয়।
উত্তর: (ঘ) উপমেয়
১.১৩ অলুক দ্বন্দ্বের উদাহরণ
(ক) তেলেভাজা,
(খ) হাটে বাজারে,
(গ) অশান্তি,
(ঘ) গায়ে হলুদ।
উত্তর: (খ) হাটে বাজারে
১.১৪ ক্রিয়াভাগ বলতে বোঝায়
(ক) ক্রিয়াগুচ্ছ,
(খ) ক্রিয়াখন্ড,
(গ) ক্রিয়াদল,
(ঘ) বিশেষণ।
উত্তর: (খ) ক্রিয়াখন্ড
১.১৫ ‘আমাদের মধ্যে যারা ওস্তাদ তারা ওই কালো জলে হরতকী ঘষত।’ বাক্যটি কোন্ শ্রেণির? বাক্য,
(ক) সরল বাক্য,
(খ) জটিল বাক্য,
(গ) যৌগিক বাক্য,
(ঘ) মিশ্র বাক্য।
উত্তর: (খ) জটিল বাক্য
১.১৬ ভাববাচ্যের সমাপিকা ক্রিয়াটি সাধারণত যে ধাতু দিয়ে গঠিত হয়, তা হল
(ক) কর,
(খ) হ,
(গ) বট্,
(ঘ) কৃ।
উত্তর: (খ) হ,
১.১৭ অনুসর্গযুক্ত কর্তা কোন্ বাচ্যে বসে?
(ক) কর্তৃবাচ্যে,
(খ) ভাববাচ্যে,
(গ) কর্মবাচ্যে,
(ঘ) কোনোটিই নয়।
উত্তর: (গ) কর্মবাচ্যে
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ ‘পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট’ বলতে কী বোঝো?
উত্তর: পলিটিক্যাল সাসপেক্ট বলতে বােঝায় রাজনৈতিক সন্দেহভাজন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেই এখানে ‘পলিটিক্যাল সাসপেক্ট বলা হয়।
২.১.২ নদেরচাঁদের দেশের নদীটি কীরকম ছিল?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “নদীর বিদ্রোহ” গল্পে উল্লিখিত নদেরচাঁদের দেশের নদীটি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণস্রোতা এবং সংকীর্ণ প্রকৃতির। নদীবক্ষটি খুব বেশি চওড়া ছিল না। এক বছর অনাবৃষ্টির ফলে নদীটির জল সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেলে নদেরচাঁদ এমনভাবে কেঁদে ফেলেছিল, যেন তার কোনো পরম আত্মীয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।
২.১.৩ “ছেলেরা খুব খুশি হলো,” ছেলেদের খুশি হওয়ার কারণ কী?
উত্তর: পান্নালাল প্যাটেলের “অদল বদল” গল্পে দেখা যায়, অমৃত ও ইসাব নিজেদের মধ্যে কুস্তি লড়তে রাজি না হওয়ায় কালিয়া জোর করে অমৃতকে খোলা মাঠে নিয়ে গিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। এতে কালিয়ার জয় হয়েছে মনে করে গ্রামের ছেলেরা আনন্দে উল্লসিত হয়।
২.১.৪ ‘পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?’ কোন অলৌকিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: এখানে যে অলৌকিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা হলো— তপনের লেখা একটি গল্প ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে এবং তা ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় ছাপা হয়ে হাজার-হাজার ছেলের হাতে হাতে ঘুরবে। ছোটোমাসি ও মেসো বেড়াতে এসে সেই পত্রিকা তপনকে দেন। নিজের নাম ও লেখা গল্প ছাপা হয়েছে দেখে তপনের বুকের রক্ত যেন ছলকে ওঠে। সে মনে করে আজই তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। এই ঘটনাকে তপন পৃথিবীর এক অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করে।
২.১.৫ ‘বড়ো চমৎকার আজকে এই সন্ধ্যার চেহারা।’ সন্ধ্যাটি কেমন?
উত্তর: ‘আজকে এই সন্ধ্যা’ বলতে ছেলেরা যেদিন জগদীশবাবুর বাড়ি ‘স্পোর্টের চাঁদা’ নিতে গিয়েছিলেন, সেই সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে। ঐ দিন সন্ধ্যা ছিল স্নিগ্ধ – শান্ত এবং চারিপাশে ছিল চন্দ্রালোকের উজ্জ্বলতা। ফুরফুরে বাতাস বইছিল এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জগদীশবাবুর বাড়ির বাগানের সব গাছের পাতাও ঝিরি-ঝিরি শব্দ করছিল। বাড়ির বারান্দায় জগদীশবাবু বসেছিলেন, সেই বারান্দায় মস্ত বড় একটি আলো জ্বলছিল। সেই আলোর কাছে একটি চেয়ারে বসেছিলেন জগদীশবাবু।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ ‘আয় আরো হাতে হাত রেখে’ কবি কার হাতে, কেন হাত রাখতে চাইছেন?
উত্তর: কবিতায় ‘আয় আরো হাতে হাত রেখে’ বলে কবি শঙ্খ ঘোষ দেশের সমস্ত মানুষকে একসাথে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি চান সকলে হাতে হাত রেখে, মিলেমিশে, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে একত্রে থাকুক। দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের প্রয়োজন — সেই কারণেই কবি এই আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এই ঐক্যই পারে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।
২.২.২ ‘পশুরা বেরিয়ে এল’ বেরিয়ে এসে কী করেছিল?
উত্তর: ‘পশুরা বেরিয়ে এসে এমন এক অশুভ শব্দ করেছিল, যা দিনের সমাপ্তি এবং অন্ধকার সময়ের সূচনার ইঙ্গিত দেয়।
২.২.৩ ‘বিধি মোরে না কর নৈরাশ।।’ উক্তিটি কার?
উত্তর: আলওলের ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতায়— ‘বিধি মোরে না কর নৈরাশ। ‘ সমুদ্রকন্যা পদ্মা উক্তিটি করেছেন।
২.২.৪ ‘অস্ত্র ফ্যালো’ শব্দবন্ধটি কবিতায় কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর: ‘অস্ত্র ফ্যালো’ শব্দবন্ধটি কবিতায় ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
২.২.৫ ‘সে জানত না…’ তার অজানা বিষয়টি কী?
উত্তর: অসুখী একজন’ কবিতায় কবির প্রিয়তমার অজানা বিষয়টি ছিলো যে কবি আর কনো দিন ফিরে আসবে না।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘তখন মনে কষ্ট হয় বইকী।’ কখন লেখকের মনে কষ্ট হয়?
উত্তর: “হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” রচনায় লেখক জানান, একসময় বাঁশের কলম, মাটির দোয়াত, ঘরে তৈরি কালি আর কলাপাতায় লেখার মাধ্যমে তাঁর লেখালেখির শুরু হয়েছিল। কিন্তু কালের প্রবাহে এসব জিনিস বিলুপ্ত হতে বসেছে। সেই সব সরল, মাটির গন্ধমাখা স্মৃতি আজ আর চোখে পড়ে না। ক্রমশ উধাও হয়ে যাওয়াতে লেখকের মনে কষ্ট হয়।
২.৩.২ ‘লক্ষণা’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: লক্ষণা হল শব্দের বৃত্তিবিশেষ। শব্দের মুখ্য অর্থের চেয়ে তার অন্য অর্থই যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে , তখন তাকে বলে লক্ষণা। যেমন, ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ – র অর্থ অরণ্যবাসীদের রোজনামচা।
২.৩.৩ “কোনো বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ বোঝা কঠিন।” প্রসঙ্গ নির্দেশ করো।
উত্তর: “আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় না-থাকায় বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু বা সন্দর্ভ বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।”
২.৩.৪ বিদেশে কী ধরনের নিব তৈরি হত?
উত্তর: বিদেশে উন্নত ধরনের টেকসই নিব তৈরি হত । বিদেশে উন্নত ধরনের নিব টেকসই করার জন্য গোরুর শিং অথবা কচ্ছপের খোল কেটে বানানো হত।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ ‘ডাক্তার ডাকো।’ এবং ‘ডাক্তার এলেন।’ রেখাঙ্কিত পদদুটি কীসের দৃষ্টান্ত?
উত্তর: ‘ডাক্তার ডাকো।’ এবং ‘ডাক্তার এলেন।— প্রথমটি সম্বােধন পদ এবং দ্বিতীয়টি কর্তৃকারক।
২.৪.২ ‘কারক’ শব্দটির ব্যাকরণগত অর্থ ও আভিধানিক অর্থ লেখো।
উত্তর: ব্যাকরণগত অর্থ:
বাংলা ব্যাকরণে কারক বলতে বোঝায় —
ক্রিয়া বা কাজের সঙ্গে যে পদটি (সাধারণত নামপদ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে এবং সেই কাজের নির্দিষ্ট ভূমিকায় অবদান রাখে, তাকেই কারক বলে।
আভিধানিক অর্থ:
‘কারক’ শব্দের মূল অর্থ হলো — কার্য বা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কারণ বা ভূমিকা পালনকারী উপাদান।
২.৪.৩ ব্যাসবাক্যসহ একটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ দাও।
উত্তর: সমাসবদ্ধ শব্দ: রাজপুত্র
ব্যাসবাক্য: যে পুত্র রাজার, সে রাজপুত্র।
২.৪.৪ “একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল।” ‘অপ্রতিভ’ ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: সমাসের নাম: অব্যয়ীভাব সমাস
ব্যাসবাক্য: প্রতিভা নেই যার — সে অপ্রতিভ।
২.৪.৫ যৌগিক ও জটিল বাক্যের একটি পার্থক্য লেখো।
উত্তর:
২.৪.৬ প্রার্থনাসূচক বাক্যের একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: “ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।”
২.৪.৭ কর্তৃবাচ্য কাকে বলে?
উত্তর: যে বাচ্যে বাক্যের কর্তা প্রাধান্য পায় এবং কর্তা অনুগামী ক্রিয়াপদ হয় সেই বাচ্যকে কর্তৃবাচ্য বলে।
২.৪.৮ ‘মুখ্যকর্ম’ ও ‘গৌণকর্ম’ কী?
উত্তর: যেসব বাক্যে দুটি কর্ম থাকে, সেখানে একটি মুখ্য কর্ম ও একটি গৌণ কর্ম হয়।
যা ক্রিয়াকে সরাসরি প্রভাবিত করে, তাকে মুখ্য কর্ম বলে এবং যা ক্রিয়াকে পরোক্ষভাবে (indirectly) প্রভাবিত করে, তাকে গৌণ কর্ম বলে।
২.৪.৯ অহংকারীকে কেউ সহ্য করে না দৃষ্টান্তটি কোন বাচ্যের?
উত্তর: অহংকারীকে কেউ সহ্য করে না দৃষ্টান্তটি বাচ্য: কর্মবাচ্য।
২.৪.১০ সহযোগী কর্তা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যেসব বাক্যে একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর যৌথভাবে কর্ম সাধন বোঝায়, সেখানে কর্তা একাধিক হলেও যৌথভাবে একটি কাজ করে — একে সহযোগী কর্তা বলে।
উদাহরণ: রিনা ও মীনা স্কুলে গেল।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ টানা পাঁচদিন মুষলধারে বৃষ্টিপাতের আগে ও পরে নদীর অবস্থা কেমন হয়েছিল?
উত্তর: পাঁচদিন আগে বর্ষার জলে নদীর জলস্রোত ছিল পঙ্কিল হলেও তাতে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল, যা পরিপূর্ণতার আনন্দের প্রকাশ মনে হয়েছিল। কিন্তু টানা পাঁচদিন মুষলধারে বৃষ্টির পরে নদী যেন খেপে গিয়েছে। তার গাঢ়তর পঙ্কিল জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ফেনোচ্ছ্বাসিত হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে। নদী এখন অনেক বেশি উদ্দাম ও ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।
৩.১.২ হরিদা পুলিশ সেজে কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন? তিনি কীভাবে মাস্টারমশাইকে বোকা বানিয়েছিলেন?
উত্তর: সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পের মূল চরিত্র হলেন হরিদা। তিনি এক অসাধারণ রূপসজ্জা ও ছদ্মবেশ ধারণের দক্ষ শিল্পী। একবার তিনি পুলিশ সেজে দয়ালবাবুর লিচু বাগানে দাঁড়িয়েছিলেন।
সে সময় চারজন স্কুলছাত্র অনুমতি না নিয়েই বাগানে ঢুকে পড়ে। হরিদা পুলিশবেশে তাদের ধরে ফেলে এবং শাস্তির ভয় দেখালে ছেলেরা ভয়ে কেঁদে ফেলে।
অবশেষে বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই এসে পৌঁছান এবং হরিদার পুলিশ সেজে থাকা ছদ্মবেশকে বুঝতে না পেরে তাকে অনুরোধ করেন ছেলেদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। তিনি আট আনা উপরি দিয়ে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেন। এভাবে হরিদা তার অভিনয়, রূপসজ্জা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মাস্টারমশাইকে বোকা বানিয়েছিলেন।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ ‘অসুখী একজন’ কবিতায় কার মাথার উপর বছরগুলি কেন পর পর পাথরের মতো নেমে এসেছিল?
উত্তর: ‘অসুখী একজন’ কবিতায় কবি তার প্ৰিয় মানুষকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারই মাথার উপর বছরগুলি পর পর পাথরের মতো নেমে এসেছিল।
কারণ, কবি তাকে অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রেখে চিরতরে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে জানত না যে কবি আর কখনো ফিরে আসবেন না। কবির প্ৰিয় মানুষ অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।
একটা সপ্তাহ আর একটা বছর কেটে যায়্। আর একটার পর একটা, পাথরের মতো পর পর বছরগুলো নেমে আসে তার মাথার ওপর।
তাই কবি বলেন—
“আর একটার পর একটা, পাথরের মতো
পর পর পাথরের মতো, বছরগুলো
নেমে এল তার মাথার ওপর।”
৩.২.২ “কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,” বস্তা কে? তাঁর একথা বলার কারণ কী?
উত্তর: অভিষেক ‘ কবিতাংশে রামচন্দ্রের পুনর্বার বেঁচে ওঠা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে রাবণ এমন উপমা ব্যবহার করেছেন ।
ইন্দ্রজিতের হাতে দু – দুবার রামচন্দ্রের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েও তিনি আবার বেঁচে ওঠেন । তাই প্রিয় পুত্রকে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিলেও বিধাতা যে তাঁর প্রতি বিরূপ তা তিনি বুঝতে পারেন । শিলা বা পাথরের জলে ভাসার মতোই মৃত মানুষের বেঁচে ওঠাও অবিশ্বাস্য ব্যাপার । বিস্ময় ও হতাশা ব্যক্ত করতে এমন উপমা ব্যবহৃত হয়েছে ।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ অপূর্বর সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে নিমাইবাবু চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক স্পষ্ট হয়েছে, তা বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: ‘পথের দাবী’ উপন্যাসের পাঠ্যাংশ অনুযায়ী নিমাইবাবু হলেন কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র অপূর্বর পিতৃবন্ধু এবং সেই সূত্রে আত্মীয়। অপূর্বর পিতা কোনো এক সময়ে তাঁকে চাকরিতে নিযুক্ত করেছিলেন। এই সম্পর্কের বন্ধনটি উভয় পক্ষই শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করে চলেছেন।
রেঙ্গুনের পুলিশ স্টেশনে বাংলা পুলিশের দারোগা রূপে নিমাইবাবুকে বিপ্লবী সব্যসাচী, যে সেখানে গিরীশ মহাপাত্র ছদ্মনামে অবস্থান করছিল, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখা যায়। তবে অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান হয়েও নিমাইবাবু গিরীশকে একজন সাধারণ গাঁজাসেবী বলে ভুল করে বসেন এবং সন্দেহ দূর করে তাকে ছেড়ে দেন।
তাঁর চরিত্রে এক স্নেহময় ও মমতাময় পিতার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে যখন তিনি গিরীশের রুগ্ণ দেহ দেখে কোমল স্বরে পরামর্শ দেন— “গাঁজা খেও না,। এ থেকেই বোঝা যায়, নিমাইবাবুর অন্তরে এক স্নেহশীল, হৃদয়বান ব্যক্তিত্ব বাস করে।
৪.২. “‘অদল-বদল’ এই আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল।” ‘অদল’, ‘বদল’ কারা? গল্পে এই উক্তিটি কীভাবে গল্পের নামকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে- আলোচনা করো।
উত্তর: ‘অদল-বদল’ গল্পে ‘অদল’ হল অমৃত এবং ‘বদল’ হল ইসাব। এই নাম দুটি এসেছে তাদের মধ্যে জামা অদল-বদলের ঘটনার পর থেকে।
হোলির দিনে কালিয়া নামে একটি ছেলে ইসাবকে অমৃত এর সাথে কুস্তি লরতে বলে । অমৃতের সাথে কুস্তি লরতে রাজি না হাওয়াই কালিয়া ইসাবকে খোলা মাঠে ছুরে ফেলে দেয় । তথন ইসাবের নতুন জামাটি পকেট কাছে দু- ইন্চি ছিঁড়ে যায়।
ইসাবের জামা ছিঁড়ে যাওয়ায় তার বাবা রেগে যাবেন ভেবে সে খুব ভয় পেয়ে যায়। তখন তার বন্ধু অমৃত নিজের জামা ইসাবকে দিয়ে নিজে ছেঁড়া জামাটি পরে নেয়। কারণ, অমৃত জানত — মা থাকলে বাবার মার থেকে সে বাঁচতে পারবে। এই আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার দৃষ্টান্ত তৈরি করে তারা।
এই জামা বদলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামের ছেলেরা মজা করে বলতে থাকে —
“অমৃত-ইসাব-অদল-বদল, ভাই অদল-বদল!”
শেষমেশ এই ‘অদল-বদল’ শব্দটাই হয়ে ওঠে গল্পের প্রতীক। গল্পে এই ঘটনা গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রামের প্রধান ঘোষণা দেন:
“আজ থেকে আমরা অমৃতকে ‘অদল’ আর ইসাবকে ‘বদল’ বলে ডাকব।”
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ ‘সমুদ্রনৃপতি সুতা’ কে? তার কোন্ বিশেষ বৈশিষ্ট্য কীভাবে আলোচ্য কবিতায় উদ্ভাসিত হয়েছে তা কবিতার উদ্ধৃতি উল্লেখ করে আলোচনা করো।
উত্তর: ‘সমুদ্রনৃপতি সুতা’ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সিন্ধুতীরের কন্যা, পদ্মা ।
এই রমণী অর্থাৎ ‘সমুদ্রনৃপতি সুতা’র বিশেষ কিছু গুণ কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে, যেমন:
“সমুদ্রনৃপতি সুতা পুণ্য নামে গুণময়তা”
এই পঙ্ক্তিতে বোঝানো হয়েছে, তিনি হলেন গুণময়, মহিমাময়, পবিত্র কন্যা—যিনি একসময় জ্ঞান, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক ছিলেন।
“সিন্ধুতীরেতে দেখি বিশ্বসভ্যতা।”
এখানে কবি বলছেন, এই নারীর (দেশের) তীরে দাঁড়িয়েই বিশ্বসভ্যতার সূচনা হয়েছে—তার গর্ভেই জন্মেছে প্রাচীন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি।
“বুকে তব লুকানো রহিছে মণিমানিক”
এই পঙ্ক্তি নির্দেশ করে যে, ‘সমুদ্রনৃপতি সুতা’র হৃদয়ে লুকিয়ে রয়েছে অপার সম্পদ—তা মণি, মানিকের রূপক হলেও তা আসলে তার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও প্রাচীন ঐশ্বর্যের প্রতীক।
এইভাবে কবি সৈয়দ আলাউল ‘সমুদ্রনৃপতি সুতা’ রূপে সিন্ধু সভ্যতাকে একটি জীবন্ত, গুণময়, স্মৃতিবহ রমণী হিসেবে কল্পনা করেছেন, যার বুকে লুকিয়ে আছে প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়। তাঁর রূপ, গুণ, বর্ণ, ঐশ্বর্য ও বিশালতার মধ্য দিয়ে কবি এক জাতীয় আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন।
৫.২ ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় প্রলয় কীভাবে উল্লাসের কারণ হয়ে উঠেছে, তা সংক্ষেপে লেখো।
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় প্রলয় শুধু ধ্বংসের প্রতীক নয়, বরং তা উল্লাসেরও কারণ হয়ে উঠেছে। কবির মতে, সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য, জড়ত্ব ও পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রলয় প্রয়োজন।
এই ধ্বংসই শুভ শক্তির আগমন ঘটিয়ে নবীন পৃথিবীর সূচনা করে।
কবি প্রলয়কে ‘কালবোশেখির ঝড়’, ‘প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল’, ‘ভয়ংকর’, ‘মহাকাল সারথি’, ও ‘নবীন’ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন।
এই বিশেষণগুলোর মাধ্যমে তিনি প্রলয়ের বিভীষিকাময় রূপের মাঝেও এক আনন্দঘন পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখেছেন।
তাই কবির চোখে প্রলয় শুধু ভয়ংকর নয়, নব সৃষ্টির আগমনী সঙ্গীতও বয়ে আনে, যা তাকে উল্লাসের কারণ করে তোলে।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ “দোয়াত যে কতরকমের হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।” ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে লেখক কালির দোয়াতের যে বৈচিত্র্যের কথা লিখেছেন, তা আলোচনা করো।
উত্তর: ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে লেখক শ্রীপান্থ দোয়াতের বিভিন্ন রকমের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, দোয়াত কেবল লেখার উপকরণ নয়, তা একসময় শিল্পরুচি ও ঐতিহ্যের প্রতীক ছিল। দোয়াত নানারকমের হতো— কাচের, কাটগ্লাসের, পোর্সেলিনের, শ্বেতপাথরের, জেডের, পিতলের, ব্রোঞ্জের, এমনকি ভেড়ার শিং দিয়েও তৈরি হতো। সোনার দোয়াতও দেখা যেত। একসময় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো ফলের পর গুরুজনরা আশীর্বাদ করতেন— “সোনার দোয়াত-কলম হোক।”
লেখক স্বনামধন্য সুভো ঠাকুরের দোয়াত-সংগ্রহ দেখে এমন সোনার দোয়াত সত্যিই দেখেছেন। সেই সংগ্রহে এমন কিছু দোয়াত ছিল, যেগুলোর সঙ্গে সাহিত্য ও ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্রদের সম্পর্ক ছিল। এসব দেখে লেখকের মনে পড়ে যায়— শেকসপিয়র, দান্তে, মিলটন, কালিদাস, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ দিক্পালরা সম্ভবত এমনই কোনো দোয়াতের কালি দিয়ে তাঁদের অমর সাহিত্য রচনা করেছিলেন। এই ভাবনাই লেখককে রোমাঞ্চিত করে তোলে।
৬.২ ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধ অনুসরণে পরিভাষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করো।
উত্তর: ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে রাজশেখর বসু পরিভাষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন—বিজ্ঞানচর্চায় পারিভাষিক শব্দ অপরিহার্য, কারণ এ ধরনের শব্দ ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা সম্ভব নয়। পরিভাষার মূল উদ্দেশ্য হল—বিদেশি শব্দের পরিবর্তে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও অর্থবোধক বাংলায় গঠিত এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা পাঠকের কাছে বোধগম্য হয় এবং একই সঙ্গে বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে।
তিনি আরও মনে করেন, পরিভাষা রচনার সময় বিজ্ঞান আলোচনার নিজস্ব রচনাপদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার, যাতে পরিভাষা শুধু অনুবাদ না হয়ে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রকৃত ভাব ও গভীরতা প্রকাশ করতে পারে। তাই বিভিন্ন শাখার বিশারদদের সহায়তায় পরিভাষা তৈরি হওয়া উচিত, যাতে তা সর্বজনগ্রাহ্য ও কার্যকর হয়।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয় মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা।”- কাদের উদ্দেশ করে একথা বলা হয়েছে? এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বক্তার কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে?
উত্তর: নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত সিরাজদ্দৌলা নাটকে নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর সভায় উপস্থিত রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, উমিচাঁদ প্রমুখ বিশিষ্ট সভ্যদের প্রতি একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেন। উক্তির মাধ্যমে নবাবের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, তা হল—তিনি একজন উদারমনের খাঁটি দেশপ্রেমিক।
নবাব সিরাজদ্দৌলা বুঝেছিলেন, বাংলা কেবল মুসলমানের বা হিন্দুর নয়—বাংলা হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত অবস্থানের মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে। বাংলার উপর ঘনিয়ে আসা দুর্দিন রোধ করতে তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আস্থা রেখেছিলেন।
তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বহিরাগত ইংরেজ শত্রুকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হলে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও ভেদাভেদ পরিহার করে হিন্দু-মুসলমান সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাঁর মতে, ধর্মের নামে বিভেদ মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তা কখনোই বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না।
এই উপলব্ধি থেকেই নবাব সিরাজদ্দৌলা কাতরভাবে সকলের প্রতি উদার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক, উদারচেতা এবং সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক শাসক।
৭.২ ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ অবলম্বনে লুৎফা চরিত্রের বিশেষ দিকগুলি আলোচনা করো।
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশে দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে সিরাজের পত্নী লুৎফা অন্যতম। নাটকে তাঁর উপস্থিতি স্বল্প হলেও তা তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর চরিত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নরূপ—
(ক) সরলতা:
সভাসদদের সঙ্গে মানসিক সংঘর্ষে যখন সিরাজ সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত, তখনই লুৎফার আবির্ভাব ঘটে। নবাবের বেগম হয়েও তিনি কখনও রাজনীতির চক্রে নিজেকে জড়াননি। বরং সহজ-সরল গৃহিণীর মতোই তিনি সংসারকেন্দ্রিক থেকেছেন। এমনকি ঘসেটির তীব্র ভর্ৎসনার পরেও লুৎফা কোনো কটুবাক্য উচ্চারণ করেননি, যা তাঁর নম্রতার পরিচয় বহন করে।
(খ) যোগ্য সঙ্গিনী:
লুৎফা স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীলা। সিরাজ যখন রাজ্য পরিচালনায় নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত, তখন তিনি স্বামীকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে একজন যোগ্য সঙ্গিনীর ভূমিকা পালন করেন। স্বামীর দুঃখ-দুর্দশায় পাশে থেকে তিনি সহায়তা করেছেন।
(গ) সহমর্মিতা:
নাটকে লুৎফা এক কোমল হৃদয়ের নারী। নবাবের চোখের জল দেখে তিনি বেদনার্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর অমঙ্গল চিন্তায় আতঙ্কিত হন। লুৎফার কাছে রাজনীতি নয়, স্বামীর কল্যাণই মুখ্য। তিনি ঘসেটিকে ‘মা’ বলে সম্মান জানালেও যখন সেই ‘মা’র মুখে প্রতিহিংসার কথা শুনেছেন, তখন তাঁর কাছে সেই সম্পর্ক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। লুৎফা সেই নারী চরিত্র, যিনি ট্র্যাজিক নায়কের পাশে থেকে তাকে ভালোবাসা, সেবা, সাহস ও আস্থা যুগিয়েছেন।
(ঘ) সাধারণ নারীচরিত্র:
মহিষী হয়েও লুৎফার মধ্যে বেগমসুলভ অহংকার দেখা যায় না। পলাশির যুদ্ধের কথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং সাধারণ এক নারীর মতোই চান না তাঁর স্বামী যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হোক।
সার্বিকভাবে লুৎফা চরিত্রটি একাধারে একজন দায়িত্বশীলা পত্নী, সহানুভূতিশীল নারী ও একজন মানবিক সঙ্গিনীর প্রতিচ্ছবি বহন করে।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ “শরীরের নাম মহাশয় যা সহাবে তাই সয়।” ক্ষিতীশ সিংহের এই উক্তিতে তার কীরূপ মানসিকতা ফুটে উঠেছে?
উত্তর: মতি নন্দী রচিত কোনি উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কথামুখে ক্ষিতীশ সিংহ একটি প্রবাদবাক্য উল্লেখ করেছেন। সেই প্রবাদবাক্যের মাধ্যমে তাঁর শরীর ও মন সম্পর্কে অপূর্ব সংযম এবং নিয়ন্ত্রণের পরিচয় পাওয়া যায়।
সংযমী ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন:
ক্ষিতীশ সিংহ ছিলেন অত্যন্ত সংযমী ও আত্মনিয়ন্ত্রিত একজন মানুষ। তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন এবং শরীর সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। নিজেই বলেছেন, “খিদের মুখে যা পাই, তাই অমৃতের মতো লাগে।” তাঁর এই মন্ত্রে তিনি চলতেন এবং সংসারেও সেই নিয়ম বজায় রাখতেন। তাঁর ঘরের খাওয়ার আয়োজন ছিল অত্যন্ত সাধারণ।
সিদ্ধ খাবারের প্রতি অনুরাগ:
ক্ষিতীশ বিশ্বাস করতেন, বাঙালিয়ানা রান্না স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। তাই তিনি প্রায় সব খাবার সিদ্ধ করেই খেতেন। তাঁর মতে, এতে খাদ্যপ্রাণ যথাসম্ভব অটুট থাকে। যদিও শুরুতে তাঁর স্ত্রী মশলা ব্যবহার করে রাঁধতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষিতীশ সিংহের গোঁড়ামি ও দৃঢ়তার কাছে তাঁকে হার মানতে হয়।
মন নিয়ন্ত্রণে শরীরচর্চার গুরুত্ব:
ক্ষিতীশ মনে করতেন, শরীরচর্চা ও সংযম পালনের মধ্য দিয়েই মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এই আদর্শ তিনি নিজে পালন করতেন এবং অন্যদের মধ্যেও তা গড়ে তুলতে চাইতেন।
বিশেষ গুণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব:
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ক্ষিতীশ সিংহের চরিত্রে সাঁতার ও সাঁতারুদের প্রতি একনিষ্ঠ দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি পক্ষপাত স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে একজন আদর্শ গড়ে তোলার কারিগর করে তুলেছে।
৮.২ ‘কোনি’ রচনা অবলম্বনে ক্ষিদ্দা ও কোনির প্রকৃত গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক মতি নন্দী রচিত কোনি উপন্যাসে ক্ষিতীশ সিংহ তথা ‘ক্ষিদ্দা’ ও কোনির মধ্যে এক নিখাদ গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ক্ষিদ্দা আগাগোড়া এক ব্যতিক্রমী মানুষ, যিনি প্রতিভাকে চিনে নিয়ে তাকে সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক পথে চালনা করার ক্ষমতা রাখেন।
সাধারণ এক দরিদ্র পরিবারের মেয়ে কোনিকে তিনি নিঃস্বার্থভাবে তৈরি করেছেন একজন যোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে। নিজের লাভ বা স্বার্থ নয়, বরং দেশের গৌরব রক্ষাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। নিজের সংসারে অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনির খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের দায়িত্ব নিয়েছেন।
ক্ষিদ্দা কঠোর, কিন্তু হৃদয়বান। কোনি কেঁদে ফেললেও তিনি প্র্যাকটিস থেকে তাকে অব্যাহতি দেননি, আবার একইসঙ্গে পিতৃতুল্য স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়েছেন। কোনিকে কখনো খাওয়ার লোভ দেখিয়ে কঠিন অনুশীলনে নিয়োজিত করেছেন, আবার দাদার মতো তাকে চিড়িয়াখানায় কুমীর দেখাতেও নিয়ে গেছেন।
কোনির শারীরিক ও মানসিক গঠন, আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের ভিত গড়ে দেওয়ার পিছনে ক্ষিদ্দার অবদান অনস্বীকার্য। কোনি যখন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেকে প্রমাণ করে, তখন সেই কঠোর গুরুক্ষিদ্দার চোখে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে—যা তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা স্পষ্ট করে।
এইভাবেই ক্ষিদ্দা ও কোনির মধ্যে একটি প্রকৃত, নিঃস্বার্থ ও আদর্শ গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যা অনুপ্রেরণার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
৮.৩ ‘গলার স্বরটা আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে।’ কার গলার স্বর? তার চিৎকার ক্রমশ হতাশায় ভেঙে পড়ল কেন?
উত্তর: ‘গলার স্বরটা আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে’ — এটি এক শ্যামবর্ণ, রুগ্ন যুবকের গলার স্বর। সে ছিল বছর পঁচিশের মতো, পরনে ছিল ধুতি ও নীল শার্ট, আর হাতে ছিল একটি চটি জোড়া।
রবীন্দ্র সরোবরে এক মাইল সীতার প্রতিযোগিতা । পঁচিশজন প্রতিযোগী । বাইশটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে।
প্রতিযোগিতা শুরু হয় । সে সরোবরের পূর্ব তীর ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছিল এবং বারবার আর্তনাদ করে চিৎকার করছিল — “কোও ও নিইই।”
তার এই চিৎকার ক্রমশ হতাশায় ভেঙে পড়েছিল, কারণ সামনের দু-ঝাঁকের সাঁতারুদের কেউ কেউ এবার মন্থর হয়ে পিছিয়ে পড়ছে। বাচ্চা ছেলে দুটির সঙ্গে কোনি আসছে বৈঠার মতো হাত চালিয়ে, দু-ধারে মাথা নাড়াতে নাড়াতে। ওদের থেকে অন্তত কুড়ি মিটার সামনে আর একটি মেয়ে, সমান তালে একই গতিতে সাঁতরে চলেছে। লাল কস্ট্যুমের মেয়েটি তার থেকে আরো তিরিশ মিটার সামনে এবং একটি ছেলের থেকে হাত দশেক পিছনে। সে সম্ভবত কোনিকে চিনতে পেরেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল কোনি পিছিয়ে পড়ছে ।
ক্ষিদা ভেবেছিলো— কোনো কম্পিটিটারের বাড়ির লোক হবে হয়তো।”
সে ছিল হয়তো কোনির ঘরের মানুষ বা খুব কাছের কেউ। তার মুখের অসহায়তা, ছুটে চলা ও চিৎকারে তার চিন্তা ও কষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।
৯। চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো:
I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of imperfect education. I tried later on to improve mine, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth.
উত্তর: “আমি বুঝতে পারলাম, খারাপ হাতের লেখা অসম্পূর্ণ শিক্ষার লক্ষণ হিসেবে ধরা উচিত। পরে আমি আমার হাতের লেখা ভালো করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। শৈশবে যে অবহেলা করেছিলাম, তা আর কখনো পূরণ করতে পারিনি।”
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ পশ্চিমবঙ্গে বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষা কোনটি শিক্ষার সর্বস্তরের মাধ্যম হওয়া উচিত এই নিয়ে দুই বান্ধবীর সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
“শিক্ষার মাধ্যম: বাংলা না ইংরেজি?”
অনী: জানিস রিয়া, আমি ভাবছি আমাদের স্কুলে সব বিষয়ের মাধ্যমে ইংরেজি করা উচিত। এতে ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার সুযোগ বাড়বে।
রিয়া: ঠিক বলছিস, ইংরেজি জানা দরকার। কিন্তু যদি মাতৃভাষা বাংলায় পড়ানো হয়, তাহলে সবাই বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। শিক্ষা তো বোঝার জন্য, মুখস্থের জন্য নয়!
অনী: কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমে পড়লে তো আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেকে তুলে ধরতে সুবিধা হয়।
রিয়া: হ্যাঁ, তাই বলে বাংলাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। ইংরেজি শেখা হোক, কিন্তু মাতৃভাষাকে শিক্ষার মূল মাধ্যম হিসেবে রাখা উচিত। বাংলা মাধ্যমে বিষয় বুঝে ইংরেজি প্রয়োগ শেখা ভালো পথ।
অনী: ঠিক বলেছিস। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যেখানে বাংলা মাধ্যমে বিষয় শেখা যায়, আর ইংরেজিতে নিজেকে প্রকাশ করার দক্ষতাও গড়ে ওঠে।
রিয়া: একদম ঠিক! মাতৃভাষায় শিক্ষাই সবার জন্য অধিক ফলদায়ী।
১০.২ বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপন-এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপন
নিজেস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, জুন ২২: গত ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে সকাল ৮টায় বিদ্যালয়ে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা হাতে হাতে ভাষা শহিদদের ছবি ও বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে অংশ নেয়। এরপর শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রধান শিক্ষক ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও মাতৃভাষার গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য দেন। ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় কবিতা পাঠ, সংগীত পরিবেশনা ও ছোট নাটিকা। অনুষ্ঠানে সবার মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও গর্বের অনুভব ছিল স্পষ্ট।
এই দিবসটি আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সচেতন করে তোলে এবং ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করিয়ে দেয়।
১১। যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লেখো: (কমবেশি ৪০০ শব্দে)
১১.১ সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর।
উত্তর:
সঙ্গীতের দেবী: সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর
ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, এক জীবন্ত কিংবদন্তি হলেন সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। তাঁর কণ্ঠে ছিল এক জাদুকরী মাধুর্য, যা বহু প্রজন্মের শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে গেছে। সুরের দুনিয়ায় তাঁর অবদান এতটাই বিশাল যে তাঁকে ‘ভারতের কোকিল’ বলা হয়।
লতা মঙ্গেশকর ১৯২৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দীনানাথ মঙ্গেশকর ছিলেন মারাঠি থিয়েটারের একজন গায়ক ও অভিনেতা। ছোটবেলা থেকেই লতার সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাবার অকালমৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি সঙ্গীত জগতে আত্মপ্রকাশ করেন।
লতা মঙ্গেশকর হিন্দি, বাংলা, মারাঠি, তামিল, তেলেগু সহ প্রায় ৩৬টি ভাষায় ৩০,০০০-এর বেশি গান গেয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে ‘আয়েগা আনেওয়ালা’, ‘লাগ জা গলে’, ‘প্যাার কিয়া তো ডরনা কেয়া’, ‘তেরে লিয়ে’, ‘এক প্যারা কা নাগমা হ্যায়’—এসব গান কালজয়ী হয়ে উঠেছে। বাংলা গানেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ‘সাগরিকা’, ‘প্রেম একবার এসেছিলো নিঃশব্দ পায়ে’, ‘ও পাখি তোর চোখে চোখে’—এমন বহু গানে তাঁর কণ্ঠ আজও বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে আছে।
শুধু গান গেয়েই নয়, সঙ্গীত পরিচালনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ‘আনন্দ ঘন’ ও ‘মালতী মাধব’ সিনেমায় তিনি সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। ২০০১ সালে তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ‘ভারত রত্ন’ প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিনি পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারসহ অসংখ্য সম্মানে ভূষিত হন।
২০২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রয়াণে সারা ভারত শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। লতা মঙ্গেশকর শুধু একজন গায়িকা নন, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের আত্মা, সংস্কৃতি ও আবেগের প্রতীক।
আজও তাঁর কণ্ঠের জাদু কোটি মানুষের মনে এক স্বর্গীয় সুরের আবেশ ছড়িয়ে দেয়। সত্যিই তিনি ছিলেন ও চিরকাল থাকবেন—এক অনন্য সুরসম্রাজ্ঞী।
১১.২ সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা।
উত্তর:
“সাহিত্য: মনুষ্যত্ব বিকাশের শ্রেষ্ঠ পাঠশালা”
সাহিত্য মানব জীবনের আয়না। মানুষের অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা, কল্পনা, স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। তাই সাহিত্য শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি এক গভীর জীবনদর্শনের বাহক। একজন মানুষ চরিত্রে, চিন্তায় ও আচরণে পূর্ণতা লাভ করতে পারে সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে। এই কারণে সাহিত্যের পাঠ জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়।
প্রথমত, সাহিত্য পাঠ আমাদের মানবিক গুণাবলি গঠনে সহায়তা করে। সাহিত্যে আমরা নানান চরিত্র, পরিস্থিতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হই। এতে করে সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা ও মমত্ববোধের বিকাশ ঘটে। আমরা অন্যের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে শিখি। সাহিত্য আমাদের হৃদয়কে সংবেদনশীল করে তোলে এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে।
দ্বিতীয়ত, ভাষাজ্ঞান ও প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সাহিত্য পাঠ অপরিহার্য। সাহিত্যের ভাষা সুন্দরের সাধনা শেখায়। সাহিত্য পড়লে শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়, বাক্যগঠনের ক্ষমতা বাড়ে এবং নিজস্ব চিন্তাধারা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারা যায়।
তৃতীয়ত, সাহিত্য ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণ হিসেবে কাজ করে। বাংলা সাহিত্যে যেমন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালের সমাজচিত্র পাওয়া যায়, তেমনি বিশ্বসাহিত্যেও বিভিন্ন সময়ের মানবজীবনের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে আমরা অতীতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারি এবং ভবিষ্যতের পথ চিনতে শিখি।
চতুর্থত, সাহিত্যে রয়েছে চিন্তা ও কল্পনার বিস্তার। বিজ্ঞান বা অঙ্ক আমাদের যুক্তি শেখায়, কিন্তু সাহিত্য আমাদের কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করে। একজন সাহিত্যপ্রেমী ব্যক্তি সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারেন।
পরিশেষে বলা যায়, সাহিত্য শুধু পরীক্ষার জন্য পড়ার বিষয় নয়, এটি জীবনের পথপ্রদর্শক। সাহিত্য পাঠ মানুষকে মননশীল, বোধসম্পন্ন ও সংস্কৃতিমনস্ক করে তোলে। তাই জীবনে সার্থকতা অর্জনের জন্য এবং একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য সাহিত্য পাঠের বিকল্প নেই। প্রতিটি শিক্ষার্থীরই উচিত নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করা, কারণ সাহিত্য মানুষকে করে তোলে সত্যিকার অর্থে মানুষ।
১১.৩ একটি ছাত্রের/ছাত্রীর আত্মকথা।
উত্তর:
আমার জীবনের পাতায় লেখা কিছু কথা
(একজন ছাত্রের আত্মকথা)
আমি একটি সাধারণ ঘরের ছেলে। আমার নাম অর্ণব। আমি একাদশ শ্রেণির ছাত্র। জন্ম হয়েছিল গ্রামের এক ছোট্ট মাটির বাড়িতে। বাবা একজন কৃষক, মা গৃহিণী। আমাদের পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও ভালোবাসা ও আত্মিক বন্ধন আমাদের প্রতিটি দিনকে সুন্দর করে তোলে।
ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ছিল আমার। প্রথম অক্ষর লেখা শিখেছিলাম মায়ের কোলে বসে, খড়ের আঁচড়ে মাটির ওপর। তারপর গ্রামের স্কুলে ভর্তি হই। ছেলেবেলায় মাটির রাস্তায় হেঁটে স্কুলে যেতাম—পিছনে বইয়ের ব্যাগ, হাতে এক টুকরো কাগজে স্বপ্ন আঁকা।
আমার প্রিয় বিষয় বাংলা ও বিজ্ঞান। বাংলায় আমি স্বপ্ন দেখি, বিজ্ঞান আমাকে যুক্তি শেখায়। মাঝে মাঝে ভাবি, বড় হয়ে শিক্ষক হব। কারণ, আমি জানি গ্রামের অনেক ছেলেমেয়েই ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারে না শুধুমাত্র পথ দেখানোর অভাবে। আমি তাদের সেই পথপ্রদর্শক হতে চাই।
আমার জীবনে কষ্ট কম নয়। অনেক সময় বই কেনার টাকাও জোটে না। তবুও আমি হার মানিনি। পড়াশোনার ফাঁকে বাবার সঙ্গে মাঠে যাই, সংসারে মায়ের হাত ধরতেও পিছপা হই না। স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাকে খুব ভালোবাসেন। তারা বলেন, “অর্ণব একদিন অনেক দূর যাবে।” এই কথাগুলো আমাকে নতুন করে সাহস যোগায়।
বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগে। তারা আমার দুঃখ বুঝতে পারে। কেউ কেউ ভাবে আমি পড়ুয়া বলে গম্ভীর, কিন্তু আসলে আমি খুব হাসিখুশি একজন ছেলে। গান শুনতে ভালো লাগে, মাঝে মাঝে কবিতাও লিখি নিজের খাতায়। সেই খাতার নাম দিয়েছি—”আমার কথা”।
জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি শিখি—ভালোবাসা, সংগ্রাম, স্বপ্ন আর সাহস। আমি জানি, আমার পথ খুব মসৃণ নয়, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি থাকলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। আজ আমি ছাত্র, আগামীতে হতে চাই একজন আলোকিত মানুষ—নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্য।
এই আমি—একজন স্বপ্ন দেখা সাধারণ ছাত্র। আমার গল্প এখানেই শেষ নয়, বরং এখান থেকেই শুরু।
১১.৪ গাছ আমাদের বন্ধু।
উত্তর:
গাছ আমাদের পরম বন্ধু
প্রকৃতি আমাদের যে অমূল্য উপহার দিয়েছে, তার মধ্যে গাছ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গাছ শুধু আমাদের সৌন্দর্যই বাড়ায় না, আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মানুষের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর নাম যদি বলতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে গাছের নাম আসবে সবার আগে।
আমাদের পরম বন্ধু গাছ—এ কথা শুধু রূপক নয়, বাস্তব। গাছ আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন সরবরাহ করে, যা ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এ ছাড়াও গাছ বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পৃথিবীর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, বন্যা ইত্যাদি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
গাছ আমাদের খাদ্যও জোগায়। আম, কাঁঠাল, লিচু, নারকেল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল ছাড়াও শাকসবজি ও মসলা গাছ থেকেও আমরা উপকার পাই। আবার নানা ভেষজ গাছ যেমন তুলসী, নিম, হরিতকী, বহেড়া ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গাছ থেকে আমরা কাঠ পাই, যা দিয়ে বাড়ি, আসবাবপত্র ও নানা রকম জিনিসপত্র তৈরি করা হয়।
শুধু আমাদের উপকারই করে না, প্রাণীদের কাছেও সে সমান উপকারী গাছ। বহু পাখি, গুইসাপ, গরু-ছাগল প্রভৃতি জীবজন্তু গাছের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া গাছ ছায়া দেয়, ক্লান্ত পথিককে আশ্রয় দেয় এবং এক অপার শান্তির অনুভূতি এনে দেয়।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকের দিনে মানুষের লোভে অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে। নির্বিচারে গাছ কেটে আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছি। বনভূমি কমে যাওয়ায় পরিবেশ দূষণ, প্রাণীকুলের বিলুপ্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তন মারাত্মক আকার নিচ্ছে।
তাই সময় এসেছে সচেতন হওয়ার। আমাদের উচিত বেশি করে গাছ লাগানো ও পরিচর্যা করা। প্রতিটি শিশু যদি একটি করে গাছ রোপণ করে এবং বড়োরা তা রক্ষা করে, তবে পৃথিবী একদিন আবার সবুজে ভরে উঠবে। গাছ আমাদের সত্যিকারের বন্ধু—যে বিনিময়ে কিছু চায় না, কেবল দেয়। এই বন্ধুর যত্ন নেওয়া আমাদের কর্তব্য।
সুতরাং, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে গাছের সঙ্গেই বন্ধুত্ব ধরে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে—গাছ বাঁচলে, মানুষও বাঁচবে।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।