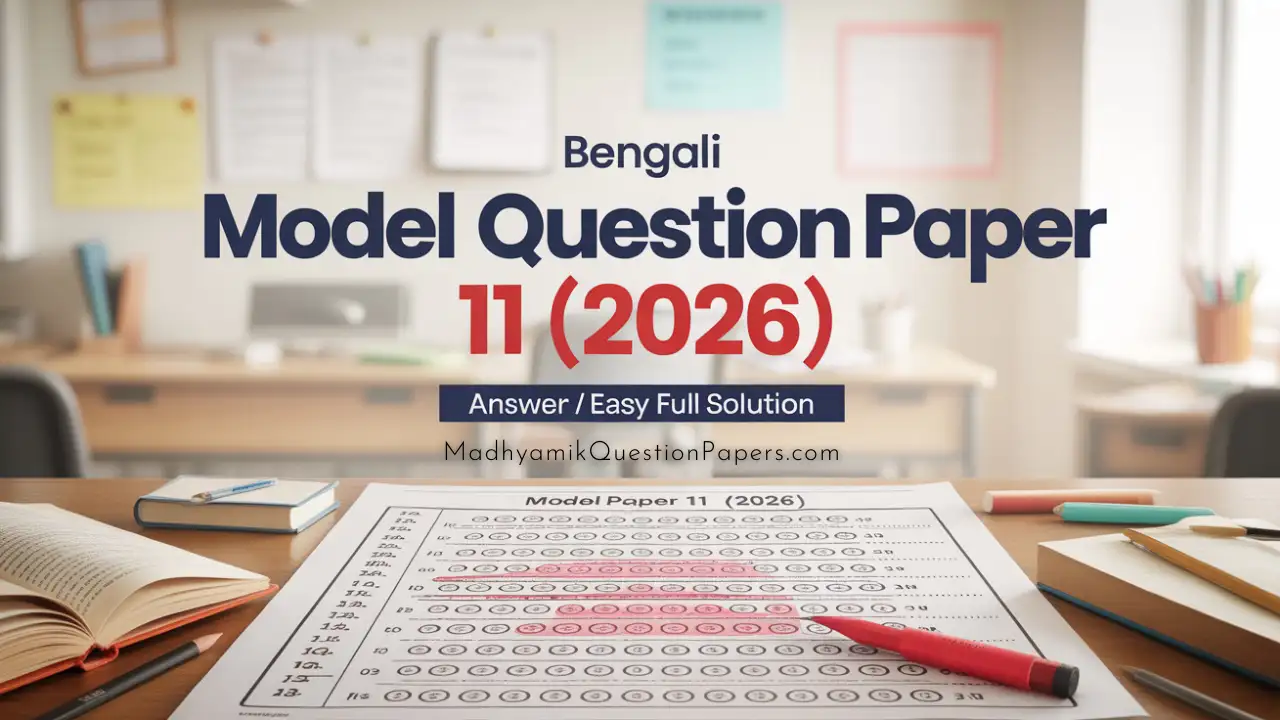আপনি কি ২০২৬ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 11 এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 11-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৬ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ “রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই।” এখানে ‘জহুরি’-র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে-
(ক) তপনকে
(খ) তপনের নতুন মেসোকে
(গ) তপনের মাসিকে
(ঘ) মেজোকাকুকে
উত্তর: (খ) তপনের নতুন মেসোকে
১.২ নাম পরিবর্তনের পর ইসাবের নাম হয়
(ক) অমৃত
(খ) অদল
(গ) কালিয়া
(ঘ) বদল
উত্তর: (ঘ) বদল
১.৩ “বড়ো ভয় করিতে লাগিল নদেরচাঁদের।” ভয়ের কারণ ছিল –
(ক) অন্ধকার
(খ) বৃষ্টি
(গ) নদীর প্রতিহিংসা
(ঘ) নদীর স্ফীতি
উত্তর: (ঘ) নদীর স্ফীতি
১.৪ ‘তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।’ কারা স্বপ্ন দেখতে পারল না?-
(ক) সেই মেয়েটি
(খ) গির্জার নান
(গ) কবিতার কথক
(ঘ) শান্ত হলুদ দেবতারা
উত্তর: (ঘ) শান্ত হলুদ দেবতারা
১.৫ ‘কবির সংগীতে বেজে উঠেছিল’ কী বেজে উঠেছিল? –
(ক) সংগীতের মূর্ছনা
(খ) সুন্দরের আরাধনা
(গ) সুরের ঝংকার
(ঘ) রাগরাগিণী
উত্তর: (খ) সুন্দরের আরাধনা
১.৬ “বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।” ‘বিধুমুখি’ হল –
(ক) প্রভাষা
(খ) প্রমীলা
(গ) লক্ষ্মী
(ঘ) মন্দোদরী
উত্তর: (খ) প্রমীলা
১.৭ লেখার পাত বলতে বোঝানো হয়ে থাকে –
(ক) লেখার কাগজকে
(খ) তালপাতাকে
(গ) কলাপাতাকে
(ঘ) শালপাতাকে
উত্তর: (গ) কলাপাতাকে
১.৮ “সকলের দাবি মেটাতেই তৈরি।” কে তৈরি? –
(ক) প্রাচীন কলম
(খ) কঙ্কাবতী
(গ) যন্ত্রযুগ
(ঘ) যন্ত্রযুগের ছাপাখানা
উত্তর: (গ) যন্ত্রযুগ
১.৯ ‘লক্ষণা’ যে অর্থ প্রকাশ করে, তা হল-
(ক) বোধমূলক
(খ) আভিধানিক
(গ) বিস্তৃত
(ঘ) সংক্ষিপ্ত
উত্তর: (গ) বিস্তৃত
১.১০ বিভক্তি–
(ক) সর্বদা শব্দের পূর্বে বসে
(খ) সর্বদা শব্দের পরে যুক্ত হয়
(গ) শব্দের পরে আলাদাভাবে বসে
(ঘ) শব্দের পূর্বে আলাদাভাবে বসে
উত্তর: (খ) সর্বদা শব্দের পরে যুক্ত হয়
১.১১ কোল্টি সমধাতুজ কর্তার দৃষ্টান্ত? –
(ক) চলো বেড়িয়ে আসি
(খ) খেলোয়াড় খেলছে
(গ) তারা লজ্জা পেল
(ঘ) লোকে বলছে
উত্তর: (খ) খেলোয়াড় খেলছে
১.১২ পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় যে সমাসে, সেটি হল
(ক) বহুব্রীহি সমাস
(খ) অব্যয়ীভাব সমাস
(গ) তৎপুরুষ সমাস
(ঘ) নিত্যসমাস
উত্তর: (গ) তৎপুরুষ সমাস
১.১৩ ‘নীলকণ্ঠ’ পদটি কোন্ সমাসের উদাহরণ? –
(ক) দ্বন্দু
(খ) কর্মধারয়
(গ) দ্বিগু
(ঘ) বহুব্রীহি
উত্তর: (ঘ) বহুব্রীহি
১.১৪ ‘ডাক্তারবাবু যে ভাবে বলেছেন, সেই ভাবে চলো।’ এই বাক্যের ক্রিয়াবিশেষণখণ্ডটি হল –
(ক) ডাক্তারবাবু
(খ) যে ভাবে বলেছেন, সেই ভাবে
(গ) ডাক্তারবাবু যেভাবে বলেছেন, সেই ভাবে
(ঘ) সেই ভাবে চলো
উত্তর: (খ) যে ভাবে বলেছেন, সেই ভাবে
১.১৫ হায়, তোমার এমন দশা কে করলে। এটি কী ধরনের বাক্য? –
(ক) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য
(খ) বিস্ময়সূচক বাক্য
(গ) নির্দেশক বাক্য
(ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্য
উত্তর: (খ) বিস্ময়সূচক বাক্য
১.১৬ বাচ্য হল বাক্যের ক্রিয়ার প্রকাশ ভঙ্গিমার এক বিশেষ রূপ। শূন্যস্থানে বসবে-
(ক) সমাপিকা
(খ) অসমাপিকা
(গ) সকর্মক
(ঘ) অকর্মক
উত্তর: (ক) সমাপিকা
১.১৭ তাকে টিকিট কিনতে হয়নি বাক্যটির কর্তৃবাচ্যের রূপ হল
(ক) তাঁর টিকিট কেনা হয়নি
(খ) তিনি টিকিট কেনেননি
(গ) তাঁর দ্বারা টিকিট ক্রীত হয়নি
(ঘ) তিনি বিনা টিকিটে চলেছেন
উত্তর: (খ) তিনি টিকিট কেনেননি
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ ‘ক্রমশ ও কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে।’ কোন্ কথা ছড়িয়ে পড়ে?
উত্তর: তপনের গল্পটি কাঁচা ছিল বলে তাতে কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছিল – তপনের মেসোমশাইয়ের এই মন্তব্যটি মুহূর্তেই সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে।
২.১.২ ‘কী অদ্ভুত ই ব্যাপার।’ কোন্ ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: অপূর্ব অফিসে থাকার ফলে এবং তেওয়ারি বর্মার নাচ দেখতে যাওয়ার কারণে বাড়ি ফাঁকা ছিল। আর এই সুযোগেই অপূর্বর বাসায় চুরি ঘটে। উদ্ধৃতাংশে এই চুরির ঘটনাটিরই উল্লেখ করা হয়েছে।
২.১.৩ ‘ইত্যবসরে এই ব্যাপার।’ কোন্ ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: অপূর্ব অফিসে থাকার ফলে এবং তেওয়ারি বর্মার নাচ দেখতে যাওয়ার কারণে বাড়ি ফাঁকা ছিল। আর এই সুযোগেই অপূর্বর বাসায় চুরি ঘটে। উদ্ধৃতাংশে এই চুরির ঘটনাটিরই উল্লেখ করা হয়েছে।
২.১.৪ ‘সে অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল।’ কষ্টের কারণ কী?
উত্তর: নদীর গর্জন ও বৃষ্টির শব্দ নদেরচাদের মনে এমন এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যে সে হতভম্ব ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এজন্য ব্রিজের ওপর থেকে উঠে যেতে চাইলেও তার দেহ ও মন সাড়া দিচ্ছিল না। কিন্তু ট্রেন চলে যাওয়ার মতো এক তীব্র শব্দে যখন তার চৈতন্য ফিরে এল, তখন সে অত্যন্ত কষ্টে উঠে দাঁড়াল।
২.১.৫ ‘নদীকে এভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত নদেরচাঁদ দিতে পারে।’ নদেরচাঁদের কৈফিয়তটি কী?
উত্তর: নদেরচাঁদের জন্ম নদীর কোলেই, বেড়ে ওঠাও নদীকে সঙ্গী করেই। নদীটি যেন তার চিরচেনা, আপন একজন মানুষ। এই সহজ সত্যকেই সে নদীর প্রতি তার গভীর ভালোবাসার সবচেয়ে সরল ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ “তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।” ‘তারা’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: পাবলো নেরুদা রচিত অসুখী একজন কবিতায় ‘তারা’ বলতে শান্ত হলুদ দেবতাদের স্বপ্ন দেখতে না পারার কথা বলা হয়েছে।
২.২.২ “জিজ্ঞাসিলান’ ওড়া বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় ‘নূতনের কেতন’ ওড়ানোর মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ও ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির দিন আর খুব দূরে নেই।
২.২.৩ ‘নূতনের কেতন’ ওড়া বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় ‘নূতনের কেতন’ ওড়ানোর মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ও ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির দিন আর খুব দূরে নেই।
২.২.৪ “সিন্ধুতীরে রহিছে মাঞ্জুস।” ‘মাঞ্জুস’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: সৈয়দ আলাওল রচিত ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতায় ‘মাঞ্জুস’ শব্দের অর্থ হল মান্দাস বা ভেলা।
২.২.৫ ‘গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে’ গানের বর্ম পরিধান করে কবি কোন্ কাজ করতে পারেন?
উত্তর: অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতায় কবি প্রকাশ করেছেন যে, গানের রক্ষাকবচ ধারণ করে তিনি হাতের ইশারায় বন্দুকের গুলিকে বিতাড়িত করতে সক্ষম।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ “ইতিহাসে ঠাঁই কিন্তু তার পাকা।” ইতিহাসে কার পাকা ঠাঁই?
উত্তর: ইতিহাসে কলমের অবস্থান চিরস্থায়ী কারন প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির পেছনে কলমের ভূমিকা অপরিসীম।
২.৩.২ “সেই আঘাতেরই পরিণতি নাকি তাঁর মৃত্যু।” কেমন আঘাতে, কার মৃত্যুর অনুমান করা হয়েছে?
উত্তর: বিখ্যাত সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছিল একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায়—লেখার কলমটি হঠাৎ অসাবধানতাবশত তাঁর বুকেই ফুটে যায়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই কলমের আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।
২.৩.৩ “যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে।”-শ্রেণি দুটি কী কী?
উত্তর: “যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে এই দুই শ্রেণির মধ্যে প্রথম শ্রেণি হল যারা ইংরেজি জানে না বা অতি অল্প জানে এবং দ্বিতীয় শ্রেণি হল যারা ইংরেজি জানে।
২.৩.৪ ‘বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: রাজশেখর বসুর ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধ অনুসারে, বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল গঠনমূলক ও গবেষণাধর্মী রচনা রয়েছে, সেগুলোই ‘বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ’ নামে পরিচিত।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
উত্তর: মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি হল – অধিকরণ কারকে ‘এ’ বিভক্ত।
২.৪.২ অনুসর্গ কাকে বলে? উদাহরণসহ বোঝাও।
উত্তর: বাংলা ব্যাকরণে, যেসব অব্যয় শব্দ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত না হয়ে সাধারণত নাম শব্দের (বিশেষ্য, সর্বনাম) পরে বসে সেই নাম শব্দটির সাথে বাক্যের অন্য পদ (যেমন – ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ) এর সম্পর্ক স্থাপন করে এবং শব্দটির অর্থকে সুনির্দিষ্ট বা পরিবর্তিত করে, তাদেরকে অনুসর্গ বলে। উদাহরণ – ঘর থেকে (বাড়ি থেকে – ‘থেকে’ অনুসর্গ যোগে উৎস বা সূচনা বোঝাচ্ছে)।
২.৪.৩ ‘অনুক্ত কর্তা’ বলতে কী বোঝো?
উত্তর: কর্ম ও ভাববাচ্যের কর্তাকে অনুক্ত কর্তা বলে। অনুক্ত কর্তার একটি উদাহরণ হল – রমার দ্বারা গান গাওয়া হয়।
২.৪.৪ কোন্ সমাসে দুটি বিজাতীয় সমস্যমান পদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়?
উত্তর: রূপক কর্মধারয় হলো এমন একটি সমাস যেখানে দুটি ভিন্ন জাতীয় পদকে একই বা অভিন্ন রূপে কল্পনা করা হয় এবং এতে একটি পদ অপরটির রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২.৪.৫ ‘তেমাথা’ ও ‘দশানন’ সমাসবদ্ধ পদ দুটির পার্থক্য কোথায়?
উত্তর: দুটিই বহুব্রীহি সমাস, কিন্তু শব্দগত উপাদান (তদ্ভব/তৎসম) এবং নির্দেশিত ব্যক্তিতে পার্থক্য রয়েছে।
২.৪.৬ ‘আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু।’ সমাসবদ্ধ পদটি চিহ্নিত করে সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: ‘আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু।’ এখানে সমাসবদ্ধ পদটি হল ‘কাকাবাবু।’ এবং সমাসের নাম হল কর্মধারয় সমাস।
২.৪.৭ ‘বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলোআনাই বজায় আছে’ সরল বাক্যে পরিণত করো।
উত্তর: ‘বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলোআনাই বজায় আছে’ এটিকে সরল বাক্যে পরিণত করলে হবে – বাবুটির স্বাস্থ্য খারাপ হলেও তার শখ আগের মতোই আছে।
২.৪.৮ বাক্য নির্মাণের শর্ত কটি ও কী কী?
উত্তর: বাক্য গঠনের মূল তিনটি শর্ত আমরা পেয়ে থাকি এইগুলি হল – আসত্তি, যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষা।
২.৪.৯ কর্মকর্তৃবাচ্যের একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: কর্মকর্তৃবাচ্যের একটি উদাহরণ হল –ছাত্রটি বইটি পড়ে।
২.৪.১০ আমার দ্বারা চিঠি লেখা হচ্ছে। (কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করো)।
উত্তর: আমার দ্বারা চিঠি লেখা হচ্ছে এটিকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করলে হবে আমি চিঠি লিখছি।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ ‘সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস।’ কোন্ জিনিসের কথা বলা হয়েছে? তা দুর্লভ কেন?
উত্তর: সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পের আলোচ্য অংশে, সবচেয়ে দুর্লভ বস্তুটি ছিল সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো।
সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পে জগদীশবাবুর বাড়িতে এক সন্ন্যাসীর সাত দিন অবস্থানের কথা জানা যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চস্তরের সাধক, যার বাসস্থান ছিল হিমালয়ের গুহায়। গোটা বছরে মাত্র একটি হরীতকী ভক্ষণ করেই তিনি জীবনধারণ করতেন; এছাড়া অন্য কোনো খাদ্য তার মুখে উঠত না। অনেকেরই ধারণা ছিল, এই সন্ন্যাসীর বয়স হাজার বছর ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই এই সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলোকে দুর্লভ বলা হয়েছে।
৩.১.২ “উনি দশ বছরের অমৃতকে জড়িয়ে ধরলেন।” ‘উনি’ কে? কেন অমৃতকে উনি জড়িয়ে ধরলেন?
উত্তর: ‘অদল বদল’ গল্পে ‘উনি’ শব্দটি দ্বারা ইসাবের পিতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।
ইসাবের জামা ছিঁড়ে যাওয়ায় ইসাবকে তার বাবার মার খাওয়া থেকে বাঁচাতে অমৃত নিজের জামার সাথে ইসাবের জামা বদলে নিয়েছিল। কারণ অমৃত বুঝতে পেরেছিল, তার নিজের মা থাকায় সে বাবার মার থেকে রক্ষা পেলেও ইসাবের কোনো মা নেই, কেবল একজন বাবাই তার একমাত্র অবলম্বন। এই দৃশ্য আড়াল থেকে দেখে অমৃতের মনের অগাধ উদারতা উপলব্ধি করে ইসাবের বাবার হৃদয় আনন্দে ভেসে যায় এবং তিনি অমৃতকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্নেহে আপ্লুত হন।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,” কে, কাকে বিধ্বস্ত করেছিলেন? কেন করেছিলেন?
উত্তর: কে, কাকে বিধ্বস্ত করেছিলেন -এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, অর্থাৎ ঈশ্বর, নিজের সৃষ্টি করা সত্তাগুলিকে বারবার বিধ্বস্ত করেছিলেন।
কারণ- প্রতিকূল মনে হলে স্রষ্টা নিজের সৃষ্টিকেই ভেঙে ফেলতেন এবং আবার নতুন করে গড়তেন। ভাঙা-গড়ার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তাঁর সৃষ্টিলীলা চলত। কবির ভাষায়, ‘উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে’ আফ্রিকা মহাদেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই ভাঙা-গড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এতে মহীসঞ্চরণ তত্ত্বেরও প্রতিফলন ঘটেছে—যেখানে ভূ-অভ্যন্তরের টেকটনিক প্লেটের নড়াচড়ার ফলে আদি মহাদেশ থেকে আফ্রিকা-সহ অন্যান্য মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।
৩.২.২ “দিগম্বরের জটায় হাসে শিশু-চাঁদের কর” ‘দিগম্বর’ কে? উদ্ধৃতিটির অর্থ কী?
উত্তর: ‘দিগম্বর- প্রদত্ত অংশে ‘দিগম্বর’ শব্দটি দ্বারা ভগবান মহাদেবকে বোঝানো হয়েছে। তিনি নটরাজ রূপে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা পরিচালনা করেন।
উদ্ধৃতিটির অর্থ- “দিগম্বরের জটায় হাসে শিশু-চাঁদের কর” — এই চিত্রকল্পে কবি ধ্বংস ও সৃষ্টির যুগল দিককে একত্রে প্রকাশ করেছেন। মহাদেবের জটায় থাকা শিশু-চাঁদ তাঁর রুদ্ররূপের মধ্যেও কোমলতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। ধ্বংসের মধ্য দিয়েই নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা জন্ম নেয়—এই ভাবনাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। কবির মতে, বিপ্লবের পথে ধ্বংস অনিবার্য হলেও তারই মধ্যে চূড়ান্তভাবে সুন্দরের উদ্ভাস ঘটে, যেমন দিগম্বরের জটায় চন্দ্রের শীতল আলো অন্ধকার ভেদ করে পথ দেখায়।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ “এই বহুরূপীর জীবন এর বেশি কী আশা করতে পারে?” কার উক্তি? গল্প অবলম্বনে বক্তার এমন উক্তির কারণ লেখো।
উত্তর: উদ্ধৃত উক্তিটি সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পের চরিত্র হরিদা-র মুখে বলা।
হরিদা পেশাগতভাবে একজন বহুরূপী। তিনি গরিব হলেও পেটের দায়ে গতে বাঁধা কাজ করতে চান না। শিল্পীমন, নির্লোভ ও স্বাধীনচেতা মানুষ হরিদা নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে মানুষকে বিস্মিত করেন— কখনও পাগল, কখনও বাইজি, কখনও আবার বিরাগী সন্ন্যাসীর রূপে।
বিরাগী সন্ন্যাসীর বেশে তিনি একদিন জগদীশবাবুর বাড়িতে যান এবং তাঁর চরিত্রে এতটাই একাত্ম হয়ে পড়েন যে, জগদীশবাবু যখন প্রণামী হিসেবে অনেক অর্থ দিতে চান, তখন হরিদা সেই অর্থ গ্রহণ না করে ফেলে চলে আসেন। কারণ, অর্থ নিলে তাঁর অভিনয়ের ভাব বা পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেত।
এই ঘটনার পর কথকরা যখন তাঁর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন হরিদা বলেন—
“এই বহুরূপীর জীবন এর বেশি কী আশা করতে পারে?”
এই উক্তিতে হরিদা জানেন, তাঁর জীবন কেবলই ছদ্মবেশের— যেখানে সত্যিকার মানুষটি সমাজের চোখে হারিয়ে গেছে। তাই তিনি জানেন, তাঁর জীবনের প্রাপ্তি সীমিত, এই অভিনয়ভরা জীবনে বড় কোনও আশা রাখাই বৃথা।
৪.২ “পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল।” ‘পথের দাবী’ পাঠ্যাংশে সব্যসাচী মল্লিক সম্পর্কে কী জানা যায়? তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কী পরিস্থিতি তৈরি হয়?
উত্তর: অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘পথের দাবী’ পাঠ্যাংশে জানা যায় যে, সব্যসাচী মল্লিক বিপ্লবী দলের প্রধান। তিনি ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ‘পলিটিক্যাল সাসপেক্ট’। রেঙ্গুনে তিনি গিরীশ মহাপাত্র নাম নিয়ে এক সাধারণ শ্রমজীবী রূপে উপস্থিত হন। তাঁর শরীর দুর্বল ও শীর্ণ, মুখে সামান্য কাশির ভাব। রোদে পুড়ে তাঁর ফরসা গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে। মাথায় চেরা সিঁথি, লেবুর তেলের গন্ধে ভরা চুল, রামধনু রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি, কালো মখমলের শাড়ি, সবুজ মোজা ও বার্নিশ করা পাম্প-শু—এই বিচিত্র সাজসজ্জা তাঁকে অদ্ভুত এক চরিত্রে পরিণত করে।
নিমাইবাবুর সামনে হাজির করা হলে পুলিশকর্মীরা তাঁর অদ্ভুত চেহারা ও গন্ধে বিরক্ত হয়। নিমাইবাবু তাঁর তার পকেট থেকে পাওয়া গাঁজার কলকে দেখে প্রশ্ন করলে, গিরীশ মহাপাত্র অবলীলায় বলে যে, সে শুধু অন্যের প্রয়োজনে গাঁজার কলকে দেয়। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর, অদ্ভুত সাজসজ্জা ও ভিন্নরকম আচরণে কেউই তাঁকে সব্যসাচী হিসেবে চিনতে পারে না। গিরীশ মহাপাত্রের কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ দেখে সবারই নিশ্চয়তা জন্মে যে, এই ব্যক্তি কখনোই সব্যসাচী মল্লিক নয়। ফলে, তাকে কিছুক্ষণ জেরা করে এবং ঠাট্টা-তামাশা করার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ “রূপে অতি রম্ভা জিনি”- ‘রম্ভা’ কে? তার রূপের সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির যে রূপচিত্র পাঠ্যাংশে বর্ণিত হয়েছে, তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।
উত্তর: “রূপে অতি রম্ভা জিনি” এই উদ্ধৃতিতে ‘রম্ভা’ শব্দটি দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের অপ্সরা রম্ভাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
রম্ভা রূপের সাথে সিংহল-রাজকন্যা পদ্মাবতীর তুলনা করা হয়েছে।
মধ্যযুগের কবি আলাওয়লের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে নায়িকা পদ্মাবতীর রূপ-বর্ণনা এক অপূর্ব কাব্যিক মহিমায় ভাস্বর। তাঁর অলকাবৃত কুন্তলরাজি পাদপ্রান্তে নেমে এসেছে, রজনীর গহন অন্ধকারকে যেন ম্লান করেছে; সিঁথিতে শোভে চাঁদবদনের শুভ্রতা। তাঁর নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় গভীর, কাজল-কালো, যেন মথুরারই এক জীবন্ত মূর্তি। কবি পদ্মাবতীর বদন-কমলকে তুলনা করেছেন পদ্মের সাথে, আর তাঁর লাবণ্যের প্রভায় মথুরার সৌন্দর্যকেও যেন করিয়াছেন নিষ্প্রভ।
৫.২ “আমি এখন হাজার হাতে পায়ে/ এগিয়ে আসি,” ‘আমি’ কে? ‘হাজার হাত-পা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কবির মনোভাব ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: জয় গোস্বামী লেখা ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় ‘আমি’ বলতে কবি নিজেকে বুঝিয়েছেন।
“অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতায় কবি জয় গোস্বামী অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংগীতের শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হোক বা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কোন শক্তি—মানুষের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে গানই হয়ে উঠেছে একটি প্রধান হাতিয়ার। কবির মতে, গান কেবলমাত্র আনন্দের বাহক নয়, এটি সংগ্রামের ক্ষেত্রে ‘বর্ম’-স্বরূপও হতে পারে। এই ‘গানের বর্ম’ পরেই কবি বন্দুকের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, গুলিকে প্রতিহত করেছেন। এভাবেই লড়াই করতে গিয়ে কবি উপলব্ধি করেছেন, তিনি একা নন—অসংখ্য মানুষ একই পথের সঙ্গী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গণআন্দোলনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যুগে যুগে গানই মানুষের প্রতিবাদের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সকলের সম্মিলিত কণ্ঠের প্রতিবাদী গান অস্ত্রের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। গানের এই সামর্থ্য এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের একত্রিত করার ক্ষমতার কথাই কবি তাঁর কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।
কবি জয় গোস্বামীর মতে, গান হলো জীবন-সংগ্রামের এক অনন্ত সম্বল। ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় তিনি প্রসারিত রাইফেলের মুখোমুখি গানকে ঢাল-তলোয়ার ও প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গান এখানে পরিণত হয়েছে মানুষের পারস্পরিক বন্ধনের এক অপরিহার্য বুনিয়াদে। কবি শিল্প ও সাহিত্যকে অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ-ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন এই রচনায়।
৬। কমিেশ ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ ‘সব মিলিয়ে লেখালেখি রীতিমতো ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠান।’ লেখালেখি ব্যাপারটিকে একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠান বলা হয়েছে কেন বুঝিয়ে লেখো।
উত্তর: আলোচ্য উদ্ধৃতাংশটি ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে । লেখক শ্রীপান্থ তাঁর কিশোর বয়সের লেখাপড়া বিষয়ে উপরিউক্ত মন্তব্যটি করেছেন ।
লেখক গ্রামের ছেলে ছিলেন বলে লেখাপড়ার প্রথম জীবনে ফাউন্টেন পেন হাতে পায়নি। বাঁশের কঞ্চির কলম ব্যবহার করতেন । যে কলম তিনি নিজের হাতে তৈরি করতেন । কলমের কালিও তাঁকে তৈরি করে নিতে হত। কলম তৈরি হতো- বাঁশের সরু কঞ্চি কেটে তাতে কলমের নিব তৈরি করা হত। কালি যাতে সহজে গড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য এর ডগা চিরে নেওয়া হত। লেখা হত কলার পাতায়। আর কালিও তৈরি করতে হত নিজেদেরকেই। কালি তৈরীর জন্য বাড়ির রান্নার কড়াই -এর তলার কালি লাউ পাতা দিয়ে ঘষে তুলে এনে পাথরের বাটিতে জলের সঙ্গে গুলে নেওয়া হত। মাঝেমধ্যে হরীতকী কিংবা আতপ চাল ভেজে পুড়িয়ে গুঁড়ো করে তাতে মেশানো হত; তারপর খুন্তি পুড়িয়ে গরম অবস্থায় জলে ছ্যাঁকা দিয়ে ফুটিয়ে নেওয়া হত। বাঁশের কলম, মাটির দোয়াত, ঘরে তৈরি কালি আর কলাপাতা—এই ছিল লেখকের লেখালেখির প্রথম সাথি। লেখক দোয়াতের কালি আর বাঁশের কঞ্চি অনেকদিন ব্যবহার করতেন । এইভাবে লেখাপড়া করার প্রসঙ্গে লেখক উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন ।
শহরের উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর বাঁশ বা কঞ্চির কলমের ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ঘরোয়া কালি তৈরি করাও থেমে যায়। কাচের দোয়াতে এখন ব্যবহার হতে থাকে কালির ট্যাবলেট বা বড়ি। তৈরি কালি সহজলভ্য হয়ে ওঠে দোয়াতেই। ফাউন্টেন পেনের জন্য আসে বিদেশি কালি। নানা ধরনের নিব ও হ্যান্ডেলের প্রচলন হয়। ফাউন্টেন পেনের নিব সোনা বা প্ল্যাটিনাম দিয়ে মুড়ে দেওয়ার চলও শুরু হয়। এই পর্যায়ে দোয়াত-কলম পরিণত হয় ঘর সাজানোর একটি জিনিসে। লেখা শুকানোর জন্য আগে বালি ব্যবহার করা হত, পরে তার জায়গা নেয় ব্লটিং পেপার। প্রথম দিকে এর চেহারা একরকম থাকলেও পরবর্তীতে তার রূপ বদলে যায়। সময়ের ব্যবধানে এসবই এখন সবই অতীত। লেখাপড়ার জন্য বিশেষ করে লেখালেখির জন্য, সঠিক জায়গায় লেখা উপস্থাপিত করার জন্য বিশাল আয়োজন করতে হত । এই সব কারণে লেখক উক্ত মন্তব্য করেছেন ।
৬.২ “যে লোক আজন্ম ইজার পরেছে তার পক্ষে হঠাৎ ধুতি পরা অভ্যাস করা একটু শক্ত।” ‘ইজার’ ও ‘ধুতি’ উপমা দুটি ব্যাখ্যা করে, প্রাবন্ধিকের বক্তব্যটি বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু তাঁর ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ শীর্ষক রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার প্রধান পাঠকসমাজ হলেন ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত এবং ইংরেজি মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চায় অভ্যস্ত ব্যক্তিবর্গ। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার পথে যে সমস্যাগুলি উপস্থিত হয়, তার প্রসঙ্গ তুলে ধরতেই তিনি এই মন্তব্যটি করেন।
বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদির পাঠকদের প্রাবন্ধিক মূলত দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণিভুক্ত পাঠকগণ ইংরেজি ভাষায় বিশেষ দক্ষ নন এবং বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সীমিত। কয়েকটি পরিভাষা কিংবা কিছু বৈজ্ঞানিক ঘটনা সম্পর্কে তাদের সাধারণ ধারণা থাকলেও, এর বাইরে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প। এদের জন্য বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা কোনও সমস্যারই বিষয় নয়। কিন্তু সমস্যাটা দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠকদের নিয়ে, যারা ইংরেজি ভাষায় দক্ষ এবং সেই মাধ্যমেই বিজ্ঞানশিক্ষায় অভ্যস্ত। বাংলায় বিজ্ঞান পাঠের সময় ইংরেজি মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও পরিভাষাগুলোই তাদের জন্য একপ্রকার বাধা সৃষ্টি করে। তাই পূর্ববর্তী জ্ঞানের এই প্রভাবকে সংযত করে তাদের বাংলা বৈজ্ঞানিক রচনা পাঠ করতে হয়, যা তাদের কাছে কষ্টসাধ্য ও সমস্যাজনক বলে প্রতিভাত হয়। এটাকে তুলনা করা চলে আজন্ম ইজার পরিহিত ব্যক্তিকে হঠাৎ করে ধুতি পরতে বাধ্য করার মতো। তাই অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করলেই কেবল এই জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “কিন্তু ভদ্রতার অযোগ্য তোমরা!” কাকে উদ্দেশ করে কথাটি বলা হয়েছে? একথা বলার কারণ কী?
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের একটি পর্বে, বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর রাজসভায় ইংরেজ দূত ওয়াটসের উদ্দেশ্যে যে প্রশ্নবাণ ছুড়ে দেন, সেটিই আলোচ্য উক্তি।
‘আলিনগরের সন্ধি’র শর্তানুযায়ী, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার যুদ্ধ পরিচালনা বা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু একদিন নবাবের হাতে কলকাতা থেকে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের একটি গোপন পত্র আসে। সেই পত্র থেকে তিনি হনন হয়ে যান, ওয়াটসনের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধের আয়োজন করছে এবং আরও সৈন্য ও নৌবহর পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। তিনি আরও জানতে পারেন, বহুদিন আগে থেকেই লর্ড ক্লাইভ নিজে নবাবের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন এবং আলিনগরের সন্ধি ভঙ্গ করতেই তারা সচেষ্ট হয়েছেন। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, নবাবের দরবারে কোম্পানির যে প্রতিনিধি ওয়াটস উপস্থিত থাকতেন, তিনিও এই ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত সিরাজ, ওয়াটসকে প্রকাশ্য দরবারে এই কথা বলতে বাধ্য করেন।
৭.২ “দুর্দিন না সুদিন?” কোন্ ঘটনা, কার কাছে দুর্দিন, কার কাছেই বা সুদিন যুক্তিসহ লেখো।
উত্তর: উদ্ধৃত অংশটি ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ থেকে গৃহীত। এর বক্তা হলেন নবাব আলিবর্দি খাঁ–এর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও নবাব সিরাজদ্দৌলার মাসি ঘসেটি বেগম।
আলিবর্দি খাঁ–এর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর প্রিয় সৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা। কিন্তু ঘসেটি বেগম চেয়েছিলেন যে, তাঁর এক বোনের পালিত পুত্র শওকতজং নবাব হোক। এই আশা পূরণ না হওয়ায় তিনি সিরাজদ্দৌলার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন এবং মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রমুখের সঙ্গে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।
সিরাজদ্দৌলা বুঝতে পারেন ঘসেটি বেগম ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার মোহে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি ঘসেটির মতিঝিল প্রাসাদ অধিকার করে তাঁকে সসম্মানে নিজের প্রাসাদে স্থান দেন। কিন্তু ঘসেটি তাতে সন্তুষ্ট হননি; বরং তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন ইংরেজ বাহিনী কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করুক। ফলে, ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ সিরাজদ্দৌলার কাছে ‘দুর্দিন’, কারণ এটি তাঁর রাজ্য ও স্বাধীনতার পতনের সূচনা। কিন্তু ঘসেটি বেগমের কাছে তা ‘সুদিন’, কারণ তাঁর কামনা ছিল সিরাজের পতন ও ধ্বংস।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় কোনির দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের পরিচয় দাও।
উত্তর: মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় কোনির দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের পরিচয় নিম্নরূপ –
দুর্ভাগ্য –
১. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বাধা – কোনিকে প্রাথমিকভাবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। জুপিটার ক্লাবের কর্মকর্তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তার এন্ট্রি বাতিল করে এবং বিভিন্ন অজুহাতে তাকে বাদ দেয়।
২. অন্যান্য প্রতিযোগীদের বৈষম্যমূলক আচরণ – কোনির সাথে অন্যান্য প্রতিযোগীরা ভালো ব্যবহার করেনি। তারা তাকে উপেক্ষা করত এবং তার সাথে মিশত না।
৩. প্রতিযোগিতায় অসুবিধা – মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় কোনির জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তার কোচ ক্ষিতীশ সিংহের অনুপস্থিতি তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে তুলেছিল।
সৌভাগ্য –
১. শেষ মুহূর্তে সুযোগ – অমিয়ার আঘাতপ্রাপ্তির কারণে শেষ মুহূর্তে কোনিকে রিলে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি তার জন্য একটি বড় সুযোগ হয়ে আসে।
২. ক্ষিতীশ সিংহের অনুপ্রেরণা – প্রতিযোগিতার সময় ক্ষিতীশ সিংহের আকস্মিক উপস্থিতি এবং অনুপ্রেরণা কোনিকে নতুন শক্তি দেয়। তার “কোনি, ফাইট!” ডাক কোনিকে উদ্দীপ্ত করে।
৩. বিজয়ী হওয়া – কোনি শেষ পর্যন্ত রিলে ইভেন্টে বিজয়ী হয়ে বাংলা দলকে চ্যাম্পিয়নশিপ এনে দেয়। এটি তার জীবনের একটি বড় সাফল্য এবং স্বীকৃতি অর্জন করে।
মাদ্রাজ প্রতিযোগিতায় কোনির জীবন সংগ্রাম, বৈষম্য এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ের একটি চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে।
৮.২ “ফাইট কোনি, ফাইট।” সাধারণ সাঁতারু থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠতে গিয়ে কোনিকে কী ধরনের ‘ফাইট’ করতে হয়েছিল, নিজের ভাষায় লেখো।
উত্তর: জনপ্রিয় লেখক মতি নন্দী রচিত ‘কোনি’ উপন্যাসে এক অসাধারণ সংগ্রামী মেয়ের জীবনকাহিনি চিত্রিত হয়েছে। শ্যামপুকুর বস্তির দরিদ্র পরিবারের মেয়ে কোনি ছোটবেলা থেকেই সাঁতারে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিল। কিন্তু সেই দক্ষতাকে জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হলে তাকে লড়তে হয়েছে নানা বাধা, বঞ্চনা ও দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে। তার জীবন যেন এক অবিরাম যুদ্ধ। সাধারণ সাঁতারু থেকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠতে গিয়ে কোনির যে সব ‘ফাইট’ করতে হয়েছে,—
১. দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ফাইট: কোনির জীবনের প্রথম ও সবচেয়ে বড় বাধা ছিল দারিদ্র্য। শ্যামপুকুর বস্তির একটি দুঃস্থ পরিবারের মেয়ে হিসেবে তিনবেলা পেট ভরে খাওয়াটাই ছিল তাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। নতুন সাঁতারের পোশাক, গগলস বা ক্লাবের সদস্যপদের খরচ জোগানো তো দূরের কথা, তার পরিবারের পক্ষে একটি সাধারণ কস্ট্যুম কিনে দেওয়াও সম্ভব ছিল না। তবু ক্ষিদ্দাদা (ক্ষিতীশ রায়) যখন তার প্রতিভা চিনতে পারেন, তখন থেকেই কোনি নিজের জীবনের প্রতিটি কষ্টকে সহ্য করে এগিয়ে যেতে থাকে। দারিদ্র্য তার স্বপ্নকে থামাতে পারেনি — বরং শক্তি জুগিয়েছে।
২. নিজের সঙ্গে ফাইট: কোনির দ্বিতীয় লড়াই ছিল নিজের ভিতরের দুর্বলতা ও হীনমন্যতার সঙ্গে। সে ছিল না ধনী বা শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, ফলে অনেক সময় নিজের অবস্থান নিয়ে লজ্জা পেত। অমিয়া যখন তাকে ‘ঝি’ বলেছিল, তখন সে গভীরভাবে অপমানিত হয়েছিল। কিন্তু এই অপমানকেই সে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। সে নিজেকে প্রশ্ন করে, “অমিয়ার রেকর্ডটা কবে ভাঙতে পারব?” — এই প্রশ্নই তার অন্তরের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এভাবেই সে নিজের অক্ষমতাকে ক্ষমতায় রূপান্তরিত করে লড়ে গেছে নিজের সঙ্গে।
৩. সমাজ ও বিদ্রূপের বিরুদ্ধে ফাইট: দরিদ্র বস্তির মেয়ে বলে কোনিকে সমাজে অনেক সময় বিদ্রূপ ও অবহেলা সহ্য করতে হয়েছে। সাঁতারের জগতে তার অবস্থান মেনে নিতে পারেনি অনেকেই। কখনো তাকে তুচ্ছ বলা হয়েছে, কখনো ‘ক্লাবের মান নষ্ট করবে’ বলে উপহাস করা হয়েছে। কিন্তু কোনি এসব উপেক্ষা করে নিজের স্বপ্নে অবিচল থেকেছে।
৪. ষড়যন্ত্র ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফাইট: জুপিটার ক্লাবে ক্ষিদ্দাদার বিরোধিতা করা কয়েকজন ব্যক্তি কোনির প্রতিভাকে মেনে নিতে পারেনি। তারা নানা ষড়যন্ত্র ও অন্যায় আচরণে তাকে ভুগিয়েছে। কখনো তাকে অকারণে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কখনো হারানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষিদ্দাদার মানসিক সাহচর্যে কোনি এসবের সামনে মাথা নত করেনি।
৫. বঞ্চনার বিরুদ্ধে ফাইট: মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় পৌঁছেও কোনিকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়। বারবার তাকে বসিয়ে রাখা হয়, প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ দেওয়া হয় না। একের পর এক রেস সে গ্যালারিতে বসে কেঁদে দেখেছে। কিন্তু তবুও সে আশা ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত সুযোগ পেয়ে নিজের প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রম দিয়ে সে প্রমাণ করে যে তার মতো সাহসী লড়াকু মেয়েকে কেউ থামাতে পারে না।
অবশেষে মাদ্রাজের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় কোনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে চ্যাম্পিয়নের আসন অর্জন করে। তার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল —
“ফাইট কোনি, ফাইট।”
এই একটি সংলাপই যেন প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের জন্য প্রেরণার উৎস। কোনির লড়াই আমাদের শেখায় — দরিদ্রতা, অপমান, বঞ্চনা বা ষড়যন্ত্র যাই আসুক না কেন, যদি আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায় থাকে, তবে সাফল্য একদিন আসবেই।
৮.৩ ‘ট্যালেন্ট ঈশ্বরের দান।” ‘ট্যালেন্ট’ কী? ‘ট্যালেন্ট’ সম্পর্কে ক্ষিতীশের মতামত কী ছিল?
উত্তর: সাধারণত ‘ট্যালেন্ট’ বা প্রতিভা বলতে কোনো ব্যক্তি বা দলের মধ্যে বিদ্যমান এক ধরনের স্বাভাবিক ও অসাধারণ দক্ষতা বা যোগ্যতাকে বোঝায়, যা অনেকাংশেই জন্মগতভাবে পাওয়া। ইংরেজি ‘ট্যালেন্ট’ শব্দের অর্থ হলো প্রতিভা।
ক্ষিতীশের মতে ছিল প্রতিভা হলো জন্মগত একটি গুণ; একে কোনোভাবেই অর্জন করা যায় না। ক্ষিতীশ সিংহ বিষ্টুধরের বক্তৃতা লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে, প্রতিভা হলো ঈশ্বরের দান—এর কোনো বিনিময় হয় না। যার মধ্যে প্রতিভা রয়েছে, সে যদি তা কাজে লাগাতে না পারে, তবে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা উচিত। তাঁর মতে, বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের কেবল খাওয়া-পরার জন্যই উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। রাশিয়ার মতো বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোতে বড় বড় খেলোয়াড়দের খাওয়া-পরার জন্য চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে সরকার সব ধরনের দায়িত্ব নিতে পারে না। তাই খেলোয়াড়দেরকে সবকিছুর জন্য সংগ্রাম করতে হয়। কেবল প্রতিভা থাকলেই চলবে না—আরাম বা আরামদায়ক জীবন নয়, বরং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই একজন খেলোয়াড়কে তার প্রতিভার স্বীকৃতি অর্জন করতে হবে।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো:
Newspaper reading has become an essential part of our life. As we get up in morning, we wait eagerly for the daily paper. Twentieth century was an age of newspapers. Through newspapers we gather information about different countries of the world.
উত্তর: সংবাদপত্র পড়া এখন আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা অধীর আগ্রহে দৈনিক পত্রিকার জন্য অপেক্ষা করি। বিংশ শতাব্দী ছিল সংবাদপত্রের যুগ। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খবর ও তথ্য জানতে পারি।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ বৃক্ষরোপণ-উপযোগিতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
সংলাপ:
বৃক্ষরোপণের উপযোগিতা
রবি: হে সুমন, দেখছিস তো, গরমে এখন বৃষ্টি পর্যন্ত হচ্ছে না! পরিবেশটা একেবারে অসহ্য হয়ে গেছে।
সুমন: হ্যাঁ রে, এর প্রধান কারণই হলো বনভূমি ধ্বংস আর গাছপালা কাটা।
রবি: ঠিক বলেছিস। তাই এখন সবাইকে বৃক্ষরোপণে অংশ নিতে হবে।
সুমন: একদম ঠিক। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, ছায়া দেয়, ফল দেয়, মাটি ধরে রাখে—সব দিক থেকেই উপকার করে।
রবি: শুধু তাই নয়, গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশ দূষণও কমায়।
সুমন: হ্যাঁ, আর পাখি, পশুপাখির আশ্রয়স্থলও গাছ। তাই গাছ কাটা মানে প্রকৃতিকে ধ্বংস করা।
রবি: তাই তো আমি ভাবছি, আমাদের স্কুলে একটা বৃক্ষরোপণ অভিযান আয়োজন করব।
সুমন: চমৎকার! আমিও থাকব। সবাই মিলে যদি সচেতন হই, তবে পরিবেশ আবার সবুজ হবে।
রবি: ঠিক বলেছিস। গাছ লাগাও, জীবন বাঁচাও—এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।
১০.২ বহরমপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
বহরমপুরে আন্তর্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা
নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর: গতকাল বহরমপুর শহরের ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল মুর্শিদাবাদ জেলা ক্রীড়া পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর যৌথভাবে। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপালসহ মোট পাঁচটি দেশের প্রায় ৬০ জন সাঁতারু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।
প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের আধুনিক সুইমিং পুলে। উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে প্রতিযোগিতা চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ইভেন্টে ভারতের সাঁতারুরা চ্যাম্পিয়ন হয়। দর্শকদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস।
শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেলা শাসক। আয়োজকরা জানান, আগামী বছর আরও বড় পরিসরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতা স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো:
১১.১ পরিবেশ সুরক্ষায় ছাত্রসমাজের ভূমিকা।
উত্তর:
পরিবেশ সুরক্ষায় ছাত্রসমাজের ভূমিকা
ভূমিকা:
বর্তমান যুগে পরিবেশ দূষণ মানবজীবনের এক ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দূষিত বাতাস, নোংরা জল, প্লাস্টিকের বর্জ্য, বননিধন—এসবই প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে। ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগব্যাধি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকার বা বিশেষজ্ঞদের নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের। বিশেষত ছাত্রসমাজ এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
মূল আলোচনা:
ছাত্রসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সচেতনতা ও কর্মশক্তি প্রবল। তাই তারা পরিবেশ রক্ষায় নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে পারে—
১. সচেতনতা বৃদ্ধি:
বিদ্যালয় ও কলেজে পরিবেশ বিষয়ে আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা সহপাঠী ও সমাজের মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারে।
২. বৃক্ষরোপণ অভিযান:
প্রতিটি বিদ্যালয় বা মহল্লায় ছাত্রদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করা যেতে পারে। “এক ছাত্র এক গাছ” প্রকল্প চালু করা হলে পরিবেশে সবুজের পরিমাণ বাড়বে।
৩. প্লাস্টিক বর্জন:
ছাত্রছাত্রীরা প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাগজ, কাপড় বা জুটের ব্যাগ ব্যবহার করতে পারে এবং অন্যদেরও তা করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।
৪. পরিচ্ছন্নতা অভিযান:
বিদ্যালয়, পাড়া-মহল্লা পরিষ্কার রাখা, বর্জ্য পৃথকীকরণে অংশগ্রহণ, ডাস্টবিন ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া—এসব কাজের মাধ্যমে তারা সমাজকে সচেতন করতে পারে।
৫. জল ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়:
প্রয়োজন ছাড়া কল খোলা না রাখা, আলো-ফ্যান বন্ধ রাখা ইত্যাদি অভ্যাস গড়ে তুলে ছাত্ররা পরিবেশবান্ধব জীবনধারার উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে।
৬. পরিবেশ আন্দোলনে অংশগ্রহণ:
বিভিন্ন এনজিও ও সরকারি প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রসমাজ বৃহত্তর পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষার কাজে যুক্ত হতে পারে।
উপসংহার:
পরিবেশ রক্ষা না হলে মানবসভ্যতা বিপন্ন হবে। ছাত্রসমাজই এই সঙ্কট মোকাবিলার সবচেয়ে কার্যকর শক্তি। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিবেশ সুরক্ষার আন্দোলন এক নতুন দিশা পেতে পারে। তাই আমাদের সকলের উচিত—ছাত্রদের এই মহান কাজে উৎসাহ দেওয়া, যাতে তারা আগামী প্রজন্মের জন্য এক সবুজ ও সুস্থ পৃথিবী উপহার দিতে পারে।
১১.২ একটি পোস্টকার্ডের আত্মকথা।
উত্তর:
একটি পোস্টকার্ডের আত্মকথা
আমি একটি ছোট্ট পোস্টকার্ড। আমার শরীর কাগজের, কিন্তু আমার বুকে লুকিয়ে থাকে অজস্র ভালোবাসা, খবর, আশা আর অভিমান। আমি ডাক বিভাগের এক সৎ কর্মচারীর মতো, মানুষের মনের কথা পৌঁছে দিই দূরে থাকা প্রিয়জনের কাছে। আজ আমি তোমাদের আমার নিজের গল্প শোনাবো।
একদিন এক দোকানে আমাকে ছাপানো হলো সুন্দর করে। আমার গায়ে ছিল দেশের মানচিত্র আর পাশে লেখা ছিল “ভারত সরকার”। আমি জানতাম, একদিন কোনো মনের কথা বয়ে নিয়ে আমি ছুটে যাবো দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।
কিছুদিন পর এক তরুণ আমাকে কিনে নিল। হাতে কলম নিয়ে সে লিখতে লাগল—“প্রিয় মা, আমি ভালো আছি। চিন্তা কোরো না। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব।” তার লেখার প্রতিটি শব্দে আমি অনুভব করলাম তার ভালোবাসা, মায়ের প্রতি টান। তারপর সে আমাকে ডাকবাক্সে ফেলে দিল।
ডাকবাক্স থেকে আমি গেলাম ডাকঘরে। সেখান থেকে ডাকপিয়ন আমাকে নিয়ে ছুটল ট্রেনে, বাসে, কখনো পায়ে হেঁটে। পথে আমি অনেক পোস্টকার্ডের সঙ্গ পেলাম—কেউ প্রেমের কথা লিখে এনেছে, কেউ বন্ধুর খবর, কেউ আবার কোনো উৎসবের নিমন্ত্রণ। আমি বুঝলাম, আমরা সবাই এক একটি অনুভূতির দূত।
অবশেষে আমি পৌঁছালাম আমার গন্তব্যে—একটি ছোট্ট গ্রামে। সেখানে এক স্নেহময়ী মা ডাকপিয়নের হাত থেকে আমাকে নিলেন। তিনি পড়লেন তার ছেলের লেখা কথা, চোখে জল এলো, কিন্তু সেই জলে ছিল আনন্দ আর সান্ত্বনা। আমি তখন গর্বে ফুলে উঠলাম—কারণ আমি তাঁর মুখে হাসি এনে দিয়েছি।
আজকের দিনে আমার কদর কমে গেছে। মোবাইল, ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া আমাকে প্রায় ভুলে গেছে। তবুও আমি জানি, যখন কেউ নিজের হাতে কলমে লেখে আর আমাকে পাঠায়, তখন সেই ভালোবাসার উষ্ণতা কোনো প্রযুক্তিই দিতে পারে না।
আমি শুধু একটি কাগজ নই, আমি স্মৃতি, আমি অনুভূতি, আমি এক যুগের সাক্ষী। আমি চাই, মানুষ যেন আবার হাতে কলম তুলে নেয়, আর আমাকে দিয়ে তাদের মনের কথা পাঠায়।
পোস্টকার্ড আজ আধুনিক যুগে হারিয়ে যেতে বসেছে, তবু মানুষের ভালোবাসা ও অনুভূতির সৎ বাহক হিসেবে আমার মূল্য চিরকাল অমলিন থাকবে।
১১.৩ ভারতপথিক রামমোহন।
উত্তর:
ভারতপথিক রামমোহন
ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁকে যথার্থই বলা হয় “ভারতপথিক” বা ভারতের নবজাগরণের পথপ্রদর্শক। তাঁর চিন্তা, কর্ম, ও সমাজসংস্কারের আদর্শ আজও ভারতবাসীর পথ আলোকিত করে চলেছে।
জন্ম ও শিক্ষাজীবন:
রামমোহন রায় ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তাঁর ছিল গভীর দখল। দেশি-বিদেশি দর্শন, ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে তিনি অল্প বয়স থেকেই গভীর অধ্যয়ন শুরু করেন।
সমাজসংস্কারক হিসেবে ভূমিকা:
রামমোহনের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজ সংস্কার। তৎকালীন সমাজে নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে মানুষ আবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে ‘সতীদাহ প্রথা’ ছিল এক ভয়ংকর সামাজিক অভিশাপ। রামমোহন তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তা ও মানবিক চেতনার দ্বারা এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর প্রচেষ্টা ও ইংরেজ শাসক লর্ড বেন্টিঙ্কের সহায়তায় ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা আইনি ভাবে বিলুপ্ত হয়।
ধর্মচিন্তা ও ব্রাহ্মসমাজ:
রামমোহন ঈশ্বরকে এক ও নিরাকার রূপে মানতেন। তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। ১৮২৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন “ব্রাহ্মসমাজ”। এই সমাজে মানবধর্ম, যুক্তি, ও নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে এক নতুন ধর্মীয় ভাবধারার প্রচার হয়।
শিক্ষা ও নারীকল্যাণে অবদান:
রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে সমাজের উন্নতি শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি ইংরেজি ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলনে উদ্যোগী হন। নারীর অধিকার রক্ষায়ও তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন এবং নারীদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতেন।
রামমোহনের ভাবধারার প্রভাব:
রামমোহনের চিন্তা ও কর্ম শুধু তাঁর যুগেই নয়, পরবর্তী প্রজন্মের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের প্রথম পথিকৃৎ—একজন সত্যিকারের মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তক।
উপসংহার:
রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত। সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও নারীমুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তাই তাঁকে যথার্থই বলা হয় “ভারতপথিক রামমোহন”—যিনি ভারতের আধুনিকতার পথে প্রথম আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেছিলেন।
১১.৪ ভারতের সাম্প্রতিক চন্দ্রাভিযান ও সাফল্য।
উত্তর:
ভারতের সাম্প্রতিক চন্দ্রাভিযান ও সাফল্য
ভূমিকা:
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আজ ভারত এক উজ্জ্বল নাম। মহাকাশ গবেষণায় ভারতের অগ্রযাত্রা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ভারতের সাম্প্রতিক চন্দ্রাভিযান “চন্দ্রযান-৩”-এর সাফল্য আমাদের গর্বিত করেছে। এটি ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়।
চন্দ্রযান-৩ এর পরিচয়:
ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) ১৪ জুলাই ২০২৩ সালে চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণ করে। এটি ছিল সম্পূর্ণ স্বদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি এক অসাধারণ মহাকাশযান। এর মূল লক্ষ্য ছিল চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে সেখানে গবেষণা চালানো। পূর্ববর্তী মিশন “চন্দ্রযান-২”-এর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবার ইসরো আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
অবতরণ ও গবেষণা:
২৩ আগস্ট ২০২৩ সালে চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে। এটি বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ভারতের এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব। চন্দ্রযানের ল্যান্ডার ‘বিক্রম’ এবং রোভার ‘প্রজ্ঞান’ চাঁদের মাটির উপাদান, তাপমাত্রা, খনিজ পদার্থ এবং ভূ-গঠন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছে। এই তথ্য ভবিষ্যতে মানব চন্দ্রাভিযানে বিশেষ সহায়ক হবে।
সাফল্যের তাৎপর্য:
চন্দ্রযান-৩ এর সফলতা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন দিশা দিয়েছে। এই অভিযানের মাধ্যমে ভারত প্রমাণ করেছে যে সীমিত বাজেটেও বড়ো সাফল্য অর্জন সম্ভব। এই সাফল্যের ফলে ভারত আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের পর চাঁদের পৃষ্ঠে সফলভাবে অবতরণকারী দেশ হিসেবে চতুর্থ স্থানে স্থান পেয়েছে।
উপসংহার:
চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য ভারতের বিজ্ঞানী সমাজের অধ্যবসায়, মেধা ও সাহসের প্রতীক। এই অভিযান ভবিষ্যতে আরও উন্নত গবেষণার পথ খুলে দিয়েছে। এই সাফল্য আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে। ভারত আজ মহাকাশ গবেষণায় এক গর্বিত শক্তি—এই চন্দ্রাভিযান তারই প্রমাণ।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।