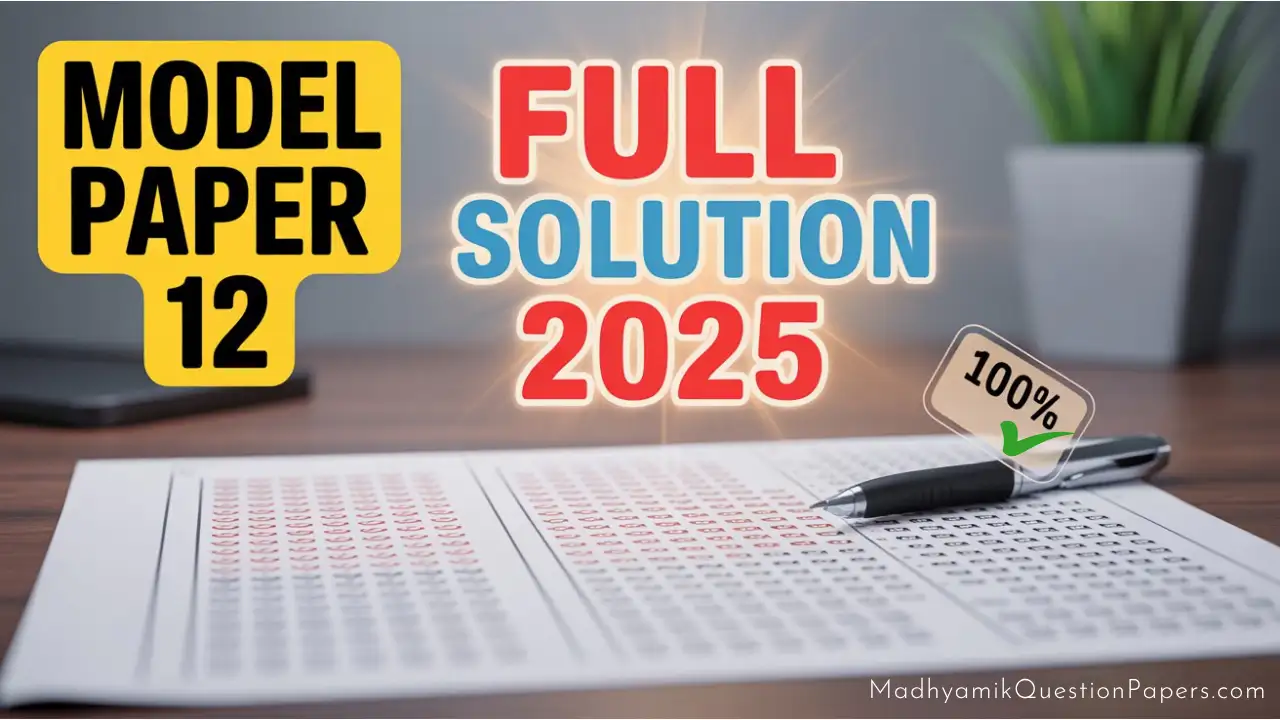আপনি কি ২০২৫ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 12 (2025) এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা Model Question Paper 12 (2025)-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৫ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ গিরীশ মহাপাত্রের রুমালে কার ছবি আঁকা ছিল?
(ক) বাঘ
(খ) সিংহ
(গ) রামধনু
(ঘ) ফুল-এর
উত্তর: (ক) বাঘ
১.২ নদেরচাঁদ কাকে কেবল বোঝাতে পারে না?
(ক) অন্যকে
(খ) ছোটোদের
(গ) বড়োদের
(ঘ) নিজেকে
উত্তর: (ঘ) নিজেকে
১.৩ ‘দুজনের গায়েই সেদিনকার তৈরি নতুন জামা।’ দিনটি হল
(ক) হোলির দিন
(খ) জন্মদিন
(গ) বর্ষার দিন
(ঘ) পুজোর দিন
উত্তর: (ক) হোলির দিন
১.৪ “আমাদের পথ নেই আর।” ‘পথ’ শব্দটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে
(ক) দু’বার
(খ) তিনবার
(গ) একবার
(ঘ) চারবার
উত্তর: (ক) দু’বার
১.৫ আফ্রিকার অন্তঃপুরে আলো ছিল
(ক) কৃপণ
(খ) দুর্বল
(গ) আবিল
(ঘ) নগ্ন
উত্তর: (ক) কৃপণ
১.৬ কোটি জয় গোস্বামীর লেখা কাব্যগ্রন্থ?
(ক) ‘বাবরের প্রার্থনা’
(খ) ‘অগ্নিবীণা’
(গ) ‘রূপসী বাংলা’
(ঘ) ‘পাতার পোশাক’
উত্তর: (ঘ) ‘পাতার পোশাক’
১.৭ ‘আমরা কলম তৈরি করতাম’ কী দিয়ে?
(ক) বাঁশের কঞ্চি
(খ) টিনের পাত
(গ) ফাইবারের স্টিক
(ঘ) নিমের ডাল
উত্তর: (ক) বাঁশের কঞ্চি
১.৮ বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে যে অলংকার চলতে পারে-
(ক) উপমা ও রূপক
(খ) উৎপ্রেক্ষা
(গ) অতিশয়োক্তি
(ঘ) যমক ও সমাসোক্তি।
উত্তর: (ক) উপমা ও রূপক
১.৯ অলংকারের প্রয়োগ কম থাকা ভালো
(ক) সংস্কৃত সাহিত্যে
(খ) সাধারণ সাহিত্যে
(গ) অনুবাদ সাহিত্যে
(ঘ) বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে
উত্তর: (ঘ) বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে
১.১০ বাংলা ব্যাকরণে অ-কারক পদের সংখ্যা হল
(ক) ১টি
(খ) ২টি
(গ) ৩টি
(ঘ) ৪টি
উত্তর: (খ) ২টি
১.১১ দুগ্গা একটা পান সেজে দে তো। নিম্নরেখ পদটি হল
(ক) কর্তৃকারক
(খ) সম্বোধন পদ
(গ) কর্মকারক
(ঘ) সম্বন্ধপদ
উত্তর: (খ) সম্বোধন পদ
১.১২ ‘সমাস’ শব্দের অর্থ
(ক) সংক্ষেপ
(খ) মিলন
(গ) বিস্তার
(ঘ) সন্ধি
উত্তর: (ক) সংক্ষেপ
১.১৩ জায়া ও পতি- দম্পতি এটি যে সমাসের উদাহরণ
(ক) দ্বন্দু সমাস
(খ) তৎপুরুষ সমাস
(গ) কর্মধারয় সমাস
(ঘ) বহুব্রীহি সমাস
উত্তর: (ক) দ্বন্দু সমাস
১.১৪ কোটি বাক্য নির্মাণের আবশ্যিক শর্ত?
(ক) যোগ্যতা
(খ) আসত্তি
(গ) আকাঙ্ক্ষা
(ঘ) সবকটিই
উত্তর: (ঘ) সবকটিই
১.১৫ পিকু ভাত খায়। বাক্যটির ‘ভাত খায়’ অংশটি হল
(ক) বিধেয়
(খ) উদ্দেশ্য
(গ) নামপদ
(ঘ) কোনোটিই নয়
উত্তর: (ক) বিধেয়
১.১৬ ‘ক্রিয়ার ভাব’ প্রাধান্য পায় যে বাচ্যে তা হল
(ক) কর্মবাচ্য
(খ) কর্তৃবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (গ) ভাববাচ্য
১.১৭ ‘ফুরফুর করে বাতাস বইছে।’ এটি কোন্ বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্তৃবাচ্য
(খ) কর্মবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (ক) কর্তৃবাচ্য
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ চুরির সময় তেওয়ারি কোথায় ছিল?
উত্তর: চুরির সময় তেওয়ারি ফয়ায় ছিল।
২.১.২ ‘হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে,’ কোন্ কথা মনে হয়েছে?
উত্তর: “হঠাৎ তার মনে হলো—রোষে, ক্ষোভে উন্মত্ত এই নদীর আর্তনাদময় জলরাশি যখন কয়েক হাত উঁচুতে উঠেছে, তখন এতক্ষণ এত নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকা মোটেই ঠিক হয়নি।”
২.১.৩ ‘আমার সঙ্গে আয়।’ অমৃত ইসাবকে এমন নির্দেশ দিল কেন?
উত্তর: ‘আমার সঙ্গে আয়।’ অমৃত ইসাবকে এমন নির্দেশ দিল কারণ ইসাবের ছেঁরা জামার সাথে নিজে্র জামাটা পরিবর্তন করাবে।
২.১.৪ তপনের লেখা গল্পের বিষয়বস্তু কী ছিল?
উত্তর: তপনের লেখা গল্পের বিষয়বস্তু সাধারণত তার অভিজ্ঞতা, সমাজের বিভিন্ন দিক এবং মানবিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।
২.১.৫ কোন্ সাজে হরিদার রোজগার সর্বাধিক হয়েছিল।
উত্তর: বাইজির ছদ্মবেশে হরিদার রোজগার সর্বাধিক হয়েছিল।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ ‘ভগবতি’র অপর নাম কী?
উত্তর: ভগবতীর অপর নাম লক্ষ্মী।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘ অভিষেক’ কবিতায় পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে।
২.২.২ ‘ওই আসে সুন্দর।’ সুন্দর কীভাবে আসে?
উত্তর: “অন্ধত্ব ও গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ সমাজকে ধ্বংস করে নব সৃষ্টি ঘটানোর জন্যই সুন্দর আসে ভয়ংকর বেশে।”
২.২.৩ ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতায় যে দুই নারীকে ‘কন্যা’ বলা হয়েছে, সে দুই কন্যা কে কে?
উত্তর: সৈয়দ আলাওলের ‘ পদ্মাবতী ‘ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘ ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতায় যে দুই নারীকে ‘কন্যা’ বলা হয়েছে, সে দুই নারী হলেন–
১- চিতোররাজ রত্নসেনের দ্বিতীয়া স্ত্রী পদ্মাবতী
২- সমুদ্ররাজের কন্যা পদ্মা ।
২.২.৪ কবি জয় গোস্বামীর ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় কোন্ কোন্ পাখির নাম রয়েছে?
উত্তর: কবি জয় গোস্বামীর ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায়— শকুন, চিল, ময়ূর, কোকিল পাখির নাম রয়েছে
২.২.৫ “উল্টে পড়ল মন্দির থেকে”
কেমনভাবে উলটে পড়ল?
উত্তর: উল্টে পড়ল মন্দির থেকে– টুকরো টুকরো হয়ে মন্দির থেকে উলটে পড়ল।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ কালি তৈরি সম্পর্কে প্রাচীনদের উপদেশটি কী ছিল?
উত্তর: কালি তৈরি সম্পর্কে প্রাচীনদের উপদেশটি ছিল—
তিল, ত্রিফলা আর শিমুল ছাল ছাগলের দুধে ফেলে লোহার পাত্রে রেখে অন্য একটি লোহার খুন্তি দিয়ে উপকরণগুলি ঘষে কালি বানানো।
২.৩.২ ‘মাছিমারা নকল’ বিষয়টি কী?
উত্তর: When the Sulpher burns in air the Nitrogen does not take part is the reactiori, কথায় ‘মাছিমারা’ নকলটি হল- যখন গন্ধক পোড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়ায় আশগ্রহণ করে না।
২.৩.৩ ‘গুটিকতক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ হয়তো তারা শিখেছে,’ শব্দগুলি কী কী?
উত্তর: ‘গুটিকতক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ হয়তো তারা শিখেছে,’ শব্দগুলি— টাইফয়েড, আয়োডিন মোটর, ক্রোটন, জেব্রা।
২.৩.৪ ‘কলম সেদিন খুনিও হতে পারে বইকী।’ বক্তব্যটি স্পষ্ট করো।
উত্তর: ‘কলম সেদিন খুনিও হতে পারে বইকী।’ বক্তব্যটি হলো– খ্রিস্টের জন্মের আগে রোমের অধীশ্বর জুলিয়াস সিজার ব্রোঞ্চের কলম দিয়ে কাসকাকে আঘাত করেছিলেন ।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ নিম্নরেখ শব্দটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো “তার আমি জামিন হতে পারি।”
উত্তর: আমি” হল কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি এবং “জামিন” হল কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি
২.৪.২ একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ দাও।
উত্তর: একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ— আমি রাহুলকে একটি বই দিলাম।
২.৪.৩ দুটি সমার্থক পদ দিয়ে তৈরি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ দাও।
উত্তর: দুটি সমার্থক পদ দিয়ে তৈরি দ্বন্দু সমাসের উদাহরণ – দুঃখ-কষ্ট, শোক-বেদনা।
২.৪.৪ উপমেয় পদ বলতে কী বোঝো?
উত্তর: উপমেয় পদ বলতে এমন পদকে বোঝায় যে ব্যক্তি বা বস্তুকে অপর ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়।
২.৪.৫ বাক্যের আকাঙ্ক্ষা বলতে কী বোঝো?
উত্তর: আকাঙ্ক্ষা হলো বাক্যের এমন একটি ধর্ম, যার দ্বারা বাক্যের একটি পদ অন্য পদকে প্রত্যাশা করে বা চায়।
২.৪.৬ উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক বলতে কী বোঝো?
উত্তর: যে পদ বা পদাংশ বাক্যের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে বা সেই উদ্দেশ্যকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে, তাকে উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক বলে।
২.৪.৭ কর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্যের মূল পার্থক্য কী?
উত্তর: “কর্তৃবাচ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কর্তা (subject) প্রধান এবং ভাববাচ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কর্ম (object) প্রধান।”
২.৪.৮ এ সমস্তই তার জানা। (কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করো)
উত্তর: কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর— “সে এ সমস্তই জানে।”
২.৪.৯ ‘সমূলে নির্মূল করিব পামরে আজি।’ কর্মবাচ্যে পরিণত করো।
উত্তর: কর্মবাচ্য: পামর নির্মূল হইবে আমাদের দ্বারা
২.৪.১০ ‘রথকে দেখা’ সমাস নির্ণয় করো।
উত্তর: ‘রথকে দেখা’— দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
৩। প্রসজ্ঞা নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ “নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে।” কে বুঝতে পেরেছে? ‘নদীর বিদ্রোহ’ বলতে সে কী বোঝাতে চেয়েছে?
উত্তর: নদীর বিদ্রোহের কারণ নদেরচাঁদের বুঝতে পেরেছিলো।
এই ছোটগল্পে লেখক শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নদীকে প্রকৃতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতি স্বতন্ত্র, সে কোনো গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে চায় না। গল্প থেকে আমরা জানতে পারি যে, সঙ্কীর্ণ ও ক্ষীণস্রোতা নদী মানুষের সভ্যতার প্রতীক—ব্রিজ দ্বারা আবদ্ধ হয়েছে।
কিন্তু শুকনো নদী পাঁচ দিনের বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। উন্মত্ত নদীর তীব্র স্রোতযুক্ত জলধারা, স্বাভাবিক চরিত্র ফিরে পেয়েছে,
উন্মত্ত নদীর তীব্র স্রোতযুক্ত জলধারা এই রূপকেই দেখে গল্পের চরিত্র নদেরচাঁদ নদীর বিদ্রোহ বলে মনে করেছে।
৩.১.২ ‘যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।’ বস্তা কে? উদ্ধৃতাংশটির কারণ আলোচনা করো।
উত্তর: ‘যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই, উক্তিটির বক্তা অপূর্ব।
এই কথা বলার কারণ হলো একদিন কয়েকজন ফিরিঙ্গি ছেলে অপূর্বকে লাথি মেরে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বের করে দেয়। অপূর্ব প্রতিবাদ করলে স্টেশনমাস্টার তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। প্ল্যাটফর্ম থাকা হিন্দুস্থানের লোক প্রতিবাদ করতে আসেনি এই চরম অপমান।
তারা কেবল এই ভেবে খুশি হয়েছিল যে অপূর্বর হাড়-পাঁজর ভাঙেনি। কিন্তু অপূর্বর যে অপমান করা হয়েছে—তা ছিল দেশেরও অপমান। আর এই অপমান কারও মনে আঘাত না দেওয়াতেই অপূর্ব এই উক্তিটি করেছিলেন।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “সে জানত না আমি আর কখনো ফিরে আসব না।” ‘সে’ কে? ‘আমি আর কখনো ফিরে আসব না’ বলার কারণ কী?
উত্তর: পাবলো নেরুদা রচিত, নবারুণ ভট্টাচার্য অনূদিত ‘অসুখী একজন’ কবিতায় ‘সে’ বলতে বোঝানো হয়েছে প্রতীক্ষায় থাকা মেয়েটিকে। কবি কথক কর্তব্যের টানে স্বদেশ ও আপনজনদের ছেড়ে সুদূরে পাড়ি জমিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও আর তাঁর দেশে ফেরা হয়নি। এই না ফেরা হয়ে ওঠে কবির জীবনের করুণ নিয়তি। কিন্তু মেয়েটি কিছুই জানত না, সে ভেবেছিল প্রিয়জন একদিন ফিরে আসবেন। তাই বছরের পর বছর সে দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে। কবি আসলে জানতেন তিনি আর কোনোদিন ফিরবেন না, তাই কবিতায় বলেছেন— “আমি আর কখনো ফিরে আসব না।”
৩.২.২ ‘বিধি মোরে না কর নৈরাশ।।’ কার প্রার্থনা? এমন প্রার্থনার কারণ কী?
উত্তর: ‘বিধি মোরে না কর নৈরাশ।।’ উল্লিখিত প্রার্থনাটি করেছেন সমুদ্রকন্যা পদ্মা।
এমন প্রার্থনার কারণ, সমুদ্রতীরে মান্দাসের উপর অচৈতন্য অবস্থায় এক অপরূপ সুন্দরী নারীকে পড়ে থাকতে দেখে পদ্মা গভীর উদ্বেগে পড়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন, কোনো ভয়াবহ সামুদ্রিক বিপর্যয়েই ওই নারীর এই অবস্থা হয়েছে। প্রতিমার মতো সেই নারীর শ্বাস চলছিল সামান্য। কন্যাটির প্রতি স্নেহানুভূতিতে উদ্বেল হয়ে পদ্মা প্রার্থনা করেন, যেন বিধাতা তাঁকে নিরাশ না করেন ও সেই কন্যাটিকে জীবন দান করেন।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ ‘কিন্তু আমাকে বাঁচানোর জন্য তো আমার মা আছে।’ কে, কাকে উক্তিটি করেছে? উক্তিটির মাধ্যমে বস্তার চরিত্রের কোন্ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে?
উত্তর: পান্নালাল প্যাটেল রচিত ‘অদল বদল’ গল্পে উক্তিটি অমৃত’ মাহারা ইসাবকে বলেছে।
এই উক্তির মাধ্যমে অমৃতের চরিত্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ পায়— তার মায়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। অমৃত জানে, দরিদ্র পরিবারের ছেলে হয়ে নতুন জামা ছিঁড়ে ফেলা বড় অপরাধ হলেও, তার মা সবসময় তার রক্ষাকর্ত্রী হয়ে থাকেন। বাবার মারমুখী রোষ থেকে মায়ের স্নেহই তাকে রক্ষা করে। কিন্তু ইসাবের তো এমন মায়ের স্নেহ নেই— এই বোধ থেকেই অমৃত তাকে রক্ষা করতে চেয়েছে। এই উক্তির মাধ্যমে অমৃতের সংবেদনশীলতা, দরদি মন এবং অমৃতের বন্ধুত্বের খাঁটি রূপ, প্রেম, বন্ধুত্ব পরিচয়ও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।
৪.২ “এই শহরের জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করেন বহুরূপী হরিদা।” হরিদা সৃষ্ট চমৎকার ঘটনাগুলির বিবরণ দাও।
উত্তর: সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদা তাঁর অভিনব বেশভূষা ও বৈচিত্র্যময় আচরণের মাধ্যমে শহরের জীবনে মাঝে মাঝেই চমৎকার সব ঘটনা সৃষ্টি করতেন। তাঁর জীবন ছিল এক নাট্যশালার মতো, সেখানে এক নতুন চরিত্রে আবির্ভাব হতো।
হরিদা সপ্তাহে বড়জোর একদিন বহুরূপী সেজে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করতেন। অধিকাংশ দিন না খেয়েও তিনি একঘেয়ে পেশা গ্রহণ না করে বেছে নিয়েছিলেন রঙিন, নাটকীয় জীবনের পথ। তাঁর সৃষ্ট কিছু উল্লেখযোগ্য চমৎকার ঘটনার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:
১. পাগলের সাজে আতঙ্ক সৃষ্টি: একদিন দুপুরে হরিদা উন্মাদ পাগলের বেশে চকের বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে মুখে লালা ছিটিয়ে, হাতে ইট তুলে যাত্রীদের দিকে তেড়ে গিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন।
২. বাইজির সাজে রাজপথে আগমন: এক সন্ধ্যায় ঠোঁটে রঙ, পায়ে ঘুঙুর পরে বাইজির সাজে নেমে নৃত্যভঙ্গিতে শহরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
৩. নকল পুলিশ হয়ে শাস্তি প্রদান: একবার পুলিশ সেজে চারজন স্কুলছাত্রকে লিচু চুরির অপরাধে আটক করেন এবং পরে এক শিক্ষক ঘুষ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনেন।
৪. সন্ন্যাসীর বেশে দার্শনিক উপদেশ: হরিদা একদিন সন্ন্যাসীর সাজে জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ধর্ম ও জীবনের বিষয়ে গভীর দার্শনিক উপদেশ দেন।
৫. বিভিন্ন রূপে আবির্ভাব: কখনও কাপালিক, কখনও কাবুলিওয়ালা, কখনও ফিরিঙ্গি সাহেব, আবার কখনও বাউলের রূপ ধারণ করে পথচলতি মানুষকে চমকে দিতেন।
এইসব বিচিত্র রূপসজ্জা ও অভিনয়ের মাধ্যমে হরিদা নিছক রুজির জন্য নয়, বরং শিল্পের প্রতি ভালোবাসা ও জীবনকে আনন্দময় করে তোলার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ “আমাদের পথ নেই কোনো” ‘আমাদের’ বলতে কবি কাদের বুঝিয়েছেন? তাদের পথ নেই কেন? তাদের সামনে কোন্ পথের সন্ধান কবি দিয়েছেন?
উত্তর: ‘আমাদের’ বলতে কবি কাদের বুঝিয়েছেন:
কবি শঙ্খ ঘোষ ‘আমাদের’ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর নিপীড়িত, ক্ষতিগ্রস্ত, শ্রমজীবী, শান্তিকামী ও অসহায় সাধারণ মানুষদের। এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশের জনগণ নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর শোষিত মানুষের প্রতীক।
তাদের পথ নেই কেন:
এখানে ‘পথ’ বলতে বোঝানো হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনের চলার পথকে। সুন্দর সমাজ ও নিরাপদ পৃথিবীই পারে এই পথকে মসৃণ করতে। কিন্তু আজকের বিশ্ব রাজনীতির নিষ্ঠুরতা, যুদ্ধ, দমন-পীড়ন এবং দারিদ্র্য সেই পথকে করে তুলেছে অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক। ফলে এইসব সাধারণ মানুষ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে; এমনকি নিজেরাই অস্তিত্বের সংকটে। তাই তারা নিজেদের পথহারা বলে মনে করছে।
তাদের সামনে কোন্ পথের সন্ধান কবি দিয়েছেন:
কবি শঙ্খ ঘোষ মানুষের মনের মধ্যে আশার আলো জ্বালাতে চেয়েছেন। তিনি এই পথহারা মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন—“আরো বেঁধে বেঁধে থাকি”। তাঁর বিশ্বাস, যতই কম মানুষ থাকি না কেন, যদি সকলে মিলিত, সংঘবদ্ধ ও বিশ্বাসভিত্তিক হয়ে একজোট হই, তবে অবশ্যই সামনে একটি নতুন পথের দুয়ার খুলে যাবে। এই পথই হবে মুক্তি ও প্রতিবাদের পথ।
৫.২ “প্রলয় বয়েও আসছে হেসে— /মধুর হেসে।” কে আসছেন? তার হাসির কারণ বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: উদ্ধৃত অংশটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতা থেকে গৃহীত। এখানে কবি বলেছেন— “প্রলয় বয়েও আসছে হেসে— / মধুর হেসে।”
এই উদ্ধৃতাংশে ‘কে আসছেন?’ — কবি বুঝিয়েছেন —অসুন্দরের অবসান ঘটাতে একদল নবীন, শক্তিশালী, বলিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবকদের। তারা যেন মহাকাল বা শিবের মতো প্রলয়স্বরূপ এক অসামান্য শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।
এই তরুণরা পরাধীন ভারতবর্ষের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অসুন্দর, অবক্ষয় ও শোষণের অবসান ঘটাতে আসছে। কবির মতে, পূর্ববর্তী প্রাচীনপন্থী সংগ্রামের ধারায় সাফল্য আসেনি, তাই এই নবপ্রজন্ম ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে সমস্ত অসুন্দরের বিনাশ ঘটিয়ে নতুন এক সুন্দরের পৃথিবী গড়তে।
তাদের মুখে ফুটে ওঠা ‘মধুর হাসি’-র তাৎপর্য হল— ধ্বংসের মধ্যেই তারা সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে। তাদের প্রলয়ানন্দ বা ধ্বংসের আনন্দ কবির কাছে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার এক শুভবার্তা। এই হাসি শুধু বিজয়ের প্রকাশ নয়, বরং এক নবযুগ গঠনের প্রত্যয়ও।
সারাংশ:
এই উদ্ধৃতিতে কবি এমন এক দল তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা বলেছেন, যারা প্রলয়ের মাধ্যমে অসুন্দর সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে মধুর হাসিতে নবজাগরণের সূচনা করতে চলেছে।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ ‘কলম এখন সর্বজনীন।’ লেখকের এই মন্তব্যের কারণ বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: ‘হারিয়ে যাওয়া কালি-কলম’ প্রবন্ধে লেখক শ্রীপান্থ কলমের বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থাপন করেছেন। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কঞ্চির কলম, পালকের কলম, নিবের কলম, ঝরনা কলম থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের ডট পেন পর্যন্ত কলমের রূপান্তর ঘটেছে। এই বিবর্তনের ফলে লেখালেখি যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি নানা ধরনের কলমও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে।
শিক্ষার প্রসার এবং বিভিন্ন পেশার চাহিদায় কলমের ব্যবহার বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সময় পণ্ডিত বা দার্শনিকের পরিচায়ক ছিল কানে গুঁজে রাখা কলম। কিন্তু বর্তমান যুগে কলম কারো একার সম্পত্তি নয়— অল্পশিক্ষিত থেকে শুরু করে শিক্ষিত, সকলেরই নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ হয়ে উঠেছে এটি।
ফলে কলম যেমন চাহিদাসম্পন্ন, তেমনি সহজলভ্য। ট্রাম, বাসে কলম বিক্রেতা দেখা যায়। লেখক রসিক ভঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন, কলম এখন এতটাই সস্তা ও সহজলভ্য যে পকেটমাররাও আর এটি চুরি করতে উৎসাহ পায় না।
বর্তমানে কলম শুধু বুক পকেটে নয়, জায়গা করে নিয়েছে পায়ের মোজা বা চুলের খোপাতেও। বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রযুক্তির প্রভাবে কলমের গঠন, রূপ ও উৎপাদনে বিপ্লব ঘটেছে। এভাবেই কলম সর্বজনীন রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।
৬.২ ‘এতে রচনা উৎকট হয়।’ কার লেখা, কোন্ রচনার অন্তর্গত লাইনটি? কোন কারণে রচনা উৎকট হয়? এর প্রতিকার কী?
উত্তর: ‘এতে রচনা উৎকট হয়।’ — এই লাইনটি রাজশেখর বসু রচিত ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধের অন্তর্গত।
কারণ:
রাজশেখর বসুর মতে, বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনার সময় অনেক লেখক প্রথমে ইংরেজিতে ভাবেন, তারপর তার হুবহু অনুবাদ বাংলায় করতে যান। এতে রচনার ভাষা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে এবং পাঠকবোধে অসহজ লাগে। ফলে রচনা উৎকট হয়ে ওঠে।
প্রতিকার:
এই সমস্যার সমাধানে লেখকদের উচিত, বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ধারা ও রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচনা করা। বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুযায়ী বিজ্ঞান রচনার সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারলেই রচনার উৎকটতা দূর হবে।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ ‘পলাশি, রাক্ষসী পলাশি!’বক্তা কে? পলাশির প্রান্তরকে তিনি রাক্ষসী বলেছেন কেন?
উত্তর: সিরাজদ্দৌলা নাট্যাংশে ‘পলাশি, রাক্ষসী পলাশি!’ — উক্তিটির বক্তা নবাব সিরাজদ্দৌলা।
তিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতা, মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইংরেজ কোম্পানির সেনারা আগমন করেছে — এই খবর পেয়ে তিনি তা বাংলার জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করেন। তাই সভাসদদের প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাদের পাঠান পলাশীর প্রান্তরে, যেখানে ইংরেজদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ হবে।
সিরাজদ্দৌলা কল্পনা করেন, পলাশীর প্রান্তরে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে, এবং সেই যুদ্ধে রক্তের বন্যা বইবে। তাই রক্ততৃষ্ণায় উন্মত্ত ও নৃশংস এক রাক্ষসীর সঙ্গে তিনি পলাশীর প্রান্তরের তুলনা করেন। তাঁর মনে হয়েছে, পলাশি যেন আবার রক্তিম হয়ে উঠতে চায়। এজন্যই তিনি আবেগভরে উচ্চারণ করেন — ‘পলাশি, রাক্ষসী পলাশি!’।
৭.২ ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।
উত্তর: সিকান্দার আবু জাফরের ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকটি নামকরণের দিক থেকে যেমন যথার্থ, তেমনি তা নাটকের অন্তর্নিহিত বক্তব্য ও সাহিত্যিক উদ্দেশ্যকে অসাধারণভাবে প্রকাশ করে। সাহিত্যে নামকরণে দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়—প্রথমত, এর ব্যবহারিক দিক বা পরিচিতি; দ্বিতীয়ত, রচনার মূল বক্তব্য ও তাৎপর্য। এ দিক থেকে বিচার করলে ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নামটি নাটকটির জন্য একেবারেই সার্থক।
নামহীন কোনো কিছুর অস্তিত্ব যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি একটি নাটককেও তার নামের মাধ্যমেই চিহ্নিত ও পৃথক করা যায়। ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নামটি নাটকটিকে অন্য নাটক থেকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে যেমন ‘রক্তকরবী’, ‘ডাকঘর’, ‘নীলদর্পণ’ ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয়েছে।
এ নাটকের প্রধান উপজীব্য চরিত্র হলেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। ইতিহাসে ইংরেজ ও তাদের পোষ্য ঐতিহাসিকেরা সিরাজকে দুর্বল ও আবেগপ্রবণ রূপে চিত্রিত করলেও সিকান্দার আবু জাফর তাকে দেখিয়েছেন একজন সাহসী, প্রজাবৎসল, স্বাধীনচেতা ও আদর্শবান শাসক হিসেবে। নাট্যকারের ভাষায়—
“প্রকৃত ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজ-উ-দ্দৌলার জীবনাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি।”
নাটকের ১২টি দৃশ্যের মধ্যে ৮টিতেই সিরাজের সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। নাটকের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র সিরাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। তাঁর স্বাধীনতাপ্রেম, আত্মমর্যাদা ও সংগ্রামী মনোভঙ্গিই নাটকের মূল প্রেরণা।
এ ছাড়া, সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যচেতনার মূল উৎস ছিল জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবোধের অনুসন্ধান। সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকটি রচিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে, যখন পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রচরিত্রের বিরুদ্ধে বাঙালির আত্মপরিচয়ের নবজাগরণ ঘটছিল। সে সময়ে সিরাজ-উ-দ্দৌলার মতো স্বজাতি ও স্বাধীনতাপ্রেমী নৃপতির কাহিনি এক গভীর তাৎপর্য বহন করত।
‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ ছাড়াও নাটকটির নাম ‘পলাশীর প্রান্তর’, ‘স্বদেশ প্রেম’ কিংবা ‘মীর জাফর’ হতে পারত, কিন্তু নাট্যের গভীরতা ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের গুরুত্ব বিচার করলে ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নামটিই সবচেয়ে যথার্থ।
অতএব, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও নাট্যকারের চেতনা—সব দিক থেকেই ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নামকরণ সার্থক, যুক্তিযুক্ত এবং যথেষ্ট নান্দনিক।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ “এটা বুকের মধ্যে পুষে রাখুক।” কী পুষে রাখার কথা বলা হয়েছে? কী কারণে এই পুষে রাখা?
উত্তর: মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসে ক্ষিতীশ সিংহ একদিন কোনিকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে যান। সেখানে তারা তিন ঘণ্টা ধরে ঘোরাঘুরি করার পর বাড়ি থেকে আনা খাবার খেতে বসেন। কিন্তু খাবারের সঙ্গে জল না থাকায় কোনি তাদের পাশেই বসে থাকা একদল ছাত্রীদের কাছে জল চাইতে যায়। ছাত্রীদের একজন দিদিমণি কোনিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে জল দিতে অস্বীকার করেন। পরে, সেই দলের একজন হিয়া মিত্র নামে একটি মেয়ে কোনিকে জল দিতে এগিয়ে আসে ,কোনি সেই জলের গ্লাস ফেলে দেয়।
এই আচরণ ছিল কোনির মানসিক প্রতিক্রিয়া, কারণ সে জল চেয়ে অপমানিত হয়েছিল। সেই অপমান কোনি সহজে ভুলতে পারেনি। হিয়ার প্রতি কোনির আক্রোশের প্রকাশ ঘটে গ্লাসটি ফেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। ক্ষিতীশ সিংহ তখন কোনিকে বলেন, রাগ মনের মধ্যে পুষে রাখতে।
কোনি হিয়াকে না চিনলেও, ক্ষিতীশ সিংহ হিয়াকে চিনতেন এবং জানতেন সে সাঁতারে অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি রবীন্দ্র সরোবরে হিয়ার সাঁতার দেখেছেন এবং বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবে গিয়ে তার প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি মনে করতেন, হিয়া মিত্র কোনির তুলনায় অনেক এগিয়ে এবং হিয়া মিত্রই ভবিষ্যতে তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হবে তাই, ক্ষিতীশ সিংহ চেয়েছিলেন সেই অপমান যেন কোনির মধ্যে থেকে যায়। কারণ সেই অপমানই তাকে অনুপ্রাণিত করবে পরিশ্রম করতে এবং একদিন হিয়াকে হারিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে।
এইভাবেই ক্ষিতীশ সিংহ কোনির মনে প্রতিযোগিতার জেদ জাগিয়ে তুলে তাকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন।
৮.২ ‘পুঁতে রাখব তোকে এই গঙ্গামাটিতে।’ কে, কাকে একথা বলেছে? তার এমন কথা বলার কারণ কী?
উত্তর: ‘পুঁতে রাখব তোকে এই গঙ্গামাটিতে।’ – কথাটি মতি নন্দী রচিত কোনি উপন্যাসে প্রধান চরিত্র কোনি বলেছিল ভাদুকে।
কোনির এমন কথা বলার কারণ— বারুণী উৎসবের দিনে গঙ্গায় আম ধরাকে কেন্দ্র করে কোনি ও ভাদুর মধ্যে মারামারি লেগে যায়। আম ধরার সময় কোনির হাতে আমটি ঠিক আসার আগে ভাদু কোনির পা টেনে তাকে ডুবিয়ে দেয়। পরে কাদার উপর মারপিট শুরু হয়। কাদায় পড়ে যায় দু-জনেই। তখনি কোনির পিঠের ওপর বসে যায়্ ভাদু।
পিঠের ওপর বসে কোনির চুল ধরে ভাদু। দলের ছেলেরা বলে ওঠে
অ্যাই অ্যাই ভাদু, চুল টানবি না কোনির। তাহলে কিন্তু আমরা আর চুপ করে থাকব না।”
কোনির পিঠের ওপর বসা ভাদু চুল ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে কোনির মাথা ধরে, কাদায় মুখটা ঘষে দেবার চেষ্টা করে। কোনি পা ছুড়ে এবং কোমরে চাড় দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে । তারপর ঝটকা দিয়ে ভাদুর ডান হাতটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে এসে কামড়ে ধরে দুটো আঙুল। চিৎকার করে ভাদু লাফিয়ে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে কোনি উঠে দাঁড়িয়ে ভাদুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং বলে “খুবলে নোব তোর চোখ, বার কর আম। আমাকে চোবানো! পুঁতে রাখব তোকে এই গঙ্গামাটিতে। হয় আম দিবি নয় চোখ নোব।”
৮.৩ ‘তবে একবার কখনো যদি জলে পাই…’ কোন প্রসঙ্গে কার এই উক্তি? এখানে জলে পাওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: উক্তিটি নেওয়া হয়েছে সাহিত্যিক মতি নন্দীর লেখা ‘কোনি’ উপন্যাস থেকে। এই উক্তিটি করেছেন উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কোনি, এবং উক্তিটি হিয়া নামক অন্য এক সাঁতারুর উদ্দেশ্যে বলা।
প্রসঙ্গ:
কোনি একজন মেধাবী কিন্তু দরিদ্র ঘরের মেয়ে। সে ক্ষিতীশ সিংহের তত্ত্বাবধানে সাঁতার শেখে। জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধি দল হিসেবে মাদ্রাজে গেলে, ধনী ঘরের মেয়েরা, বিশেষত হিয়া, কোনিকে তাচ্ছিল্য করে। তারা তার পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক অবস্থান দেখে তাকে হীন চোখে দেখে এবং যোগ্যতাকে অবহেলা করে। এমনকি কোনির ওপর চুরির অপবাদ দেওয়া হয় এবং তাকে চরও মারা হয়।
এই পরিস্থিতিতে অপমানিত কোনি মুখ বুঝে সব সহ্য করে। তবে সে জানে, জলে অর্থাৎ সাঁতারের প্রতিযোগিতায় ধনী-দরিদ্রের কোনো ভেদাভেদ চলে না। সেখানে বিচার হয় কেবল দক্ষতার। তাই কোনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বলে—
‘তবে একবার কখনো যদি জলে পাই’, অর্থাৎ সাঁতারের আসল প্রতিযোগিতায় যদি একবার হিয়ার মুখোমুখি হতে পারে, তবে সে প্রমাণ করে দেবে কে বড়ো আর কে ছোটো।
‘জলে পাওয়া’ বলতে বোঝানো হয়েছে সাঁতারের প্রতিযোগিতায় নেমে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। এটি প্রতীকী অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে— যেখানে কোনি বিশ্বাস করে, প্রকৃত মেধা ও পরিশ্রমই জয়ী হবে, সামাজিক অবস্থান নয়।
৯। চলিত গদ্যে শুঙ্গানুবাদ করো:
Once a father whose son had fallen in evil company gave him a basket of good mangoes with one bad in it. Next day the good mangoes were found rotten. The man told the boy that the bad mango had spoilt the good ones. He added that bad company likewise made good boys bad.
উত্তর: একবার এক বাবা, যার ছেলে খারাপ সঙ্গের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, তাকে একটি পাকা আমের ঝুড়ি দিলেন—সেই ঝুড়িতে একটি পচা আমও ছিল। পরের দিন দেখা গেল সব ভালো আম পচে গেছে। তখন সেই ব্যক্তি ছেলেকে বললেন, দেখলে, ওই একটা পচা আম বাকি ভালোগুলোও নষ্ট করে ফেলেছে। তিনি আরও বললেন, “ঠিক তেমনি খারাপ সঙ্গও ভালো ছেলেদের খারাপ করে তোলে।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ রক্তদানের উপযোগিতা সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষকের কাল্পনিক সংলাপ আলোচনা করো।
উত্তর:
রক্তদানের উপযোগিতা: ছাত্র ও শিক্ষকের কাল্পনিক সংলাপ
ছাত্র: স্যার, রক্তদান সম্পর্কে সবাই এত গুরুত্ব দেয় কেন?
শিক্ষক: খুব ভালো প্রশ্ন। রক্তদান মানবতার এক মহান দৃষ্টান্ত। একজন সুস্থ মানুষ রক্তদানের মাধ্যমে একজন অসুস্থ বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে।
ছাত্র: রক্ত দিলে কি শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে?
শিক্ষক: একেবারেই না। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কয়েক মাস অন্তর নিরাপদে রক্ত দিতে পারে। এতে শরীরে কোনও ক্ষতি হয় না, বরং এটি স্বাস্থ্য ভালো রাখে।
ছাত্র: আমরা ছাত্র হিসেবে কীভাবে এই কাজে অংশ নিতে পারি?
শিক্ষক: প্রথমত সচেতন হতে হবে, তারপর অন্যদের সচেতন করতে হবে। কলেজ বা স্কুলে রক্তদান শিবির আয়োজন করে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা উচিত।
ছাত্র: বুঝলাম স্যার, রক্তদান শুধু একটি দায়িত্ব নয়, এটি আমাদের মানবিক কর্তব্যও।
শিক্ষক: ঠিক বলেছ, এটাই একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয়।
১০.২ জলের অপচয় রোধে সচেতনতা শিবির বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
জলের অপচয় রোধে সচেতনতা শিবির
নিজেস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, জুন ২০২৫: জলের অপচয় রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের আয়োজন করে স্থানীয় পরিবেশবিষয়ক সংস্থা ‘জলবন্ধু’।
শিবিরে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ডঃ অভিজিৎ দে। তিনি জলের গুরুত্ব, ভবিষ্যৎ জলের সংকট এবং দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে আমরা সচেতনভাবে জল ব্যবহার করতে পারি, সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।
শিবিরে পোস্টার প্রদর্শনী, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও একটি সংক্ষিপ্ত নাটিকার মাধ্যমে জলের অপচয়ের কুফল তুলে ধরা হয়।
এই শিবিরের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জলের সঠিক ব্যবহার ও অপচয় রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত হলে সমাজ উপকৃত হবে।
১১। যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লেখো: (কমভেশি ৪০০ শব্দে)
১১.১ প্রকৃতির আশীর্বাদ ও অভিশাপ।
উত্তর:
প্রকৃতির আশীর্বাদ ও অভিশাপ
প্রকৃতি মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার মাঝেই লুকিয়ে আছে জীবনের মূল সুর, আনন্দের উৎস এবং জীবনের ধারক-বাহক উপাদানসমূহ। কিন্তু এই প্রকৃতিই কখনও কখনও রুদ্ররূপ ধারণ করে হয়ে ওঠে মানবজাতির জন্য অভিশাপস্বরূপ। তাই প্রকৃতিকে একদিকে যেমন আশীর্বাদরূপে ধরা যায়, তেমনি অন্যদিকে তা অভিশাপেও পরিণত হতে পারে।
প্রকৃতির আশীর্বাদ অসীম। নদী, পাহাড়, সাগর, বায়ু, বৃক্ষলতা, সূর্যরশ্মি, বৃষ্টি—সবই প্রকৃতির দেওয়া উপহার। এগুলো ছাড়া মানবজীবন এক মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। জমি চাষের জন্য প্রয়োজন বৃষ্টি, খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন উর্বর মাটি, শ্বাসের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ বাতাস, আর প্রাণধারণের জন্য চাই বিশুদ্ধ পানি। গ্রীষ্মে যখন সূর্য প্রখর, তখন হাওয়া ও বৃক্ষের ছায়া আশীর্বাদের মতো কাজ করে। শীতের পর বসন্তের আগমন প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য এবং পুনর্জীবনের বার্তা দেয়।
কিন্তু প্রকৃতি সবসময় মধুর রূপে থাকে না। কখনও কখনও মানুষ যখন প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে, তখন সে রুদ্ররূপ ধারণ করে অভিশাপ হয়ে আসে। ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, ঝড়, সুনামি, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি প্রকৃতির সেই অভিশপ্ত রূপের বহিঃপ্রকাশ। অতিবৃষ্টিতে প্লাবিত হয় গ্রামের পর গ্রাম, প্রাণহানি ঘটে, ফসল নষ্ট হয়। ভূমিকম্পে মুহূর্তে ধ্বংস হয় শহর, ঘরবাড়ি। খরায় মানুষ-পশুপাখি কষ্টে দিন কাটায়। এইসব বিপর্যয় মানবসভ্যতাকে বারবার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়।
প্রকৃতির এই আশীর্বাদ ও অভিশাপের পেছনে অনেকাংশে মানুষের ভূমিকাও রয়েছে। বনভূমি নিধন, অতিরিক্ত কারখানা স্থাপন, নদী ও জলাধার দখল, দূষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে প্রকৃতি তার প্রতিক্রিয়া দেখায়—রুদ্ররূপে ফিরে আসে।
অতএব, প্রকৃতিকে যেন শুধু আশীর্বাদরূপে রাখা যায়, তার জন্য আমাদের দায়িত্বশীল হতে হবে। গাছ লাগাতে হবে, জল ও বায়ুর অপচয় রোধ করতে হবে, পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান বজায় রেখে চললে প্রকৃতি হবে আমাদের চিরকালের বন্ধু ও আশীর্বাদ। তা না হলে তার অভিশাপ আমাদের ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দেবে।
উপসংহার:
প্রকৃতির রূপ দ্বিমুখী—তাতে যেমন আশীর্বাদ আছে, তেমনি অভিশাপও। মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য, প্রকৃতির শুভদিককে ধারণ করা এবং তার রুদ্র রূপকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা। তবেই প্রকৃতি হয়ে উঠবে মানবজাতির চিরন্তন আশীর্বাদ।
১১.২ লকডাউনের একটি দিন।
উত্তর:
লকডাউনের একটি দিন
২০২০ সালের শুরুতেই করোনা মহামারির প্রকোপে বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে পড়ে। সংক্রমণ রোধে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় লকডাউন, অর্থাৎ ঘরবন্দি হয়ে পড়ি আমরা সকলে। লকডাউনের প্রতিটি দিনই এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তবে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে তার প্রথম কটি দিনের একটি।
সেই দিনটির সকালটা ছিল অনেকটা নিরব। পাড়ার কোলাহল, রাস্তার গাড়ির শব্দ—সব যেন হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে। পাখির ডাক, গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি হঠাৎ করেই যেন স্পষ্টভাবে কানে আসতে শুরু করল। ঘুম থেকে উঠে দেখি বাবা, মা, আর বোন সকলে ঘরেই। এই দৃশ্যটি যেমন অস্বাভাবিক, তেমনই আনন্দেরও—সকলেই একসঙ্গে, কাজের তাড়া নেই, স্কুল নেই, অফিস নেই।
প্রাতঃরাশ শেষে মা আমাদের ডেকে বললেন ঘরের জিনিসপত্র একটু গুছিয়ে ফেলতে। আমি বইয়ের তাক গুছোলাম, পুরনো ম্যাগাজিন আর নোট খুঁজে পেলাম যেগুলি দীর্ঘদিন ধুলোয় ঢাকা ছিল। বাবা পুরনো অ্যালবাম খুলে বসে গেলেন, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল স্মৃতিচারণা। সারাদিন কেটে গেল গল্প, রান্না, বই পড়া, ছাদে পায়চারি আর টিভিতে খবর দেখার মধ্যে দিয়ে।
তবে এইদিনের সবচেয়ে বড় উপলব্ধি ছিল—জীবন কতটা অনিশ্চিত! আমরা এতদিন যা স্বাভাবিক বলে ভেবেছি, তা যে কত অস্থায়ী হতে পারে, তা লকডাউনের দিনগুলোতেই উপলব্ধি করি। সেই দিন মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্ববোধ আরও বেড়ে যায়—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, মুখে মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি।
তবে ঘরে বসে থেকেও অনেকে সমাজের জন্য কাজ করেছে। কেউ কেউ পথকুকুরদের খাবার দিয়েছে, কেউ দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি নিজেও অনলাইনে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে একটি ছোট সচেতনতা প্রচার চালিয়েছিলাম, যাতে করে গ্রামে বসবাসকারী মানুষরাও সচেতন হন।
লকডাউনের সেই দিনটি কষ্টের ছিল, কিন্তু এক গভীর শিক্ষার দিনও ছিল। পরিবার, প্রকৃতি এবং নিজেকে জানার এক বিরল সুযোগ এনে দিয়েছিল সেই নিস্তব্ধ, অনিশ্চিত কিন্তু মানবিকতায় ভরা দিনটি।
শেষ কথা: লকডাউনের একটি দিন আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল, জীবনের প্রকৃত মূল্য কী এবং ছোট ছোট মুহূর্তগুলিও কতটা মূল্যবান হতে পারে।
১১.৩ তোমার জীবনের লক্ষ্য।
উত্তর:
আমার জীবনের লক্ষ্য
প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা অত্যন্ত জরুরি। জীবনের লক্ষ্য ছাড়া মানুষ দিশাহীন নৌকার মতো, যা বাতাসের দাপটে কখন কোথায় ভেসে যাবে, বলা যায় না। জীবনের লক্ষ্য মানুষকে সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তার চেষ্টাকে সফলতার রূপ দেয়।
আমার জীবনের লক্ষ্য একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া। ছোটবেলা থেকেই আমি আমার শিক্ষকদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অনুভব করে এসেছি। তাঁদের জ্ঞান, ব্যবহার এবং পাঠদানের ভঙ্গিমা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ধীরে ধীরে আমার মনে হয়েছে, মানুষের মন গঠন এবং ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পেছনে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। সেই থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ভবিষ্যতে একজন সৎ, মেধাবী ও দায়িত্ববান শিক্ষক হব।
শিক্ষকতা শুধু একটি পেশা নয়, এটি একটি ব্রত। একজন প্রকৃত শিক্ষক শুধুমাত্র পাঠ্যবই পড়ান না, তিনি ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনের দিকেও বিশেষ নজর দেন। আমি চাই, আমি এমন একজন শিক্ষক হই, যিনি ছাত্রদের মনে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ জাগিয়ে তুলবেন, তাদের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন। আমি গ্রামবাংলার দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষা সহজলভ্য করতে চাই, যারা নানা প্রতিকূলতার কারণে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে।
আমার এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমি কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করব। নিয়মিত পাঠ্যচর্চা, ভালো ফলাফল এবং শিক্ষক হিসেবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করব। পাশাপাশি মানবিক গুণাবলি যেমন—সহানুভূতি, সহনশীলতা, ভালোবাসা ও ধৈর্য অর্জনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করব।
এই লক্ষ্য আমার জীবনে এক বিশেষ অনুপ্রেরণা। যখনই পড়াশোনায় ক্লান্তি আসে, তখন এই লক্ষ্যই আমাকে আবার উজ্জীবিত করে তোলে। আমি বিশ্বাস করি, যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকা যায়, তবে একদিন সফলতা আসবেই।
সুতরাং, একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া আমার জীবনের লক্ষ্য। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী প্রতিটি দিন সৎভাবে সংগ্রাম করে যাব। একজন শিক্ষক হিসেবে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারলে, আমার জীবন সত্যিই সার্থক হবে।
১১.৪ তোমার প্রিয় দেশনায়ক।
উত্তর:
আমার প্রিয় দেশনায়ক
দেশনায়ক শব্দটি শুনলেই যে মানুষটির মুখ মনে পড়ে, তিনি হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বীর যোদ্ধাই নন, তিনি ছিলেন এক দৃঢ়চেতা, সাহসী, আদর্শবাদী এবং দুরদর্শী নেতা। তাঁর তেজস্বী নেতৃত্ব, অনমনীয় দেশপ্রেম এবং কর্মনিষ্ঠা তাঁকে আমার প্রিয় দেশনায়কে পরিণত করেছে।
নেতাজির জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি, ওড়িশার কটক শহরে। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন একজন বিখ্যাত আইনজীবী। সুভাষচন্দ্র কিশোর বয়স থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ইংরেজ সরকারের ICS (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষায় পাশ করেও তিনি দেশসেবার জন্য চাকরি ত্যাগ করেন। কারণ, তাঁর লক্ষ্য ছিল পরাধীন ভারতকে মুক্ত করা।
তিনি বিশ্বাস করতেন, শুধু অহিংস আন্দোলনে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তাই তিনি ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ গঠন করেন এবং স্লোগান দেন— “তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।” তাঁর এই বলিষ্ঠ আহ্বানে বহু যুবক দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন।
নেতাজি জাতীয় ঐক্যের প্রতীক ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান— সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ফৌজ আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল।
তিনি ছিলেন এক অসাধারণ সংগঠক ও অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তা। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আজও আমাদের প্রেরণা জোগায়। যদিও তাঁর মৃত্যু রহস্যাবৃত, তবুও তিনি বাঙালির হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।
নেতাজি আমার প্রিয় দেশনায়ক, কারণ তিনি কখনও নিজস্ব স্বার্থ দেখেননি। দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, আত্মত্যাগ ছাড়া কোনো বড় কিছু অর্জন সম্ভব নয়।
আজকের তরুণ প্রজন্ম যদি নেতাজির আদর্শকে অনুসরণ করে, তবে একটি উন্নত, আত্মনির্ভর এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়া সম্ভব।
নেতাজির জীবনের আদর্শ ও সংগ্রাম চিরকাল আমার মনে অনুপ্রেরণা জোগাবে। তাঁর নাম শুনলেই গর্বে বুক ভরে ওঠে। তাই নিঃসন্দেহে সুভাষচন্দ্র বসুই আমার প্রিয় দেশনায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।