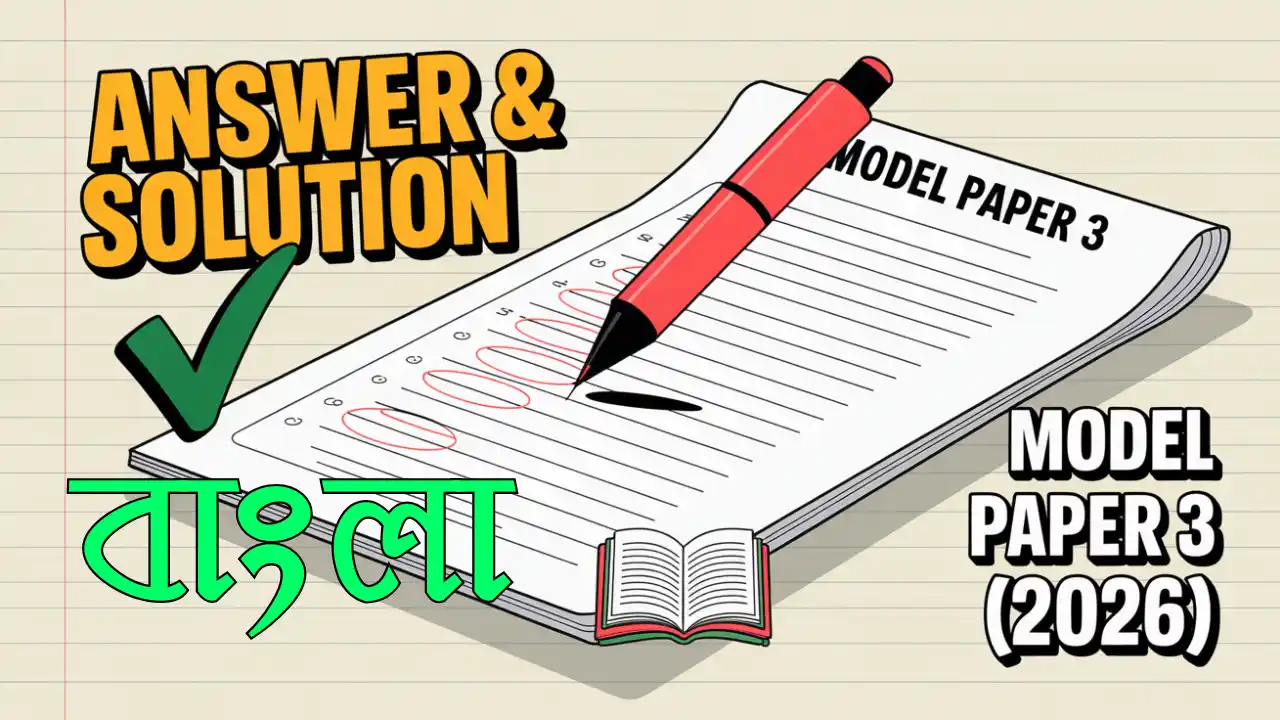আপনি কি ২০২৬ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 3 এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 3-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৫ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ “আমাদের থাকলে আমরাও চেষ্টা করে দেখতাম।”উক্তিটি-
(ক) তপনের মামার
(খ) তপনের বাবার
(গ) তপনের মেজোকাকুর
(ঘ) তপনের ছোটোকাকুর
উত্তর: (গ) তপনের মেজোকাকুর
১.২ পুলিশ সেজে হরিদা দাঁড়িয়েছিলেন
(ক) জগদীশবাবুর বাড়িতে
(খ) চকের বাস স্ট্যান্ডে
(গ) দয়ালবাবুর লিচু বাগানে
(ঘ) চায়ের দোকানে
উত্তর: (গ) দয়ালবাবুর লিচু বাগানে
১.৩ ‘কিছুটা যেতেই অমৃতের নজরে এল’- অমৃতের নজরে কী এসেছিল।-
(ক) কালিয়া মাটিতে পড়ে গেছে
(খ) নিম গাছের তলায় ছেলের দল
(গ) গলি থেকে পাঠান বেরোচ্ছেন
(ঘ) ইসাবের জামার পকেট ছিঁড়ে গেছে
উত্তর: (ঘ) ইসাবের জামার পকেট ছিঁড়ে গেছে
১.৪ “দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;” উদ্ধৃতাংশে ‘মানহারা মানবী’ বলতে বোঝানো হয়েছে-
(ক) আফ্রিকা মহাদেশকে
(খ) বসুধাকে
(গ) ভারতবর্ষকে
(ঘ) পশ্চিম দুনিয়াকে
উত্তর: (ক) আফ্রিকা মহাদেশকে
১.৫ “হাসিবে মেঘবাহন;” ‘মেঘবাহন’ বলতে বোঝানো হয়েছে-
(ক) দেবরাজ ইন্দ্রকে
(খ) অগ্নিদেবকে
(গ) দেবাদিদেব মহাদেবকে
(ঘ) রামচন্দ্রকে
উত্তর: (ক) দেবরাজ ইন্দ্রকে
১.৬ ‘মধ্যেতে যে কন্যাখানি’ কন্যাটি কে?
(ক) উর্বশী
(খ) রম্ভা
(গ) পদ্মাবতী
(ঘ) পদ্মা
উত্তর: (গ) পদ্মাবতী
১.৭ ওস্তাদ কলমবাজদের বলা হয়
(ক) শ্রুতিলেখক
(খ) লিপিকর
(গ) ক্যালিগ্রাফিস্ট
(ঘ) পেশকার
উত্তর: (গ) ক্যালিগ্রাফিস্ট
১.৮ “অনেক ধরে ধরে টাইপ-রাইটারে লিখে গেছেন মাত্র একজন।” তিনি হলেন
(ক) সত্যজিৎ রায়
(খ) অন্নদাশঙ্কর রায়
(গ) রাজশেখর বসু
(ঘ) সুবোধ ঘোষ
উত্তর: (খ) অন্নদাশঙ্কর রায়
১.৯ ‘অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী’ এটি একটি বাংলা
(ক) অলংকার
(খ) ধাঁধা
(গ) প্রবাদ
(ঘ) ছড়া
উত্তর: (গ) প্রবাদ
১.১০ অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাকে বলা হয়-
(ক) প্রযোজ্য কর্তা
(খ) প্রযোজক কর্তা
(গ) নিরপেক্ষ কর্তা
(ঘ) ব্যতিহার কর্তা
উত্তর: (গ) নিরপেক্ষ কর্তা
১.১১ রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় এই বাক্যের কর্তাটি হল-
(ক) প্রযোজ্য কর্তা
(খ) সহযোগী কর্তা
(গ) ব্যতিহার কর্তা
(ঘ) সমধাতুজ কর্তা
উত্তর: (গ) ব্যতিহার কর্তা
১.১২ পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় কোন্ সমাসে?
(ক) তৎপুরুষ
(খ) কর্মধারয়
(গ) দ্বন্দু
(ঘ) ক ও খ উভয়ই
উত্তর: (ঘ) ক ও খ উভয়ই
১.১৩ ‘উপনগরী’ সমাসটি গড়ে উঠেছে
(ক) সাদৃশ্য অর্থে
(খ) সামীপ্য অর্থে
(গ) পশ্চাৎ অর্থে
(ঘ) বীলা অর্থে
উত্তর: (খ) সামীপ্য অর্থে
১.১৪ ‘বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না।’ এটি কী ধরনের বাক্য?-
(ক) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য
(খ) নির্দেশক বাক্য
(গ) বিস্ময়সূচক বাক্য
(ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্য
উত্তর: (ক) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য
১.১৫ ‘রাতে বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে’ বাক্যটি হল-
(ক) জটিল বাক্য
(খ) যৌগিক বাক্য
(গ) আবেগসূচক বাক্য
(ঘ) সন্দেহবাচক বাক্য
উত্তর: (ঘ) সন্দেহবাচক বাক্য
১.১৬ ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ এই বাকাটি যে বাচ্যের দৃষ্টান্ত, তা হল
(ক) ভাববাচ্য
(খ) কর্মবাচ্য
(গ) কর্মকর্তৃবাচ্য
(ঘ) কর্তৃবাচ্য
উত্তর: (ঘ) কর্তৃবাচ্য
১.১৭ যে বাক্যে কর্ম কর্তারূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বলে-
(ক) কর্মবাচ্য
(খ) কর্তৃবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ “আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন।” বক্তার কোন্ দিনটি সবচেয়ে দুঃখের?
উত্তর: যেদিন বক্তা অর্থাৎ তপন নিজের লেখা গল্পটি মুদ্রিত আকারে হাতে পেয়েছিল সেই দিনটিকে বক্তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন বলে উল্লেক করা হয়েছে।
২.১.২ “ভ্রমণ করে দেখবার তো কোনো দরকার হয় না।” বক্তার কেন ভ্রমণ করে দেখবার দরকার হয় না?
উত্তর: সুবোধ ঘোষের ‘বহুরুপী’ গল্পে বিরাগী হরিদার মতে, ভ্রমণ করে তীর্থস্থান দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, তাঁর বিশ্বাস—হরিদার অন্তরের মধ্যেই সব তীর্থ বিরাজমান। তাই বাইরের পৃথিবী ঘুরে দেখার পরিবর্তে অন্তর্জগতের সাধনাই প্রকৃত তীর্থদর্শন। এজন্যই তিনি মনে করেন, ভ্রমণ করে আলাদা করে তীর্থ দেখবার দরকার হয় না।
২.১.৩ ‘ও নিয়ম রেলওয়ে কর্মচারীর জন্য,’ বক্তা কোন্ নিয়মের কথা বলেছেন?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পথের দাবী গল্পে বক্তা যে নিয়মের কথা বলেছেন সেটি হল – প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের রাত্রে কেউ বিরক্ত করতে পারবে না, অর্থাৎ তাঁদের ঘুমে কোনো ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না।
২.১.৪ ‘বলতে গেলে ছেলেদুটোর সবই একরকম, তফাত শুধু এই যে,’ তফাতটা কী?
উত্তর: অমৃত আর ইসাবের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও তফাত ছিল এই যে,
অমৃতের বাবা-মা আর তিন ভাই ছিল, ইসাবের ছিল শুধু তার বাবা।
২.১.৫ কোন্ ট্রেন নদেরচাঁদকে পিষে দেয়?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্প থেকে নেওয়া আলোচ্য অংশে ৭ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি নদেরচাঁদকে পিষে দেয়।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ ‘বছরগুলো / নেমে এল তার মাথার ওপর।’ বছরগুলো কীভাবে নেমে এসেছিল?
উত্তর: কবি পাবলো নেরুদা রচিত ‘অসুখী একজন’কবিতায় কথকের জন্য
অপেক্ষারতা নারীর ‘মাথার ওপর’ বছরগুলো পাথরের মতো নেমে এসেছিল।
২.২.২ “উঠিল পবন-পথে ঘোরতর রবে,/ রথবর,” এই প্রসঙ্গে কবির ব্যবহৃত উপমাটি লেখো।
উত্তর: “উঠিল পবন-পথে ঘোরতর রবে,/ রথবর,” এই প্রসঙ্গে কবির ব্যবহৃত উপমাটি হল – মৈনাক শৈল।
২.২.৩ ‘মাভৈঃ মাভৈঃ।’ শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: ‘মাভৈঃ মাভৈঃ।’ শব্দটির অর্থ হল ভয় কোরো না।
২.২.৪ ‘পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন।’ পঞ্চকন্যা কীভাবে চেতনা ফিরে পেল?
উত্তর: সমুদ্রকন্যা পদ্মার সখীদের সেবাশুশৃষায় পঞ্চকন্যা চেতনাফিরে পেল।
২.২.৫ ‘বর্ম খুলে দ্যাখো আদুড় গায়ে’ বর্ম খুলে কবি কী দেখতে বলেছেন।
উত্তর: কবি জয় গোস্বামীর লেখা অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতায় কবি বর্ম খুলে গান দেখার কথা বলেছেন।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘লাঠি তোমার দিন ফুরাইয়াছে।’ কথাটি কে বলেছিলেন?
উত্তর: ‘লাঠি তোমার দিন ফুরাইয়াছে।’ কথাটি বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়।
২.৩.২ ‘কলম সেদিন খুনিও হতে পারে বইকী।’ কোন্ ঘটনার প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে?
উত্তর: বিখ্যাত লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মারা গিয়েছিলেন নিজের
হাতের কলম হঠাৎ অসাবধানতাবশত বুকে ফুটে গিয়ে। এই ঘটনার প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে ,
‘কলম সেদিন খুনিও হতে পারে বইকী’ ।
২.৩.৩ ‘কালিদাসের এই উক্তি কাব্যেরই উপযুক্ত, ভূগোলের নয়।’ কোন্ উক্তিটির কথা এখানে বলা হয়েছে?
উত্তর: ‘কালিদাসের এই উক্তি কাব্যেরই উপযুক্ত, ভূগোলের নয়।’ এখানে হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড উক্তিটির কথা বলা হয়েছে
২.৩.৪ ছেলেবেলায় রাজশেখর বসু কার লেখা জ্যামিতি বই পড়তেন?
উত্তর: ছেলেবেলায় প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু ব্রহ্মমোহন মল্লিকের লেখা
বাংলা জ্যামিতি বই পড়তেন।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ নির্দেশকের কাজ কী?
উত্তর: ‘নির্দেশক’ শব্দটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়, যেমন – নাটক নির্দেশক নাটকের অভিনেতা ও অন্যান্য কর্মীকে পরিচালনা করেন। রসায়নে, নির্দেশক হলো এমন রাসায়নিক পদার্থ যা রং পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্রবণ অ্যাসিডিক না ক্ষারীয় তা শনাক্ত করা হয়।
২.৪.২ অ-কারক পদ কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর: অ-কারক পদ দুই প্রকার। দুই প্রকার অ-কারক পদ হল – সম্বন্ধ পদ এবং সম্বোধন পদ।
২.৪.৩ রূপে তোমায় ভোলাব না। চিহ্নিত পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
উত্তর: রূপে’ পদটির কারক হল করণ কারক এবং বিভক্তি হল সপ্তমী বা এ বিভক্তি।
২.৪.৪ সমাস কাকে বলে?
উত্তর: অর্থের দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠন করার প্রক্রিয়াকে সমাস বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পদের বিভক্তি লোপ পায় এবং একটি নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়।
২.৪.৫ ‘শতাব্দী’ ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: শতাব্দী’ শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো – শত বর্ষের সমাহার এবং ‘শতাব্দী’ শব্দটির সমাস হল দ্বিগু সমাস।
২.৪.৬ দ্বিগু সমাস কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর: দ্বিগু সমাসকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যাই যথা – ১. সমাহার দ্বিগু। ২. তদ্ধিতার্থক দ্বিগু।
২.৪.৭ যৌগিক বাক্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
উত্তর: যৌগিক বাক্যের দুটি বৈশিষ্ট্য হল – ১. দুটি বা ততোধিক স্বাধীন ধারা থাকে। ২. সমান গুরুত্বের ধারণাগুলিকে সংযুক্ত করে।
২.৪.৮ ‘নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।’ নস্ত্যর্থক বাক্যে পরিবর্তন করো।
উত্তর: নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন’ বাক্যটির নস্ত্যর্থক বাক্যে পরিবর্তন করলে হবে ‘নিমাইবাবু কথা বলিলেন না’ বা ‘নিমাইবাবু চুপ করিয়া থাকিলেন না’।
২.৪.৯ হিংসার দ্বারা মহৎ কার্য সাধিত হয় না। (কর্তৃবাচ্যে)
উত্তর: “হিংসার দ্বারা মহৎ কার্য সাধিত হয় না” এই বাক্যটি কর্তৃবাচ্য রূপান্তরিত করলে হবে, “হিংসা মহৎ কার্য সাধিত করতে পারে না” বা “হিংসার মাধ্যমে মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না”।
২.৪.১০ লুপ্তকর্তা ভাববাচ্যের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।
উত্তর: লুপ্তকর্তা ভাববাচ্যের সংজ্ঞা: লুপ্ত কর্তা ভাববাচ্য হলো এমন এক ধরনের বাচ্য যেখানে কর্তা উহ্য থাকে অর্থাৎ বাক্যে কর্তা অনুপস্থিত থাকে এবং ক্রিয়াপদটি প্রধান বা মুখ্য হয়ে ওঠে। এই বাচ্যে ক্রিয়ার অর্থের ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়, কর্ম থাকে না এবং কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বিভক্তি থাকতে পারে।
লুপ্তকর্তা ভাববাচ্যের উদাহরণ: “পাখি পাকা ফল খায়” (কর্তৃবাচ্য) বাক্যটি ভাববাচ্যে পরিবর্তিত হয়ে হবে “পাখির পাকা ফল খাওয়া হয়”।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ ‘খুবই গরিব মানুষ হরিদা।’ হরিদার পরিচয় দাও। তাঁর দারিদ্র্যের ছবি ‘বহুরূপী’ গল্পে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে?
উত্তর: সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পে হরিদা এক দরিদ্র মানুষ। শহরের অতি সরু গলির ভিতরে তাঁর ছোটো ঘর। নিয়মিত কোনো অফিস বা দোকানে চাকরি করা তাঁর স্বভাবে সইত না; তাই সংসার রোজগারহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। দারিদ্র্যের জন্য অনেক সময় তাঁর উনুনে শুধু জলই ফোটে, ভাত ফোটে না। তবে একঘেয়ে জীবিকা নির্বাহের কাজ করতে তিনি একেবারেই রাজি ছিলেন না। বহুরূপী সেজে যা কিছু অল্প আয় করতেন, তাই দিয়েই কখনও আধবেলা, কখনও একবেলা খেয়ে তাঁর দিন কাটত। এইভাবেই গল্পে হরিদার দারিদ্র্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
৩.১.২ “নদেরচাঁদ সব বোঝে, নিজেকে কেবল বুঝাইতে পারে না।” নদেরচাঁদ কী বোঝে? সে নিজেকে বোঝাতে পারে না কেন?
উত্তর: নদেরচাঁদ বুঝতে পারে যে, নদীর প্রতি তার যে গভীর মায়া ও আকর্ষণ, তা একধরনের অস্বাভাবিকতা।
নদেরচাঁদ জানে, একজন স্টেশনমাস্টারের পক্ষে এই ধরনের আবেগপ্রবণতা সঙ্গত নয় এবং তার এই অনুভূতি সবার কাছে গ্রহণযোগ্যও নয়। তবুও তার হৃদয় নদীর প্রতি এক অদ্ভুত টান অনুভব করে, যা সে নিজেও পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই টান থেকে সে মুক্ত হতে চাইলেও পারে না, কারণ তার মন বারবার নদীর দিকে ছুটে যেতে চায়। ফলে, নদেরচাঁদ সবকিছু বুঝেও নিজের মনে নিজেকে বোঝাতে পারে না।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “এবার মহানিশার শেষে / আসবে ঊষা অরুণ হেসে”- ‘মহানিশা’ কী? এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কবি কীসের ইঙ্গিত দিয়েছেন?
উত্তর: ‘মহানিশা’: ‘মহানিশা’ বলতে কবি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে অন্ধকারময় অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন।
তাৎপর্য বিশ্লেষণ: পৃথিবীজুড়ে কবি নজরুল স্থিতাবস্থার ভাঙন লক্ষ করেছেন। পরাধীনতা এবং সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার মধ্য দিয়ে যে অন্ধকার নেমে এসেছে তার অবসান ঘটবে, সভ্যতার নতুন সূর্যোদয় ঘটবে, কবি এরকমটাই প্রত্যাশা করেছেন। মহাদেব ধ্বংসের দেবতা হলেও তাঁর কপালে থাকে চাঁদ। একইভাবে ধ্বংসের মধ্যে সুন্দরকে বারবার প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই কবির প্রত্যাশা যে, সেই চাঁদের আলোয় ঘর ভরে যাবে।
৩.২.২ “অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো…” কবি কোথায় অস্ত্র রাখতে বলেছেন? তাঁর একথা বলার কারণ কী?
উত্তর: অস্ত্র রাখার স্থান: কবি গানের দুটি পায়ে অস্ত্র রাখতে বলেছেন।
এ কথা বলার কারণ: জয় গোস্বামী তাঁর ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় যুদ্ধবাজ মানুষদের উদ্দেশে এই আহ্বান জানিয়েছেন। ক্ষমতার নেশায় মেতে ওঠা মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হাতে তুলে নেয় অস্ত্র। অস্ত্র হিংস্রতার প্রতীক। মানুষের পৃথিবীতে অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ অস্ত্রই সভ্যতার শেষ কথা নয়। তার বদলে চাই গান যা সাম্যের আর সুন্দরের কথা বলে। তাই কবি অস্ত্র ফেলে গানকেই জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার করতে বলেছেন। এখানে কবির মানবতাবাদী মনোভাবটিই প্রকাশিত।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ ‘বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলোআনাই বজায় আছে’ বাবুটি কে? তার স্বাস্থ্য ও শখের পরিচয় দাও।
উত্তর: বাবুটির পরিচয়: এখানে বাবুটি বলতে শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ রচনাংশের অন্যতম চরিত্র গিরীশ মহাপাত্রের কথা বলা হয়েছে।
স্বাস্থ্য ও শখের পরিচয়: গিরীশ মহাপাত্রের বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিক সন্দেহে তাকে থানায় ধরে আনা হয়। রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে যাওয়া লোকটি কাশতে কাশতে ভিতরে প্রবেশ করে। কাশির দমক দেখে মনে হয়েছিল তার আয়ু আর বেশিদিন নেই। মাথার সামনে বড়ো বড়ো চুল থাকলেও ঘাড় ও কানের কাছে চুল প্রায় ছিল না। আর চুল থেকে বেরোচ্ছিল লেবুর তেলের উগ্র গন্ধ। এর সঙ্গে মানানসই ছিল তার পোশাকও। গায়ে ছিল জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি। তার বুকপকেট থেকে বাঘ-আঁকা একটি রুমালের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছিল। পরনে ছিল বিলাতি মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি। পায়ে সবুজ রঙের ফুলমোজা যেটা হাঁটুর ওপরে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। পায়ে ছিল বার্নিশ করা পাম্পশু, যার তলাটা আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো। আর হাতে ছিল হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া একগাছি বেতের ছড়ি।
৪.২ “পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?” কোন্ ঘটনাকে ‘অলৌকিক’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে? সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্প অনুসরণে বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: জ্ঞানচক্ষু’ গল্পে যে ঘটনাকে অলৌকিক বলা হয়েছে, তা হলো তপনের লেখা প্রথম গল্পটির সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় প্রকাশ। দীর্ঘদিন ধরে সে আশা করছিল যে, একদিন তার গল্প কোনো পত্রিকায় ছাপা হবে। ছোটোমেসো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গল্পটি ছাপানোর ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তপন নিজের চোখে যখন সত্যিই দেখে যে তার লেখা গল্প পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়েছে, তখন তার কাছে ঘটনাটি একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হয়।
অলৌকিক বলা হয়েছে এই কারণে যে, সাধারণ এক ছাত্রের লেখা গল্প ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে হাজার হাজার পাঠকের হাতে পৌঁছে যাওয়া তপনের কাছে এক অসম্ভব কল্পনার মতো ছিল। তাই সে এই ঘটনাকে অলৌকিক বলে আখ্যা দেয়।
এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তপন ভীষণ আনন্দিত ও অভিভূত হয়। তার মনে আত্মবিশ্বাস জাগে, লেখক হিসেবে তারও পরিচয় তৈরি হচ্ছে। ছাপার অক্ষরে নিজের গল্প দেখার আনন্দ তার কাছে জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ ‘সেই মিষ্টি বাড়ি’ সম্বন্ধে লেখক যে ছবি এঁকেছেন, তা নিজের ভাষায় লেখো।
উত্তর: পাবলো নেরুদার কবিতা “অসুখী একজন”-এ “সেই মিষ্টি বাড়ি”-র চিত্র যেন এক রঙিন শৈশবের ছবিপট। কবি সেখানে দেখেছেন শান্তির আশ্রয়, যেখানে চারদিকে ছিল প্রাচুর্য আর স্নিগ্ধতা। বাড়িটিতে ছিল এক স্বপ্নময় আবহ—গোলাপি গাছ, ঝুলন্ত বিছানা, আর ছোট ছোট নানা জিনিসের সমাহার। প্রতিটি কোণ, প্রতিটি কক্ষ যেন জীবনের সুখস্মৃতি নিয়ে ভরপুর।
কবি লিখেছেন, সেই মিষ্টি বাড়িতে তিনি পেয়েছিলেন নিরাপত্তা, আনন্দ এবং অবাধ স্বাধীনতা। প্রিয়জনদের ভালোবাসায় ভরা পরিবেশে শৈশব কেটেছিল খেলাধুলা আর হাসিখুশির মাঝে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, গাছপালা আর ছায়াঘেরা পরিবেশ সেই বাড়িকে করে তুলেছিল আরও মধুর।
আজকের দুঃসহ বাস্তবতার তুলনায় কবির কাছে সেই বাড়ি এক অমূল্য ধন, সুখ ও প্রশান্তির প্রতীক। তাই তিনি স্মৃতির দ্বারে ফিরে গিয়ে বারবার অনুভব করেন—“সেই মিষ্টি বাড়ি” তাঁর জীবনের চিরন্তন আনন্দভূমি, এক হারানো স্বর্গরাজ্য।
৫.২ ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতাটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করো।
উত্তর: ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতাটি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান মুসলিম কবি সৈয়দ আলাওল রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের একটি অংশ। এই অংশে সিংহল দেশের রাজকন্যা পদ্মাবতী ও তার চার সখী একসময় সমুদ্রজলে পতিত হয়ে গভীর সমুদ্রে অবস্থিত এক রহস্যময় নগরীতে পৌঁছে যায়। এই নগরীর বর্ণনায় কবি এক স্বপ্নিল, রূপকথার মতো পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন—যেখানে দুঃখ, কষ্ট বা পাপের কোনো স্থান নেই। নগরীটি সত্য, ধর্ম ও সদাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে বাস করেন সমুদ্রনৃপতির কন্যা পদ্মা।
পদ্মা এক সুন্দর পার্বত্য উদ্যানের নির্মাতা, যেখানে রকমারি ফুল ও ফলের সমারোহ রয়েছে। সেই পথেই একসময় তিনি পদ্মাবতী ও তার সখীদের অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাদের অবস্থা দেখে পদ্মা ধারণা করেন, হয়তো তারা স্বর্গ থেকে পতিত কোনো অপ্সরা, অথবা কোনো ভয়ংকর সামুদ্রিক ঝড়ে ভেসে এসেছে। পদ্মা তাদের বাঁচানোর জন্য নিজের সমস্ত বিদ্যা, তন্ত্র-মন্ত্র ও মহৌষধি প্রয়োগ করেন। অবশেষে পদ্মাবতী ও তার সখীদের জ্ঞান ফিরে আসে।
এইভাবেই ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতাটি এক কল্পলোকীয় সৌন্দর্য, মানবিক সহানুভূতি ও রহস্যে ঘেরা এক মনোমুগ্ধকর আখ্যান রচনা করে, যা ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ “আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই।” কারা কালি তৈরি করতেন? তাঁরা কীভাবে কালি তৈরি করতেন?
উত্তর: আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই’—এখানে ‘আমরা’ বলতে প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ ও তাঁর সতীর্থদের বোঝানো হয়েছে। তাঁদের কালি তৈরি করতে সাহায্য করতেন মা, পিসি ও দিদিরা।
প্রাচীনকালে ভালো কালি তৈরির একটি প্রচলিত রীতি ছিল—
“তিল ত্রিফলা শিমুল ছালা,
ছাগ দুগ্ধে করি মেলা।
লৌহ পাত্রে লোহায় ঘসি,
ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।”
কিন্তু শ্রীপান্থরা এত আয়োজন করতে পারতেন না। তাই সহজ পদ্ধতিতে কালি প্রস্তুত করতেন। সেই সময় রান্না হতো কাঠের আগুনে। ফলে কড়াইয়ের নিচে জমে থাকা কালি লাউপাতা দিয়ে ঘষে তুলে একটি পাথরের বাটিতে রাখা হত। তাতে জল মিশিয়ে গুলে নিলে কালি তৈরি হতো।
যারা কালি তৈরিতে দক্ষ ছিল, তারা কালো জলে হরতকী ঘষত কিংবা ভাজা আতপ চাল বেটে মিশিয়ে নিত। পরে খুন্তির গোড়া লাল করে জলে ছ্যাঁকা দিলে জল টগবগ করে ফুটে উঠত। শেষে ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে দোয়াতে ভরে নিলেই লেখার উপযুক্ত কালি তৈরি হয়ে যেত।
৬.২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন? এই সমিতিতে কারা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও পরামর্শ কী ছিল?
উত্তর: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালে একটি পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত করে। এই সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদেরা—
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভাষাতত্ত্ববিদ),
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (আইনবিদ ও শিক্ষাবিদ),
ড. মেঘনাদ সাহা (প্রখ্যাত পদার্থবিদ),
ড. মেঘনাদ ভট্টাচার্য (রসায়নবিদ), এবং ড. বিমানবিহারী মজুমদার (ইতিহাসবিদ)।
তাঁদের মূল কর্মপদ্ধতি ছিল বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ভাষা থেকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরিভাষা সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় যথাযথ প্রতিশব্দ নির্ধারণ করা। এ কাজে তাঁরা নানান শব্দকোষ, জার্নাল ও গবেষণা পত্র ব্যবহার করেন।
সমিতির সুপারিশ ছিল—
১. পরিভাষা প্রণয়নে বাংলা ভাষার প্রচলিত শব্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
২. প্রয়োজনে সংস্কৃতভিত্তিক শব্দ গ্রহণ করা।
৩. নতুন ধারণার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন শব্দ রচনা করা।
এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি সুসংহত বাংলা পরিভাষা ভাণ্ডার তৈরি করা, যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার সহজ ও সমৃদ্ধ হয়। এর ফলে বাংলায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার পথ সুগম হয়।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “তোমাকে আমরা তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে পারি, জান?” বক্তা কে? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি এই হুংকারের কারণ কী?
উত্তর: বক্তা: উদ্ধৃত অংশে বক্তা হলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা। তিনি মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়ার্টসকে উদ্দেশ করে এই কথা বলেছেন। এখানে ‘আমরা’ বলতে নবাব স্বয়ং, তাঁর সৈন্যবাহিনী এবং রাজকর্মচারীদের বোঝানো হয়েছে।
হুংকারের কারণ :
মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসেন। সিংহাসনে বসার পর থেকেই ইংরেজরা তাঁকে উপেক্ষা করতে থাকে এবং নানা ক্ষেত্রে অসহযোগিতা প্রদর্শন করে। এরই প্রতিক্রিয়ায় সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করে শহরের নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখেন। পরে ওয়াটসন ও ক্লাইভ কলকাতা পুনর্দখল করে এবং আলিনগরের সন্ধি সম্পন্ন হয়। সেই সন্ধির শর্ত সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য ওয়ার্টসকে রাজদরবারে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়।
কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওয়ার্টস আসলে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নৌসেনাপতি ওয়াটসনের লেখা চিঠি ও ওয়ার্টসের নিজস্ব পত্র থেকেই তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পায়। এতে বোঝা যায়, বাংলার স্বাধীনতা নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।
নবাব সিরাজদ্দৌলা বুঝতে পারেন, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীর একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যু। তাই তিনি ওয়ার্টসকে সতর্ক করে বলেন—“তোমাকে আমরা তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে পারি, জান?” তাঁর এই হুংকার শুধু একজন বিদেশি প্রতিনিধিকে উদ্দেশ করে নয়, বরং ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ়তা ও স্বাধীনচেতা মনোভাবেরই প্রকাশ।
৭.২ “তোমাদের কাছে আমি লজ্জিত।” কে, কার কাছে লজ্জিত? তাঁর লজ্জিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশে নবাব সিরাজদ্দৌলা ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা-র কাছে লজ্জা প্রকাশ করেন। লজ্জিত হওয়ার কারণ ছিল রাজনৈতিক ও বাস্তব পরিস্থিতি। মঁসিয়ে লা নবাবের দরবারে এসেছিলেন ইংরেজদের আক্রমণ থেকে চন্দননগর রক্ষার জন্য নবাবের সাহায্য চাইতে। সিরাজদ্দৌলা স্বীকার করেন যে ফরাসিরা বহুদিন ধরে বাংলায় বাণিজ্য করেছে এবং কখনও তাঁর বা বাংলার স্বার্থবিরোধী আচরণ করেনি। কিন্তু ইংরেজরা নবাবের অনুমতি ছাড়াই চন্দননগর অধিকার করেছে এবং ফরাসিদের সমস্ত কুঠি ছাড়ার দাবি তুলেছে—এসব বিষয়ে নবাব অবগত ছিলেন। তবু তিনি ফরাসিদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারলেন না। কলকাতা জয়ের লড়াই ও পূর্ণিয়ায় শওকত জঙ্গের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর বিপুল লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হয়েছিল। উপরন্তু তাঁর মন্ত্রীরাও নতুন যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন না। তাই ফরাসিদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে পারলেন না। এই অসহায় অক্ষমতার কারণেই নবাব সিরাজদ্দৌলা মঁসিয়ে লা-র কাছে লজ্জিত বোধ করেন।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ “তোর আসল লজ্জা জলে, আসল গর্বও জলে।” কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি। বস্তার এমন মন্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: উৎস ও প্রসঙ্গ :
মতি নন্দী রচিত ‘কোনি’ উপন্যাস থেকে উক্তিটি গৃহীত। কোনি প্রতিভাবান সাঁতারু হলেও সংসারের দারিদ্র্যের কারণে লীলাবতীর দর্জির দোকানে ঝাঁট দেওয়া ও ফাইফরমাশ খাটতে হয়। একদিন অমিয়া সেখানে ব্লাউজ করাতে গিয়ে কোনিকে দেখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—“তুই এখানে ঝিয়ের কাজ করিস?” এতে কোনি লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করে। ঘটনাটি ক্ষিতীশকে জানালে ক্ষিতীশ তাকে সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে বলেন—“তোর আসল লজ্জা জলে, আসল গর্বও জলে।”
তাৎপর্য :
ক্ষিতীশের এই বক্তব্যে গভীর তাৎপর্য নিহিত—
1. সম্মানের আসল ক্ষেত্র : কোনির জীবন ও স্বপ্ন সাঁতারের সঙ্গে জড়িয়ে। তার গর্ব বা লজ্জা নির্ভর করবে জলে তার সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর। বাইরের কাজ, যেমন দর্জির দোকানে ফাইফরমাশ খাটা, তার প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করে না।
2. অমিয়ার তাচ্ছিল্যের প্রতিবাদ : অমিয়া দোকানে কোনিকে হেয় করলেও ক্ষিতীশ বুঝিয়ে দেন—ওটা কোনির প্রকৃত কর্মক্ষেত্র নয়। একজন খেলোয়াড়ের গৌরব খেলায়, অন্যত্র নয়।
3. অনুপ্রেরণাদান : ক্ষিতীশের উক্তি কোনিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তিনি বোঝাতে চান—পরিশ্রম করে সাঁতারে সফল হলেই কোনি সত্যিকারের গর্ব অর্জন করবে। তাই বাইরের সমালোচনায় ভেঙে না পড়ে তার উচিত মন দিয়ে সাঁতার শেখা।
উপসংহার :
অতএব, ক্ষিতীশের উক্তিটি কোনিকে নতুনভাবে আত্মবিশ্বাস জোগায়। এতে প্রতিভাবান সাঁতারু হিসেবে নিজের স্বপ্নের জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনুপ্রেরণা নিহিত রয়েছে।
৮.২ “এত কেচ্ছাসাধন করেন। বাঁচবেন কী করে?” কে, কোন্ প্রসঙ্গে, কাকে কথাগুলি বলেছিলেন? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কেচ্ছাসাধনের বর্ণনা দাও।
উত্তর: উক্তিটি মতি নন্দীর “কোনি” উপন্যাসে বলা হয়েছে। এখানে বক্তা হলেন লীলাবতী দেবী, যিনি ক্ষিতীশ ঘোষকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলেছিলেন। প্রসঙ্গত, ক্ষিতীশবাবু সাঁতার প্রশিক্ষক হলেও আর্থিকভাবে দারিদ্রসঙ্কুল। তিনি সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের সাঁতারু হিসেবে গড়ে তোলেন। এই অক্লান্ত সংগ্রাম ও সাধনাকেই লীলাবতী ব্যঙ্গ করে “কেচ্ছাসাধন” বলে অভিহিত করেছিলেন।
ক্ষিতীশবাবুর কেচ্ছাসাধনের বর্ণনা:
ক্ষিতীশবাবুর জীবনটাই এক বিরাট সংগ্রাম। তিনি আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হলেও কখনও স্বার্থের কথা ভাবেননি। সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে প্রতিভা খুঁজে এনে তাঁদের সাঁতারে সফল করার জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দেন। ক্লাব কর্তৃপক্ষের অবহেলা, অর্থাভাব কিংবা সমাজের বিদ্রূপ—কোনো কিছুই তাঁকে থামাতে পারেনি। কোনির মতো অসহায় মেয়েকেও তিনি দৃঢ়ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিযোগিতার আসরে তুলে ধরেছিলেন।
উপসংহার :
অতএব, ক্ষিতীশবাবুর এই তথাকথিত *“কেচ্ছাসাধন”*ই শেষ পর্যন্ত কোনির বিজয়ের মাধ্যমে সার্থক হয়ে ওঠে এবং তাঁর নিঃস্বার্থ পরিশ্রম সমাজের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়।
৮.৩ “আমার মেয়েদের আমি উইথড্র করে নিচ্ছি।” কোন্ পরিস্থিতিতে, কে এমন মন্তব্য করেন?
উত্তর: মন্তব্য— মতি নন্দী রচিত ‘কোনি’ উপন্যাস থেকে উক্তিটি গৃহীত। আলোচ্য উক্তিটি বলেছেন বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবের প্রশিক্ষক ও হিয়া মিত্রের কোচ প্রণবেন্দু বিশ্বাস।
পরিস্থিতি—
ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বাংলা মহিলা সাঁতারু দল নির্বাচনের সময় এই ঘটনা ঘটে। ক্ষিতীশ ঘোষের বিরোধী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে কোনির দলে অন্তর্ভুক্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। অথচ প্রণবেন্দু বিশ্বাস আগে থেকেই কোনির সাঁতারের অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করেছিলেন। একজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক হিসেবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলায় স্প্লিন্ট ইভেন্টে কোনির সমকক্ষ আর কেউ নেই। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, কোনিকে দলে নিলে বাংলা মহারাষ্ট্রের কাছ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে। তাই অন্যায়ভাবে কোনিকে বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানান এবং ধীরেন ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। শেষপর্যন্ত তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, যদি কোনিকে বাংলা দলে নেওয়া না হয় তবে তিনি বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবের সমস্ত মেয়েদের উইথড্র (প্রত্যাহার) করে নেবেন। তাঁর এই কঠোর অবস্থান ও প্রতিবাদের ফলেই শেষমেশ কোনির দলে জায়গা নিশ্চিত হয়।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো:
Student life is the stage of preparation for future. This is the most important period of life. A student is young today, but he will be a man tomorrow. He has different duties.
উত্তর: ছাত্রজীবন ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির পর্যায়। এটি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। আজ একজন ছাত্র তরুণ, কিন্তু আগামী দিনে সে হবে পূর্ণ মানুষ। তার নানা ধরনের কর্তব্য রয়েছে।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ নারী স্বাধীনতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
কাল্পনিক সংলাপ: নারী স্বাধীনতা
রাহুল : শোন অর্পিতা, আজকাল সব জায়গায় নারী স্বাধীনতার কথা শোনা যায়। তুমি কী মনে করো, মেয়েরা সত্যিই কি স্বাধীন হয়েছে?
অর্পিতা : পুরোপুরি হয়নি রাহুল। মেয়েরা আজ পড়াশোনা করছে, চাকরি করছে, খেলাধুলায় অংশ নিচ্ছে। কিন্তু সমাজের মানসিকতা পুরোপুরি বদলায়নি।
রাহুল : হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। এখনো অনেক পরিবারে মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা গুরুত্ব পায় না। বিয়ের সিদ্ধান্ত, চাকরির সিদ্ধান্ত—সবকিছুতেই চাপিয়ে দেওয়া হয়।
অর্পিতা : নারী স্বাধীনতা মানে কেবল বাইরে কাজ করার সুযোগ নয়, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার অধিকারও।
রাহুল : তাহলে কি আমাদের প্রজন্মের উচিত মেয়েদের সমান সুযোগ দেওয়া?
অর্পিতা : অবশ্যই। ছেলে-মেয়ে সমান—এটা মেনে নিলে সমাজেই প্রকৃত নারী স্বাধীনতা আসবে।
রাহুল : একমত আমি। নারীকে সম্মান না দিলে কোনো জাতিই উন্নতি করতে পারে না।
১০.২ তোমার বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনী নিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত
নিজেস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২৫: গত শনিবার আমাদের বিদ্যালয়ে এক মনোজ্ঞ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. সুমন দত্ত।
নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা নানা অভিনব প্রজেক্ট নিয়ে অংশ নেয়। সৌরশক্তি চালিত যন্ত্র, পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন, রোবট, পানিশোধন যন্ত্রসহ একাধিক সৃজনশীল মডেল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাবনী শক্তি দেখে মুগ্ধ হন।
শেষে বিচারকমণ্ডলী শ্রেষ্ঠ প্রজেক্ট নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদান করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও গবেষণার আগ্রহ জাগাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো:
১১.১ বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ।
উত্তর:
বিজ্ঞান : আশীর্বাদ না অভিশাপ
ভূমিকা
বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। তবে এর ব্যবহারই নির্ধারণ করে—বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ।
বিজ্ঞানের আশীর্বাদ
১. যোগাযোগের উন্নতি – টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয়।
২. যাতায়াত ব্যবস্থা – ট্রেন, বাস, বিমান ও জাহাজ ভ্রমণকে করেছে সহজ, দ্রুত ও আরামদায়ক।
৩. চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রগতি – এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, সার্জারি, অঙ্গ প্রতিস্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে অসংখ্য জীবন রক্ষা হচ্ছে।
৪. কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি – বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, সার, কীটনাশক ও উন্নত বীজ ব্যবহারের ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫. শিক্ষা ও বিনোদন – টেলিভিশন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট জ্ঞানার্জন ও বিনোদনের ক্ষেত্রে এনেছে বিপ্লব।
বিজ্ঞানের অভিশাপ
১. অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার – পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা বিশ্বকে করেছে অনিরাপদ।
২. পরিবেশ দূষণ – শিল্পোন্নতির ফলে বায়ু, জল ও মাটি দূষিত হয়ে মানুষের অস্তিত্ব হুমকির মুখে।
৩. প্রযুক্তির অপব্যবহার – টেলিভিশন, মোবাইল ও ইন্টারনেট অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে।
৪. মানবিক মূল্যবোধের অবনতি – যন্ত্রনির্ভরতা মানুষের মধ্যে ভোগবাদ ও অস্থিরতা বাড়াচ্ছে।
৫. যুদ্ধবিগ্রহ বৃদ্ধি – বৈজ্ঞানিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিশ্বশান্তিকে হুমকির মুখে ফেলছে।
উপসংহার
বিজ্ঞান নিজে আশীর্বাদও নয়, অভিশাপও নয়। এর সদ্ব্যবহার মানবকল্যাণ আনে, আর অপব্যবহার ধ্বংস ডেকে আনে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো বিজ্ঞানকে শুধু মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো।
১১.২ একটি নদীর আত্মকাহিনি।
উত্তর:
একটি নদীর আত্মকাহিনি
আমি এক নদী। আমার জন্ম হয়েছিল বহু দূরের পাহাড়ি গহ্বরে, ক্ষুদ্র ঝরনার কলকল ধ্বনির ভেতর দিয়ে। তখন আমি ছিলাম শিশু— সরল, নিষ্পাপ, অস্থির স্রোতের মতো। পাহাড়ি পাথরে আঘাত খেতে খেতে হাসতে হাসতে আমি নেমে এসেছিলাম সমতলে। সূর্যের আলোয় আমার বুক ঝলমল করত, চাঁদের আলোয় আমি যেন রূপোলি ফিতা হয়ে বয়ে যেতাম। আমার শৈশব ছিল উচ্ছ্বাসে ভরা, আমি গান গাইতাম, নেচে চলতাম, সবাইকে আনন্দ দিতাম।
যৌবনে পৌঁছে আমি হলাম প্রবল, শক্তিশালী। আমার তীরবর্তী ভূমিকে আমি উর্বর করে তুললাম, মানুষের জীবন ভরিয়ে দিলাম শস্যে। আমার জলে নৌকা ভেসেছে, মাঝির গান কেঁপে উঠেছে বাতাসে। আমার জলে ভেসে এসেছে সভ্যতার আলো, গড়ে উঠেছে গ্রাম, শহর, শিল্প। কখনো আমি প্রেমের প্রেরণা হয়েছি, কখনো বিদ্রোহের সঙ্গীত। কবিরা আমার রূপ দেখে আমাকে তুলনা করেছেন মাতৃরূপী দানবতীর সঙ্গে।
তবু আমার জীবনে কেবল স্নেহ নেই, আছে প্রলয়ও। বর্ষার দিনে আমি ফুলে-ফেঁপে উঠি, ভাঙি ঘরবাড়ি, ডুবিয়ে দিই মাঠঘাট। কিন্তু তবু আমার ক্রোধেও লুকিয়ে থাকে দান— নতুন পলি মেখে আমি উর্বর করি কৃষকের জমি। আমার সব রূপেই মানুষের কল্যাণ লুকিয়ে থাকে।
কিন্তু আজ আমি দুঃখী। আমার বুক ভরেছে ময়লা-আবর্জনায়। কারখানার বর্জ্য, প্লাস্টিক, পলিথিনে আমার জলে আর সেই নির্মলতা নেই। মাছেরা মরে যাচ্ছে, জেলেদের সংসার ভাঙছে। আমার তীর দখল হয়ে যাচ্ছে, আমার বুক সংকুচিত হয়ে আসছে। আমি কাঁদি, কিন্তু কেউ শোনে না আমার আর্তি।
তবু আমি থামতে চাই না। আমি জানি, আমি আছি বলেই জীবন আছে। আমি বাঁচলে সভ্যতা বাঁচবে, শস্য বাঁচবে, মানুষের প্রাণ বাঁচবে। আমি চাই মানুষ আবার আমাকে ভালোবাসুক, আমাকে রক্ষা করুক।
আমি এক নদী— অশেষ, অনন্ত। জন্ম থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে পুনর্জন্ম— আমি বয়ে চলেছি, বয়ে চলব চিরকাল, মানবজাতির সাথি হয়ে।
১১.৩ সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর।
উত্তর:
সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর
ভূমিকা
ভারতীয় সঙ্গীতজগতে যাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তিনি হলেন সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। তাঁর গানে যেমন ছিল স্বর্গীয় সুরের মাধুর্য, তেমনি ছিল আত্মার গভীর টান। তাঁকে ভারতবর্ষের “কোকিলকণ্ঠী” বললে অত্যুক্তি হয় না।
জন্ম ও শৈশব
লতা মঙ্গেশকরের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে। তাঁর পিতা দীননাথ মঙ্গেশকর ছিলেন নাট্যকলা ও সঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পী। ছোটবেলা থেকেই লতা সঙ্গীতচর্চায় অভ্যস্ত হন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর সংসারের দায় কাঁধে তুলে নেন। জীবনের সংগ্রাম সঙ্গীতের পথেই তাঁকে এগিয়ে দেয়।
সঙ্গীতজগতে প্রবেশ
১৯৪২ সালে মারাঠি চলচ্চিত্রে গান গেয়ে তিনি কেরিয়ার শুরু করেন। পরে হিন্দি সিনেমার জগতে প্রবেশ করে একের পর এক অমর সৃষ্টি উপহার দেন। তাঁর গলার স্বর ছিল অদ্ভুত মধুর ও আবেগময়। হিন্দি, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি সহ বহু ভাষায় তিনি গান গেয়েছেন।
গান ও জনপ্রিয়তা
তাঁর গাওয়া অসংখ্য গান আজও সমান জনপ্রিয়। “আয়েগা আনেওয়ালা” গানটির মাধ্যমে তিনি সারা দেশে খ্যাতি অর্জন করেন। শুধু চলচ্চিত্রের গানই নয়, তিনি বহু ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক গানও গেয়েছেন।
পুরস্কার ও সম্মান
সঙ্গীতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান “ভারতরত্ন” লাভ করেন। এছাড়া “পদ্মভূষণ”, “পদ্মবিভূষণ” সহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তবে পুরস্কারের থেকেও বড় কথা, তিনি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে চিরকালীন আসন দখল করেছেন।
উপসংহার
লতা মঙ্গেশকর শুধু এক জন শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক যুগের প্রতীক। তাঁর কণ্ঠে অগণিত মানুষ দুঃখে সান্ত্বনা পেয়েছেন, সুখে আনন্দ পেয়েছেন। ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর সুরেলা কণ্ঠ আজও বেঁচে আছে প্রতিটি ভারতীয়র মনে। তাঁকে যথার্থই বলা হয় “সুরসম্রাজ্ঞী”।
১১.৪ একটি সাম্প্রতিক ট্রেন দুর্ঘটনা
উত্তর:
একটি সাম্প্রতিক ট্রেন দুর্ঘটনা
ভূমিকা
ট্রেন হলো মানুষের অন্যতম প্রধান গণপরিবহন ব্যবস্থা। প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী এই পরিবহনের উপর নির্ভর করে চলাফেরা করে। কিন্তু কখনও কখনও অসতর্কতা, যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা মানবীয় ভুলের কারণে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, যা বহু প্রাণহানি ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ট্রেন দুর্ঘটনা তারই দৃষ্টান্ত।
ঘটনার বিবরণ
গত মাসে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের নিকটে একটি মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। সকালে কলকাতা থেকে মালের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া একটি এক্সপ্রেস ট্রেন বর্ধমান স্টেশনের অদূরে লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনটির একাধিক বগি হঠাৎ করেই লাইন থেকে ছিটকে যায় এবং পাশের মাঠে উল্টে পড়ে। যাত্রীতে পরিপূর্ণ বগিগুলিতে সৃষ্টি হয় তীব্র চিৎকার আর হাহাকার। মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকে নেমে আসে বিভীষিকার চিত্র। অনেক যাত্রী প্রাণ হারান, আবার অনেকে গুরুতর জখম হন।
উদ্ধারকাজ ও সরকারি ব্যবস্থা
দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয় মানুষ ছুটে আসেন উদ্ধারকাজে। আহতদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ, দমকল ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। লম্বা সময় ধরে চলে বগি কেটে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের কাজ। সরকারি হিসেবে জানা যায়, এই দুর্ঘটনায় বহু যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয় এবং আহতদের চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করছে।
কারণ অনুসন্ধান
দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে রেল কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক অনুমান, ত্রুটিপূর্ণ সিগন্যাল ব্যবস্থা অথবা রেললাইনের দুর্বলতার কারণেই এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবও দায়ী হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের মত।
উপসংহার
এমন দুর্ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দেয় যে, রেলযাত্রা নিরাপদ হলেও অবহেলা বা গাফিলতির কারণে মুহূর্তের মধ্যে তা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। তাই রেলপথের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও কর্মীদের সতর্কতা অপরিহার্য। যাত্রীদেরও সচেতন থাকা উচিত এবং নিয়ম ভঙ্গ করা উচিত নয়। সাম্প্রতিক এই ট্রেন দুর্ঘটনা গোটা দেশকে শোকস্তব্ধ করে তুলেছে। অসংখ্য নিরীহ যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন, বহু পরিবার অশান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। এমন দুর্ঘটনা যেন আর না ঘটে, তার জন্য সকলের মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।