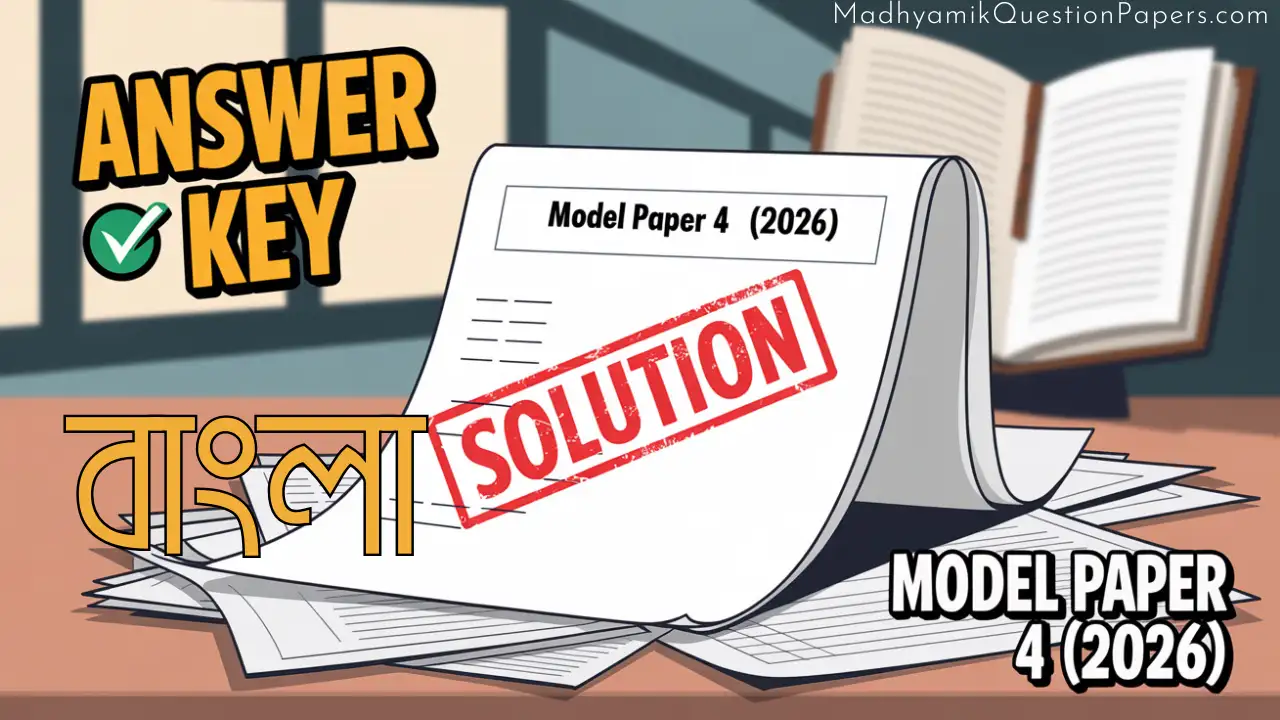২০২৬ সালের মাধ্যমিক বাংলা Model Question Paper 4 এর সমাধান খুঁজছেন? আপনার খোঁজ এখানেই শেষ!
এই আর্টিকেলে পাবেন প্রতিটি প্রশ্নের নির্ভুল ও সহজবোধ্য উত্তর, যা আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করবে। MadhyamikQuestionPapers.com গত ২০১৭ সাল থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশ্নপত্র ও সমাধান দিয়ে আসছে—এবং ২০২৬ সালের মডেল প্রশ্নপত্রের সমাধানও এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ এক সন্ন্যাসী এসে জগদীশবাবুর বাড়িতে ছিলেন-
(ক) চারদিন
(খ) তিনদিন
(গ) সাতদিন
(ঘ) পাঁচদিন
উত্তর: (গ) সাতদিন
১.২ ‘কিন্তু বুনোহাঁস ধরাই যে এদের কাজ;’ বস্তা হলেন-
(ক) নিমাইবাবু
(খ) রামদাস
(গ) জগদীশবাবু
(ঘ) অপূর্ব
উত্তর: (খ) রামদাস
১.৩ অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নদেরচাঁদ তার স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন
(ক) দু’দিন ধরে
(খ) সমস্ত দিন ধরে
(গ) একবেলা ধরে
(ঘ) তিন দিন ধরে
উত্তর: (ক) দু’দিন ধরে
১.৪ ‘অথবা এমনই ইতিহাস’ ইতিহাস যেমন
(ক) গৌরবময়
(খ) স্মরণীয়
(গ) চোখমুখ ঢাকা
(ঘ) যন্ত্রণার
উত্তর: (গ) চোখমুখ ঢাকা
১.৫ বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে-
(ক) শংকর
(খ) ভয়ংকর
(গ) দিগম্বর
(ঘ) শুভংকর
উত্তর: (খ) ভয়ংকর
১.৬ “গান বাঁধবে সহস্র উপায়ে” কে গান বাঁধবে?
(ক) চিল
(খ) কোকিল
(গ) শকুন
(ঘ) ময়ূর
উত্তর: (খ) কোকিল
১.৭ চিনারা চিরকালই লেখার জন্য ব্যবহার করে আসছে-
(ক) তুলি
(খ) ব্রোঞ্জের শলাকা
(গ) হাড়
(ঘ) নল-খাগড়া
উত্তর: (ক) তুলি
১.৮ চলন্তিকা কী?
(ক) সুগ্রাহী কাগজ
(খ) বিদেশের কালি
(গ) বাংলা অভিধান
(ঘ) ফাউন্টেন পেন
উত্তর: (গ) বাংলা অভিধান
১.৯ রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম
(ক) বনফুল
(খ) শ্রীপান্থ
(গ) পরশুরাম
(ঘ) রূপদর্শী
উত্তর: (গ) পরশুরাম
১.১০ যে সব শব্দ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসে কারকের রূপদান করে, তা হল-
(ক) বিভক্তি
(খ) উপসর্গ
(গ) অনুসর্গ
(ঘ) প্রত্যয়
উত্তর: (গ) অনুসর্গ
১.১১ আর কাউকে পায়ের ধুলো নিতে দেননি সন্ন্যাসী। নিম্নরেখ পদটি-
(ক) ক্রিয়াবাচক পদ
(খ) সম্বোধন পদ
(গ) কর্মকারক
(ঘ) সম্বন্দ্বপদ
উত্তর: (ঘ) সম্বন্দ্বপদ
১.১২ সমাসে একাধিক পদ মিলিত হয়ে যে নতুন পদটি গঠন করে, তাকে বলে
(ক) সমস্যমান পদ
(খ) সমস্তপদ
(গ) বিগ্রহ বাক্য
(ঘ) নামপদ
উত্তর: (খ) সমস্তপদ
১.১৩ কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন-নিম্নরেখ পদটি কোন্ সমাসের উদাহরণ?-
(ক) কর্মধারয় সমাস
(খ) তৎপুরুষ সমাস
(গ) বহুব্রীহি সমাস
(ঘ) দ্বন্দু সমাস
উত্তর: (গ) বহুব্রীহি সমাস
১.১৪ “এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল।” বাক্যটি কোন্ শ্রেণির?-
(ক) সরল বাক্য
(খ) জটিল বাক্য
(গ) যৌগিক বাক্য
(ঘ) মিশ্রবাক্য
উত্তর: (ক) সরল বাক্য
১.১৫ ‘তোমার ভালো হোক।’ বাক্যটি
(ক) অনুজ্ঞাবাচক
(খ) নির্দেশক
(গ) প্রার্থনাসূচক
(ঘ) প্রশ্নসূচক
উত্তর: (গ) প্রার্থনাসূচক
১.১৬ ‘শাঁখ বাজে’- কী জাতীয় বাচ্য?
(ক) কর্তৃবাচ্য
(খ) কর্মবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
১.১৭ কর্মবাচ্যের কর্তাকে বলে
(ক) ব্যতিহার কর্তা
(খ) কর্ম কর্তা
(গ) উক্ত কর্তা
(ঘ) অনুক্ত কর্তা
উত্তর: (খ) কর্ম কর্তা
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ ‘মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে সেটা।’ মেসোর উপযুক্ত কাজটি কী?
উত্তর: তপনের ছোটোমাসি মনে করেন, তপনের লেখা গল্পটি ছোটোমেসো যদি একটু সংশোধন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন, তবে সেটাই হবে মেসোর উপযুক্ত কাজ।
২.১.২ ‘কিন্তু ওই ধরনের কাজ হরিদার জীবনের পছন্দই নয়।’ কোন্ ধরনের কাজ হরিদার পছন্দ ছিল না?
উত্তর: প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পের হরিদা চরিত্রটি একটি স্বতন্ত্র ও স্বপ্নবিলাসী মানসিকতার অধিকারী। তার জীবনদর্শন সাধারণ চাকরি বা ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বা বলা চলে এক ঘেয়ে কাজ তার পছন্দ না ।
২.১.৩ “তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?” কোন্ ‘বস্তুটি’ পকেটে ছিল?
উত্তর: গিরীশ মহাপাত্রের পকেটে যে ‘বস্তুটি’ থাকার কথা বলা হয়েছে, সেটি হল গাঁজার কলকে বা গাঁজা রাখার জন্য ব্যবহৃত একটি ছোট থলি। এটি গাঁজা সংরক্ষণ ও বহনের জন্য ব্যবহার করা হত।
২.১.৪ ‘ইসাবের মেজাজ চড়ে গেল।’ ইসাবের মেজাজ চড়ে যাওয়ার কারণ কী?
উত্তর: অমৃত যখন কুস্তি লড়তে রাজি হল না, তখন কালিয়া তাকে জবরদস্তি মাটিতে ফেলে দেয়। এই অপমানজনক দৃশ্য দেখেই ইসাবের মেজাজ চড়ে যায়।
২.১.৫ ‘নদেরচাঁদ গর্ব অনুভব করিয়া।’ এতকাল নদেরচাঁদ কীসের জন্য গর্ব অনুভব করেছে?
উত্তর: নদেরচাঁদ নিজেকে খুবই গর্বিত মনে করছিল, কারণ তার স্টেশনের পাশে থাকা নদীর উপরে সেই নতুন সেতুটিকে রাঙিয়ে তোলা হয়েছিল।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ “তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।” কারণ কী?
উত্তর: “যুদ্ধ রক্তের এক অগ্নিগিরির মতো, যা থেকে জন্ম নেয় শিশুমৃত্যু ও মানুষের নিরাশ্রয় হওয়ার করুণ ইতিহাস। এর দাবানলে পুড়ে যায় সমতলের সব শান্তি। এমনকি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মন্দিরে ধ্যানমগ্ন যে দেবতারা, তারাও এই অগ্নিসংকটে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েন। এটা তাদের স্বপ্নের পতন—বিশ্ববিধানকে নিয়ন্ত্রণ করার সেই অমোঘ ক্ষমতার অবসান। সুতরাং, এটা কেবলমাত্র মূর্তির পতন নয়; এটা হল মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঐশ্বরিকতারই চূড়ান্ত পরাজয়।”
২.২.২ “আমাদের ঘর গেছে উড়ে” উদ্ধৃতাংশটিতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উত্তর: আধুনিক বিশ্বে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে দুর্বল দেশগুলি। একপক্ষীয় সামরিক হামলায় বোমাবর্ষণ চালানো হয় এসব রাষ্ট্রের ওপর। এর ফলে শান্তিপ্রিয়, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়। আগ্রাসনকারী দেশগুলি তাদের যুদ্ধবিমান নিয়ে আকাশপথে হামলা চালায় এবং নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে। এর ফলস্বরূপ নিরীহ বেসামরিক জনগণ তাদের বসতভিটা হারিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। কবি আলোচ্য অংশে যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার বারবার লঙ্ঘিত হয়।
২.২.৩ “এসো যুগান্তের কবি,” কবির ভূমিকাটি কীরূপ হবে?
উত্তর: “ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আফ্রিকার জনগণের ওপর অত্যাচার ছিল মানবতার মর্যাদাহানিকর এক অধ্যায়। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। যুগান্তের কবিরা হলেন তাদেরই কণ্ঠস্বর। মানবতাবাদী কবিকেও আজ আফ্রিকার দ্বারে দাঁড়িয়ে সত্য ও সুন্দরের নামে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং এই ক্ষমাই হবে সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।”
২.২.৪ ‘শ্রীযুত মাগন গুণী’ মাগন গুণী কে?
উত্তর: মাগন গুণী ছিলেন আরাকানের রাজা থদো-মিন্তারের প্রধানমন্ত্রী। তিনিই আলাওলকে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন।
২.২.৫ “আঁকড়ে ধরে সে খড়কুটো” ‘খড়কুটো’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: কবি অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর সম্বল হিসেবে গানকে আঁকড়ে ধরেছেন। বিশ্বজুড়ে চলমান হিংসা ও হানাহানির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে মাত্র এক-দুটি গানই ভরসা। এই স্বল্পসম্বলতার কথাই প্রকাশ করতে তিনি ‘খড়কুটো’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘লেখে তিন জন।’ এই তিন জনের পরিচয় দাও।
উত্তর: শ্রীপান্থ রচিত ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ রচনায় উল্লিখিত “তিন জন” বলতে কালি, কলম ও মনকে বোঝানো হয়েছে।
২.৩.২ ‘সেই আঘাতেরই পরিণতি নাকি তাঁর মৃত্যু।’ কোন্ আঘাতের পরিণতিতে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: বিখ্যাত লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় একটি দুর্ঘটনাবশতঃ তাঁর নিজের হাতের কলম বুকে ফুটে যাওয়ার কারণে।
২.৩.৩ ‘সম্পাদকের উচিত’ সম্পাদকের কী উচিত বলে লেখক মনে করেছেন?
উত্তর: রাজশেখর বসুর মতে, বাংলায় প্রকাশিত বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে অল্পবিদ্যার দরুন ভ্রান্ত তথ্য মুদ্রিত হয়। এই সকল ভ্রান্তি পাঠকমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য তার ধারণা, অখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের পূর্বে সম্পাদকের কর্তব্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের দ্বারা তা পরীক্ষণ করানো। তাহলে প্রকাশিত বিষয়ের নির্ভুলতা রক্ষিত হবে এবং পাঠকগণও যথার্থ জ্ঞানলাভে সমর্থ হবেন।
২.৩.৪ “আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন” শব্দের ‘ত্রিবিধ কথা’ কী?
উত্তর: রাজশেখর বসু রচিত ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে যে, শব্দের তাত্পর্য ব্যাখ্যায় আলংকারিকেরা অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা এই তিনটি বৃত্তির কথা উল্লেখ করেন।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ ফাঁকি দিয়ে ওপরে ওঠা যায় না। নিম্নরেখ পদটি কোন্ কারক?
উত্তর: “ফাঁকি দিয়ে” পদটি এখানে অধিকরণ কারক নির্দেশ করছে, কারণ এটি “ওঠা” ক্রিয়াটি কী উপায়ে বা কীসের সাহায্যে সম্পাদিত হচ্ছে তা বোঝাচ্ছে। এটি ক্রিয়ার মাধ্যম বা পদ্ধতির তথ্য প্রদান করে, যা বাংলা ব্যাকরণে অধিকরণ কারকের একটি মূল কাজ।
২.৪.২ নিরপেক্ষ কর্তার একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: নিরপেক্ষ কর্তা হলো কর্তৃবাচ্যের একটি বিশেষ ধরন, যেখানে বাক্যের কর্মপদই কর্তার ভূমিকা পালন করে। “বাঁশি বাজে” বাক্যটি এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
২.৪.৩ ‘দম্পতি’ পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: “দম্পতি” একটি দ্বন্দ্ব সমাস, যার ব্যাসবাক্য হলো “জায়া ও পতি”। এই সমাসে ‘জায়া’ এবং ‘পতি’ শব্দ দুটি একত্রিত হয়ে শব্দটি গঠিত হয়েছে।
২.৪.৪ নিত্যসমাস কী? একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: নিত্যসমাস হল এমন এক বিশেষ সমাস যেখানে শব্দযুগল সর্বদা একত্রে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এদের জন্য আলাদা কোনো ব্যাসবাক্য থাকে না, তাই সেগুলোর অর্থ বোঝাতে সাধারনত একটি ব্যাসবাক্য বা অন্য পদের সহায়তা নেওয়া হয়। উদাহরণ – অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর।
২.৪.৫ অনেক জিনিসই সুলভ নয়। ইতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো।
উত্তর: “অনেক জিনিসই সুলভ নয়” বাক্যটিকে ইতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয় “অনেক জিনিসই দুষ্প্রাপ্য” বা “অনেক জিনিসই দুর্লভ”।
২.৪.৬ যোগ্যতাহীন বাক্যের একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: “যোগ্যতাহীন বাক্যের একটি উদাহরণ হলো: ‘বর্ষার রোদে প্লাবনের সৃষ্টি হয়’। এই বাক্যটি যৌক্তিকভাবে ভুল, কারণ রোদের কারণে প্লাবন হয় না, যা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।”
২.৪.৭ বিধেয় প্রসারকের একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: ‘আমার ছোট ভাই কচি ও সবুজ আম খাচ্ছে’— এই বাক্যটি বিধেয় প্রসারণের একটি উদাহরণ। এখানে ‘কচি ও সবুজ আম’ অংশটি বিধেয় প্রসারকের কাজ করছে, যা মূল ক্রিয়া ‘খাচ্ছে’ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য যুক্ত করে তা প্রসারিত করছে।
২.৪.৮ ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের সময় বিভক্তিগত পরিবর্তনটি উল্লেখ করো।
উত্তর: “ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তনের সময় কর্তার সঙ্গে প্রথমা বিভক্তি (০ বিভক্তি) ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার পুরুষ, বচন ও কাল অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়।”
২.৪.৯ ‘গভীরভাবে সংকল্প করে তপন,’ কর্মবাচ্যে পরিবর্তন করো।
উত্তর: “গভীরভাবে সংকল্প করে তপন” বাক্যটির কর্মবাচ্যে রূপ হল – ‘তপন দ্বারা গভীরভাবে সংকল্প করা হলো’।
২.৪.১০ এখন আপনার কী খাওয়া হবে? বাক্যটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
উত্তর: “এখন আপনার কী খাওয়া হবে?” – এই বাক্যটি কর্মবাচ্যের একটি উদাহরণ।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ ‘আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়ো?’ কাকে একথা বলা হয়েছে? তাকে একথা বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়ো?’—এই উক্তিটি বিরাগীবেশী হরিদা জগদীশবাবুকে উদ্দেশ করে বলেছেন।
সাধুবেশে হরিদা যখন জগদীশবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হন, তখন সাধুসঙ্গপ্রিয় জগদীশবাবু তাঁকে দেখে খুব আনন্দিত হন এবং স্বাগত জানান। কিন্তু সেই সময় জগদীশবাবু বারান্দায় একটি চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি সেখান থেকে উঠে এসে সাধুকে প্রণাম বা যথাযথ সম্মান জানাননি।
এই আচরণ হরিদার কাছে অসম্মানের বলে মনে হয়। তাঁর ধারণা হয়, বিপুল সম্পদের জন্য জগদীশবাবু অহংকারী হয়ে উঠেছেন এবং নিজেকে যেন ভগবানের চেয়েও ঊর্ধ্বে ভাবছেন। তাই বিরক্ত হয়ে হরিদা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন— “আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়ো?”
৩.১.২ ‘তিনি ঢের বেশি আমার আপনার।’ বক্তার আপনজন কে? বক্তা কেন এমন কথা বলেছেন?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘পথের দাবী’ উপন্যাসটির পটভূমি হলো স্বদেশি আন্দোলন। পরাধীন ভারতবর্ষকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য যে স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, সব্যসাচী ছিলেন তাদেরই প্রতিচ্ছবি। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য তিনি ছিলেন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও সদাসর্বদা প্রস্তুত। ‘পথের দাবী’ পাঠ্যাংশে আমরা দেখি, সব্যসাচী গিরীশ মহাপাত্রের ছদ্মবেশ ধারণ করে কীভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পরোক্ষভাবে তাদেরকে বিদ্রূপ করেই পালাতে সক্ষম হন। পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতেই তিনি এ ধরনের ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতেন। স্বদেশি আদর্শে বিশ্বাসী অপূর্ব অন্তর থেকে সমর্থন করত সব্যসাচীকে। অপূর্ব জানত, সব্যসাচীর এই সংগ্রাম দেশের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসারই প্রকাশ; এই মহান দেশকে স্বাধীন করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। সব্যসাচীকে গ্রেপ্তারে পুলিশের তৎপরতা ছিল চরমে। দেশের অর্থে পুষ্ট হয়ে, দেশের লোক দিয়েই তারা সব্যসাচীকে শিকারের মতো তাড়া করছিল। অন্যদিকে, পুলিশকর্তা নিমাইবাবু ছিলেন অপূর্বর আত্মীয়; অপূর্ব তাকে ‘কাকা’ বলে ডাকত। এই সম্পর্কের কারণে অপূর্ব নিজেও ছিল গভীর লজ্জা ও অপমানবোধে জর্জরিত। সেই লজ্জা থেকেই অপূর্বর উচ্চারণ দেশ ও দেশবাসীকে যে এই লাঞ্ছনা ও অধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চায়, সেই সব্যসাচী অপূর্বর নিকট আত্মীয়স্বজন এমনকি নিমাই কাকার থেকেও অনেক বেশি আপন এবং কাছের মানুষ।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ ‘অসুখী একজন’ কবিতায় কার মাথার ওপর বছরগুলি কেন পর পর পাথরের মতো নেমে এসেছিল?
উত্তর: ‘অসুখী একজন’ কবিতায় কবি তার প্রিয় মানুষটিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে অপেক্ষায় রেখে চিরতরে চলে গেলেও, সে জানত না যে কবি আর কখনো ফিরে আসবেন না। তাই, তার প্রিয় মানুষটি দরজার পাশে অপেক্ষা করতেই থাকে। সময় কেটে যায়—একটা সপ্তাহ, একটা বছর, আর তারপর একটার পর একটা বছর পাথরের মতো করে তার মাথার ওপর নেমে আসে। এই বেদনাদায়ক অনুভূতিই কবির কথায় ফুটে উঠেছে –
‘আর একটার পর একটা, পাথরের মতো
পর পর পাথরের মতো, বছরগুলো
নেমে এল তার মাথার ওপর।’
৩.২.২ ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।’ কার, কোন কবিতার পঙ্ক্তি? এমন মন্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: “জলই পাষাণ হয়ে আছে’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত শঙ্খ ঘোষের ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতাটি যুদ্ধবিধ্বস্ত, বিপন্ন ও আশ্রয়হীন মানুষের প্রতি এক গভীর সহমর্মিতার দলিল। সমাজে ধ্বংস, হিংসা, শোষণ ও অবিচার যখন সর্বগ্রাসী রূপ নেয়, মানুষের অস্তিত্ব যখন চরম সংকটে পড়ে, ঠিক তখনই কবি একত্রিত হয়ে বেঁচে থাকার এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’—এই সরল গভীর আহ্বান একদিকে যেমন মানবিক বন্ধন ও সংহতির কথা বলে, অন্যদিকে তেমনই একটি সংগ্রামী চেতনারও ইঙ্গিতবাহী; পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার।”
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ “তপন আর পড়তে পারে না। বোবার মতো বসে থাকে।” তপনের এরকম অবস্থার কারণ বর্ণনা করো।
উত্তর: “জ্ঞানচক্ষু” আশাপূর্ণা দেবীর রচিত একটি গল্প। এই গল্পের নায়ক তপন লেখক হতে চান। তাঁর ধারণা ছিল, লেখকেরা সাধারণ মানুষ নন; তাঁরা মহাজ্ঞানী, অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু নতুন মেসোমশায়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর এই ধারণা বদলে যায়। মেসোমশায়ের উৎসাহে তপন একটি গল্প লেখে এবং মেসোমশাই সেই গল্পটি ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় ছাপানোর প্রতিশ্রুতি দেন। পত্রিকায় গল্পটি ছাপা হওয়ার পর, তপন তা পড়ে হতবাক হয়ে যান। গল্পের প্রতিটি লাইন নতুন ও সুন্দরভাবে সাজানো। তপন নিজের লেখা গল্পটিকে চিনতেই পারলেন না। তাঁর মনে হল, এটা তাঁর লেখা গল্পই নয়। নিজের গল্পের এমন আমূল পরিবর্তন দেখে তপন অত্যন্ত দুঃখিত ও অপমানিত বোধ করেন। তিনি বুঝতে পারেন, মেসোমশাই তাঁর গল্পের সর্বত্রই সংশোধন (কারেকশন) করে দিয়েছেন। এই অবস্থায় গল্পটি আর পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি বাকরুদ্ধের মতো নিঃশব্দে বসে রইলেন।
৪.২ “নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে।” নদীর বিদ্রোহের কারণ কী ছিল? ‘সে’ কীভাবে তা বুঝতে পেরেছিল?
উত্তর: নদীর বিদ্রোহের কারণ ছিল মানুষের তৈরি বাঁধ ও নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো। শুকনো নদী টানা পাঁচ দিনের বৃষ্টিতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে এবং তীব্র স্রোতবান হয়ে ওঠে। মানুষ প্রযুক্তির সাহায্যে নতুন সেতু বানিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। এই নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধ। ফলস্বরূপ, নদী যেন প্রতিশোধ নিতে চায় এবং তার রুদ্ররূপ ধারণ করে মানুষের অহংকারের প্রতীক ওই সেতু ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। নদীর উন্মত্ত জলধারার মধ্যে দিয়ে সে যেন অনুভব করতে পেরেছিল প্রকৃতির রোষ। মানুষের অহেতুক হস্তক্ষেপ ও অহংকার প্রকৃতির মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, তা সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই সে নদীর এই বিদ্রোহকে কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বরং একটি ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ হিসেবেই অনুভব করেছিল।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ “আমি এখন হাজার হাতে পায়ে / এগিয়ে আসি,” ‘আমি’ কে? ‘হাজার হাত পা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে। কবির মনোভাব ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: উক্ত অংশটি বাংলার আধুনিক কবি জয় গোস্বামীর “অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতা থেকে উদ্ধৃত। এখানে ‘আমি’ বলতে কেবল কবিতার কথককে নয়, বরং অস্ত্রের ভয়কে অগ্রাহ্য করা এক সাধারণ মানুষের মুখপাত্রকে বোঝানো হয়েছে, যে একসাথে অসংখ্য মানুষের প্রতীক।
ব্যক্তি মানুষ ক্ষুদ্র, কিন্তু যখন মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে তখন সে অসীম শক্তির অধিকারী হয়। এই ঐক্যের শক্তিকেই কবি প্রকাশ করেছেন “হাজার হাতে-পায়ে” চিত্রকল্পে। অর্থাৎ, এটি সম্মিলিত মানবতার প্রতীকী রূপ। অস্ত্র ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু মানুষের ঐক্যবদ্ধ মানসিক শক্তি তাকে পরাভূত করতে পারে। তাই কবি দৃপ্ত স্বরে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি হাজার হাতে-পায়ে এগিয়ে আসেন, উঠে দাঁড়ান এবং গুলির সামনে অবিচল থাকেন। এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় কবির মনোভাব—তিনি বিশ্বাস করেন অস্ত্রের চেয়ে মানবতার শক্তিই শ্রেষ্ঠ, আর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই প্রকৃত মুক্তির পথ।
৫.২ ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
উত্তর: “বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় ‘প্রলয়োল্লাস’ শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ‘প্রলয়’ অর্থ সম্পূর্ণ ধ্বংস বা বিনাশ, আর ‘উল্লাস’ অর্থ আনন্দের তীব্র বহিঃপ্রকাশ বা উৎফুল্লতা। এই কবিতায় দুটি বিপরীতার্থক শব্দকে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে। বর্তমান সমাজে যেখানে সর্বত্র বিরাজ করছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জাতিগত বিভেদ, কুসংস্কার – এমন এক জরাগ্রস্ত সমাজের কঠিন পরিস্থিতিতে কবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে এই সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধ্বংসের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর, সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ নতুন সমাজ। মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন সমাজ নির্মাণের আনন্দই কবির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রলয় এখানে কালবৈশাখীর রূপ নিয়ে প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তিতে, বজ্রশিখার মশাল হাতে সমাজে আবির্ভূত হয়েছে। এর ভয়ংকর হাসি, উন্মত্ততা ও ধ্বংসাত্মক রূপ তুলনীয় দেবাদিদেব মহাদেবের নটরাজ নৃত্যের সঙ্গে। মহাকালের সারথির বেশে প্রলয় এই সমাজের সকল আনুষ্ঠানিকতা ও গতানুগতিকতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে অমানিশার অবসান ঘটাবে; অসুন্দরকে বিলীন করবে। তাই ধ্বংসের প্রতীক হলেও, বিধ্বংসী রূপ ধারণ করলেও প্রলয় আসলে স্নিগ্ধ, মধুর ও শান্তিময় এক নতুন প্রভাতেরই সূচনা করছে। তাই এই ভয়ংকর রূপধারী প্রলয়ই আমাদের কাম্য – এটি যথার্থই সুন্দর, এবং একে সাদরে উল্লাসধ্বনির মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া উচিত। কবিতার এই নামকরণ যে সম্পূর্ণ সার্থক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।”
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ ‘কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য।’ কলম কাদের কাছে অস্পৃশ্য। কলম সম্পর্কে লেখক কেন এরকম বলেছেন?
উত্তর: “হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” রচনায় সময়ের পরিবর্তনে লেখনী সরঞ্জামের বিবর্তনকে নিখিল সরকার একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যের মাধ্যমে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আধুনিকতার স্রোতে কলম মানুষের হাত থেকে ক্রমশ অপসৃত হচ্ছে। সময়ের প্রবাহে বাঁশের কলম, পালকের কলমের স্থান দখল করে নেয় ফাউন্টেন পেন, এবং পরবর্তীতে সস্তার বলপেন বাজার কাঁপায়। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে লেখক উল্লেখ করেন যে, কলম এখন এমন সহজলভ্য যে পকেটমাররাও তা চুরি করতে আগ্রহী নয় – “কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য”।এককালে লেখার একমাত্র মাধ্যম ছিল বাঁশের কলম, যা লেখকরা নিজেরাই তৈরি করতেন শৈশবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের কলমের স্থান নেয় পালকের কলম, তারপর আসে ফাউন্টেন পেন ও বলপেনের যুগ। কলম এতটাই সাধারণ হয়ে ওঠে যে ফেরিওয়ালারাও তা বিক্রি করতে শুরু করে। লেখকের চোখে ধরা পড়ে, আধুনিক তরুণেরা বুকপকেটে নয়, বরং কাঁধের ছোট পকেটে কলম রাখে; এমনকি ভিড়ের ট্রাম বা বাসে নারীরা তাদের খোঁপাতেও কলম গুঁজে রাখেন। লেখকের ভাষায়, এটি এক ধরনের “বিস্ফোরণ – কলমের বিস্ফোরণ”। সস্তায় উৎপাদিত হওয়ার কারণে কলম সহজলভ্য ও সর্বসাধারণের হয়ে ওঠে, এবং তার প্রাচীন গৌরব হারায়। ফলে, একসময় যেসব পকেটমার নিঃসংকোচে কলম চুরি করত, তারাও এখন আর তাতে আগ্রহ দেখায় না – কলম তাদের কাছেও এখন “অস্পৃশ্য”।
৬.২ ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে পরিভাষা রচনা প্রসঙ্গে লেখক যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা আলোচনা করো।
উত্তর: রাজশেখর বসু রচিত ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পরিভাষা রচনার সমস্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অভাবের কারণে বিজ্ঞানচর্চা ব্যাহত হয়।
একসময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী লেখক বিভিন্ন বিষয়ে পরিভাষা তৈরি করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা একত্রে আলোচনা করে কাজ করেননি, তাই সেই পরিভাষাগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় ছিল না; একই বিষয়ে একাধিক ভিন্ন শব্দ গঠিত হয়েছিল।
এই অসুবিধা কাটাতে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরিভাষা সমিতি গঠন করে। এখানে বিভিন্ন শাখার জ্ঞানী ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে একত্রিতভাবে পরিভাষা সংকলন করেন। ফলে সেই সংকলনটি হয় অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও যথাযথ। তবে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন, এই কাজকে আরও বিস্তৃত আকারে করা উচিত। তাঁর মতে, যতদিন উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা তৈরি না হয়, ততদিন ইংরেজি শব্দ বাংলা বানানে লিখে ব্যবহার করাই শ্রেয়। সর্বোপরি, নতুন পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আলোচনার নিজস্ব রচনাশৈলীর দিকেও খেয়াল রাখা অপরিহার্য।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ ‘তোমার কথা আমার চিরদিনই মনে থাকবে।’ কার কথা বলা হয়েছে? কেন তার কথা বক্তার মনে থাকবে?
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটক থেকে উদ্ধৃত উক্তিতে ‘তোমার’ বলতে ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা–কে বোঝানো হয়েছে। ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করে ফরাসিদের কুঠি দখল করলে ফরাসিরা নবাব সিরাজদ্দৌলার দ্বারস্থ হয়। কিন্তু কলকাতা বিজয় ও যুদ্ধে লোকবল ও অর্থবল হ্রাস পাওয়ায় নবাব আর নতুন করে ইংরেজদের সঙ্গে শত্রুতা বাড়াতে চাননি। তখন মঁসিয়ে লা নবাবকে জানান যে, তাঁরা বাধ্য হয়ে ভারত ছাড়তে যাচ্ছেন, আর এতে ইংরেজরা সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য আক্রমণ করবে। মঁসিয়ে লা–এর এই সতর্কবাণী ছিল আন্তরিক ও সত্য। তাই নবাব তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হয়ে বলেন যে, তাঁর এই সৎ উপদেশ ও বন্ধুভাবাপন্ন সতর্কবার্তা চিরদিন তাঁর মনে থাকবে।
৭.২ ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ অবলম্বনে সিরাজদ্দৌলার চরিত্রবৈশিষ্ট্য আলোচনা করে।
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে জাতীয় মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁর চরিত্রে দেশাত্মবোধ, সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মসমালোচনার সাহস এবং দুর্বল মানসিকতার মতো নানা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট।
প্রথমত, তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বাংলার মঙ্গলকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বিদেশি শক্তির আগ্রাসন থেকে দেশকে বাঁচাতে তিনি শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করতে কিংবা অধস্তনের কাছে ক্ষমা চাইতেও দ্বিধা করেননি। দ্বিতীয়ত, তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলা কেবল মুসলমানের নয় বা হিন্দুর নয়—বরং হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিতেই ব্রিটিশদের প্রতিরোধ সম্ভব। তৃতীয়ত, সিরাজ ছিলেন আত্মসমালোচক। বাংলার বিপদের জন্য তিনি শুধু ষড়যন্ত্রকারীদের নয়, নিজের ত্রুটিকেও দায়ী করেছিলেন। তবে চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়, তিনি মানসিকভাবে কিছুটা দুর্বল ছিলেন। শত্রুর ষড়যন্ত্র বুঝলেও কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারেননি।
উপসংহার:
সব মিলিয়ে, নাট্যকার সিরাজদ্দৌলাকে দেশপ্রেমিক, ধর্মনিরপেক্ষ, আত্মসমালোচক অথচ দুর্বলতাগ্রস্ত এক মানুষ হিসেবেই চিত্রিত করেছেন। তাঁর চরিত্র আমাদের শেখায়—ব্যক্তিগত দুর্বলতা থাকলেও দেশপ্রেম ও সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত মানসিকতাই একজন মানুষকে প্রকৃত নায়কের মর্যাদা দেয়।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ ‘সাঁতার নয়, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অপমান সহ্য করার।’ কে, কাকে একথা বলেছে? কোন্ প্রসঙ্গে তার এই উক্তি?
উত্তর: সাঁতার নয়, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অপমান সহ্য করার।” — উক্তিটি মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসের কোচ ক্ষিতীশ বা খিদ্দা কোনিকে উদ্দেশ করে বলেছেন। ঘটনাটি ঘটে তখন, যখন ক্ষিতীশ দরিদ্র পরিবার থেকে আসা প্রতিভাবান মেয়ে কোনিকে নিয়ে জুপিটার ক্লাবে ভর্তি করাতে যান। ক্লাব কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে হরিচরণ ও প্রফুল্ল বসাক, কোনিকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের চোখে দেখে। তারা কোনিকে “যে-সে মেয়ে” বলে খাটো করে এবং জানিয়ে দেয় যে ক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী তাকে ট্রায়াল পরীক্ষায় বসতে হবে। হরিচরণ কোনিকে আর একবার দেখে নিয়ে, গম্ভীরস্বরে বলে , “এ ক্লাবের কাউকে স্ট্রোক শেখাতে হলে, শেখাবে ক্লাবেরই ট্রেনাররা। কাল সকালে আসুক। বন্দনা কি টুনু ওর ট্রায়াল নেবে।”
এতে ক্ষিতীশ অপমানিত হন, কিন্তু ধৈর্য ধরে অপমান সহ্য করেন।
বাইরে বেরিয়ে কোনি যখন প্রশ্ন করে—“ভর্তি হলো না?” তখন ক্ষিতীশ বলেন যে, তাদের দুজনকেই পরীক্ষা দিতে হবে। কোনি অবাক হয়ে ভাবে, কোচ কি সাঁতার জানেন না? তখনই ক্ষিতীশ বেদনাভরে বলেন, “সাঁতার নয়, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অপমান সহ্য করার।”
এই উক্তি শুধু ব্যক্তিগত দুঃখ প্রকাশ নয়, বরং সমাজে গরিব মানুষের প্রতি ধনী শ্রেণির অবজ্ঞা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক। ক্ষিতীশ বুঝিয়ে দেন—জীবনের বড় লড়াই শুধু প্রতিযোগিতায় নয়, অপমান সহ্য করে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত।
৮.২ ‘ইচ্ছে থাকলেও ওকে সাঁতার শেখাবার সামর্থ্য আমার নেই।” কে বলেছিল? বক্তার এরুপ বক্তব্যের কারণ কী?
উত্তর: বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসে উক্ত কথাটি কোনির দাদা কমল বলেছিল ক্ষিতীশ সিংহকে লক্ষ্য করে।
শ্যামপুকুর বস্তির বাসিন্দা কমল ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল মানুষ। একসময় সে অ্যাপোলো ক্লাবের দক্ষ সাঁতারু হলেও পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। অন্নসংস্থানের তাগিদে তাকে সাঁতার ছেড়ে মোটর গ্যারেজে কাজ করতে হয়। ফলে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে না পারার দুঃখ তার মনে গভীরভাবে গেঁথে যায়।
অভাবী সংসারে প্রতিদিন অন্নসংস্থানের জন্য সংগ্রাম করতে হওয়ায় কোনিকে সাঁতার শেখাবার সামর্থ্য তার ছিল না। তবে বোনকে ভালো সাঁতারু হিসেবে গড়ে তুলতে তার আগ্রহ ছিল প্রবল। এজন্যই সে ধার করে কোনিকে কস্টিউম কিনে দেয় এবং প্রতিযোগিতায় উৎসাহ জোগায়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তাকে স্বীকার করতেই হয়েছিল— অর্থনৈতিক অক্ষমতার কারণে সে নিজে কোনিকে সাঁতার শেখাতে পারবে না। তাই ক্ষিতীশ সিংহের কাছে সে এই কথা বলেছিল। – “ইচ্ছে থাকলেও ওকে সাঁতার শেখাবার সামর্থ্য আমার নেই”।
৮.৩ চিড়িয়াখানায় কোনিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে কী ঘটেছিল? এই ঘটনা থেকে ক্ষিতীশের কী মনে হয়েছিল।
উত্তর: “কোনি” উপন্যাসে ক্ষিতীশ সিংহ কোনিকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিন ঘণ্টা ঘোরার পর, তারা দুজন বাড়ি থেকে নিয়ে আসা খাবার খেতে বসে। কিন্তু তাদের সঙ্গে খাবার জল ছিল না। সেই সময় কোনি পাশে খেতে বসা একটি ছাত্রীদলের কাছে জল চাইতে যায়, কিন্তু সেই দলের একজন দিদিমণি তাকে জল না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। পরে, ওই দলের হিয়া মিত্র নামের একটি মেয়ে কোনিকে জল দিতে এলে, কোনি আগের অপমানের জবাবে সেই জলের গ্লাস ফেলে দেয়। জলের গ্লাস ফেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে হিয়ার প্রতি কোনির আক্রোশ প্রকাশ পায়। ক্ষিতীশ সিংহ কোনির মতো হিয়া মিত্রকে চিনত না, কিন্তু তিনি হিয়াকে চিনতেন। শুধু চিনতেনই না, তিনি জানতেন যে কোনির চেয়ে হিয়া মিত্র সাঁতারে অনেক বেশি দক্ষ। রবীন্দ্র সরোবরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় হিয়ার সাঁতার ক্ষিতীশ সিংহ দেখেছেন। বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবে গিয়েও হিয়ার ট্রেনিং দেখে এসেছেন। এই ঘটনা থেকে ক্ষিতীশের ধারণা হয়েছিল যে হিয়াই কোনির ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী। এই অপমানের যন্ত্রণাই কোনিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং হিয়া মিত্রকে হারিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা জাগিয়ে রাখবে। ক্ষিতীশ সিংহ কোনিকে এই অপমানটি পুষে রাখতেও বলেন, যাতে তা তাকে অনুপ্রেরণা দেয়।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো:
Home is the first school where the child learns his first lesson. He sees, hears and begins to learn at home. It is home that builds his character. In a good home honest and healthy men are made. Bad influence at home spoils a child.
উত্তর: বাড়িই হলো শিশুর প্রথম বিদ্যালয়, যেখানে সে জীবনের প্রথম পাঠ শিখে। সে বাড়িতে দেখে, শোনে এবং শেখা শুরু করে। বাড়িই তার চরিত্র গড়ে তোলে। ভালো বাড়ির পরিবেশে সৎ ও সুস্থ মানুষ তৈরি হয়। কিন্তু খারাপ প্রভাব শিশুর জীবনকে নষ্ট করে দেয়।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
বিষয় : ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত
রাহুল : অর্ণব, বল তো, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কটা কেমন হওয়া উচিত?
অর্ণব : আমার মতে, শিক্ষক হচ্ছেন ছাত্রের পথপ্রদর্শক। তাই সম্পর্কটা হওয়া উচিত পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে।
রাহুল : একেবারে ঠিক। ছাত্ররা যদি শিক্ষকের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা না দেখায়, তবে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা যায় না।
অর্ণব : আবার শিক্ষকেরও দায়িত্ব হলো ছাত্রদের প্রতি স্নেহ, ধৈর্য ও সহমর্মিতা দেখানো। শুধু পাঠদান নয়, জীবনের নীতি ও মূল্যবোধ শেখানোও জরুরি।
রাহুল : সত্যি তাই। শিক্ষক যদি বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়ান, তবে ছাত্ররা নির্ভয়ে নিজেদের সমস্যা বলতে পারে এবং সহজেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
অর্ণব : আর ছাত্রদেরও উচিত মনোযোগী হওয়া, শিক্ষকের উপদেশ মেনে চলা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
রাহুল : সঠিক বলেছিস। আসলে, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক যদি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের ওপর দাঁড়ায়, তবে শিক্ষার পরিবেশ সুন্দর ও সফল হয়।
১০.২ ‘নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী’ এ বিষয়ে সংবাদপত্রের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী
নিজেস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৫: সম্প্রতি বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। চাল, ডাল, তেল, সবজি প্রভৃতির দাম গত কয়েক সপ্তাহে দ্বিগুণের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো ভীষণভাবে সমস্যায় পড়েছে।
ক্রেতাদের অভিযোগ, পাইকারি বাজারে পর্যাপ্ত মজুত থাকলেও খুচরো বাজারে অসাধু ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ ন্যায্যমূল্যে দ্রব্য কিনতে পারছেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবহন খরচ বৃদ্ধি, জ্বালানির দাম ওঠা এবং অসাধু মজুতদারির কারণেই এই মূল্যবৃদ্ধি।
সরকার জানিয়েছে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই বাজার তদারকির জন্য বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের আশা, সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণে আসবে।
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবস্থ রচনা করো:
১১.১ মানবসভ্যতায় প্রযুক্তিবিদ্যা ও আমরা।
উত্তর:
মানবসভ্যতায় প্রযুক্তিবিদ্যা ও আমরা
ভূমিকা:
মানবসভ্যতার বিকাশে প্রযুক্তিবিদ্যা এক অপরিহার্য অঙ্গ। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন আগুন জ্বালাতে শিখল, তখন থেকেই প্রযুক্তির সূচনা। তারপর ধাপে ধাপে পাথরের হাতিয়ার, ধাতুর ব্যবহার, কৃষির উন্নতি—সবই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছে। আধুনিক যুগে এসে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি আমাদের জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।
মূল আলোচনা:
প্রযুক্তি আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখছে। যোগাযোগব্যবস্থায় মোবাইল, টেলিফোন, ইন্টারনেট মানুষকে মুহূর্তে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার, প্রজেক্টর, অনলাইন ক্লাস নতুন দিগন্ত খুলেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত চিকিৎসা মানুষকে দীর্ঘায়ু দিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক যন্ত্র, সার, কীটনাশক ও সেচব্যবস্থার উন্নতি খাদ্য উৎপাদনে বিপ্লব এনেছে। শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তি অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে আরও শক্তিশালী করেছে।
তবে প্রযুক্তির প্রভাব সবসময় ইতিবাচক নয়। এর অপব্যবহার সমাজ ও মানবসভ্যতার জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত যন্ত্রনির্ভরতা মানুষের শ্রম ও সুস্বাস্থ্য কমিয়ে দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করছে। পারমাণবিক অস্ত্র, জৈব অস্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার মানবজাতিকে ভয়াবহ বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। শিল্পায়নের ফলে পরিবেশদূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আজ বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তাই প্রযুক্তি ব্যবহারে সংযম ও দায়িত্বশীলতা প্রয়োজন। এর যথাযথ প্রয়োগই পারে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে।
উপসংহার:
সব মিলিয়ে বলা যায়, প্রযুক্তিবিদ্যা মানবসভ্যতার এক মহাশক্তি। এর সঠিক ব্যবহার আমাদের জীবনকে করে সহজ, আরামদায়ক ও আধুনিক। কিন্তু অপব্যবহার মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারে। তাই প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ করাই আমাদের মূল দায়িত্ব।
১১.২ তোমার জেলার পর্যটন কেন্দ্র।
উত্তর:
আমার জেলার পর্যটন কেন্দ্র
আমার জেলা হলো বাঁকুড়া। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহাসিক এই জেলা বহু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির ভান্ডার। তাই একে বলা হয় “বাংলার মাটির শহর”। এ জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলি শুধু স্থানীয় মানুষকেই নয়, দূর-দূরান্তের পর্যটককেও আকর্ষণ করে।
প্রথমেই উল্লেখ করা যায় বিষ্ণুপুর শহরের কথা। এই শহর প্রাচীন মল্লরাজাদের রাজধানী ছিল। এখানে রয়েছে অসংখ্য পোড়ামাটির মন্দির, যেমন—রাসমঞ্চ, শ্যামরায় মন্দির, জোরবাংলা মন্দির ইত্যাদি। সূক্ষ্ম নকশায় অলংকৃত এই মন্দিরগুলো বাংলার স্থাপত্যশৈলীর গৌরব বহন করে। এখানকার বালুচরী শাড়ি দেশ-বিদেশে খ্যাত।
জয়পুর জঙ্গলও এক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। বিস্তীর্ণ অরণ্য, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ মনোমুগ্ধকর। শরৎ কিংবা শীতকালে এখানে ভ্রমণ করলে প্রকৃতির অপরূপ রূপ উপভোগ করা যায়।
এছাড়াও মুকুটমনিপুর বাঁকুড়ার আরেকটি রত্ন। কংসাবতী নদীর ওপর নির্মিত বৃহৎ বাঁধ প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে স্বর্গতুল্য। বাঁধের বিস্তীর্ণ জলাশয়, আশপাশের পাহাড় আর সূর্যাস্তের দৃশ্য সত্যিই অপরূপ। নৌকাভ্রমণের আনন্দ পর্যটকদের আকর্ষণ করে।
সুসুনিয়া পাহাড়ও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি প্রাচীন ইতিহাস বহন করছে। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা ব্রাহ্মী লিপি ঐতিহাসিক নিদর্শন। এখানে প্রচুর ঔষধি গাছ পাওয়া যায়। বহু মানুষ ট্রেকিংয়ের জন্যও এই পাহাড়ে আসেন।
শিল্প-সংস্কৃতির দিক থেকেও বাঁকুড়া বিশেষ সমৃদ্ধ। এখানকার বিখ্যাত বাঁকুড়া ঘোড়া মাটির শিল্পকর্ম হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। গ্রামীণ হাটবাজারে আজও এই শিল্পের ঝলক দেখা যায়।
আমার জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলি যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য, তেমনি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় ভরপুর। তাই ভ্রমণপিপাসু মানুষদের কাছে বাঁকুড়া সবসময়ই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আমার গর্ব, আমি এমন একটি জেলার বাসিন্দা, যেখানে ইতিহাস, শিল্প ও প্রকৃতি একসূত্রে গাঁথা।
১১.৩ বন্ধুত্ব।
উত্তর:
বন্ধুত্ব
মানুষ সামাজিক প্রাণী। একা মানুষ কোনোদিন পূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে না। তাই জন্মের পর থেকেই মানুষ পরিবার, সমাজ ও নানা সম্পর্কের বন্ধনে জড়িয়ে থাকে। সেই সম্পর্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ও আন্তরিক সম্পর্ক হলো বন্ধুত্ব।
বন্ধুত্ব হলো দু’টি বা ততোধিক হৃদয়ের মেলবন্ধন, যেখানে নেই স্বার্থ, নেই ভেদাভেদ। সত্যিকারের বন্ধুত্ব জীবনের অমূল্য সম্পদ। বন্ধু আমাদের দুঃখের সাথি, সুখের অংশীদার। সংকটে, কষ্টে, দুঃসময়ে যে পাশে দাঁড়ায়, তাকেই প্রকৃত বন্ধু বলা যায়। এ কারণেই প্রবাদ আছে— “সঙ্কটে বন্ধু যে, সে-ই প্রকৃত বন্ধু।”
বিদ্যালয়জীবনে বন্ধুত্বের সূচনা হয়। সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে পড়াশোনা, খেলা, আনন্দ-বিনোদন জীবনের মধুর স্মৃতি হয়ে থাকে। আবার এই বয়সের বন্ধুত্ব আমাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। ভালো বন্ধু আমাদের সৎ, পরিশ্রমী ও আদর্শ মানুষ হতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে, খারাপ বন্ধুর প্রভাবে জীবনের পথ বিপথগামী হয়ে যেতে পারে। তাই বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।
ইতিহাসেও আমরা সত্যিকারের বন্ধুত্বের বহু দৃষ্টান্ত পাই। কৃষ্ণ-সুদামা কিংবা কর্ণ-দুর্যোধনের বন্ধুত্ব আজও আলোচনার বিষয়। সাহিত্যে বন্ধুত্বের সৌন্দর্য অনেক কবি-লেখক তুলে ধরেছেন। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন— “বন্ধু, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ।”
আধুনিক সমাজে বন্ধুত্ব আরও বিস্তৃত আকার নিয়েছে। আজ ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্তে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠছে। তবে ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের চেয়ে বাস্তব জীবনের বন্ধুত্বই অধিক মূল্যবান, কারণ সেখানে থাকে প্রত্যক্ষ সহানুভূতি ও সহযোগিতা।
সত্যিকার বন্ধুত্ব নিঃস্বার্থ ও স্থায়ী। এর মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনের কষ্ট লাঘব করে, সাহস পায়, আশা জাগায়। জীবনে অনেক কিছু হারালেও যদি একজন প্রকৃত বন্ধু পাশে থাকে, তবে সে মানুষ আবার নতুন করে জীবন গড়তে পারে।
বন্ধুত্ব মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তা আমাদের জীবনকে করে আনন্দময়, করে শক্তিশালী। তাই আমাদের উচিত সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং তা রক্ষা করা। কারণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বন্ধু আমাদের আশ্রয়, ভরসা ও আলোর দিশারি।
১১.৪ বাংলার উৎসব
উত্তর:
বাংলার উৎসব
বাংলা যেন উৎসবের দেশ। ঋতুবৈচিত্র্যে ভরা এই বাংলার মানুষের জীবনে উৎসবের ভূমিকা অপরিসীম। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই উৎসব মানুষের মনে আনন্দের ঢেউ তোলে। এই উৎসবগুলো শুধু বিনোদনের নয়, মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যেরও প্রতীক।
বাংলার সবচেয়ে বড়ো উৎসব হলো দুর্গাপূজা। আশ্বিন মাসে চারদিন ধরে চলে এই মহোৎসব। পাড়া-মহল্লায়, ক্লাবে, ঘরে ঘরে মণ্ডপ সাজে। দেবীর প্রতিমা, শিল্পকলা, আলোকসজ্জা, সব মিলিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে গোটা বাংলা। শারদোৎসব বাঙালির কাছে এক পরম মিলনমেলা।
শুধু দুর্গাপূজা নয়, বাংলায় আরও বহু উৎসব পালিত হয়। দোলযাত্রা বা হোলি বসন্তের আগমনে মানুষকে রঙে রঙিন করে তোলে। রথযাত্রা বিশেষত গ্রামীণ জনজীবনে ভক্তির আবহ তৈরি করে। কালীপূজা, সরস্বতীপূজা ও লক্ষ্মীপূজাও বাঙালির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল-আজহা উৎসবও সমান উৎসাহে পালিত হয়। এ ছাড়া মহরমও বাংলায় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়।
বাংলার কৃষিজীবনকে ঘিরেও বহু উৎসবের প্রচলন আছে। নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ গ্রামীণ জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এদিন হালখাতা খোলা হয়, ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের মিষ্টি খাওয়ায়। নবান্ন উৎসব ধানের নতুন ফসল ঘরে ওঠার আনন্দে পালিত হয়। এ সব উৎসব মানুষের সঙ্গে মাটির সম্পর্ককে গভীর করে।
এছাড়া স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী প্রভৃতি জাতীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবও বাংলার মানুষ গভীর আবেগের সঙ্গে পালন করে।
বাংলার উৎসব শুধু আনন্দের উপলক্ষ নয়, সমাজজীবনের বন্ধনও দৃঢ় করে। উৎসবের সময় মানুষ ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হয়। পাড়ায়, গ্রামে, শহরে সব জায়গায় উৎসব সৃষ্টি করে ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ।
বাংলার উৎসব বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতিকে বহুমাত্রিক রঙে রাঙিয়ে তোলে। এই উৎসবগুলোই বাঙালির প্রাণশক্তি ও ঐক্যের প্রতীক। তাই বলা যায়, উৎসব ছাড়া বাংলা কল্পনাই করা যায় না।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।