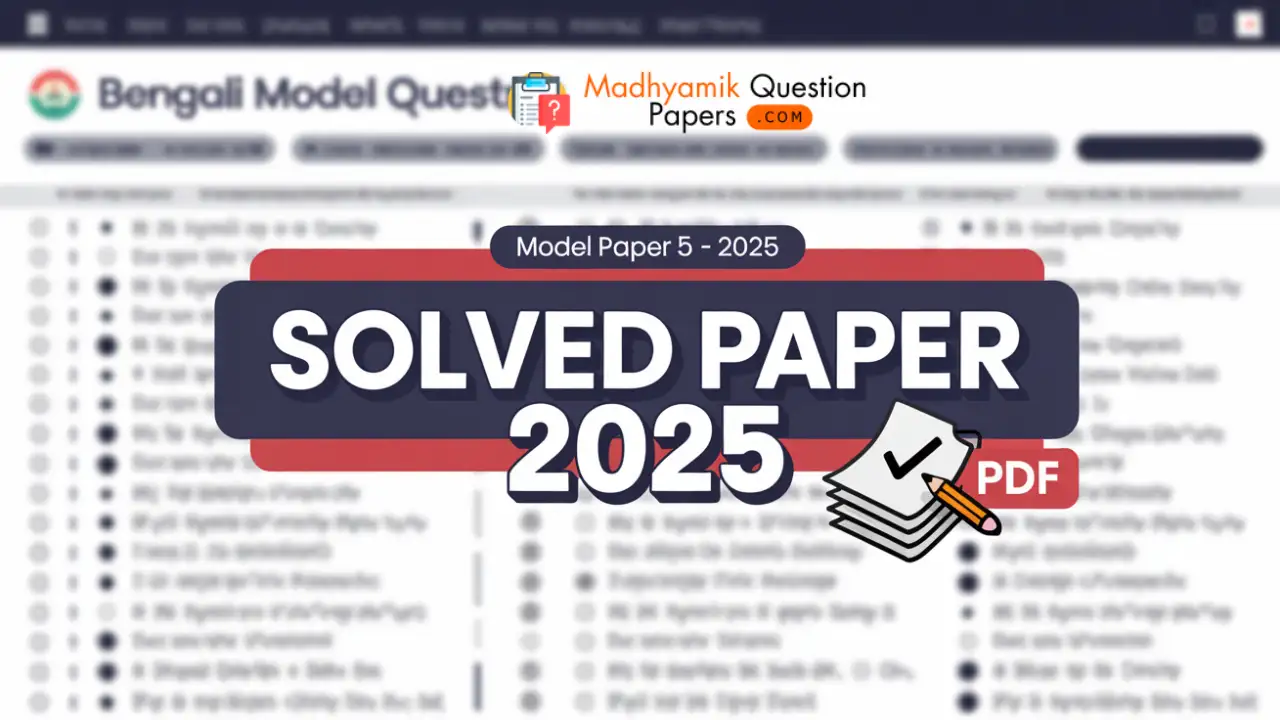আপনি কি ২০২৫ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 5 (2025) এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা Model Question Paper 5 (2025)-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৫ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়া তপনের গল্পটির নাম
(ক) ‘ইস্কুলের গল্প’
(খ) ‘একদিন’
(গ) ‘প্রথম দিন’
(ঘ) ‘রাজার কথা’
উত্তর: (গ) ‘প্রথম দিন’
১.২ এক সন্ন্যাসী এসে জগদীশবাবুর বাড়িতে ছিলেন
(ক) চারদিন,
(খ) তিনদিন,
(গ) সাতদিন,
(ঘ) পাঁচদিন
উত্তর: (গ) সাতদিন
১.৩ ‘সে কী মুষলধারায় বর্ষণ’ পাঁচদিনের বর্ষণের পর কতক্ষণ বর্ষণ থেমেছিল?
(ক) একঘণ্টা,
(খ) দুই ঘণ্টা,
(গ) তিন ঘণ্টা,
(ঘ) চার ঘণ্টা।
উত্তর: (গ) তিন ঘণ্টা
১.৪ শঙ্খ ঘোষের প্রকৃত নাম-
(ক) প্রিয়দর্শী ঘোষ,
(খ) নিত্যপ্রিয় ঘোষ,
(গ) নিত্যগোপাল ঘোষ,
(ঘ) চিত্তপ্রিয় ঘোষ।
উত্তর: (ঘ) চিত্তপ্রিয় ঘোষ
১.৫ “তোরা সব জয়ধ্বনি কর।”‘তোরা’ কারা?
(ক) দেশের যুবসমাজ,
(খ) কুসংস্কার আচ্ছন্ন দেশবাসী,
(গ) প্রবীণদের দল,
(ঘ) ছাত্রছাত্রী।
উত্তর: (খ) কুসংস্কার আচ্ছন্ন দেশবাসী
১.৬ “আমার শুধু একটা কোকিল” এই ‘কোকিল’টি হল
(ক) কবির অনুভূতির জগৎ,
(খ) বসন্তের দূত,
(গ) এক ঋষিবালক,
(ঘ) একটি গ্রামের মানুষ।
উত্তর: (ক) কবির অনুভূতির জগৎ
১.৭ ‘লিপিশিল্প’ কথাটির সঙ্গে কার নাম সংযুক্ত?
(ক) সত্যজিৎ রায়,
(খ) সন্দীপ রায়,
(গ) ভারতচন্দ্র,
(ঘ) সমরেশ বসু
উত্তর: (ক) সত্যজিৎ রায়
১.৮ আমাদের দেশে তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সুসাধ্য হবে, যখন এ দেশে
(ক) বাংলায় প্রচুর পারিভাষিক শব্দ তৈরি হবে,
(খ) বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ঘটবে,
(গ) মাতৃভাষার প্রতি মানুষের প্রীতির মনোভাব গড়ে উঠবে,
(ঘ) লেখকেরা অনুবাদের আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
উত্তর: (খ) বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ঘটবে
১.৯ দোয়াতে তৈরি কালির একটি বাহারি নাম হল
(ক) সুকন্যা,
(খ) সুরেখা,
(গ) সুরেলা,
(ঘ) সুলেখা।
উত্তর: (ঘ) সুলেখা
১.১০ তিলে তেল হয়, দুধে ছানা এটি
(ক) তারতম্যবাচক অপাদান,
(খ) বিবৃতিবাচক অপাদান,
(গ) অবস্থানবাচক অপাদান,
(ঘ) স্থানবাচক অপাদান।
উত্তর: (খ) বিবৃতিবাচক অপাদান
১.১১ অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাকে বলা হয়
(ক) প্রযোজ্য কর্তা,
(খ) প্রযোজক কর্তা,
(গ) নিরপেক্ষ কর্তা,
(ঘ) ব্যতিহার কর্তা।
উঠল: (গ) নিরপেক্ষ কর্তা
১.১২ যে সমাসে সমস্যমান পদদুটির উভয়পদই বিশেষ্য ও পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে বলে-
(ক) তৎপুরুষ সমাস,
(খ) কর্মধারয় সমাস,
(গ) দ্বন্দু সমাস,
(ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস
উত্তর: (খ) কর্মধারয় সমাস
১.১৩ ‘পুরুষসিংহ’ শব্দটির ব্যাসবাক্য হল
(ক) সিংহের ন্যায় পুরুষ,
(খ) পুরুষের ন্যায় সিংহ,
(গ) পুরুষ রূপ সিংহ,
(ঘ) পুরুষ সিংহের ন্যায়।
উত্তর: (ঘ) পুরুষ সিংহের ন্যায়
১.১৪ ‘সাপেক্ষ পদ’ কী জাতীয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়?
(ক) সরল বাক্যে,
(খ) জটিল বাক্যে,
(গ) যৌগিক বাক্যে,
(ঘ) প্রশ্নসূচক বাক্যে
উত্তর: (খ) জটিল বাক্যে
১.১৫ ভাত দিয়ে হাত খাও। এই বাক্যে অভাব
(ক) যোগ্যতার,
(খ) আকাঙ্ক্ষার,
(গ) সমাপিকা ক্রিয়ার,
(ঘ) আসত্তির।
উত্তর: (ক) যোগ্যতার
১.১৬ তাকে টিকিট কিনতে হয়নি-বাক্যটির কর্তৃবাচ্যের রূপ হল-
(ক) তার টিকিট কেনা হয়নি,
(খ) তিনি টিকিট কেনেননি,
(গ) তার দ্বারা টিকিট ক্রীত হয়নি,
(ঘ) তিনি বিনা টিকিটে চলেছেন।
উত্তর: (খ) তিনি টিকিট কেনেননি
১.১৭ ‘জন্ম নিল ফাউন্টেন পেন।’ উদাহরণটি হল
(ক) ভাববাচ্য,
(খ) কর্মবাচ্য,
(গ) কর্তৃবাচ্য,
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য।
উত্তর: (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ ‘মনে হলে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।’ কোন্ কথা মনে করে অপূর্বর এই মনোবেদনা?
উত্তর: অপূর্ব বিনাদোষে ফিরিঙ্গি যুবকদের হাতে মার খাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত ভারতীয়রা অভ্যেসবশত এর কোনো প্রতিবাদ করেনি । এই কথা মনে করেই অপূর্বর এই মনোবেদনা ।
২.১.২ ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদেরচাঁদ কে?
উত্তর: ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদেরচাঁদ হলো- ত্রিশ বছর বয়সী একজন ষ্টেশনমাস্টার। নদীর প্রতি তার ভালোবাসা, তার অনুভূতি এবং উপলব্ধি হল গল্পের মূল বিষয়।
২.১.৩ ‘আবেগ ভরা গলায় হাসান বললেন,…’- হাসান কী বলেছিলেন?
উত্তর: আবেগ ভরা গলায় হাসান বলেছিলেন, তিনি একুশ জনকেও পালন করতে রাজি আছেন
যদি অমৃতের মতো ছেলে পাই ।
২.১.৪ “শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন,” সংকল্পটি কী?
উত্তর: তপনের সংকল্প:
তপন এই দুঃখের দিনে দাঁড়িয়ে সংকল্প করে যে, যদি সে কোনোদিন তার লেখা ছাপাতে দেয়, তাহলে সে নিজে গিয়েই নিজের কাঁচা লেখা জমা দেবে — তা ছাপা হোক বা না হোক।
২.১.৫ হরিদার বিরাগী বেশ কীরূপ ছিল?
উত্তর: এক মনোরম সন্ধ্যায় জগদীশবাবু বাড়ির বারান্দায় একটি চেয়ারে বসেছিলেন। তখনই বিরাগীর বেশধারী হরিদার আগমন ঘটে। ধবধবে সাদা উত্তরীয় গায়ে, ছোটো বহরের সাদা থান পরা হরিদাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন জগতের সীমার ওপার থেকে হেঁটে এসেছেন।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ “ঘুচাব এ অপবাদ,” কোন্ অপবাদের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: রামচন্দ্রের সঙ্গে লঙ্কার ঘোরতর যুদ্ধে লঙ্কার মহা-মহা রথীদের মৃত্যু ঘটছিল। এই যুদ্ধে রাবণের আর এক বীর পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু ঘটে এবং রাবণের আর এক ভাই, শূলী কুম্ভকর্ণেরও মৃত্যু হয়।
এইসব মৃত্যুই রাবণকে মহাশোকে আচ্ছন্ন করে তোলে। মহাশোকে দগ্ধ হয়ে রাবণ নিজেই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।
তবুও, এই বিপদের মুহূর্তে রাবণের শ্রেষ্ঠপুত্র বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিৎ আমোদ-প্রমোদে মেতে ছিলেন—নিজের স্ত্রী ও তাঁর সখীদের সঙ্গে।
এই দুর্দিনে তাঁর পিতার পাশে থাকার কথা থাকলেও, তিনি ছিলেন না।
এই কারণেই বক্তার কাছে ইন্দ্রজিতের এই আচরণ ছিল অপবাদের বিষয়
২.২.২ ‘কালবোশেখির ঝড়’-কে ‘নূতনের কেতন’ বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: কালবৈশাখী ঝড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও তা পুরাতনকে ধ্বংস করে নূতনের আগমনের সংকেত বহন করে।
এই কারণেই কবি কালবৈশাখীকে বলেছেন ‘নূতনের কেতন’।
তার দাপট ও ধ্বংসের মধ্যেও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বার্তা লুকিয়ে থাকে।
২.২.৩ “শ্রীযুত মাগন গুণী”- ‘মাগন গুণী’ কে?
উত্তর: মাগন ছিলেন রোসাঙরাজ নরপতির বিশ্বস্ত মন্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর পর মাগন রাজার মুখ্য পাত্ররূপে নিযুক্ত হন। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে থদো-মিনতারের মৃত্যু হলে মাগন, রাজার নাবালক পুত্র চন্দ্রসুধর্মার অভিভাবক হিসেবে, বিধবা রাজপত্নীকে রাজকার্যে সাহায্য করেন। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে বা তার পরবর্তী কোনো সময়ে মাগন ঠাকুরই আলাওলকে আরাকানের অমাত্যসভায় আনেন। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ, শাস্ত্রজ্ঞানী, বিদ্যোৎসাহী, কাব্যরসিক এবং সাহিত্যসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক।
২.২.৪ “মাথায় কত শকুন বা চিল”- ‘শকুন বা চিল’ শব্দটি কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর: ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় শকুন ও চিল এই দুটি মাংসাশী পাখিকে যুদ্ধবাজ, ক্ষমতালিপ্সু ও সুযোগসন্ধানী মানুষের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংখ্যায় তারা অল্প হলেও, মানবইতিহাসে তাদের উপস্থিতি চিরকালীন ও উল্লেখযোগ্য।
২.২.৫ পাবলো নেরুদার প্রকৃত নাম লেখো।
উত্তর: পাবলো নেরুদার প্রকৃত নাম ছিল “নেফতালি রিকার্ডো রেয়েস বাসোয়াল্টো”
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘দোয়াত যে কত রকমের হতে পারে,’ কতরকমের দোয়াতের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: হারিয়ে যাওয়া কালি কমল ‘ প্রবন্ধে লেখক কাচের, মাটির , কাট গ্লাসের , শ্বেতপাথরের , জেডের ,পোর্সেলিনের, পিতলের , ব্রোঞ্জের ভেড়ার শিংয়ের ও সোনার তৈরি দোয়াতের কথা বলেছেন ।
২.৩.২ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় বাধা কোথায়?
উত্তর: ১. বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শেখার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ বা পরিভাষা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি।
২. শিক্ষিত মানুষদের মাঝে অনেকেই মনে করে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ভালোভাবে প্রকাশ করা যায় না, তাই তারা বাংলা বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী নয়।
এগুলোই মূল কারণ, যার জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় বাধা রয়েছে।
২.৩.৩ ‘এই রকম ভুল লেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনিষ্টকর।’ ভুল লেখাটি কী?
উত্তর: ভুল লেখাটি হল–অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তারা জীবের বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ মাত্র। তবে ওজন গ্যাস স্বাস্থকর।
২.৩.৪ ‘তাই নিয়ে আমাদের প্রথম লেখালেখি।’ কী নিয়ে লেখকদের প্রথম লেখালেখি?
উত্তর: বাঁশের কলম, মাটির দোয়াত, ঘরে তৈরি কালি আর লেখার কলাপাতা নিয়ে লেখকদের প্রথম লেখালেখি।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ ‘মেঘে বৃষ্টি হয়।’ রেখাঙ্কিত পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
উত্তর: ‘মেঘে বৃষ্টি হয়।’
মেঘে — অধিকরণ কারক, সপ্তমী বিভক্তি।
২.৪.২ অনুসর্গ বলতে কী বোঝো? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে সকল শব্দ বা অব্যয় বাক্যের মধ্যে অবস্থিত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের পরে আলাদাভাবে বসে শব্দ বিভক্তির কাজ করে তাদের অনুস্বর্গ বা পরসর্গ বলে ।
অনুসর্গ বলতে এমন একটি অব্যয় পদকে বোঝায়, যা একটি শব্দের পরে বসে সেই শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক স্থাপন করে।
সংজ্ঞা:
যে অব্যয় পদ শব্দের পরে বসে এবং তার সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক বোঝায়, তাকে অনুসর্গ বলে।
উদাহরণ:
ঘরের ভিতরে, গাছের নিচে, রাহুলের সঙ্গে, বিদ্যালয়ের পরে।
২.৪.৩ না-তৎপুরুষ ও না-বহুব্রীহি সমাসের মূল পার্থক্য লেখো।
উত্তর: না-তৎপুরুষ- যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে ‘না’ বা ‘ন’ যুক্ত থাকে এবং পরপদের ওপর জোর পড়ে।
না-বহুব্রীহি- যে বহুব্রীহি সমাসে ‘না’ বা ‘ন’ যুক্ত থাকে এবং সমাসবদ্ধ পদ অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝায়।
২.৪.৪ ‘আমরা ভিখারি বারোমাস।’ রেখাঙ্কিত পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: ভিখারি বারোমাস — ব্যাসবাক্য: আমরা বারো মাস ভিখারি।
সমাসের নাম: কর্মধারয় সমাস।
২.৪.৫ অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলতে কী বোঝো? উদাহরণ দাও।
উত্তর: অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলতে এমন বাক্য বোঝায়, যার দ্বারা কারো প্রতি অনুমতি বা অনুমোদন প্রকাশ করা হয়।
সংজ্ঞা:
যে বাক্যে অনুরোধ বা অনুমতির ভাব প্রকাশ পায়, তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে।
উদাহরণ:
১: তুমি এখন যেতে পারো।
২: খেলতে দাও ওকে।
৩: প্রশ্ন করো, আমি উত্তর দিচ্ছি।
২.৪.৬ “নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে।” জটিল বাক্যে পরিণত করো।
উত্তর: জটিল বাক্যে পরিণত রূপ:
সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, নদীর বিদ্রোহের কারণ কী।
এখানে “যে নদীর বিদ্রোহের কারণ কী” — এটি একটি উপবাক্য, যা মূল বাক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জটিল বাক্য গঠন করেছে।
২.৪.৭ ‘তপন গড়গড়িয়ে পড়ে যায়।’ ভাববাচ্যে পরিণত করো।
উত্তর: ভাববাচ্যে পরিণত রূপ:
তপনের দ্বারা গড়গড়িয়ে পড়ে যাওয়া হয়।
২.৪.৮ সম্বন্ধপদ ও সম্বোধন পদের পার্থক্য কী?
উত্তর: সম্বন্ধপদ
- সংজ্ঞা-যে পদ দ্বারা দুটি বা ততোধিক পদের মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো হয়, তাকে সম্বন্ধপদ বলে।
ব্যবহার
- এটি সাধারণত নামের আগে বা পরে ব্যবহৃত হয়ে সম্পর্ক বোঝায়।
সম্বোধনপদ
- সংজ্ঞা: যে পদ দ্বারা কাউকে ডাকা বা সম্বোধন করা হয়, তাকে সম্বোধনপদ বলে।
ব্যবহার
- এটি বাক্যের শুরুতে বা মাঝে ব্যবহৃত হয়, ডাকার উদ্দেশ্যে।
২.৪.৯ ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের একটি শর্ত লেখো।
উত্তর: ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের শর্ত
যে কাজটি হচ্ছে, সেই কাজটি কে করছে—তা নির্দিষ্ট করে দিতে হয়।
নিয়ম অনুযায়ী:
ভাববাচ্য বাক্যে কর্তা অস্পষ্ট থাকে। তাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে কর্তার দ্বারা কাজ হওয়া প্রকাশ করলে বাক্যটি কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত হয়।
উদাহরণ (নিয়ম অনুযায়ী):
ভাববাচ্য: পাঠটি পাঠ করা হচ্ছে।
কর্তৃবাচ্য: শিক্ষক পাঠটি পাঠ করছেন।
২.৪.১০ ভাববাচ্যে কর্তা লুপ্ত অবস্থায় আছে (লুপ্ত কর্তা ভাববাচ্য), এরকম একটি বাক্য লেখো।
উত্তর: ভাববাচ্যে কর্তা লুপ্ত অবস্থায় আছে (লুপ্ত কর্তা ভাববাচ্য), এরকম একটি বাক্য হলো – “বইটা পড়া হলো।”
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উন্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ ‘বিকেলে চায়ের টেবিলে ওঠে কথাটা।’ বিকেলে চায়ের টেবিলে কোন্ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছিল?
উত্তর: “বিকেলের চায়ের আসরে তপনের ছোটমেসো তপনের একটি লেখা ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন—সেই কথাই আলোচনার বিষয় ছিল।”
৩.১.২ “যাঁকে খুঁজছেন তাঁর কালচরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।” ‘কালচর’ বলতে কী বোঝো? কালচরের কথা ভাবতে বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: ‘কালচার’ একটি ইংরেজি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ ‘সংস্কৃতি’। মানুষের লেখাপড়া, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ—সবই কালচারের অন্তর্ভুক্ত।
‘পথের দাবী’ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র অপূর্ব আগে থেকেই পুলিশের বড়কর্তা নিমাইবাবুর মুখে বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিক সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন। তিনি সব্যসাচীর শিক্ষাদীক্ষা, ব্যক্তিত্ব, চাতুর্য এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শিতার কথা জেনে মনে মনে ধারণা করেছিলেন যে সব্যসাচী একজন শিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিসম্মত ব্যক্তি।
তিনি মনে করেছিলেন, একজন মুক্তিপথের অগ্রদূত হিসেবে সব্যসাচী দেশে-বিদেশে নানা বিদ্যা অর্জন করেছেন এবং বহু ভাষায় দক্ষ। ফলে তাঁর বেশভূষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদিও নিঃসন্দেহে উন্নতমানের হবে—এই ছিল অপূর্বর ভাবনা।
কিন্তু বাস্তবে সব্যসাচী মল্লিক ওরফে গিরীশ মহাপাত্র-এর ভগ্নস্বাস্থ্য, অদ্ভুত বেশভূষা ইত্যাদি এতটাই নিম্নরুচির মনে হয়েছিল যে তা সকলের হাসির উদ্রেক করেছিল। এমন একজন মানুষের কালচারের সঙ্গে সব্যসাচী মল্লিকের কালচারের কোনো তুলনাই চলে না।
এই কারণেই অপূর্ব নিমাইবাবুকে প্রশ্নোদ্ধৃত কথাটি বলেছিলেন।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো পায়ে” উক্তিটি কোন কবিতার অংশ? কেন অস্ত্র ফেলার কথা কবি উল্লেখ করেছেন?
উত্তর: উক্তিটি জয় গোস্বামী রচিত “অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতার অংশ।
এখানে কবি যুদ্ধ ও সহিংসতার প্রতীক “অস্ত্র”-কে পরিত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি চান মানুষ ঘৃণা ও হিংসা ছেড়ে মানবতা, ভালোবাসা ও শিল্পের পথে ফিরে আসুক। অস্ত্র পায়ের নিচে রাখার অর্থ এটি ত্যাগ করা ও অবমূল্যায়ন করা—যাতে মানবিক বোধ এবং গান জয়ী হয়।
৩.২.২ “দিগম্বরের জটায় হাসে শিশু-চাঁদের কর” ‘দিগম্বর’ কে? ‘শিশু-চাঁদের কর’ হাসার অর্থটি বোঝাও।
উত্তর: পরিচয়: এখানে ‘দিগম্বর’ বলতে মহাদেব বা শিবকে বোঝানো হয়েছে। ‘দিগম্বর’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো “দিকই যাঁর বসন”, অর্থাৎ যিনি বস্ত্রহীন। শিব জটা ধারণ করেন এবং বস্ত্রহীন থাকেন, তাই তাঁকে দিগম্বর বলা হয়েছে।
তাৎপর্য: মহাদেবের কপালে তৃতীয় নেত্রের স্থানে অর্ধচন্দ্র শোভা পায়। এই অর্ধচন্দ্রই জটাশোভিত, সর্বত্যাগী শিবের শরীরে অতুলনীয় সৌন্দর্য যোগ করেছে। অর্ধচন্দ্র অসম্পূর্ণ, তাই কবি একে ‘শিশু চাঁদ’ বলে উল্লেখ করেছেন। কবি এখানে বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক দিকের মধ্যেও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, যা শিশু চাঁদের নির্মল হাসির সঙ্গে তুলনীয়। কবির বিশ্বাস, অন্যায় ও অত্যাচারের অবসানে সমাজে সৌন্দর্য ও শুভবোধের প্রতিষ্ঠা ঘটবে, যা শিশু চাঁদের হাসির মতো ধীরে ধীরে চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ “তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।” কে হাসি গোপন করল? তার হাসি পাওয়ার কারণ কী?
উত্তর: অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে গিরীশ মহাপাত্রের অদ্ভুত সাজসজ্জা থানায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে অপূর্ব তা দেখে মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করেছিল।
গিরীশের মাথার সামনের দিকে ছিল বড় বড় চুল, কিন্তু দুপাশে ও পিছনে চুল ছিল না বললেই চলে। সেই চুল থেকে নেবুর তেলের উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, যা সকলের মাথা ধরে দেওয়ার মতো ছিল।
তার গায়ে ছিল জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি এবং পরনে ছিল বিলেতি মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি। পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে বাঘ আঁকা রুমালের কিছু অংশ বাইরে বেরিয়ে ছিল, কিন্তু উত্তরীয় ছিল না।
তার পায়ে ছিল সবুজ রঙের ফুল মোজা, যা হাঁটুর ওপর লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা, এবং পরনে ছিল বার্নিশ করা পাম্প শু। জুতোর তলায় লোহার নাল লাগানো ছিল, যাতে তা মজবুত ও টেকসই হয়।
এছাড়া, তার হাতে ছিল হরিণের শিং-এর হাতল দেওয়া এক গাছি বেতের ছড়ি, যা জাহাজভ্রমণের ধাক্কায় কিছুটা নোংরা হয়ে গিয়েছিল।
এই বিচিত্র ও অস্বাভাবিক সাজসজ্জা দেখে অপূর্বের মনে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে এবং তাই সে মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করেছিল।
৪.২ “চমকে উঠলেন জগদীশবাবু।” জগদীশবাবুর পরিচয় দাও। তিনি কেন চমকে উঠলেন?
উত্তর: জগদীশবাবুর পরিচয়
সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পে জগদীশবাবু একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তিনি একজন অবস্থাপন্ন ও জ্ঞানী ব্যক্তি।
শান্ত ও সৌম্যকান্তি-
সাদা মাথা ও সাদা দাড়িতে তাঁকে যথেষ্টই সৌম্য এবং শান্ত দেখায়। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর প্রবল ভক্তি ছিল।
আশীর্বাদ লাভের চেষ্টা-
জগদীশবাবু অর্থের সাহায্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ সহজে লাভের চেষ্টা করেছিলেন। হিমালয়ের গুহায় বাস করা এক সন্ন্যাসীর কাঠের খড়মে সোনার বোল লাগিয়ে তিনি তাঁর ‘দুর্লভ’ পায়ের ধুলো সংগ্রহ করেছিলেন। এতে তাঁর সরল ভক্তি ছিল না।
বিরাগীর সেবা-
বিরাগীর বেশধারী হরিদাকে দেখে জগদীশবাবু বিচলিত হয়ে ওঠেন। তাঁকে বাড়িতে থাকতে অনুরোধ করেন এবং তাঁর সেবা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।
ভক্তিভাবনা ও সচ্ছল জীবনযাত্রা-
শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুতেই সফল না হয়ে তিনি তাঁর তীর্থযাত্রার জন্য ১০১ টাকা প্রণামি হিসেবে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভক্তিভাবনার সঙ্গে তাঁর সচ্ছল জীবনযাত্রার বিষয়টি বারবার যুক্ত হয়ে উঠেছে।
তাঁর বিনয়, সাধুসঙ্গ লাভের ইচ্ছা ও শান্তির সন্ধান—এই গুণগুলি জগদীশবাবুর চরিত্রকে আলাদা করে তোলে।
জগদীশবাবুর চমকে ওঠার কারণ-
এক মনোরম সন্ধ্যায় জগদীশবাবু বাড়ির বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে ছিলেন। ঠিক তখনই বিরাগীর বেশধারী হরিদার আগমন ঘটে। ধবধবে সাদা উত্তরীয় গায়ে, ছোটো বহরের সাদা থান পরা হরিদাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন জগতের সীমার ওপার থেকে হেঁটে এসেছেন। তাঁকে দেখেই জগদীশবাবু চমকে ওঠেন।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে হো-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ “আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায়।” মেয়েটি কীসের প্রতীক হিসেবে কবিতায় প্রতিভাত হয়েছে? ‘মেয়েটি আমার অপেক্ষায়’ এর দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উত্তর: পাবলো নেরুদার কবিতা “অসুখী একজন”-এ “মেয়েটি” মূলত একটি প্রতীক। এটি একদিকে প্রেম, সম্পর্ক ও মানসিক আশ্রয়ের প্রতীক; অন্যদিকে, এটি আশার একটি আলো বা অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার রূপক হিসেবেও প্রতিভাত হয়। এই মেয়েটি কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘সে’-র জীবনে একটি মাত্র উজ্জ্বল দিক, যার কথা মনে করে সে জীবনের ক্লান্তি ও একঘেয়েমি থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে চায়।
“মেয়েটি আমার অপেক্ষায়” — এই চরণে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, সমস্ত যন্ত্রণা, একাকীত্ব ও দৈনন্দিন ক্লান্তির মধ্যেও ‘সে’ জানে কোথাও একজন অপেক্ষা করছে — যে তাকে ভালোবাসে, অনুভব করে। এটি তার জীবনে একমাত্র আশার বাতিঘর। মেয়েটির অপেক্ষা যেন তাকে জীবনের ভার বইবার শক্তি জোগায়, যদিও সে নিজেও জানে না কবে পৌঁছাবে বা আদৌ পৌঁছাতে পারবে কিনা।
এই চরণটি নিঃসঙ্গ মানুষের আশা, আত্মিক আকাঙ্ক্ষা এবং সম্পর্কের টানাপোড়েনের গভীর প্রতিফলন। এটি শুধু প্রেমের কথা নয়, বরং জীবনের যে কোনো অর্থপূর্ণ সম্পর্কের টানাপোড়েন ও মানসিক আশ্রয়ের প্রতীক হিসেবেও দেখা যায়।
৫.২ ‘আফ্রিকা’ কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে, তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আফ্রিকা’ কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কবি এখানে আফ্রিকাকে উপনিবেশিক শাসনের শিকার এক নিঃসহায়, নিপীড়িত ভূখণ্ড হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শোষণ, অবমাননা ও যন্ত্রণার ভার বহন করে এসেছে।
ইউরোপীয় শাসকরা আফ্রিকার স্বর্ণভূমিকে লুণ্ঠন করেছে, তার মানুষকে দাসে পরিণত করেছে এবং তার কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছে। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদ। তিনি বলেন, আফ্রিকা আজ জেগে উঠছে—তার শৃঙ্খল রক্তে ভিজে গেছে, কিন্তু সেই রক্তই তাকে দিয়েছে আত্মশক্তি।
শেষে কবি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, আফ্রিকা নবজীবনে উদিত হয়ে বিশ্বসভায় শান্তি ও মানবতার বাণী নিয়ে ফিরবে।
উপসংহার:
এই কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নিপীড়িত আফ্রিকার পক্ষ নিয়েছেন এবং শোষকদের বিরুদ্ধে ন্যায়ের কণ্ঠ তুলে ধরেছেন। এই কাব্য যেন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এক মানবিক ও নৈতিক প্রতিবাদ।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ ‘বিমর্ষ ওয়াটারম্যান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন’। ওয়াটারম্যান কে? তিনি বিমর্ষ হয়েছিলেন কেন? তাঁর প্রতিজ্ঞার ফল কী হয়েছিল?
উত্তর: ওয়াটারম্যান কে-
এই প্রবন্ধে লেখক শ্রীপান্থ ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। ওয়াটারম্যান ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী, যিনি নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়িক কারণে তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে তাঁর ফাউন্টেন পেন (ঝরনা কলম) বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।
বিমর্ষ হয়ার কারণ-
একবার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের সময় তিনি দোয়াত ও কলম সঙ্গে নিয়ে যান। দলিল লেখার মাঝপথে দোয়াতটি হঠাৎ উল্টে গিয়ে কাগজে কালি ছড়িয়ে পড়ে। কালি জোগাড় করতে তিনি বাইরে যান, আর এই সুযোগে অন্য এক ব্যবসায়ী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে চুক্তি পাকা করে চলে যান। এই ঘটনায় ওয়াটারম্যান হতাশ হয়ে পড়েন এবং তিনি স্থায়ীভাবে কালি ও কলম সমস্যার সমাধানের প্রতিজ্ঞা করেন।
প্রতিজ্ঞার ফল-
এই প্রতিজ্ঞা থেকেই জন্ম নেয় ফাউন্টেন পেন। এরপর থেকে আর কালি সংগ্রহের জন্য ছুটোছুটি করতে হয়নি। পরবর্তীতে ওয়াটারম্যান ছাড়াও পার্কার, সোয়ান প্রভৃতি কোম্পানি নানা রকম ঝরনা কলম বাজারে আনে। ফলে লেখালেখি আরও সহজ ও সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।
লেখকের মতে, এক সময় কলেজের প্রতিটি ছাত্রের পকেটে ফাউন্টেন পেন দেখা যেত। ধীরে ধীরে কঞ্চির কলম, খাগের কলম, পালকের কলম ইত্যাদি পুরনো লেখন সামগ্রী হারিয়ে যায়।
৬.২ ‘বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ’ কী? বাংলা ভাষায় ‘বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ’ লেখার জন্য কীরূপ রচনা পদ্ধতি আবশ্যক বলেছেন লেখক?
উত্তর: বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ বা রচনাকে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ বলা হয়েছে।
অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে রচনা সহজ হয়। এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। স্থান বিশেষে পারিভাষিক শব্দ বাদ দেওয়া চলে, যেমন ‘অমেরুদন্ডী’র বদলে লেখা যেতে পারে, যেসব জন্তুর শিরদাঁড়া নেই। কিন্তু ‘আলোকতরঙ্গ’র বদলে আলোর কাঁপন বা নাচন লিখলে কিছু মাত্র সহজ হয় না। পরিভাষার উদ্দেশ্য ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থ সুনির্দিষ্ট করা। যদি বার বার কোনো বিষয়ের বর্ণনা দিতে হয় তবে অনর্থক কথা বেড়ে যায়, তাতে পাঠকের অসুবিধা হয়। সাধারণের জন্য যে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লেখা হয় তাতে অল্প পরিচিত পারিভাষিক শব্দের প্রথমবার প্রয়োগের সময় তার ব্যাখ্যা (এবং স্থলবিশেষে ইংরেজি নাম) দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু পরে শুধু বাংলা পারিভাষিক শব্দটি দিলেই চলে।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ ঘসেটি সিরাজের প্রতি যতটা নির্মম, সিরাজকে কী ততটা নির্দয় বলে মনে হয়েছে?
উত্তর: না, সিরাজকে ঘসেটি বেগমের মতো নির্মম বা নিষ্ঠুর মনে হয় না। নাটকে ঘসেটি বেগম একটি ষড়যন্ত্রকারী চরিত্র, যিনি সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন। তিনি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায় এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে আঁতাত করেন। সিরাজের মৃত্যুতে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল।
অন্যদিকে, সিরাজ ছিল এক দেশপ্রেমিক ও আদর্শবান শাসক। তিনি কখনও নিজে থেকে ঘসেটির বিরুদ্ধে কোনো নিষ্ঠুরতা করেননি, বরং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মীরজাফর ও ঘসেটির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সিরাজের রাগ ও কঠোরতা ছিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু তা ছিল রাজধর্ম ও ন্যায়বিচারের কারণে।
অতএব, ঘসেটির নির্মমতা ছিল ব্যক্তিস্বার্থে, আর সিরাজের কঠোরতা ছিল দেশ ও ন্যায়ের পক্ষে — তাই সিরাজকে নির্মম বলা যায় না।
৭.২ ‘তোমার কথা আমার চিরদিনই মনে থাকবে।’ কার কথা বলা হয়েছে? কেন তাঁর কথা মনে থাকবে?
উত্তর: নবাব সিরাজদ্দৌলার দরবারে উপস্থিত ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লার সঙ্গে নবাব সিরাজের সম্পর্কের ওপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিম্নরূপ:
নবাব সিরাজদ্দৌলার ফরাসিদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। মঁসিয়ে লার কাছে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে এটি স্বীকার করেছেন। তিনি বাংলা দেশের ফরাসিদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেছেন। নবাব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, ফরাসিরা কখনো তার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেননি। ইংরেজরা চন্দননগর দখল করার পর ফরাসিরা নবাবের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল, কিন্তু নবাব অসহায় হয়ে তাদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। তিনি মঁসিয়ে লার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাও করেন।
মঁসিয়ে লা-ও এই বন্ধুত্বের কারণে দেশ ছেড়ে যাওয়া অনিবার্য হলেও নবাবকে তাঁর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন। সিরাজ মঁসিয়ে লার আন্তরিকতার পরিচয় দেখতে পান। তাই চিরবিচ্ছেদের সময় নবাব সিরাজ মঁসিয়ে লাকে বলেন, তাঁর কথাগুলো তিনি চিরকাল মনে রাখবেন।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ ‘চ্যাম্পিয়নরা জন্মায়, ওদের তৈরি করা যায় না।’ কোনির জীবন চিত্র উল্লেখ করে মন্তব্যটি বিচার করো।
উত্তর: সাহিত্যিক মতি নন্দীর “কোনি” উপন্যাসে জুপিটার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বিনোদ ভড়ের কথার প্রসঙ্গে কোচ ক্ষিতীশ সিংহ বলেন, “চ্যাম্পিয়নরা জন্মায় না, তৈরি করা যায়।” তাঁর মতে, প্রতিভাধর সাঁতারুকে কঠোর ও নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়নে পরিণত করা সম্ভব। এজন্য একজন কোচকে সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়, যেন তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন কার মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়নের সম্ভাবনা।
উপন্যাসে বারুণীর দিনে গঙ্গার ঘাটে আম কুড়াতে গিয়ে কোনির আগ্রাসী মনোভাব ও চমৎকার সাঁতার দেখে ক্ষিতীশ সিংহ তাঁর মধ্যে চ্যাম্পিয়নের ছাপ লক্ষ্য করেন। পরে, কুড়ি ঘণ্টার অবিরাম হাঁটা প্রতিযোগিতায় কোনির অসাধারণ ধৈর্য ও মানসিক দৃঢ়তা দেখে তিনি নিশ্চিত হন যে, কোনির মধ্যে রয়েছে একজন চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠার সমস্ত গুণ।
এই বিশ্বাস থেকেই ক্ষিতীশ তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনিকে গড়ে তোলেন একজন দক্ষ সাঁতারুতে। বহু বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে কোনি একসময় জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করে। তাই বলা যায়, বক্তার প্রশ্নোধৃত উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য নয়—কারণ কোনি তার বাস্তব উদাহরণ যে চ্যাম্পিয়ন তৈরি করা যায়।
৮.২ বিষ্টুচরণ চরিত্রটির মধ্যে হাস্যরস ও সততার যে পরিচয় রয়েছে, তা ‘কোনি’ উপন্যাস অবলম্বনে লেখো।
উত্তর: মতি নন্দীর “কোনি” উপন্যাসে বিষ্টুচরণ একটি উল্লেখযোগ্য পার্শ্বচরিত্র। তিনি কোচ ক্ষিতীশ সিংহের (খিদ্দার) ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে সরলতা ও সততা, তেমনি রয়েছে সহজাত হাস্যরস।
বিষ্টুচরণ পেশায় একজন পেশাদার ধোপা হলেও মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল। যখন খিদ্দা কোনিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব নেন এবং আর্থিক সংকটে পড়েন, তখন বিস্টুচরণ খিদ্দাকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তার আচরণে কোনো অহংকার নেই; বরং সে সহজ-সরল এবং স্পষ্টভাষী।
তার ব্যবহারিক বুদ্ধি ও রসিকতা পাঠকের মনে স্বস্তি আনে। নানা জটিল পরিস্থিতিতে সে নিজের সরলতা ও হাস্যরস দিয়ে পরিবেশকে হালকা করে তোলে। আবার, বন্ধু খিদ্দার প্রতি তার নিষ্ঠা ও সহমর্মিতা তার সততার পরিচয় দেয়।
সব মিলিয়ে, বিস্টুচরণ চরিত্রটি উপন্যাসে হাস্যরস ও মানবিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে, যা গল্পের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
৮.৩ ‘তুমুল হৈচৈ পড়ে গেল প্রণবেন্দুর এই কথায়’ কোন্ কথা প্রণবেন্দু বলেছিলেন? তার পরিণতি কী হল?
উত্তর: ‘কোনি’ উপন্যাসে প্রণবেন্দু একজন সাহসী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তরুণ। তিনি একদিন বলেন,
“যদি বস্তির মেয়েরা সাঁতার না শিখতে পারে, তাহলে আমরা লজ্জিত হব।”
এই মন্তব্য বস্তির প্রচলিত মানসিকতার বিরোধিতা করে। ফলে প্রণবেন্দুর কথায় বস্তির লোকজনের মধ্যে তুমুল হৈচৈ পড়ে যায়। কেউ তার সাহসের প্রশংসা করে, কেউ আবার তীব্র সমালোচনা করে।
তবে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণবেন্দু নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন। তার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে খিদ্দা কোনিকে সাঁতার শেখানোর দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে কোনি কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সফল হয়।
এইভাবে প্রণবেন্দুর সাহসী কথার পরিণতি হয় ইতিবাচক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে ওঠে।
৯। চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো:
Education has no end. So you should keep up your studies. Many young men close their books when they have taken their degrees and learn no more. Therefore they very soon forget all they have ever learnt. If you want to continue your education, you must find time for serious reading.
উত্তর: শিক্ষার কোনো শেষ নেই। তাই তোমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। অনেক তরুণ ডিগ্রি অর্জনের পর বই বন্ধ করে দেয় এবং আর কিছু শেখে না। ফলে তারা খুব তাড়াতাড়ি যা শিখেছিল সব ভুলে যায়। যদি তুমি তোমার শিক্ষা চালিয়ে যেতে চাও, তাহলে তোমাকে মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য সময় বের করতে হবে।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ ‘সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও’ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
রাহুল: আরে তনু, কেমন আছিস? তোর হাতটা বাঁধা কেন?
তনু: আর বলিস না, গত সপ্তাহে বাইক চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করলাম।
রাহুল: কী! কিভাবে হলো?
তনু: হেলমেট পরিনি, আর একটু তাড়াহুড়ো করছিলাম। সামনে থেকে একটা গাড়ি ঘুরে গেল, আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম।
রাহুল: এটা তো খুবই খারাপ হয়েছে। তুই জানিসই তো, “সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও” – এটা শুধু একটা স্লোগান নয়, বাস্তব জীবনের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ।
তনু: একদম ঠিক বলেছিস। এখন বুঝছি, একটু সতর্ক থাকলেই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।
রাহুল: তাই তো বলি, হেলমেট পরা, নিয়ম মানা আর ধৈর্য নিয়ে গাড়ি চালানো খুব দরকার।
তনু: হ্যাঁ রে, এখন থেকে আমি সব সময় সাবধানে চালাবো। জীবনের চেয়ে কিছুই বড় নয়।
রাহুল: ভালো কথা বলেছিস। এই অভিজ্ঞতা তোর জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকুক।
১০.২ বেআইনিভাবে গাছ কাটার বিরুদ্ধে এলাকার মানুষের সমবেত প্রতিরোধ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
বেআইনিভাবে গাছ কাটার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর প্রতিরোধ
নিজেস্ব সংবাদদাতা, রতনপুর, মে ২৪: গতকাল রতনপুরে রায়পাড়া অঞ্চলে বেআইনিভাবে গাছ কাটার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীরা একত্র হয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। জানা গেছে, একটি নির্মাণ সংস্থা সেখানে নতুন বহুতল নির্মাণের উদ্দেশ্যে রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটি পুরনো নিম ও শিরীষ গাছ কেটে ফেলছিল। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করতে বলেন।
গাছ কাটার অনুমতির কাগজপত্র দেখাতে বলা হলে নির্মাণকর্মীরা কিছুই দেখাতে পারেননি। এরপরই এলাকাবাসী মিছিল ও ধর্না কর্মসূচি শুরু করেন এবং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বন দফতরের আধিকারিকরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং গাছ কাটা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।
এই ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, পরিবেশ রক্ষায় সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও ঐক্যবদ্ধতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এলাকাবাসীর এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং অনুপ্রেরণামূলক।
১১। যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লেখো: (কমবেশি ৪০০ শব্দে)
১১.১ ইনটারনেট ও আধুনিক জীবন।
উত্তর:
ইন্টারনেট ও আধুনিক জীবন
আজকের বিশ্বে ইন্টারনেট আধুনিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি হলো এই ইন্টারনেট। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে—শিক্ষা, যোগাযোগ, ব্যবসা, বিনোদন এমনকি চিকিৎসা পরিষেবাতেও ইন্টারনেটের প্রভাব সুস্পষ্ট।
প্রথমত, ইন্টারনেট আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করে তুলেছে সহজ, দ্রুত এবং কার্যকর। এখন আমরা মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে থাকা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি, ভিডিও কল করতে পারি বা বার্তা পাঠাতে পারি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে আরও বিস্তৃত ও দৃঢ় করেছে।
দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট একটি বিপ্লব এনেছে। অনলাইন ক্লাস, ডিজিটাল লাইব্রেরি, ইউটিউব, গুগল ইত্যাদি আমাদের অগাধ তথ্যের জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
তৃতীয়ত, ই-কমার্স ও অনলাইন ব্যাংকিংয়ের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটাই সহজ ও গতিশীল হয়েছে। ঘরে বসেই পণ্য কেনাকাটা করা, বিল প্রদান, টাকার লেনদেন সম্ভব হয়েছে ইন্টারনেটের সাহায্যে। এই প্রযুক্তি কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্তও উন্মোচন করেছে।
তবে ইন্টারনেটের এই আশীর্বাদস্বরূপ ব্যবহারের পাশাপাশি কিছু অভিশাপও রয়েছে। অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার মানুষকে আসক্ত করে তোলে। পড়াশোনা ও কাজের প্রতি মনোযোগ কমে যায়, শরীর ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। সামাজিক বন্ধন দুর্বল হতে থাকে। তাছাড়া সাইবার অপরাধ, ভুয়া খবর ও ব্যক্তিগত তথ্য চুরির মতো সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।
অতএব, বলা যায়, ইন্টারনেট আধুনিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও এর সঠিক ও সচেতন ব্যবহার অপরিহার্য। যদি আমরা এর সদ্ব্যবহার করি, তবে এটি আমাদের জীবনকে আরও সহজ, উন্নত ও সুন্দর করে তুলতে পারে। অন্যথায় এটি আমাদের ক্ষতির কারণও হতে পারে। তাই প্রযুক্তির এই দানকে আশীর্বাদে পরিণত করতে হলে আমাদের দায়িত্বশীল ব্যবহার করতেই হবে।
১১.২ চরিত্রগঠনে খেলাধুলার ভূমিকা।
উত্তর:
চরিত্রগঠনে খেলাধুলার ভূমিকা
মানবজীবনে সুস্থ শরীর ও সুন্দর মন গঠনের জন্য যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি খেলাধুলাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু শরীর চর্চা নয়, খেলাধুলা মানুষের চরিত্রগঠনে বিশাল ভূমিকা পালন করে। একজন মানুষ যত বেশি খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তত বেশি তিনি শৃঙ্খলাপরায়ণ, আত্মনিয়ন্ত্রিত ও দলগত মনোভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।
খেলাধুলা আমাদের মধ্যে নিয়মিত জীবনযাপন ও শৃঙ্খলার অভ্যাস গড়ে তোলে। খেলোয়াড়দের নিয়ম মেনে চলতে হয়, সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করতে হয় এবং নিয়মিত অনুশীলন করতে হয়। এই অভ্যাসগুলো ধীরে ধীরে মানুষের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
এছাড়া খেলাধুলা মানুষের মধ্যে সহনশীলতা ও সহমর্মিতার গুণ তৈরি করে। প্রতিযোগিতার মাঠে জয়-পরাজয় দুটোই স্বাভাবিক। খেলোয়াড়েরা পরাজয় মেনে নেওয়ার শিক্ষা পায় এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে ভালো করার অনুপ্রেরণা পায়। এই মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরশীলতা চরিত্রের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
দলগত খেলাগুলোর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ‘টিমওয়ার্ক’ বা দলবদ্ধভাবে কাজ করার শিক্ষা পায়। একজন খেলোয়াড় জানে কীভাবে সহখেলোয়াড়দের সঙ্গে সমন্বয় করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং দলকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিতে হয়। এই দলগত মানসিকতা পরবর্তীতে সমাজ ও কর্মক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
খেলাধুলা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে রাখে এবং মনকে প্রফুল্ল করে তোলে। এটি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে খারাপ অভ্যাস যেমন মাদকাসক্তি, অপরাধ প্রবণতা বা প্রযুক্তি আসক্তি থেকে দূরে রাখতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
তবে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলাকে গুরুত্ব না দিলে শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। আজকের দিনে স্কুল-কলেজে শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান নয়, খেলাধুলার যথাযথ সুযোগও তৈরি করা দরকার।
সুতরাং বলা যায়, খেলাধুলা শুধু শরীর গঠন করে না, এটি মন ও চরিত্র গঠনেরও শক্তিশালী মাধ্যম। একজন সৎ, দৃঢ়চেতা ও সহানুভূতিশীল নাগরিক তৈরিতে খেলাধুলার অবদান অপরিসীম। তাই আমাদের সকলের উচিত নিয়মিত খেলাধুলার চর্চা ও উৎসাহ দেওয়া, যেন সমাজে আরও সুস্থ ও সুনাগরিক তৈরি হয়।
১১.৩ একটি নদীর আত্মকথা।
উত্তর:
একটি নদীর আত্মকথা
আমি একটি নদী। কবে কোথা থেকে আমার জন্ম, সে কথা আজ আর কেউ মনে রাখে না। কোন এক অজানা পাহাড়ের কোলে ঝরনার জলধারায় আমার সূচনা। তারপর পাহাড়, পর্বত, বন, গ্রাম, শহর পার হয়ে আমি ছুটে চলেছি সমুদ্রের উদ্দেশে—নিরবচ্ছিন্ন, অবিরাম।
প্রথমে আমি ছিলাম ছোট, সরু আর কিশোরীর মতো চঞ্চল। আমার ধারায় ছিল সরলতা, উচ্ছ্বাস ও প্রাণ। শিশুদের কলরব, পাখিদের কূজন, আর গ্রামের মানুষের আনন্দ আমার বুকে বাজত। কৃষক আমার জল দিয়ে সেচ দিত তার ফসলের জমি। আমার বুক চিরে নৌকা বয়ে নিয়ে যেত বাজারে চাল, ডাল, মাছ ও কাঠ। আমি তখন ছিলাম মানুষের বন্ধু, ভরসা আর জীবনের উৎস।
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি বদলাতে থাকলাম। শহর আমার তীরে এসে বসতি গড়ল। প্রথমে আনন্দ পেয়েছিলাম মানুষের কাছে থাকতে পেরে। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝলাম, মানুষ কেবল গ্রহণ করতে জানে, দিতে জানে না। তারা আমার বুকে ফেলে দেয় ময়লা, আবর্জনা, বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য। আমার স্বচ্ছ জল আজ মলিন, আমার বুকে প্রাণ নেই বললেই চলে। মাছেরা পালিয়ে গেছে, জলজ উদ্ভিদ মরে গেছে, শিশুরা আর আমার জলে নামে না।
আমি আজ ক্লান্ত, বিষণ্ন। আমার বুক কেটে বাঁধ বানানো হয়েছে, আমাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তো চলমান, বাধা আমার চরিত্র নয়। তবুও মানুষ বারবার আমাকে বেঁধে রেখেছে নিজেদের স্বার্থে। আমি প্রতিবাদ করি না, শুধু নীরবে বয়ে চলি, যেহেতু এটাই আমার ধর্ম।
তবে আমি এখনও স্বপ্ন দেখি—কোনো একদিন মানুষ বুঝবে, আমি শুধু জলধারা নই, আমি জীবন। তারা আবার আমাকে ভালবাসবে, আমার পবিত্রতা ফিরিয়ে দেবে। আমি আবার কুলকুল ধারায় বইব, ফসল সিঁচে দেব, পাখিদের গান শুনব, আর শিশুদের হেসেখেলে নেমে পড়া দেখব।
আমি একটি নদী—আমি সৃষ্টি করি, আমি ধ্বংস করি না। শুধু চাই মানুষ আমাকে ভালোবাসুক, কারণ তাদের জীবনের সঙ্গে আমার অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।
১১.৪ বাংলার লোকসংস্কৃতি।
উত্তর:
বাংলার লোকসংস্কৃতি
বাংলার মাটি যেমন উর্বর, তেমনি উর্বর এর সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার। লোকসংস্কৃতি হলো সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত সেই সব সংস্কৃতি যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুখে মুখে, আচারে ও রীতিতে বেঁচে থাকে। এটি গ্রামীণ সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। বাংলার লোকসংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য, আত্মপরিচয় ও সংস্কারবোধের ধারক ও বাহক।
বাংলার লোকসংস্কৃতির মূল উপাদানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: লোকগান, লোকনৃত্য, লোককথা, পটচিত্র, হাট-বাজার, মেলা, লোকনাট্য এবং প্রথাগত হস্তশিল্প।
লোকগানের মধ্যে বাউল, ভাটিয়ালি, জারি-সরিফা, মারফতি ও ভাওয়াইয়া বিশেষ জনপ্রিয়। বাউল গান জীবন ও সাধনার এক অপূর্ব দার্শনিক প্রকাশ। নদীঘেরা বাংলায় ভাটিয়ালি গান মাঝিদের প্রাণের সঙ্গী।
লোকনৃত্যের মধ্যে যেমন রয়েছে গম্ভীরা ও চৌদ্দোল, তেমনি লোকনাট্যে দেখা যায় পালাগান, যাত্রা ও কীর্তনের ছোঁয়া। এইসব লোকনাট্যের মাধ্যমে মানুষ আনন্দ পায়, আবার সমাজ ও ধর্মীয় শিক্ষাও লাভ করে।
বাংলার লোকশিল্পও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পটচিত্র, মৃৎশিল্প, কাঠের খোদাই, শীতলপাটি, নকশিকাঁথা ইত্যাদি লোকশিল্প আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সমাদৃত।
লোকসংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর সরলতা ও প্রাণবন্ততা। এটি মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উৎসব-পার্বণ, জন্ম-মৃত্যু, বিয়ে কিংবা ফসল তোলার মতো ঘটনাগুলোর সঙ্গেও লোকসংস্কৃতির সংযোগ অটুট। বাংলা নববর্ষ, পৌষমেলা, চড়ক, গাজনের মতো নানা লোকউৎসব আজও মানুষকে একত্র করে রাখে।
তবে আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে লোকসংস্কৃতি আজ কিছুটা অবহেলিত ও বিলুপ্তপ্রায়। নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত নয়। তাই লোকসংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে দরকার সচেতনতা, শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি এবং যথাযথ সংরক্ষণ।
সুতরাং, বাংলার লোকসংস্কৃতি কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি আমাদের শেকড়, আমাদের আত্মপরিচয়। এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারে এবং বাংলার প্রকৃত রূপ চিনতে শেখে।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।