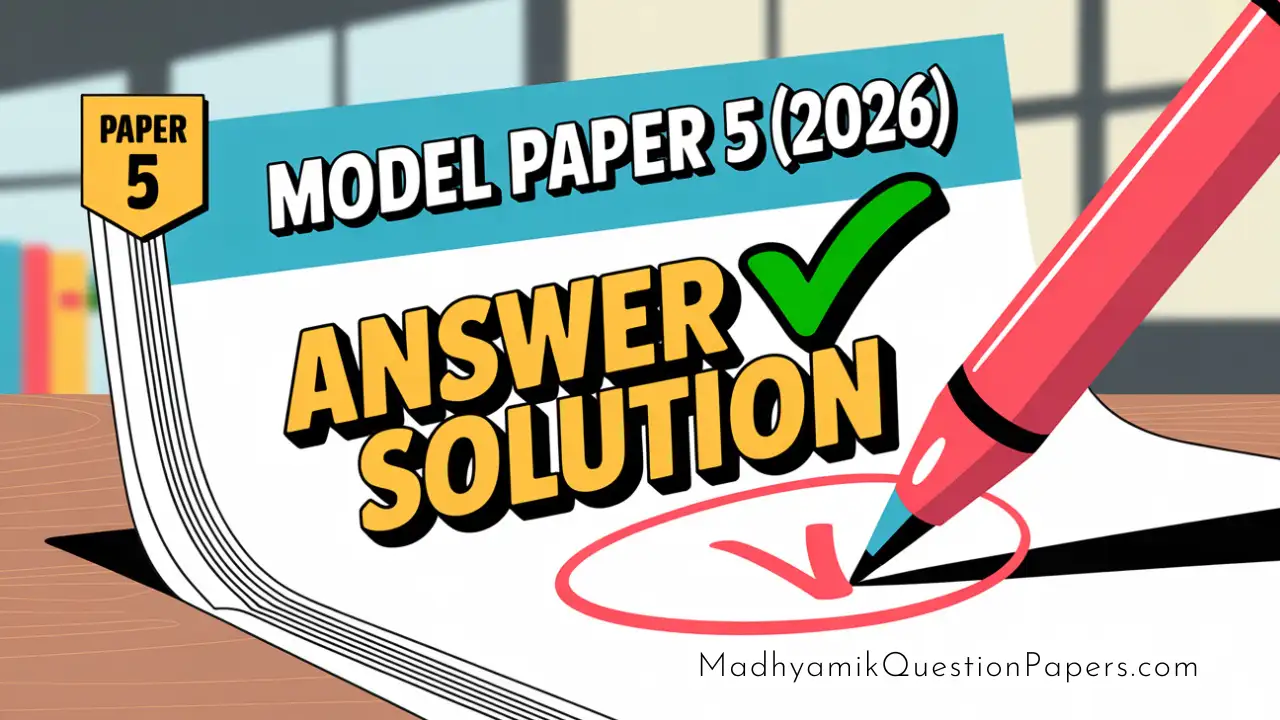আপনি কি ২০২৬ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 5 এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 5-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৬ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ তপনের মেসোমশাই কোন্ পত্রিকার সম্পাদককে চিনতেন? –
(ক) ‘শুকতারা’
(খ) ‘আনন্দমেলা’
(গ) ‘সন্ধ্যাতারা’
(ঘ) ‘দেশ’
উত্তর: (গ) ‘সন্ধ্যাতারা’
১.২ ‘ও আমাকে শিখিয়েছে, খাঁটি জিনিস কাকে বলে।’- উক্তিটির বক্তা হলেন-
(ক) গ্রামপ্রধান
(খ) অমৃত
(গ) ইসাব
(ঘ) পাঠান
উত্তর: (ঘ) পাঠান
১.৩ নদেরচাঁদ নদীকে দেখেনি-
(ক) তিনদিন
(খ) পাঁচদিন
(গ) সাতদিন
(ঘ) একদিন
উত্তর: (খ) পাঁচদিন
১.৪ “যেখানে ছিল শহর / সেখানে ছড়িয়ে রইল…” কী ছড়িয়ে রইল?-
(ক) পায়ের দাগ
(খ) কাঠকয়লা
(গ) গোলাপি গাছ
(ঘ) প্রাচীন জলতরঙ্গ
উত্তর: (খ) কাঠকয়লা
১.৫ আফ্রিকাকে কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?
(ক) নিবিড় বনস্পতি
(খ) প্রাচী ধরিত্রী
(গ) রুদ্র সমুদ্রের বাহু
(ঘ) কৃপণ আলো
উত্তর: (গ) রুদ্র সমুদ্রের বাহু
১.৬ ‘হায়, বিধি বাম মম প্রতি।’ বক্তা কে?
(ক) রাবণ
(খ) মেঘনাদ
(গ) বীরবাহু
(ঘ) প্রমীলা
উত্তর: (ক) রাবণ
১.৭ বাঙালি সাংবাদিকদের ‘বাবু কুইল ড্রাইভারস’ বলেছিলেন কে? –
(ক) লর্ড আমহার্স্ট
(খ) লর্ড কার্জন
(গ) লর্ড ওয়েলেসলি
(ঘ) লর্ড ক্যানিং
উত্তর: (খ) লর্ড কার্জন
১.৮ ‘যার পোশাকি নাম স্টাইলাস,’ কার পোশাকি নাম? –
(ক) কুইল
(খ) নল-খাগড়া
(গ) খাগের কলম
(ঘ) ব্রোঞ্জের শলাকা
উত্তর: (ঘ) ব্রোঞ্জের শলাকা
১.৯ যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয়, তাদের প্রথম শ্রেণিটি
(ক) ইংরেজি ভাষায় দক্ষ
(খ) বাংলা ভাষায় দক্ষ
(গ) ইংরেজি জানে না বা অতি অল্প জানে
(ঘ) ইংরেজি জানে এবং ইংরেজি ভাষায় অল্পাধিক বিজ্ঞান পড়েছে
উত্তর: (গ) ইংরেজি জানে না বা অতি অল্প জানে
১.১০ “তিনি আহারে বসেছেন” এখানে ‘আহারে’ হল
(ক) কর্মকারকে ‘এ’ বিভক্তি
(খ) অধিকরণ কারকে ‘এ’ বিভক্তি
(গ) করণ কারকে ‘এ’ বিভক্তি
(ঘ) নিমিত্ত কারকে ‘এ’ বিভক্তি
উত্তর: (ঘ) নিমিত্ত কারকে ‘এ’ বিভক্তি
১.১১ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
(ক) কারক
(খ) অ-কারক
(গ) সমাপিকা
(ঘ) অসমাপিকা
উত্তর: (ক) কারক
১.১২ যে সব পদ মিলিত হয়ে সমাস হয়, তাদেরকে বলে-
(ক) সমস্যমান পদ
(খ) সমস্তপদ
(গ) পূর্বপদ
(ঘ) সমাসবদ্ধ পদ
উত্তর: (ক) সমস্যমান পদ
১.১৩ একটি নিত্যসমাসের উদাহরণ হল-
(ক) গণ্যমান্য
(খ) গ্রামান্তর
(গ) চালভাজা
(ঘ) গোলাপজল
উত্তর: (খ) গ্রামান্তর
১.১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘গীতাঞ্জলি’ লিখে নোবেল পুরস্কার পান– এই বাক্যের নিম্নরেখ অংশটি হল-
(ক) উদ্দেশ্য
(খ) উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক
(গ) বিধেয়
(ঘ) বিধেয়ের সম্প্রসারক
উত্তর: (ঘ) বিধেয়ের সম্প্রসারক
১.১৫ “ছেলেটি এবার পড়ত বসবে” এই বাক্যটির ‘পড়তে বসবে’ অংশটি হল-
(ক) বিশেষণখণ্ড
(খ) বিশেষ্যখণ্ড
(গ) ক্রিয়াখণ্ড
(ঘ) ক্রিয়াবিশেষণখণ্ড
উত্তর: (গ) ক্রিয়াখণ্ড
১.১৬ বিভিন্ন বাচ্যে আলাদা হয়
(ক) কর্তা
(খ) ক্রিয়া
(গ) কর্তার রূপ
(ঘ) ক্রিয়ার প্রকাশভঙ্গি
উত্তর: (ঘ) ক্রিয়ার প্রকাশভঙ্গি
১.১৭ “একটি সভা আহ্বান করো।” এটি ভাববাচ্যে পরিবর্তন করলে হবে
(ক) একটি সভা আহূত হয়েছে
(খ) একটি সভা আহ্বান করা হোক
(গ) একটি সভা ডাকা হবে
(ঘ) একটি সভা আয়োজিত হবে
উত্তর: (খ) একটি সভা আহ্বান করা হোক
২ কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ “এর মধ্যে তপন কোথা?”– উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: “এর মধ্যে তপন কোথা?”—এই উক্তির মাধ্যমে তপনের অসহায়তার প্রকাশ ঘটেছে। ছোটো মেসোমশাই গল্পটি সংশোধন করার নামে আসলে গোটা লেখাটাই নতুন করে নিজের পাকা হতে সাজিয়ে দেন। ফলে গল্পের প্রতিটি লাইনই হয়ে ওঠে একেবারে নতুন বা ভিন্ন স্বাদের। তপন নিজের লেখার কোনো ছাপই সেখানে খুঁজে পায় না। তাই তার মনে হয়, এই গল্পে আর তার কোনো অস্তিত্ব বা লেখকসত্তার প্রকাশ নেই।
২.১.২ “হরিদার কাছে আমরাই গল্প করে বললাম,”– কোন্ গল্পের প্রসঙ্গ উদ্ধৃতাংশে রয়েছে?
উত্তর: বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পে, জগদীশবাবুর বাড়িতে এক সন্ন্যাসীর আগমন ও হরিদার সাথে তাঁর ঘটা ঘটনাগুলোর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে।
২.১.৩ “ইহা যে কতবড়ো ভ্রম তাহা কয়েকটা স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল।” ‘ভ্রম’-টি কী?
উত্তর: অপূর্ব ভেবেছিল, প্রথম শ্রেণির যাত্রী হওয়ায় আরাম করে প্রভাতকাল পর্যন্ত তার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না এবং কেউ তাকে বিরক্তও করবে না। কিন্তু এ যে কতবড়ো ভ্রম তা কয়েকটা স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল।
২.১.৪ “ওরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।–” তারা কী কারণে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল?
উত্তর: “পান্নালাল প্যাটেলের ‘অদল বদল’ গল্পের অমৃত ও ইসাব ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। নতুন জামা পরে বেরোনো অমৃতকে কালিয়া জোর করে খোলা মাঠে টেনে নিয়ে যায়, কুস্তির জন্য চ্যালেঞ্জ করে এবং তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে। ইসাব তার বন্ধুর এই অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, কালিয়ার হাত ধরে তাকেই লড়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজিতও করে। কিন্তু লড়াইয়ের মধ্যে ইসাবের নতুন জামার পকেটটি অনেকখানি ছিঁড়ে যায়। নতুন জামা ছেঁড়ার জন্য বাবার কাছে ভয়ানক মার খেতে হবে—এই ভয়েই দুই বন্ধু তখন আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।”
২.১.৫ নদেরচাঁদ কত বছর স্টেশন মাস্টারি করেছে?
উত্তর: নদেরচাঁদ চার বছর স্টেশন মাস্টারের কাজ করেছে।
নদেরচাঁদ মোট চার বছর ধরে স্টেশন মাস্টারের দায়িত্ব পালন বা স্টেশন মাস্টারি কাজ করেছে ।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ পাবলো নেরুদার প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: পাবলো নেরুদার প্রকৃত নাম ছিল রিকার্দো এলিসের নেফতালি রেইয়েস বাসোয়ালতো।
২.২.২ ‘এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।’– বক্তা কোন্ কলঙ্কের কথা বলেছেন?
উত্তর: বক্তা ইন্দ্রজিতের মতে, তার মতো যোগ্য পুত্র সত্ত্বেও যদি তার পিতা রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে যান, তাহলে তা হবে একটি কলঙ্কময় ঘটনা।
২.২.৩ ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি কোন্ কাব্যের অন্তর্গত?
উত্তর: “প্রলয়োল্লাস” কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত “অগ্নিবীণা” কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতা।
২.২.৪ ‘অতি মনোহর দেশ’ –দেশটিকে মনোহর বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: সৈয়দ আলাওল রচিত ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতায় সমুদ্রকন্যা পদ্মার জন্য একটি মনোরম প্রাসাদের কল্পনা করা হয়েছে, যাকে সমুদ্রমাঝারি এক দ্বীপভূমির মতো দেখায়। কবি এই স্থানটিকে অতি মনোহর দেশ ও এক দিব্যপুরী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, সেখানে কোনো প্রকার দুঃখ বা কষ্ট নেই; বরং শুধুমাত্র সত্যধর্ম ও সদাচারের বসবাস। এছাড়াও সেখানে রয়েছে একটি পর্বত এবং নানান ফুলে শোভিত এক অপূর্ব উদ্যান, যেখানে গাছগুলো নানা রকমের ফল ও ফুলে পরিপূর্ণ।
২.২.৫ “রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে” কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: কবির মতে, গানে হিংসা, নৈরাজ্য, রক্তপাত ও সন্ত্রাস থেকে মুক্তির সন্ধান রয়েছে।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘দার্শনিক তাঁকেই বলি’ কাকে প্রাবন্ধিক দার্শনিক বলেন?
উত্তর: লেখকের মতে, ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ রচনায় যে ব্যক্তি কানে কলম গুঁজে বিশ্ব খোঁজেন, তিনিই হলেন প্রকৃত দার্শনিক।
২.৩.২ ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’-এ বর্ণিত সবচেয়ে দামি কলমটির কত দাম?
উত্তর: “হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” গল্পে বর্ণিত সবচেয়ে দামি কলমটির মূল্য ছিল আড়াই হাজার পাউন্ড।
২.৩.৩ ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কী সমিতি নিযুক্ত করেছিল?
উত্তর: ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত করেছিল।
২.৩.৪ বাংলা ভাষার প্রকৃতি বিরুদ্ধ একটি অনুবাদের উদাহরণ দাও।
উত্তর: বাংলা ভাষার প্রকৃতি বিরুদ্ধ অনুবাদ হলো—যখন বিদেশি ভাষার বাক্যগঠন হুবহু বাংলায় বসানো হয়
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ সমধাতুজ কর্ম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যখন কোনো বাক্যে ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হয়, তখন সেই কর্মকে ‘সমধাতুজ কর্ম’ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ – ‘আমি একটা ভালো ঘুম ঘুমিয়েছি।
২.৪.২ বিভক্তি কাকে বলে?
উত্তর: বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সাথে বাক্যের অন্যান্য শব্দের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী যে সকল অর্থবিহীন লগ্নক ব্যবহৃত হয়, তাদেরই ব্যাকরণের পরিভাষায় বিভক্তি বলা হয়।
২.৪.৩ “তপন বইটা ফেলে রেখে চলে যায়,”– ‘বইটা’ পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
উত্তর: তপন বইটা ফেলে রেখে চলে যায়” বাক্যে ‘বইটা’ পদটির কারক হলো কর্মকারক এবং এর বিভক্তি হলো শূন্য বিভক্তি। কারণ ‘টা’ একটি নির্দেশক অব্যয়, যা বিশেষ্যের সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করে কিন্তু কারক-বিভক্তি হিসেবে কাজ করে না।
২.৪.৪ ‘অলোপ সমাস’ কাকে বলে?
উত্তর: যে সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে বলা হয় অলোপ বিভক্তি সমাস।
২.৪.৫ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো: বহুব্রীহি।
উত্তর: বহুব্রীহি হল এক প্রকার সমাস। এই সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ—উভয়েরই মূল অর্থ গৌণ হয়ে একটি তৃতীয় বা নতুন অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। এর ব্যাসবাক্য হলো—’বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার’ এবং এর সমস্তপদ বা সমাসনাম হলো ‘বহুব্রীহি’।
২.৪.৬ ‘সমাস’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: “সমাস” শব্দের অর্থ হল সংক্ষেপ, মিলন অথবা একাধিক পদের এক পদের মধ্যে সমন্বয়।
২.৪.৭ যে রক্ষক, সে-ই ভক্ষক। (সরল বাক্যে পরিণত করো)
উত্তর: যে রক্ষক, সে-ই ভক্ষক” বাক্যটিকে সরল বাক্যে পরিণত করলে হবে “রক্ষকই ভক্ষক”।
২.৪.৮ উদ্দেশ্য প্রসারকের একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: “আমাদের পাড়ার ছেলেটি মাঠে ফুটবল খেলছে” – এটি একটি উদ্দেশ্য প্রসারকের উদাহরণ।
২.৪.৯ ‘আন রথ তারা করি;’। (ভাববাচ্যে পরিণত করো)
উত্তর: ‘আন রথ তারা করি’— এই বাক্যটির ভাববাচ্যে রূপ হবে ‘রথ আনা হোক’ বা ‘আমার দ্বারা রথ আনা হোক’।
২.৪.১০ বাচ্য কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর: বাংলা ভাষায় বাচ্য প্রধানত তিন প্রকার; যেমন – কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য এবং ভাববাচ্য।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ “পত্রিকাটি সকলের হাতে হাতে ঘোরে,”- কোন্ পত্রিকা, কেন সকলের হাতে হাতে ঘুরছিল?
উত্তর: সারা বাড়িতে আনন্দের শোরগোল পড়ে যায়, যখন জানা যায় তপনের লেখা গল্পটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ওর মেসোমশাইয়ের সেই ছাপিয়ে দেওয়া সন্ধ্যাতারা পত্রিকাটি সবার হাতে হাতে ঘুরতে থাকে।
৩.১.২ ‘কিন্তু পারিবে কি?’ –কী পারা নিয়ে নদেরচাঁদ সংশয় প্রকাশ করেছে? সংশয়ের কারণ কী ছিল?
উত্তর: নদেরচাঁদ নদীর প্রবল উত্তাল রূপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, নদী রোষে উন্মত্ত হয়ে ব্রিজ ভাঙতে, বাঁধ চুরমার করে স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে চায়। কিন্তু এই ইট, সিমেন্ট, পাথর, লোহালক্কড়ে গড়া শক্ত ব্রিজ এবং মানুষের হাতে তৈরি বাঁধ নদী ভাঙতে পারবে কি না, সেই নিয়েই সে সংশয় প্রকাশ করে। কারণ, প্রকৃতির অসীম শক্তি থাকলেও মানুষের গড়া কৃত্রিম বাঁধন ভাঙা সহজ নয়। তাই নদীর বিদ্রোহী স্রোতের পক্ষে এই বাঁধন ছিন্ন করা কতটা সম্ভব—সে প্রশ্নই তাকে ভাবিত করে।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;” -কাকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে? ‘মানহারা মানবী’ সম্বোধনের কারণ কী?
উত্তর: ‘আফ্রিকা’ কবিতায় যুগান্তকারী কবিকে মানহারা মানবীর দ্বারে দাঁড়াতে বলা হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আফ্রিকা’ কবিতায় আফ্রিকাকে ‘মানহারা মানবী’ বলা হয়েছে; কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শোষিত, লুণ্ঠিত ও অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও আফ্রিকার নিজস্ব স্বকীয়তা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিকে ধারণ করে তার অস্তিত্ব রক্ষার যে সংগ্রাম, তা এক অপমানিত নারীর মতো, যে সকল প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও তার স্বতন্ত্র সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।
৩.২.২ “পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন।”- ‘পঞ্চকন্যা’ কারা? তারা কীভাবে চেতনা ফিরে পেল?
উত্তর: নির্দিষ্ট অংশটি আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ আলাওল রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতায়, সিন্ধু নদের তীরে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা এক অপরূপা কন্যা ও তার চার সখীকে একত্রে ‘পঞ্চকন্যা’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সমুদ্রকন্যা পদ্মা সিন্ধুতীরে ভেলায় ভাসমান এই পঞ্চকন্যাকে উদ্ধার করেন। তাদের চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে পদ্মা সর্বপ্রথম নিরঞ্জনের কাছে প্রার্থনা করেন। পাশাপাশি, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়। পদ্মার আদেশে সখীরা পঞ্চকন্যাকে নতুন বস্ত্রে আবৃত করে একটি উদ্যানে নিয়ে যান। সেখানে আগুন জ্বালিয়ে (শেক দেওয়া), তন্ত্র-মন্ত্র প্রয়োগ এবং মহৌষধি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। প্রায় চার দণ্ডকাল (প্রায় ৯৬ মিনিট) ধরে অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষার পর কন্যাটির চৈতন্য ফিরে আসে।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ ‘বহুরূপী’ গল্প অবলম্বনে হরিদা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: হরিদা একজন দক্ষ বহুরূপী, যাঁর প্রতিটি অভিনয় শিল্পীর নিখুঁত সত্তার স্বাক্ষর বহন করে। বাইজী, পাগল বা পুলিশ—নানা রূপে তিনি শ্রোতাদেরকে বারবার বিস্মিত করেছেন। দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁর সততা ও পেশার প্রতি নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। পুলিশের ছদ্মবেশে মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে নেওয়া ঘুষের জন্য তিনি পরবর্তীতে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর পেশাকে কেবল ভালোবাসতেন তাই নয়, এর প্রতি ছিল গভীর এক দায়বদ্ধবোধ। বিরাগীর ভেশে জগদীশবাবুর দেওয়া টাকা ফেরত দেওয়া এরই প্রমাণ। তবে হরিদার মধ্যে বাস্তববোধের কিছুটা অভাব ছিল। তাঁর চুলায় হাঁড়িতে জল ফুটলেও ভাত থাকত না, তবু তিনি থাকতেন নির্বিকার। অভাব-অনটন মেনে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল না, কিন্তু একঘেয়ে জীবনযাপন করতে তিনি রাজি ছিলেন না। তিনি চাকরির নিয়মিত ধারায় আবদ্ধ হতে চাননি। কল্পনায় বেঁচে থাকাই ছিল তাঁর স্বভাব, তাই বাস্তবের দুঃখকষ্ট তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারত না। জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য না এলেও, তাঁর রূপসাধনা তাঁকে একজন সত্যিকার শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হরিদা হলেন একজন সংগ্রামী, নিষ্ঠাবান ও একনিষ্ঠ শিল্পীর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।
৪.২ “কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি।” কে, কার সম্পর্কে একথা বলেছেন? তার দৃষ্টিকে ‘আশ্চর্য’ বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: এই উক্তিটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘পথের দাবী’ গ্রন্থের চরিত্র অপূর্বর। এটি তিনি গিরীশ মহাপাত্রের উদ্দেশ্যে বলেন।
গিরীশ মহাপাত্রের পোশাক-অপোশাকে মিল নেই, শরীরও দুর্বল, তবু চোখের দৃষ্টি ছিল প্রখর। গভীর জলাধারের মতো তার সেই গভীর দৃষ্টি তাকে সবার চেয়ে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। সেই চোখেরই এক অগাধ তলদেশে তার সামান্য যে প্রাণশক্তি অবশিষ্ট ছিল, তা লুকিয়ে থাকত—মৃত্যুও সেখানে পৌঁছতে সাহস পায় না। শুধু এই কারণেই সে যেন এখনও জীবিত। এই কারণের জন্যই তার দৃষ্টিকে ‘আশ্চর্য’ বলা হয়েছে।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ “আমাদের শিশুদের শব / ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে!” শিশুদের শব ছড়িয়ে রয়েছে কেন? শিশুদের শব দেখে কবির মনের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল?
উত্তর: শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায় সময় ও সমাজের নানাবিধ অস্থিরতাকে চিত্রিত করেছেন। চারদিকে ধ্বংসের এক অনিবার্য আয়োজন। ‘ডানপাশে ধ্বস’ ও ‘বাঁয়ে গিরিখাদ’ যেন সর্বনাশের প্রতীক। মাথার ওপর বোমারু বিমানের বিচরণ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে। আর যুদ্ধের অর্থই হলো ধ্বংস ও মৃত্যু, যার পরিণামে মানুষের চলার পথ বিঘ্নিত হয় এবং তারা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। এই ধ্বংসের উন্মত্ততাই শিশুদের জীবন কেড়ে নেয়। ‘কাছে দূরে’ অর্থাৎ সর্বত্রই শিশুদের মৃতদেহ ছড়িয়ে থাকে। শিশুমৃত্যুই সভ্যতার জন্য সর্বনাশের বার্তা বহন করে; যুদ্ধের নৃশংসতার এটি এক জীবন্ত প্রতীক। শিশুদের মৃত্যু কোনো সাধারণ মৃত্যু নয়, কারণ তারাই তো ভবিষ্যৎ সমাজের নির্মাতা। তাদের প্রাণহানি মানেই সভ্যতার ভবিষ্যৎ শূন্য হয়ে পড়া। দ্বিতীয়ত, শিশুদের মৃত্যু সমাজের বাকি মানুষদেরও মৃত্যুভয়ে আক্রান্ত করে তোলে— “আমরাও তবে এইভাবে/এ মুহূর্তে মরে যাব না কি?” ‘কাছে দূরে’ ছড়িয়ে থাকা ‘শিশুদের শব’ সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করে, তাদের মনে এক গভীর বিপন্নবোধের সৃষ্টি করে, যার মূলে রয়েছে এই নিষ্পাপ প্রাণগুলির মৃত্যু।
৫.২ “চিত্রের পোতলি সমা/ নিপতিত মনোরমা” কাকে, কেন ‘চিত্রের পোতলি সমা’ মনে হয়েছে? তিনি কেন নিপতিত হন এবং তারপর তার কী অবস্থা হয়েছিল?
উত্তর: চিত্রের পুতুলের সঙ্গে তুলনার কারণ – সমুদ্রতীরে অচেতন পদ্মাবতীকে পুতুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল সমুদ্রকন্যা পদ্মা। কখনও মনে হয়েছিল, সেই সৌন্দর্য রম্ভাকেও পরাজিত করতে পারে; কখনও বা মনে হয়েছে, ইন্দ্রের অভিশাপগ্রস্ত কোনো বিদ্যাধরি পৃথিবীতে এসে পড়েছেন। এই অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্যই তাঁকে ছবির পুতুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।”
রানা রত্নসেনের সাথে বিয়ের পর পদ্মাবতী সমুদ্রপথে চিতোরে আসছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ে তাদের জাহাজ ডুবে যায়। কলার মান্দাসে আশ্রয় নিলেও আর রক্ষা পাওয়া যায়নি। পদ্মাবতী রত্নসেন থেকে আলাদা হয়ে যান। এরপর আঘাতপ্রাপ্ত রাজকন্যা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সমুদ্র তীরে অচেতন অবস্থায় তাঁর চার সখীকে নিয়ে ভেসে উঠেন।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ ‘ফাউন্টেন পেন’ বাংলায় কী নামে পরিচিত? নামটি কার দেওয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে? ফাউন্টেন পেন-এর জন্ম ইতিহাস লেখো।
উত্তর: “হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” প্রবন্ধে বর্ণিত ফাউন্টেন পেন বাংলায় ‘ঝরনা কলম’ নামে পরিচিত।
এই সুন্দর ও অর্থবহ বাংলা নামটির নামকরণ করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বের অনেক আবিষ্কারের মতোই এই ঝরনা কলমের আবিষ্কারের পেছনেও রয়েছে একটি আকর্ষণীয় ঘটনা। এই পেনের স্রষ্টা লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যান ছিলেন একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। সেই সময়ের প্রচলন অনুযায়ী, তিনি কাজে বের হতেন দোয়াত ও কলম নিয়ে। একবার, তিনি একটি বড় চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে যান। চুক্তিপত্রটি লেখা হচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ করেই দোয়াতটি উল্টে যায় এবং সমস্ত কালি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশৃঙ্খলা সামলাতে ওয়াটারম্যানকে নতুন কালি আনতে বাইরে যেতে হয়। ফিরে এসে দেখেন, সেই সুযোগে অন্য ব্যবসায়ী চুক্তিটি করে নিয়ে গেছেন। এই বিরক্তিকর ও ক্ষতিজনক ঘটনা থেকেই তাঁর মনে একটি নির্ভরযোগ্য কলম তৈরির পরিকল্পনা জন্মায়। কালি যাতে সহজে ঝরে না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন একটি নতুন ধরনের কলম, যা ফাউন্টেন পেন বা ঝরনা কলম নামে পরিচিত। এভাবে, একটি ছোটো দুর্ঘটনা থেকেই লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যান লেখালেখির জগতে খুলে দিলেন ‘কালির এক অফুরন্ত ঝরনা’।
৬.২ “কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে যত কম থাকে ততই ভালো।” কী কম থাকার কথা বলা হয়েছে? সেই বিষয়গুলিকে পরিস্ফুট করো।
উত্তর: রাজশেখর বসুর ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধটি থেকে আলোচ্য অংশটি গৃহীত হয়েছে। এতে আলংকারিকদের বর্ণিত শব্দের তিনটি শক্তি—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনায় এগুলির ব্যবহার যথাসম্ভব সীমিত রাখা উচিত। এক্ষেত্রে কম ব্যবহারের সুবিধা হলো – ‘অভিধা’ শক্তি দ্বারা শব্দ তার স্পষ্ট ও মৌলিক অর্থ প্রকাশ করে, যা ‘অভিধেয়’ বা ‘বাচ্যার্থ’ নামে পরিচিত। ‘লক্ষণা’ শক্তি কাজ করে যখন বাচ্যার্থের সূত্র ধরে একটি গৌণ বা সম্পর্কিত অর্থ বোঝায়। আর ‘ব্যঞ্জনা’ হলো সেই শক্তি যার মাধ্যমে অভিধা ও লক্ষণাকে অতিক্রম করে একটি সম্পূর্ণ নতুন ও গূঢ় অর্থ প্রকাশ পায়; যেমন—’অর্ধচন্দ্র’ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে চাঁদের অংশ না বোঝালেও ব্যঞ্জনায় এটি ‘গলাধাক্কা’ অর্থ বহন করে। সাহিত্যে এই শক্তিগুলির ব্যবহার চলে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক রচনায় অলংকার পরিহার্য। এর কারণ, বিজ্ঞান হলো জ্ঞানের বিষয়, তাই এর ভাষা হতে হবে সহজ, সরল ও স্পষ্ট। রূপক বা উপমার কিছু সীমিত প্রয়োগ হয়তো হতে পারে, কিন্তু অলংকারের আধিক্য পাঠকের জন্য বোধগম্যতাকে জটিল করে তোলে।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “আমার এই অক্ষমতার জন্যে তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।” বক্তা কোন্ বিষয়ে তাঁর অক্ষমতার কথা বলেছেন? তাঁর ক্ষমা চাওয়ার কারণ কী?
উত্তর: প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর “সিরাজদ্দৌলা” নাটক থেকে সংগৃহীত, যার বক্তা নবাব সিরাজদ্দৌলা নিজেই। তিনি ফরাসি প্রতিনিধি মসিয়ে লা-কে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলেন। ইংরেজ-ফরাসি দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে ইংরেজরা নবাবের অনুমতি ছাড়াই চন্দননগর দখল করে নেওয়ায়, ফরাসিরা নবাবের কাছে সুবিচার চাইলে তিনি তাদের সাহায্য করতে ব্যর্থ হন। ফরাসিদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত সহানুভূতি থাকলেও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও পরিস্থিতির চাপে তিনি হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম হন। এই অসহায়ত্ব ও নিজের অক্ষমতার জন্য তিনি আন্তরিক লজ্জা ও অনুতপ্তি প্রকাশ করে ফরাসি প্রতিনিধির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।
৭.২ ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ অবলম্বনে লুৎফা চরিত্রের বিশেষ দিকগুলি আলোচনা করো।
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশে দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে সিরাজের পত্নী লুৎফা অন্যতম। নাটকে তাঁর উপস্থিতি স্বল্প হলেও তা তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর চরিত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নরূপ—
(ক) সরলতা:
সভাসদদের সঙ্গে মানসিক সংঘর্ষে যখন সিরাজ সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত, তখনই লুৎফার আবির্ভাব ঘটে। নবাবের বেগম হয়েও তিনি কখনও রাজনীতির চক্রে নিজেকে জড়াননি। বরং সহজ-সরল গৃহিণীর মতোই তিনি সংসারকেন্দ্রিক থেকেছেন। এমনকি ঘসেটির তীব্র ভর্ৎসনার পরেও লুৎফা কোনো কটুবাক্য উচ্চারণ করেননি, যা তাঁর নম্রতার পরিচয় বহন করে।
(খ) যোগ্য সঙ্গিনী:
লুৎফা স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীলা। সিরাজ যখন রাজ্য পরিচালনায় নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত, তখন তিনি স্বামীকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে একজন যোগ্য সঙ্গিনীর ভূমিকা পালন করেন। স্বামীর দুঃখ-দুর্দশায় পাশে থেকে তিনি সহায়তা করেছেন।
(গ) সহমর্মিতা:
নাটকে লুৎফা এক কোমল হৃদয়ের নারী। নবাবের চোখের জল দেখে তিনি বেদনার্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর অমঙ্গল চিন্তায় আতঙ্কিত হন। লুৎফার কাছে রাজনীতি নয়, স্বামীর কল্যাণই মুখ্য। তিনি ঘসেটিকে ‘মা’ বলে সম্মান জানালেও যখন সেই ‘মা’র মুখে প্রতিহিংসার কথা শুনেছেন, তখন তাঁর কাছে সেই সম্পর্ক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। লুৎফা সেই নারী চরিত্র, যিনি ট্র্যাজিক নায়কের পাশে থেকে তাকে ভালোবাসা, সেবা, সাহস ও আস্থা যুগিয়েছেন।
(ঘ) সাধারণ নারীচরিত্র:
মহিষী হয়েও লুৎফার মধ্যে বেগমসুলভ অহংকার দেখা যায় না। পলাশির যুদ্ধের কথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং সাধারণ এক নারীর মতোই চান না তাঁর স্বামী যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হোক।
সার্বিকভাবে লুৎফা চরিত্রটি একাধারে একজন দায়িত্বশীলা পত্নী, সহানুভূতিশীল নারী ও একজন মানবিক সঙ্গিনীর প্রতিচ্ছবি বহন করে।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
৮.১ জুপিটার ক্লাবে ক্ষিতীশের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি কী ছিল? এগুলির উত্তরে ক্ষিতীশের বক্তব্য কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা নিজের ভাষায় লেখো।
উত্তর: “কোনি” উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, যার রচয়িতা মতি নন্দী, জুপিটার ক্লাবের একটি সভার বর্ণনা রয়েছে। ক্ষিতীশের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাঁতারুদের অভিযোগ নিয়ে আলোচনার জন্য এই সভা ডাকা হয়েছিল। সভায় পৌঁছে ক্ষিতীশ সকলকে জানান যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি চিঠিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। হরিচরণ তখন দাবি করেন যে, ক্লাবের জন্য মেডেল জয়ী এবং সম্মান বয়ে আনা অনেক সাঁতারুকেই ক্ষিতীশ সিংহ অকারণে অপমান করেছেন, যার ফলে তারা ক্লাব ছেড়ে চলে গেছেন। এর জবাবে ক্ষিতীশ প্রতিবাদ করে বলেন যে, সাঁতারুরা কঠোর পরিশ্রমের বদলে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করে। হরিচরণ ক্ষিতীশের ব্যাখ্যা শুনতে অস্বীকার করে অভিযোগের তালিকা পেশ করতে থাকেন। বদু চাটুজ্জে মন্তব্য করেন যে, ক্ষিতীশের প্রতি সাঁতারুদের কোনও শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নেই। তিনি উল্লেখ করেন যে, ক্ষিতীশ নিজে কোনও প্রতিযোগিতায় মেডেল জিতেননি, অন্যদিকে হরিচরণ ছিলেন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং অলিম্পিয়ান। ক্ষিতীশ তাঁর বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ স্বীকার করে নেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে, জুপিটার ক্লাব যাতে ভারতের সেরা হয় সেই আশায়ই তিনি সাঁতারুদের প্রতি কঠোর ছিলেন। তাঁর মতে, ক্লাবের সাঁতারুদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও মনোযোগের মারাত্মক অভাব রয়েছে। কিন্তু যখন হরিচরণ দাবি করেন যে, এই একই সাঁতারুদের দিয়েই ভালো ফলাফল সম্ভব এবং তিনিই তা করতে পারেন, তখন ক্ষিতীশ মুখ্য প্রশিক্ষকের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দেন। ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে কেউই এতে আপত্তি করেননি। ফলে ক্লাবের সাথে ক্ষিতীশের চিরবিচ্ছেদ ঘটে। সকলেই চেয়েছিল যে ক্ষিতীশ তাঁর দায়িত্ব থেকে সরে যান।
৮.২ ‘অবশেষে কোনি বাংলা সাঁতার দলে জায়গা পেল।’ কোনি কীভাবে বাংলা সাঁতার দলে জায়গা পেল, তা লেখো।
উত্তর: মতি নন্দী রচিত কোনি” উপন্যাসে বাস্তবে কোনির সাঁতার কাটা শুরু গঙ্গায়। সেখান থেকে বাংলা দলে জায়গা করে নেওয়া নিঃসন্দেহে সহজ কাজ ছিল না। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার কারণে তাকে শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের কাছে বারবার হেয়প্রতিপন্ন হতে হয়েছে। কোনির নাম প্রথম বাংলা দলে তুলে ধরেন প্রণবেন্দু বিশ্বাস। তিনি কোনির প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও তার প্রশিক্ষক ছিলেন এবং জোর দিয়ে বলেন, “কনকচাঁপা পালকে বাংলা দলে রাখতেই হবে।” মাদ্রাজের BASA-র নির্বাচনী সভায় তিনি কোনির পক্ষে কথা বলেন। কিন্তু জুপিটারের (বাংলা দলের কর্তাব্যক্তি) ক্ষিতীশ রায়ের বিরোধিতার কারণে তারা কোনিকে দলে রাখতে অস্বীকার করেন। এর আগে একটি প্রতিযোগিতায় কোনিকে অকারণে অযোগ্য ঘোষণা করে প্রথম হওয়া সত্ত্বেও তাকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়। হরিচরণ ও ধীরেন ঘোষের গোপন ষড়যন্ত্রে এই কাজগুলি করা হয়। তবে প্রণবেন্দু বাবু ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহারাষ্ট্রের রমা যোশিকে হারানোর মতো ক্ষমতা যদি কারও থাকে, তা হলো কোনির। তিনি এ-ও বলেন যে, কোনিকে বাদ দিলে বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবকেও বাদ দিয়ে বাংলা সাঁতার দল গঠন করতে হবে। তখন ধীরেন ঘোষ ভাবে, একটি মেয়ের জন্য এত সমস্যা হলে তাকে নিয়েই নেওয়া ভালো। এইভাবে নানা বাধা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে, প্রণবেন্দু বাবুর ন্যায়সংগত লড়াই এবং সুবিচারের ফলে, কোনি বঙ্গদেশের নয়নের মণি হওয়ার সুযোগ পায়।
৮.৩ বিষ্টুচরণ ধরের পরিচয় দাও। তার চেহারা ও খাদ্যাভ্যাসের বিবরণ দাও।
উত্তর: মতি নন্দী, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ক্রীড়াপ্রেমী লেখক, তাঁর যুগান্তকারী ‘কোনি’ উপন্যাসে বিষ্টুচরণ ধর নামের একটি অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসে এই চরিত্রটির বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন— “বিষ্টু ধর (পাড়ার ডাকে বেষ্টাদা) আই.এ. পাস, অত্যন্ত বনেদি বংশের, খান সাথেক তার বাড়ি ও বড় বাজারে ঝাড়ন-মশলার কারবার এবং সর্বোপরি, সাড়ে তিন মণ ওজনের এক দেহের মালিক।” তার এই বিশাল দেহটি তার সমবয়সী চল্লিশ বছরের একটি বিশ্বস্ত অস্টিন গাড়ি সর্বত্র বহন করে বেড়ায়। তানপুরা, তবলা, সারেগামা— এই বিচিত্র সুরে মালিশ করানোর মধ্যে দিয়ে সে এক পরম তৃপ্তি পায়। আর সেই মালিশওয়ালা তার ডান হাঁটু বিষ্টুর কোমরে চেপে ধরে, পিস্টনের মতো তার মেরুদণ্ড বরাবর ঘাড় পর্যন্ত দ্রুত ওঠানামা করতে থাকে। বর্তমানে ভোটে দাঁড়ানোর এক সুপ্ত বাসনা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আর এই বাসনা পূরণের তাগিদেই সে পাড়ার বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করে এবং অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিষ্টু চরিত্রটি হল এক হাস্যকর, পরোপকারী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।
বিষ্টুচরণের মুখে তাঁর খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনা শুনে আমাদের হাসি পায়। বিশালাকায়, অর্থাৎ সাড়ে তিন মণ ওজনের এই মানুষটিই এখন ডায়েটিং শুরু করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আগে প্রতিদিন আধ কিলো ক্ষীর খেতেন, এখন খান তিনশো গ্রাম; জলখাবারে কুড়িটি লুচি খেতেন, এখন পনেরোটি; ভাত খান মেপে—আড়াইশো গ্রাম চালের; রাতে রুটি বারোটি। ঘি খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন—গরম ভাতের সঙ্গে চার চামচের বেশি নয়। বিকেলে দু’গ্লাস মিছরির শরবত আর চারটি করে কড়া পাকের মিষ্টি। বাড়িতে রাধাগোবিন্দের মূর্তি থাকায় তিনি মাংস খান না। বিষ্টুচরণের এই খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনায় বাঙালির চিরন্তন ভোজনরসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো :
Honesty is a great virtue. If you do not deceive others, if you do not tell a lie, if you are strictly just and fair in your dealings with others, you are an honest man. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. Every man trusts an honest man. None can prosper in life if he is not honest.
উত্তর: সততা একটি মহান গুণ। তুমি যদি কাউকে প্রতারণা না করো, মিথ্যে কথা না বলো, অন্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে ন্যায্য ও সৎ থাকো, তবে তুমি একজন সৎ মানুষ। সততাই হলো সর্বোত্তম নীতি। সৎ মানুষকে সবাই সম্মান করে। সবাই একজন সৎ মানুষের ওপর ভরসা করে। যে সৎ নয়, সে জীবনে কোনোদিন প্রকৃত সাফল্য পেতে পারে না।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ মাধ্যমিকের পর কী বিষয় নিয়ে পড়বে এ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
মাধ্যমিকের পর কী বিষয় নিয়ে পড়বো
রাহুল: শোন শুভ, মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রায় শেষ। এখন তো ভাবতে হবে কোন বিষয়ে পড়ব। তুমি কী ভেবেছ?
শুভ: হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। আমার তো বিজ্ঞান বিষয়ে খুব আগ্রহ। ডাক্তার হতে চাই, তাই জীববিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাই।
রাহুল: খুব ভালো। আমি আবার সংখ্যার প্রতি বেশি টান অনুভব করি। তাই আমি বাণিজ্য বিভাগ নিতে চাই। ভবিষ্যতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার ইচ্ছে আছে।
শুভ: দারুণ ব্যাপার! তবে তুমি কি মনে করো বাণিজ্য নিয়ে ভালো সুযোগ পাওয়া যাবে?
রাহুল: অবশ্যই। এখন ব্যবসা ও অর্থনীতির জগতে বাণিজ্য শিক্ষার গুরুত্ব অনেক। আর বিজ্ঞান নিয়েও তো অসংখ্য সুযোগ রয়েছে।
শুভ: ঠিক বলেছো। আসলে আগ্রহ আর পরিশ্রম থাকলে সব বিষয়েই সাফল্য পাওয়া যায়।
রাহুল: একদম ঠিক। তাহলে আমাদের দুজনেরই লক্ষ্য ঠিক হয়ে গেল। এবার শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে।
১০.২ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘প্লাস্টিক বর্জন বিষয়ে সচেতনতা শিবির’-এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
বিদ্যালয়ে প্লাস্টিক বর্জন বিষয়ে সচেতনতা শিবির
নিজেস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৫: গতকাল স্থানীয় একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্লাস্টিক বর্জন বিষয়ে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিবিরের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।
শিবিরে বক্তারা প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারা জানান, প্লাস্টিক পরিবেশ ও প্রাণিজগতের জন্য মারাত্মক হুমকি। প্লাস্টিক বর্জ্য মাটি ও জল দূষণ ঘটায়, এমনকি পশুপাখির জীবনও বিপন্ন করে তোলে। প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাপড়, কাগজ ও জৈব-বান্ধব দ্রব্য ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে পোস্টার ও স্লোগান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিবির শেষে সকলে শপথ নেয়— “প্লাস্টিক নয়, পরিবেশবান্ধব জিনিসই ব্যবহার করব।”
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো:
১১.১ বিজ্ঞান ও কুসংস্কার।
উত্তর:
বিজ্ঞান ও কুসংস্কার
মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। বিজ্ঞান মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় এনেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ছোঁয়া লেগেছে। বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, যোগাযোগব্যবস্থা, পরিবহন, প্রযুক্তি—সবকিছু বিজ্ঞানের দান। তবুও সমাজের অনেক কোণে আজও কুসংস্কারের অস্তিত্ব টিকে আছে।
বিজ্ঞান হলো যুক্তি, প্রমাণ ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জ্ঞানের ভান্ডার। অন্যদিকে কুসংস্কার হলো অজ্ঞতা, ভয় এবং অযৌক্তিক বিশ্বাসের ফল। যেমন—গ্রহণকালে অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ, পেঁচা ডাকলে অমঙ্গল, গর্ভবতী মহিলার বাইরে বেরোনো অনুচিত ইত্যাদি। এসব ধারণার পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই।
কুসংস্কার সমাজের উন্নয়নে বড়ো বাধা। এটি মানুষকে অন্ধবিশ্বাসী করে তোলে। অনেক সময় রোগের সঠিক চিকিৎসার পরিবর্তে মানুষ ঝাড়ফুঁক বা ওঝার কাছে ছুটে যায়। ফলে অনেক জীবন অকালেই নষ্ট হয়। আবার কুসংস্কারের কারণে নারী নির্যাতন, ডাইনী অপবাদ ইত্যাদি অপরাধও সমাজে ঘটে থাকে।
অন্যদিকে, বিজ্ঞান মানুষকে মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদী মনোভাব শেখায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, মহাকাশ জয় হয়েছে, প্রযুক্তির উন্নতিতে পৃথিবী হয়েছে ছোট। তাই সমাজকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে হলে বিজ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা, গ্রামে গ্রামে সচেতনতা শিবির, গণমাধ্যমে প্রচার—এসব উদ্যোগ মানুষকে কুসংস্কার থেকে দূরে রাখতে সহায়ক।
এ কথা সত্য, বিজ্ঞান ও কুসংস্কার কখনো একসঙ্গে চলতে পারে না। যেখানে বিজ্ঞান আছে, সেখানে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের স্থান নেই। তাই শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞানের পথেই এগোতে হবে।
বিজ্ঞান মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আর কুসংস্কার টেনে ধরে পেছনে। আমাদের উচিত বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হওয়া এবং কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলা। তবেই সমাজ হবে উন্নত, সুস্থ ও সুন্দর।
১১.২ একটি কলমের আত্মকথা।
উত্তর:
একটি কলমের আত্মকথা
আমি একটি কলম। আমার জন্ম এক নামী কলম কারখানায়। চকচকে রূপ, সুন্দর নকশা আর মসৃণ নিব নিয়ে দোকানের কাঁচের আলমারিতে সাজানো হয়েছিলাম। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আমাকে দেখত, কেউ হাতে নিত, আবার ফেরত রেখে দিত। অবশেষে একদিন এক স্কুলছাত্র আমাকে কিনে নিল। সেদিন থেকে শুরু হলো আমার জীবনের আসল গল্প।
ছেলেটি আমাকে তার কলমদানি বা পকেটে যত্ন করে রাখত। আমার কালো কালি দিয়ে সে লেখার খাতায় অক্ষর এঁকে দিত। কখনো কবিতা লিখত, কখনো গণিতের অঙ্ক করত। পরীক্ষার খাতায় আমাকে দিয়েই সে সুন্দর করে উত্তর লিখত। আমি ভীষণ খুশি হতাম, কারণ আমার অস্তিত্বের প্রকৃত সার্থকতা মানুষের কাজে লাগাতেই।
আমাকে দিয়ে শুধু পড়াশোনার কাজই হয়নি, আরও অনেক আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কখনো বন্ধুর কাছে চিঠি লিখেছে, কখনো ডায়রির পাতায় তার মনের কথা লিখে রেখেছে। আমার কালির রেখায় জমে উঠেছে হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার গল্প। আমি অনুভব করেছি, মানুষের মনের সমস্ত আবেগ-অভিব্যক্তির সঙ্গী হয়ে উঠতে পারলেই কলমের জীবন সফল হয়।
তবে আমার জীবন সবসময় সহজ ছিল না। অনেক সময় আমাকে অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে, আবার হারিয়েও ফেলা হয়েছে। কখনো কালি শেষ হয়ে গেলে আমাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলার কথাও ভেবেছে সে। কিন্তু আবার নতুন কালি ভরে আমাকে ব্যবহার করেছে। বুঝেছি, মানুষের জীবনে জিনিসের মূল্য তখনই বোঝা যায়, যখন সেটি কাজে লাগে।
আজ আমি কিছুটা পুরোনো হয়ে গেছি। আমার রঙ ফিকে হয়েছে, নিব ঘষে গেছে। হয়তো খুব শিগগিরই আমাকে বাদ দিয়ে নতুন কলম কিনবে সে। তবুও আমার আফসোস নেই। কারণ আমি আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছি।
আমি গর্বিত যে, আমার কালির রেখায় কোনো ছাত্র তার জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচন করেছে, কোনো কবি তার স্বপ্ন এঁকেছে, আর কোনো মানুষ তার আবেগ প্রকাশ করেছে। আমি জানি, যতদিন মানুষ লিখতে চাইবে, ততদিন কলম মানুষের সেরা সঙ্গী হয়ে থাকবে।
১১.৩ উৎসবে ধর্মনিরপেক্ষতা।
উত্তর:
উৎসবে ধর্মনিরপেক্ষতা
ভারত একটি বহুধর্মবিশিষ্ট দেশ। এখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখসহ নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করেন। ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতি হলেও উৎসবের আনন্দে সকলে মিলেমিশে যায়। এই মিলনই আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার মূল ভিত্তি। বাংলার উৎসবগুলিতেও আমরা সেই ঐক্যের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট দেখতে পাই।
বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এটি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলেও সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দে শরিক হয়। প্রতিমা দর্শন, আলোকসজ্জা দেখা, মেলা ঘোরা— এসব আনন্দে ধর্মভেদ থাকে না। অনেক মুসলিম শিল্পী প্রতিমা গড়েন, মুসলিম ও খ্রিস্টান বন্ধুরা সানন্দে প্যান্ডেলে যায়। এভাবেই দুর্গাপূজা হয়ে ওঠে মিলনমেলা।
তেমনি ঈদুল-ফিতর বা ঈদুল-আজহা শুধু মুসলিমদের নয়, সমগ্র বাংলার উৎসব। ঈদের দিনে হিন্দু প্রতিবেশীরাও মুসলিম বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে সেমাই খায়, শুভেচ্ছা জানায়। আবার ক্রিসমাস এলে পার্ক স্ট্রিট আলোকসজ্জায় ভরে ওঠে, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সেখানে আনন্দ উপভোগ করে। গুরুনানক জয়ন্তী বা মহরমও বহু মানুষের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।
এছাড়া জাতীয় উৎসবগুলো যেমন স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, গান্ধীজয়ন্তী— এগুলো সব ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সমানভাবে পালিত হয়। এসব উৎসব আমাদের জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে।
উৎসবে ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে বড় দিক হলো, মানুষ ভেদাভেদ ভুলে একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। উৎসবের আনন্দ কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিকও বটে। ধর্মীয় ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও উৎসবই আমাদের একত্র করে।
বাংলার উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয়— মানবতাই আসল ধর্ম। আনন্দ, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছড়িয়ে দিতে হলে উৎসবে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা জরুরি। এভাবেই উৎসব হয়ে ওঠে সত্যিকার অর্থে মানুষের উৎসব।
১১.৪ মহাকাশ গবেষণায় সাম্প্রতিককালে ভারতের সাফল্য।
উত্তর:
মহাকাশ গবেষণায় সাম্প্রতিককালে ভারতের সাফল্য
ভারত আজ মহাকাশ গবেষণায় বিশ্বের অন্যতম অগ্রগণ্য দেশ। স্বাধীনতার পর সীমিত প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও ভারত মহাকাশ বিজ্ঞানে ধাপে ধাপে অসাধারণ উন্নতি করেছে। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) একাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, যা দেশকে আন্তর্জাতিক পরিসরে গর্বিত করেছে।
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলো চন্দ্রযান-৩–এর সাফল্য। ২০২৩ সালের ২৩ জুলাই উৎক্ষেপণের পর আগস্ট মাসে চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ কৃতিত্ব অর্জনকারী ভারত প্রথম দেশ। এর ফলে ভারত মহাকাশ গবেষণায় এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। চন্দ্রযান-৩ এর মাধ্যমে চাঁদের মাটি, খনিজ ও পরিবেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।
আরও এক গর্বের অধ্যায় হলো আদিত্য-এল১ মিশন। সূর্য অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপিত এ উপগ্রহ ভারতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। সূর্যের করোনা, সৌরঝড় ও বিকিরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ মিশন ভবিষ্যতে মানবসমাজকে উপকৃত করবে।
এছাড়া ভারত ইতিমধ্যেই সফলভাবে বহু উপগ্রহ কক্ষপথে পাঠিয়েছে। যোগাযোগ, আবহাওয়া পূর্বাভাস, কৃষি, প্রতিরক্ষা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব উপগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০১৭ সালে ভারত একসঙ্গে ১০৪টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিল। সাম্প্রতিককালে ভারত অন্যান্য দেশকেও স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে সহযোগিতা করছে, যা ভারতের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
আগামী দিনে ভারতের লক্ষ্য আরও বড়ো। মানববাহী মহাকাশ অভিযান গগনযান মিশন ইতিমধ্যেই প্রস্তুতিতে রয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতীয় মহাকাশচারীরা মহাকাশে যাত্রা করবে। পাশাপাশি মঙ্গল গ্রহে দ্বিতীয় অভিযান মঙ্গলযান-২–এর পরিকল্পনাও চলছে।
মহাকাশ গবেষণায় ভারতের সাম্প্রতিক সাফল্য শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নয়, জাতীয় গৌরব বৃদ্ধিতেও বিরাট অবদান রেখেছে। এসব সাফল্য প্রমাণ করেছে যে সীমিত সম্পদ নিয়েও দৃঢ় মনোবল, কঠোর পরিশ্রম ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ভারত বিশ্বমঞ্চে সবার কাতারে দাঁড়াতে সক্ষম। ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানে ভারত নিঃসন্দেহে আরও নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।