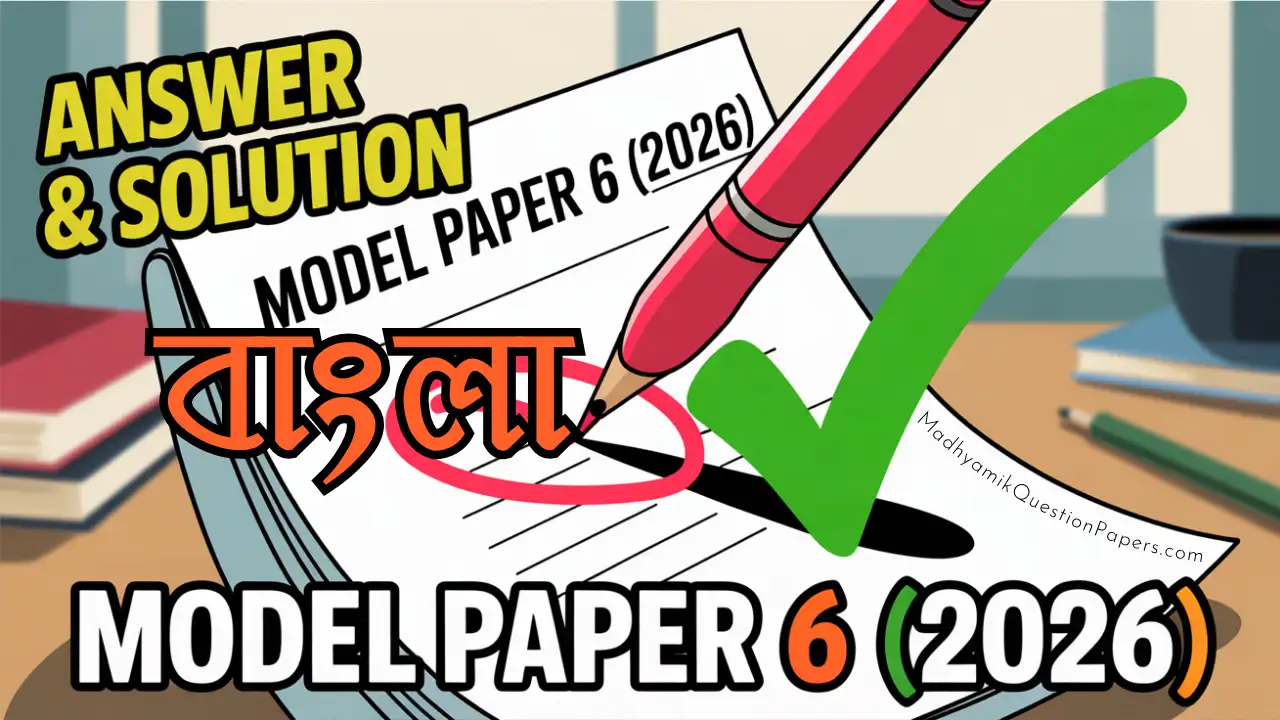আপনি কি মাধ্যমিকের বাংলা Model Question Paper 6 প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন? দেখে নিন 2026 WBBSE বাংলা Model Paper 6-এর সঠিক উত্তর ও বিশ্লেষণ। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 6- এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৬ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ সন্ন্যাসী সারা বছর খেতেন-
(ক) একটি বেল
(খ) একটি আমলকি
(গ) একটি হরিতকি
(ঘ) একটি বহেড়া
উত্তর: (গ) একটি হরিতকি
১.২ গিরীশ মহাপাত্রের ট্যাঁকে পাওয়া গিয়েছিল
(ক) দুটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা
(খ) একটি টাকা ও গণ্ডা-চারেক পয়সা
(গ) দুটি টাকা ও গণ্ডা-চারেক পয়সা
(ঘ) একটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা
উত্তর: (খ) একটি টাকা ও গণ্ডা-চারেক পয়সা
১.৩ ‘অদল বদল’ গল্পটি বাংলায় তরজমা করেছেন-
(ক) অর্ঘ্যকুসুম করগুপ্ত
(খ) অর্ঘ্যকুসুম সেনগুপ্ত
(গ) অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত
(ঘ) অর্ঘ্যকুসুম দাশগুপ্ত
উত্তর: (গ) অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত
১.৪ ‘দিগম্বরের জটায় হাসে’-
(ক) মহাপ্রলয়
(খ) শিশু-চাঁদের কর
(গ) চামর
(ঘ) দিগন্তরের কাঁদন
উত্তর: (খ) শিশু-চাঁদের কর
১.৫ ‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশটি কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? –
(ক) ‘লোরচন্দ্রাণী’
(খ) ‘পদ্মাবতী’
(গ) ‘সতীময়না’
(ঘ) ‘তোহফা’
উত্তর: (খ) ‘পদ্মাবতী’
১.৬ গান কোথায় কোথায় ঘুরবে?
(ক) নদীতে
(খ) যুদ্ধক্ষেত্রে
(গ) দেশগাঁয়ে
(ঘ) ক ও গ উভয়েই
উত্তর: (ঘ) ক ও গ উভয়েই
১.৭ পালকের কলমের ইংরেজি নাম হল
(ক) স্টাইলাস
(খ) ফাউন্টেন পেন
(গ) কুইল
(ঘ) রিজার্ভার পেন
উত্তর: (গ) কুইল
১.৮ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় একটি প্রধান বাধা হল
(ক) বাংলা ভাষার প্রতি অনীহা
(খ) ইংরেজির প্রতি আকর্ষণ
(গ) বাংলা পারিভাষিক শব্দ কম
(ঘ) বাংলা পারিভাষিক শব্দ বেশি
উত্তর: (গ) বাংলা পারিভাষিক শব্দ কম
১.৯ এক পাউন্ড সমান কত টাকা?
(ক) সত্তর টাকা
(খ) পঁচাত্তর টাকা
(গ) আট টাকা দশ আনা
(ঘ) একশো এক টাকা
উত্তর: (খ) পঁচাত্তর টাকা
১.১০ কলমে কায়স্থ চিনি নিম্নরেখ পদটি
(ক) অপাদান কারক
(খ) কর্তৃকারক
(গ) করণ কারক
(ঘ) কর্মকারক
উত্তর: (গ) করণ কারক
১.১১ ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্কহীন পদকে বলে
(ক) অনুসর্গ
(খ) নিমিত্ত কারক
(গ) অ-কারক
(ঘ) কর্তৃকারক
উত্তর: (গ) অ-কারক
১.১২ যে সমাসে সমস্যমান পদ দুটির উভয়পদই বিশেষ্য ও পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে বলে-
(ক) তৎপুরুষ সমাস
(খ) কর্মধারয় সমাস
(গ) দ্বন্দু সমাস
(ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস
উত্তর: (খ) কর্মধারয় সমাস
১.১৩ ‘রাজপথ’ শব্দটির ব্যাসবাক্য হল-
(ক) রাজা যে পথে চলে
(খ) রাজার পথ
(গ) রাজার দ্বারা চালিত পথ
(ঘ) পথের রাজা
উত্তর: (ঘ) পথের রাজা
১.১৪ চলন্ত গাড়িতে উঠতে যেও না। বাক্যটি
(ক) সরল বাক্য
(খ) যৌগিক বাক্য
(গ) জটিল বাক্য
(ঘ) নির্দেশক বাক্য
উত্তর: (ক) সরল বাক্য
১.১৫ একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে-
(ক) জটিল বাক্যে
(খ) সরল বাক্যে
(গ) যৌগিক বাক্যে
(ঘ) মিশ্রবাক্যে
উত্তর: (খ) সরল বাক্যে
১.১৬ ‘ঢাক বাজে’ এটি কোন্ বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্মবাচ্য
(খ) কর্মকর্তৃবাচ্য
(গ) কর্তৃবাচ্য
(ঘ) ভাববাচ্য
উত্তর: (খ) কর্মকর্তৃবাচ্য
১.১৭ দ্বারা, দিয়া ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়-
(ক) কর্তৃবাচ্যে
(খ) কর্মবাচ্যে
(গ) ভাববাচ্যে
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্যে
উত্তর: (খ) কর্মবাচ্যে
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ “সূচিপত্রেও নাম রয়েছে।” সূচিপত্রে কী লেখা ছিল?
উত্তর: আশাপূর্ণা দেবীর ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পে সন্ধ্যাতারা পত্রিকার সূচিপত্রে লেখা ছিল— ‘প্রথম দিন’ (গল্প), শ্রী: তপন কুমার রায়।
২.১.২ “সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস।” দুর্লভ জিনিসটি কী ছিল?
উত্তর: সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পের আলোচনা অংশে, জগদীশবাবুর গৃহে আগত সন্ন্যাসীর চরণধূলিকেই যে একটি দুর্লভ বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেটিই হল মূল আলোচ্য বিষয়।
২.১.৩ “অপূর্ব রাজি হইয়াছিল।” কোন্ কথায় অপূর্ব রাজি হয়েছিল?
উত্তর: রামদাসের স্ত্রীর অনুরোধে অপূর্ব এতে রাজি হয়েছিল যে, অপূর্বর মা বা কোনো আত্মীয় রেঙ্গুনে এসে ভালো ব্যবস্থা করা পর্যন্ত সে তার হাতের বানানো সামান্য কিছু খাবারই খাবে।
২.১.৪ “হঠাৎ অমৃতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল,” বুদ্ধি’-টা কী ছিল?
উত্তর: ইসাবের নতুন জামা ছিঁড়ে গেছে দেখে অমৃতের মাথায় এল যে, সে নিজের জামার সাথে ইসাবের জামা অদলবদল করে দেবে।
২.১.৫ ‘চিঠি পকেটেই ছিল।’ কোন্ চিঠি?
উত্তর: এখানে নদেরচাঁদ কর্তৃক তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী বিরহ-বেদনাপূর্ণ চিঠিটির উল্লেখ করা হয়েছে যা নদেরচাঁদের পকেটেই ছিল।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ ‘অসুখী একজন’ কবিতা অনুসরণে কথকের ঘর-গৃহস্থালির পরিচয় দাও।
উত্তর: কবিতার এই অংশ থেকে কথকের ঘর ও গৃহস্থালির একটি মর্মস্পর্শী ছবি পাওয়া যায়। এটি ছিল একটি শান্তিপূর্ণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর স্থান—যেখানে ঝুলন্ত বিছানা, করতলসদৃশ পাতা বিশিষ্ট গোলাপি গাছ, চিমনি এবং জলতরঙ্গের মতো উপাদান মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রিয় আবাস গড়ে উঠেছিল।
২.২.২ “পায়ে পায়ে হিমানীর বাঁধ” ‘পায়ে পায়ে’ বলতে কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: কবিতায় ‘পায়ে পায়ে হিমানীর বাঁধ’ অংশে ‘পায়ে পায়ে’ বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন প্রতি পদক্ষেপে, নিরবচ্ছিন্ন ও অবিরামভাবে। ‘হিমানীর বাঁধ’ এখানে এমন এক বাধা বা প্রতিবন্ধকতার প্রতীক, যা মানুষের জীবন-পথে ক্রমাগত সৃষ্টি হয় এবং তার অগ্রযাত্রাকে বিঘ্নিত করে।
২.২.৩ “কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে” আলোর কৃপণতার কারণ কী?
উত্তর: আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঘন চিরহরিৎ অরণ্যে সূর্যের আলো প্রায় প্রবেশই করতে পারে না। তাই সেখানে আলোর আগমন ‘কৃপণ’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
২.২.৪ “বিধি মোরে না কর নৈরাশ।।” বক্তা কোন্ বিষয়ে নিরাশ হতে চান না?
উত্তর: সমুদ্রযাত্রার ক্লান্তিতে অচেতন পদ্মাবতীর প্রাণসঞ্চার করতে চেয়েও, বক্তা সমুদ্রের কন্যা পদ্মার মনে মিথ্যা আশার সঞ্চার করতে অনিচ্ছুক।
২.২.৫ ‘আদুড় গায়ে’ বলতে কী বোঝো?
উত্তর: “আদুড়” শব্দের মানে হলো আবরণহীন; তাই “আদুড় গায়ে” বলতে বোঝায় খালি গায়ে।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ “সেটা অবশ্য ইচ্ছাকৃত নয়,” কোনটা ইচ্ছাকৃত নয়?
উত্তর: কবি শ্রীপান্থের লেখা হারিয়ে যাওয়া কালি কলম প্রবন্ধে ভিড়ের ট্রামে বাসে যাতায়াতের ফলে কোনো কোনো মহিলা চুলে কলম ধারণ করেন। এই বিষয়েই উক্তিটি করা হয়েছে।
২.৩.২ ‘এক সময় বলা হতো’ কী বলা হত?
উত্তর: কবি শ্রীপান্থের লেখা হারিয়ে যাওয়া কালি কলম প্রবন্ধে এক সময় বলা হতো – কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফেতে রাজপুত।
২.৩.৩ ‘অরণ্যে রোদন’ শব্দটির ব্যঞ্জনাগত অর্থ কী?
উত্তর: “অরণ্যে রোদন” বাগ্ধারাটির ব্যঞ্জনার্থ হলো — অনর্থক বা নিষ্ফল প্রচেষ্টা অথবা বৃথা চেষ্টা।
২.৩.৪ “বাংলায় বিজ্ঞান শেখা তাদের সংস্কারের বিরোধী নয়।” কাদের পক্ষে এই শিক্ষা সংস্কার বিরোধী নয়?
উত্তর: রাজশেখর বসুর লেখা ”বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান” প্রবন্ধ অবলম্বনে বাংলা পরিভাষা আয়ত্ত করে বাংলায় বিজ্ঞান শেখা বিষয় ইংরেজি না-জানা পাঠকদের কাছে সংস্কারের বিরোধী নয় বলে মনে করা হয়েছে।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ প্রযোজ্য কর্তার একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: প্রযোজ্য কর্তার একটি উদাহরণ – শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়ান।
২.৪.২ কারক ও অ-কারকের প্রধান পার্থক্যটি কী?
উত্তর: কারক ও অ-কারকের প্রধান পার্থক্য
১. কারক :
কারক হলো বাক্যে ব্যবহৃত নামপদ ও ক্রিয়াপদের মধ্যে সেই সম্পর্ক, যা নামপদটিকে ক্রিয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত করে। অর্থাৎ কারক থাকলে বোঝা যায়, কোন নামপদটি কীভাবে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত।
২. অ-কারক :
অ-কারক হলো সেই সকল নামপদ, যা ক্রিয়াপদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় বা কোনো সম্পর্ক নির্দেশ করে না। তবে বাক্যে থাকলেও তারা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় না।
২.৪.৩ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো: ‘মনমাঝি’।
উত্তর: ‘মনমাঝি’ পদটির ব্যাসবাক্য হল – মনই হলো মাঝি যার। ‘মনমাঝি’ পদটির সমাস হল – বহুব্রীহি সমাস।
২.৪.৪ সমাস ও সন্ধির দুটি পার্থক্য নির্দেশ করো।
উত্তর: সমাসের দুটি পার্থক্য হল –
১. সমাসে দুই বা ততোধিক পদ মিলে একটি নতুন পদ সৃষ্টি হয় এবং সেসব পদের মধ্যেকার বিভক্তি (যেমন — কারক, প্রত্যয় ইত্যাদি) লুপ্ত হয়। যেমন — ‘রাজার পুত্র’ শব্দটি সমাসনিষ্পন্ন হয়ে ‘রাজপুত্র’ হয়েছে।
২. সমাস হলো পদগঠন সম্পর্কিত একটি পদগত প্রক্রিয়া।
সন্ধির দুটি পার্থক্য হল – ১. সন্ধির ফলে দুটি ধ্বনি পরস্পর মিলিত হয়ে একটি নতুন ধ্বনি তৈরি করে, নতুন শব্দ নয়। শুধু উচ্চারণেরই পরিবর্তন দেখা যায়। ‘বিদ্যা + আলয়’ = বিদ্যালয়-এ এই বিষয়টি দেখা যায়।
২. সন্ধি হল একটি ধ্বনিগত বা বর্ণগত প্রক্রিয়া, যা শব্দের উচ্চারণ ও বানানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
২.৪.৫ উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক বলতে কী বোঝো?
উত্তর: কোনো বাক্যে কর্তা বা উদ্দেশ্য কী, তা আরও স্পষ্ট করে যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, তাকেই উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক বলে।
২.৪.৬ ‘তাঁদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে।’ প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত করো।
উত্তর: ‘তাঁদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে।’ বাক্যটিকে প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত করলে হবে “তাঁদের কি নূতন করে শিখতে হচ্ছে?”
২.৪.৭ আলোচ্য বাক্যটি থেকে বিশেষ্যখণ্ড এবং ক্রিয়াখণ্ড চিহ্নিত করো- তারপর ছুটি ফুরোলে মেসো গল্পটি নিয়ে চলে গেলেন।
উত্তর: তারপর ছুটি ফুরোলে মেসো গল্পটি নিয়ে চলে গেলেন। এখানে বিশেষ্যখণ্ড গুলি হল – ছুটি, মেসো, গল্পটি এবং ক্রিয়াখণ্ড গুলি হল – ফুরোলে, নিয়ে চলে গেলেন।
২.৪.৮ ‘বধূরা প্রদীপ তুলে ধর।’ কর্মবাচ্যে রূপান্তর করো।
উত্তর: ‘বধূরা প্রদীপ তুলে ধর।’ বাক্যটি কর্মবাচ্যে রূপান্তর করলে হবে – “বধূদের দ্বারা প্রদীপ তুলে ধরা হোক।”
২.৪.৯ একটি অকর্মক ক্রিয়ার ভাববাচ্যের উদাহরণ দাও।
উত্তর: “সবাই একদিন মরবে” – এটি অকর্মক ক্রিয়ার ভাববাচ্যের একটি উদাহরণ।
২.৪.১০ সিঁড়ি থেকে নামা হল। বাক্যটিকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করো।
উত্তর: “সিঁড়ি থেকে নামা” এই বাক্যাংশটিকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করলে হবে “আমি সিঁড়ি থেকে নামছি” বা “সে সিঁড়ি থেকে নামছে”।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ “বাবাই একদিন এঁর চাকরি করে দিয়েছিলেন।” বক্তা কে? তাঁর বাবা কাকে, কী চাকরি করে দিয়েছিলেন?
উত্তর: শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ গল্পের যে অংশটি নেওয়া হয়েছে, সেখানে যে মন্তব্যটি করা হয়েছে, তার বক্তা হলেন অপূর্ব।
অপূর্ব বলেছিল, নিমাইবাবু পুলিশ অফিসার, সে আমাদের আত্মীয় আর বাবুর বন্ধু। উনিই তাকে পুলিশে চাকরি করিয়ে দিয়েছেন।
৩.১.২ ‘মানুষ কি তাকে রেহাই দিবে?’ কার সম্পর্কে এই উক্তি? কেন এই উক্তি?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদী সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে সাধারণ স্টেশনমাস্টার নদেরচাঁদ নদীকে পরমাত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো ভালোবাসত। নদীর প্রতি তার ছিল এক গভীর, অবিচ্ছেদ্য টান; তার জীবনের অর্ধেকই যেন জুড়ে ছিল নদী। যেখানেই সে থেকেছে, সেখানকার নদীকেই সে আপন করে নিয়েছে। কাজের সূত্রে সে এক প্রশস্ত, জলভরা কিন্তু বাঁধা-বাঁধা নদীর সঙ্গে পরিচিত হয়। মানুষ ব্রিজ আর বাঁধ দিয়ে নদীটিকে বন্দী করে রেখেছে। একদিন প্রবল বৃষ্টির পর নদীর উচ্ছ্বসিত, ফেনিল জলরাশি দেখে নদেরচাঁদের মনে হয়, নদী যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ব্রিজ-বাঁধ ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সে যেন ফিরে পেতে চাইছে তার স্বাধীন, স্বাভাবিক গতি। এইভাবে নদী যেন যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে আর প্রকৃতির উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতি ইঙ্গিত করছে। এমন দৃশ্য দেখে নদেরচাঁদের মনে হয়েছে, আজ নদী বিদ্রোহ করে যদি তার বন্দিদশা কাটিয়ে উঠতেও পারে, তবু মানুষ তাকে ছাড়বে না। নিজেদের প্রয়োজনে তারা আবারও তাকে বন্দী করবে, আবার গড়ে তুলবে ব্রিজ ও বাঁধ। সেই প্রশস্ত নদীকে পরিণত করবে একটি ক্ষীণস্রোতা খালে।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর।” ‘সে’ কে? ভেঙে আবার গড়ার বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: উক্ত অংশে ‘সে’ শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে মহাদেবকে নির্দেশ করলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাধ্যমে দেশের তরুণ বিপ্লবীদের কথাই বলা হয়েছে।
মহাদেব তাঁর রুদ্ররূপে অসুন্দরকে বিনাশ করে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক সেভাবাই দেশের তরুণ বিপ্লবীরা ধ্বংসের মহারোষ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারকে আঘাত করা। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই ধ্বংসযজ্ঞের তাণ্ডব সহ্য করতে অক্ষম। অথচ সেই ধ্বংসের আড়ালেই লুকিয়ে আছে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও নতুন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। কবি তাই এই ধ্বংসকে ‘কালভয়ংকরের বেশে সুন্দরের আগমন’ বলে বর্ণনা করেছেন।
৩.২.২ ‘আমি এখন হাজার হাতে পায়ে / এগিয়ে আসি,’ কে এগিয়ে আসেন? হাজার হাতে পায়ে এগিয়ে আসা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: “অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতায় শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী সাধারণ মানুষদের এগিয়ে আসার ডাক দেওয়া হয়েছে।
“অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতায় কবি জয় গোস্বামী অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংগীতের শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হোক বা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কোন শক্তি—মানুষের আন্দোলন ও প্রতিবাদের ক্ষেত্রে গানই হয়ে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে একটি প্রধান হাতিয়ার। কবির মতে, গান কেবলমাত্র আনন্দের উৎস নয়, এটি সংগ্রামের সময় ‘বর্ম’-এর ভূমিকাও নিতে পারে। এই ‘গানের বর্ম’ পরেই কবি বন্দুকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, বুলেটকে প্রতিহত করেছেন। আর এই সংগ্রামে তিনি দেখেছেন যে তিনি একা নন, অসংখ্য মানুষ একই পথের সঙ্গী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন গণআন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, যুগে যুগে গানই মানুষের প্রতিবাদের অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠেছে। সকলের সম্মিলিত কণ্ঠের প্রতিবাদী গান অস্ত্রের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। গানের এই বিশেষ শক্তি এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের একত্রিত করার তার ক্ষমতাকেই কবি এই কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ “সত্যিই তপনের জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনটি এল আজ?” কোন্ দিনটির কথা বলা হয়েছে? দিনটি সম্পর্কে এই উচ্ছ্বাসের কারণ লেখো।
উত্তর: যে দিন তপনের ছোটোমাসি আর মেসোমশাই সন্ধ্যাতারা পত্রিকা নিয়ে তাদের বাড়িতে এসেছিলেন, আর যে পত্রিকায় তপনের প্রথম গল্প ছাপা হয়েছিল—আশাপূর্ণা দেবীর ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পে সেই দিনেরই কথা বলা হয়েছে।
আশাপূর্ণা দেবীর ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পে নতুন মেসোমশাইকে দেখার পর লেখকদের সম্পর্কে তপনের যে রোমান্টিক ধারণা ছিল, তা সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। সে আবিষ্কার করে, লেখকরাও খুব সাধারণ মানুষ। এই আবিষ্কার তপনের মনে জাগিয়ে তোলে লেখক হওয়ার ইচ্ছা, আর সে লিখে ফেলে তার জীবনের প্রথম গল্পটি। ছোটোমাসির হাত দিয়ে সে গল্পটি পৌঁছে দেয় মেসোমশাইয়ের কাছে। মেসোমশাই কিছু সংশোধনের কথা বললেও তপনের চিন্তার মৌলিকতায় খুশি হয়ে গল্পটি ছাপানোর আশ্বাস দেন। এরপর শুরু হয় তপনের অপেক্ষার দিনগুলি। অবশেষে, ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার গল্প—’প্রথম দিন’। কিন্তু যে দিনটি তার জীবনের ‘সবচেয়ে সুখের দিন’ হওয়ার কথা ছিল, সেটিই হয়ে ওঠে ‘সবচেয়ে দুঃখের দিন’। ছাপার অক্ষরে নিজের নামে লেখা দেখাটাকে সে যেভাবে ‘অলৌকিক’ মনে করেছিল, সেই লেখাই তাকে প্রায় বাকরুদ্ধ করে দেয়। চারদিকে তার গল্পের প্রশংসা হলেও, মেসোমশাইয়ের মহানুভবতাই বেশি আলোচিত হতে থাকে। গল্পটি পড়তে গিয়ে তপনের অপমান তীব্রতর হয় যখন সে দেখে, গল্পের একটি লাইনও তার লেখা নয়—মেসোমশাই পুরো গল্পটিই নতুন করে লিখে দিয়েছেন। সেই গল্প থেকে লেখক তপন সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে। তপনের চোখ ভেসে ওঠে জলে।
৪.২ “খাঁটি মানুষ তো নয়, এই বহুরুপীর জীবন এর বেশি কী আশা করতে পারে?” এই উক্তির প্রেক্ষিতে বহুরূপী হরিদার চরিত্র বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পটির কাহিনি বিকশিত হয়েছে হরিদার চরিত্রকে ঘিরে। তাঁর চরিত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, সেগুলো হল –
বৈচিত্র্যান্বেষী: হরিদার পছন্দ ছিল না কোনো গতানুগতিক বা নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা কাজ। কাজের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি আর স্বাধীনতার স্বাদ খুঁজে নিতেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন বহুরূপীর পেশা।
সামাজিকতা: হরিদার চরিত্রে সামাজিকতার দিকটি খুবই স্পষ্ট। শহরের অতি সরু একটি গলির মধ্যে তাঁর ছোট্ট ঘরটিই ছিল কথক ও তাঁর তিন বন্ধুর সকাল-সন্ধ্যার আড্ডার স্থান। চা, চিনি, দুধ তারা নিজেরাই নিয়ে আসতেন, আর হরিদা উনুনের আঁচে জল ফুটিয়ে দিতেন।
পেশাদারিত্ব: কখনো বাসস্ট্যান্ডের পাগল, কখনো রাজপথের বাইজি, বাউল, কাপালিক, বুড়ো কাবুলিওয়ালা বা ফিরিঙ্গি সাহেব—এমন নানা রূপে হরিদাকে দেখা গেছে। শুধু পোশাকই নয়, চরিত্রের সাথে তাঁর আচরণও ছিল পুরোপুরি মানানসই।
সততা: গল্পের শেষে হরিদার চরিত্রটি তার পরিণতিতে পৌঁছায়। বিরাগীর ছদ্মবেশে জগদীশবাবুকে মুগ্ধ করলেও, তাঁর আতিথ্য গ্রহণ বা প্রণামি নিতে হরিদা রাজি হননি। এভাবেই তিনি তাঁর পেশাগত সততা বজায় রেখে অর্থলোভকে পরিত্যাগ করেন।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ “আয় আরো হাতে হাত রেখে/ আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।” ‘হাতে হাত রেখে’ কথাটির মধ্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? কবি কেন আরো বেঁধে বেঁধে থাকার কথা বলেছেন?
উত্তর: সমাজের অস্থিরতা মানবজীবনকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে, যুদ্ধের ডাক দেয়, নিয়ে আসে ধ্বংস ও মৃত্যু। মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। শিশুদের লাশ ছড়িয়ে থাকে চারপাশে। সাধারণ মানুষের ইতিহাস উপেক্ষিতই থেকে যায়। বাঁচতে হয় ভিক্ষা করে কিংবা পরের দয়ার উপর নির্ভর করে। এমন এক প্রতিকূল পরিবেশে সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ থাকার জরুরি কথাটিই কবি তাঁর উক্তিতে বলেছেন।
কবি অস্থির সময়ে সারা বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা, ধ্বংস ও মৃত্যুর চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানে নানাবিধ বাধার কারণে গতিরোধ হয়েছে, পথ হয়ে উঠেছে দুর্গম। মাথার উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় বোমারু বিমান। ধ্বংস ও মৃত্যুর আগমন যেন নিশ্চিত। যুদ্ধের কারণে মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে মৃত শিশুদের দেহ। অন্যদিকে, ক্ষমতাবানদের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের অবদানের ইতিহাসকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, তাদের অধিকারকেও মান্যতা দেওয়া হয় না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ দয়া-দাক্ষিণ্য ভিক্ষা করে বেঁচে আছে। মনুষ্যত্বের এমন বিপর্যয়ের পরেও কি এই পৃথিবী টিকে থাকবে—কবির মনে এই নিয়ে সন্দেহ জাগে। কিন্তু আশাবাদী কবি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেন যে, এই যুদ্ধ, হত্যা ও বঞ্চনা কখনো চূড়ান্ত সত্য হতে পারে না। সমাজে এখনও অনেক শুভবোধসম্পন্ন মানুষ বাস করেন। তারা যদি একত্রিত হয়, তারা অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে পারবে। সেজন্য প্রয়োজন একসাথে থাকা, সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলা এবং হাতে হাত রাখা।
৫.২ “সভ্যের বর্বর লোভ” কাদের তথাকথিত ‘সভ্য’ বলা হয়েছে? তাদের বর্বর লোভের যে পরিচয় ‘আফ্রিকা’ কবিতায় রয়েছে তা আলোচনা করো।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আফ্রিকা’ কবিতায় তথাকথিত ‘সভ্য’ বলতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তিগুলোর কথা বলা হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘আফ্রিকা’ কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দ্বারা আফ্রিকার ওপর চালিত অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনার কাহিনি তুলে ধরেছেন। প্রাকৃতিকভাবে দুর্গম এই মহাদেশটি দীর্ঘকাল ইউরোপীয় শক্তিগুলির দৃষ্টির বাইরে ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগে এসে প্রায় সমগ্র আফ্রিকাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপনিবেশে পরিণত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে আফ্রিকাকে ব্যবহার করা হয় ক্রীতদাস সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে। পরবর্তীতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নজর পড়ে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর। এ কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্বের মোট খনিজ সম্পদের ৩০ শতাংশই আফ্রিকায় উৎপাদিত হয়। সোনা ও প্ল্যাটিনামের মতো মূল্যবান সম্পদে আফ্রিকা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাই প্রায় সকল শক্তিশালী ইউরোপীয় দেশই সেখানে নিজেদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। কেবল আফ্রিকার নির্লজ্জ শোষণই নয়, তাদের অধিকার হরণ করার করুণ ইতিহাসও রচিত হয়। ইউরোপীয় শক্তিগুলি আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তারা মানবতার চরম লাঞ্ছনাও ঘটিয়েছে। ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে যিনি অনুরোধ করেছিলেন, সেই অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন— “বিষম অত্যাচার করেছে বর্বর সাম্রাজ্যলোভী, অর্থলোভী ইউরোপীয় দল,… অধিকাংশ আফ্রিকানের হাড় ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়ানো, প্রায় কেউই বাড়ি ফেরেনি।” মুসোলিনির ইতালি আফ্রিকার আবিসিনিয়া আক্রমণ করে দেশটিকে নিঃস্ব ও রক্তাক্ত করে তোলে। আফ্রিকা পরিণত হয় উন্নত সভ্যতার তথাকথিত ‘নির্লজ্জ অমানবতা’র চরম প্রকাশক্ষেত্রে।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা।” প্রবন্ধ অনুসরণে ঘটনাটি বিবৃত করো।
উত্তর: “হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” রচনায় লেখক উল্লেখ করেছেন, কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের একটি নামী দোকানে তিনি একদিন ফাউন্টেন পেন কিনতে গিয়েছিলেন। ফাউন্টেন পেনের আবিষ্কার পেনের জগতে এক বিপ্লব এনে দিয়েছিল, যেন অফুরন্ত কালির একটি ফোয়ারা খুলে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পরের কোনো এক দিন, লেখক সেই নামী দোকানটিতে ফাউন্টেন পেন কিনতে যান। দোকানদার তাঁকে পার্কার, শেফার, ওয়াটারম্যান, সোয়ান, পাইলট—নানা রকম পেনের নাম ও তাদের দাম জানান। লেখকের মুখভঙ্গি এবং তাঁর পকেটের অবস্থা আঁচ করে দোকানদার তাঁকে একটি সস্তা জাপানি পাইলট কলম কিনতে পরামর্শ দেন। এরপর দোকানদার পেনটির ঢাকনা খুলে এটিকে একটি কাঠের বোর্ডের উপর ছুড়ে মারেন। সার্কাসে যেমন জীবন্ত মানুষের দিকে ছুরি ছোঁড়ার পরও সে অক্ষত থাকে, তেমনই বোর্ড থেকে পেনটি তুলে দোকানদার দেখান যে এর নিবটি সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। তারপর তিনি দু-এক লাইন লিখেও দেখান। তখন পনেরো-ষোলো বছরের এক কিশোর লেখকের কাছে পেনটি এক জাদুকরী পেনের মতোই মনে হয়। পরবর্তী জীবনে লেখক অনেক ফাউন্টেন পেন কিনলেও, বহুদিন পর্যন্ত তিনি সেই জাপানি পাইলট পেনটি খুব যত্ন করে রেখেছিলেন।
৬.২ “আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন” ‘শব্দের ত্রিবিধ কথা’ কী? ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে এই ‘ত্রিবিধ কথা’-র প্রসঙ্গ এসেছে কেন?
উত্তর: শব্দের ত্রিবিধ কথা বলতে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা বোঝানো হয়েছে।
১. অভিধা –
- শব্দের মুখ্য অর্থ প্রকাশের ক্ষমতাকে অভিধা বলে।
উদাহরণ: “সিংহ পুরুষের প্রতীক”—এখানে “সিংহ” কেবল প্রাণী নয়, বরং সাহসী ও পরাক্রমশালী পুরুষকেও বোঝায়।
২. লক্ষণা –
- যখন কোনো শব্দের গৌণ অর্থ মুখ্য হয়ে ওঠে, তখন তাকে লক্ষণা বলে।
উদাহরণ: “রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম”—এখানে রাস্তার অবস্থা নয়, বরং দেরি হওয়ার ভাব প্রকাশ করা হয়েছে।
৩. ব্যঞ্জনা –
- যখন অভিধা ও লক্ষণায় সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয় না এবং শব্দ থেকে নতুন তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়, তখন তাকে ব্যঞ্জনা বলে।
- উদাহরণ: “বৃষ্টি পড়ে টিপটিপ, নদী বয়ে যায় কুলুকুলু”—এখানে ধ্বনি ও আবহ থেকে বিশেষ অনুভূতি ফুটে উঠেছে।
প্রসঙ্গঃ
- ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে এই ত্রিবিধ কথার উল্লেখ এসেছে, কারণ বিজ্ঞানকে স্পষ্ট, যথাযথ ও কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে হলে ভাষার সঠিক প্রয়োগ জরুরি। প্রবন্ধকার বোঝাতে চেয়েছেন—বাংলা ভাষা অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার সঠিক ব্যবহার করতে পারলেই বিজ্ঞানচর্চার জন্য উপযুক্ত ও শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ ‘আজ বিচারের দিন নয়, সৌহার্দ্য স্থাপনের দিন।’ কে, কার উদ্দেশে এই উক্তি করেছেন? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, বস্তার এরূপ মন্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: নবাব সিরাজদ্দৌলা মীরজাফরকে উদ্দেশ্য করেই আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।
সিরাজ উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। মীরজাফর, রাজবল্লভ এবং তাঁর নিজ রাজসভারই কিছু কর্মচারী ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বিচক্ষণ নবাব বুঝতে পেরেছিলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে তখন কঠোর পদক্ষেপ নিলে উলটো ফলই ঘটবে। বরং মীরজাফরকে বুঝিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারলে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক সহজ হবে। তাই যখন মীরজাফর নবাবের উদ্দেশ্যে বললেন, “নবাব কি প্রকাশ্য দরবারেই আমার বিচার করতে চান?” তখন নবাব সংযত হয়ে বিচারের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। তাঁর মনে হলো, বাংলা যখন বিপদগ্রস্ত, নবাবের সিংহাসন যখন টলমল করছে, তখন ক্রোধ সংবরণ করাই সর্বোত্তম। তাই সিরাজ আন্তরিক ভঙ্গিতে নিজের এবং বাংলার করুণ দশার কথা বর্ণনা করে মীরজাফরের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন।
৭.২ ‘মনে হয়, ওর নিশ্বাসে বিষ, ওর দৃষ্টিতে আগুন, ওর অঙ্গ-সঞ্চালনে ভূমিকম্প।’ উদ্ধৃতিটির আলোকে ঘসেটি বেগমের চরিত্রবৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
উত্তর: নাটকে চিত্রায়িত ঘসেটি বেগমের চরিত্রটি মূল ইতিহাসের একটি যথাযথ রূপায়ণ।
ষড়যন্ত্রকারী: ঘসেটি বেগম ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার খালা। তিনি চাইতেন আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর যেন তার স্বামী বাংলার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর সিরাজের সিংহাসনলাভ নিশ্চিত হয়ে ওঠে। নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ায় এবং সিরাজের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ঘসেটি বেগম ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন।
প্রতিহিংসাপরায়ণ: ঘসেটি বেগমের প্রথম সংলাপ— ‘ওখানে কী দেখছ মূর্খ, বিবেকের দিকে চেয়ে দেখো!’— সন্তানতুল্য সিরাজের প্রতি কখনও যথার্থ বলে মনে হয় না। তার বক্তব্যে প্রতিহিংসার প্রকাশ স্পষ্ট— ‘আমার রাজ্য নেই, তাই আমার কাছে রাজনীতিও নেই— আছে কেবল প্রতিহিংসা।’ নিরীহ লুৎফা বেগমকেও অকারণে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য শুনিয়েছেন এই দুর্বিনীত নারী।
উপসংহার: লুৎফা বেগমের তার সম্পর্কে মূল্যায়ন— ‘ওর নিশ্বাসে বিষ, ওর দৃষ্টিতে আগুন, ওর অঙ্গসঞ্চালনে ভূমিকম্প!’— এটি স্পষ্টই প্রমাণ করে যে একজন নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে ঘসেটি বেগম নাটকে সম্পূর্ণ সার্থক।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ কোনির পারিবারিক জীবনের পরিচয় দাও।
উত্তর: “কোনি” হল মতি নন্দীর একই নামের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই উপন্যাসে কোনি ও তার পরিবারের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের করুণ কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।
অভাবগ্রস্ত সংসার: পিতার মৃত্যুর পর, কোনির দাদা কমল সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। সে একটি গারেজে মাসে মাত্র দেড়শো টাকা বেতনে কাজ করে। এই সামান্য আয় দিয়েই সে তার মা ও ভাইবোনদের মুখে খাবার তুলে দেয়।
বাসস্থানের দুরবস্থা: কোনিদের থাকার জন্য কোনো উপযুক্ত ঘরও নেই। তাদের মাত্র একটি তক্তাপোশ আছে, যার উপর তোশক পর্যন্ত নেই—কয়েকটি ছোট চিটচিটে বালিশই শোয়ার একমাত্র সম্বল। দড়িতে টাঙানো জামা-কাপড়। তাদের খোলার চালের ঘরে আছে মাত্র একটি জানালা, যার নিচে থকথকে পাঁকে ভরা একটি নর্দমা।
দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ: কমল নিজেও একদিন বড় সাঁতারু হওয়ার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে তার সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। সে জানত কোনির ভিতর অসাধারণ প্রতিভা লুকিয়ে আছে, কিন্তু সেই প্রতিভার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করার সাধ্য তার ছিল না। সংসারে দুবেলা দু মুঠো খাবার জোগাড় করাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত, একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে কমলের জীবনসংগ্রাম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
নিঃস্ব সংসারে সাহায্যের হাত: সম্পূর্ণ রোজগারহীন হয়ে পড়া কোনিদের সংসারে এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ক্ষিতীশ। ‘প্রজাপতি’ দোকানে কাজ করে কোনি মাসে চল্লিশ টাকা পায়। অন্যদিকে, ছাঁট কাপড় সেলাই করে কোনির মা সামান্য কিছু আয় করেন। এইভাবে দারিদ্র্যকে নিত্যসঙ্গী করেই কোনিদের সংসার কোনোমতে চলতে থাকে।
৮.২ ‘সাঁতারু অনেক বড়ো সেনাপতির থেকে।’- উক্তিটি কার? উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।
উত্তর: প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসের ক্ষিতীশ চরিত্রটি আলোচ্য উক্তিটির বক্তা।
ক্ষিতীশ বিষ্টু ধরের জন্য একটি বক্তৃতা লিখে দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় লেখা ছিল যে খেলোয়াড়দের গৌরবেই দেশ আলোকিত হয়। বিষ্টু ধর একাগ্রচিত্তে বক্তৃতাটি পড়ছিলেন। মাঝখানে দম নেওয়ার জন্য তিনি যখন একটু থামলেন, ঠিক তখনই ক্ষিতীশ তাঁর মূল বক্তব্যটি উপস্থাপন করেন। ক্ষিতীশের বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে একজন প্রকৃত নায়কই আদর্শ হয়ে ওঠেন। সে সাঁতারুই হোক বা সেনাপতি—দেশের গৌরব তার সাফল্যের উপরই নির্ভর করে। তবে ক্ষিতীশের মতে, সেনাপতির চেয়ে একজন সাঁতারু অনেক বড়ো। কারণ, সেনাপতি দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন। আর যুদ্ধে মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই প্রাণহানির জন্য তিনি নিজ দেশে সম্মান পেলেও, প্রতিপক্ষ দেশের মানুষ তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু একজন সাঁতারুর সম্মান কোনো দেশ বা সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। দেশে দেশে ও যুগে যুগে, সমগ্র বিশ্বের মানুষের হৃদয়ে একজন সফল সাঁতারুর জন্য শ্রদ্ধার আসন সদা প্রস্তুত। একজন মহান সাঁতারু জীবনের ও প্রাণের প্রতীক; অন্যদিকে একজন সেনাপতি মৃত্যু ও ধ্বংসের। মহান সাঁতারুরা সমগ্র বিশ্বকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে থাকেন। ক্ষিতীশের বিশ্বাস, একটি পদকের চেয়ে এই অবদান অনেক বেশি মূল্যবান।
৮.৩ ‘ক্ষিতীশের একটা হাত তোলা। চোয়াল শক্ত।’ ক্ষিতীশ সিংহের এই রকম প্রতিক্রিয়ার কারণ কী?
উত্তর: জুপিটারে কোনিকে ভরতি করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার পর, ক্ষিতীশ একরকম বাধ্য হয়েই অ্যাপোলো ক্লাবে যোগ দেন। সেখানকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট নকুল মুখুজ্জে তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং কোনিকে সাঁতার শেখার সুযোগও করে দেন। এই ঘটনায় দুশ্চিন্তা কাটলেও, ক্ষিতীশের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তিনি জুপিটারকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। দীর্ঘদিনের সেই ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার বেদনায় তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সারারাত তাঁর চোখে ঘুম আসে না। মনটা ঘুরেফিরে কেবলই একই প্রশ্ন করতে থাকে- “আমি কি ঠিক কাজ করলাম? অ্যাপোলোয় আসাটা কি উচিত হয়েছে?” এক কঠিন মানসিক যন্ত্রণা তাঁকে অস্থির করে তোলে। এমন সময় ভেলো এসে অ্যাপোলোয় যোগদানের জন্য তাঁকে প্রশংসা করে। কিন্তু মনের কষ্টে ভারাক্রান্ত ক্ষিতীশ চুপ করে থাকেন। ভেলো তখন বলে, “জুপিটারকে এবার শায়েস্তা করা দরকার। বুঝলে ক্ষিদ্দা, তুমি শুধু ওই নাড়ির টানগুলো একটু ভুলে যাও…” ইতিমধ্যেই জুপিটার ও অ্যাপোলোর মধ্যে টানাপড়েনে তাঁর মন ক্ষতবিক্ষত ছিল। ভেলোর এই কথায় ক্ষিতীশের সমস্ত কষ্ট ও রাগ একত্রিত হয়ে একটি তীব্র শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো:
Good books are storehouses of knowledge and wisdom. Anyone who has the key can enter these storehouse and helps himself. What is the key ? Simply the ability to read. He who can read store his mind with the great thoughts of the great thinkers of the world. The man who never opens a book has an empty mind.
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ বিদ্যালয়ে ‘মিড-ডে-মিল’ নিয়ে দুই বন্ধুর যুক্তিপূর্ণ সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
বিদ্যালয়ে ‘মিড-ডে-মিল’ নিয়ে দুই বন্ধুর যুক্তিপূর্ণ সংলাপ
রাহুল : শোন অরুণ, আমার তো মনে হয় বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল দেওয়া খুবই দরকার। এতে গরিব ছাত্ররা পেট ভরে খেতে পারে।
অরুণ : হ্যাঁ, ঠিক বলছ, তবে অনেকে বলে এতে সময় নষ্ট হয়। পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে।
রাহুল : তা ঠিক নয়। বরং পেট খালি থাকলে ছাত্রদের মন পড়াশোনায় থাকে না। খাবার পেলে তারা মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারে।
অরুণ : আচ্ছা, কিন্তু খাবারের মান সব সময় ভালো হয় কি?
রাহুল : মান উন্নত করার জন্য সরকার ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবসময় নজর রাখছে। স্বাস্থ্যকর খাবার পেলে ছাত্রদের শারীরিক বিকাশও ভালো হয়।
অরুণ : শুনেছি এতে বিদ্যালয়ে উপস্থিতিও বেড়েছে।
রাহুল : একদম ঠিক। অনেক গরিব পরিবার তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হচ্ছে।
অরুণ : তাই বুঝি। তাহলে মিড-ডে-মিল শুধু খাওয়ার ব্যবস্থা নয়, শিক্ষার প্রসারেও বড় ভূমিকা রাখছে।
রাহুল : হ্যাঁ, তাই তো বলি—মিড-ডে-মিল শিক্ষার সহায়ক শক্তি।
১০.২ তোমার এলাকায় অরণ্য সপ্তাহ পালিত হল এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর: অরণ্য সপ্তাহ পালন
আমাদের এলাকায় গত সপ্তাহে ‘অরণ্য সপ্তাহ’ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়েছে। স্থানীয় বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত ও বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং গ্রামবাসীরা সকলে মিলে বিভিন্ন ফলজ, ঔষধি ও ছায়াদার গাছ রোপণ করেন। বনদপ্তরের কর্মকর্তারা বন সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বননিধনের ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশ রক্ষার ওপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। গ্রামে সচেতনতা র্যালিরও আয়োজন করা হয়, যেখানে পরিবেশ বাঁচাও, গাছ লাগাও ইত্যাদি স্লোগান তোলা হয়। সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচির ফলে গ্রামবাসীর মধ্যে পরিবেশ রক্ষার প্রতি সচেতনতা বেড়েছে। অরণ্য সপ্তাহের এই উদ্যোগ আমাদের এলাকায় সবুজায়নের বীজ বপন করেছে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে একটি সুন্দর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।
উপসংহার : অরণ্য সপ্তাহের এই আয়োজন আমাদের সকলকে পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকারে দৃঢ় করেছে।
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো:
১১.১ বিপন্ন পৃথিবীর আর্তনাদ।
উত্তর: বিপন্ন পৃথিবীর আর্তনাদ
আজকের পৃথিবী যেন নিজের সন্তানদের কাছে আর্তনাদ করছে। একসময় সবুজে ঢাকা, নদীনালা আর বনভূমিতে ভরপুর এই পৃথিবী ধীরে ধীরে প্রাণশূন্য হয়ে পড়ছে। মানুষ সভ্যতার অগ্রগতির নামে প্রকৃতিকে যে নির্দয়ভাবে ধ্বংস করেছে, তার ফলেই পৃথিবী আজ বিপন্ন।
বর্তমানে মানুষের অতি ভোগবাদী মনোভাবই প্রকৃতি ধ্বংসের প্রধান কারণ। বনভূমি নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে, যার ফলে বন্যপ্রাণীরা বাসস্থান হারাচ্ছে। শিল্পায়নের দাপটে বায়ু ও জল দূষিত হয়ে পড়ছে। কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া বাতাসে মিশে মানুষ ও প্রাণী—সবার জীবনকেই বিপন্ন করে তুলছে। প্লাস্টিক দূষণ সমুদ্রকে বিষাক্ত আবর্জনার স্তূপে পরিণত করছে। যানবাহনের কালো ধোঁয়া থেকে সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিনহাউস প্রভাব, যার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। হিমবাহ গলছে, সমুদ্রের জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, অগ্নিকাণ্ডের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে চলেছে। এসবই পৃথিবীর এক ভয়াবহ সংকটের ইঙ্গিত বহন করছে।
পৃথিবীর এই আর্তনাদ শুধুমাত্র প্রকৃতির নয়, মানবজাতির অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। কারণ মানুষই প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদি প্রকৃতি ধ্বংস হয়, তবে মানুষের টিকে থাকাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই আজ প্রয়োজন প্রকৃতিকে বাঁচানোর। বৃক্ষরোপণ করতে হবে, প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, শিল্পকারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে মানতে হবে। সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে এবং পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে অংশ নিতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে দূষণ রোধ ও নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে।
আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবী আমাদের বাসস্থান, তাই তাকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে কখনোই মানবসভ্যতা টিকে থাকতে পারবে না। যদি আমরা আজই পরিবেশ সংরক্ষণের পথে না এগোই, তবে আগামী দিনে পৃথিবী হবে এক মরুভূমি, যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না।
উপসংহার : বিপন্ন পৃথিবীর আর্তনাদ আসলে আমাদের নিজের বেঁচে থাকার ডাক। পৃথিবীকে বাঁচানো মানেই নিজেদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করা। তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে পৃথিবীকে আবার সবুজ ও প্রাণময় করে তুলি।
১১.২ একটি বর্ষণমুখর দিনের অভিজ্ঞতা।
উত্তর:
একটি বর্ষণমুখর দিনের অভিজ্ঞতা
বর্ষাকাল বছরের একটি অনন্য ঋতু। এ সময় আকাশ ভরে ওঠে কালো মেঘে, আর মাটিতে নামে ঝুমঝুম বৃষ্টি। এমনই এক বর্ষণমুখর দিনের অভিজ্ঞতা আজও আমার মনে সতেজ হয়ে আছে।
সেদিন সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘলা। বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে ছাতা থাকলেও প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় তাতে কোনো লাভ হল না। ভিজে সারা শরীর, বই-খাতা সব ভিজে গিয়েছিল। ভিজতে ভিজতেই আমি স্কুলে পৌঁছালাম। ক্লাসরুমে ঢুকতেই দেখি, অনেকেই একইভাবে ভিজে গেছে। আমাদের পড়াশোনার পরিবেশ যেন হঠাৎ করেই উৎসবমুখর হয়ে উঠল।
দুপুর নাগাদ বৃষ্টি আরও বেড়ে গেল। জানালার বাইরে চারদিক ভরে উঠল জলরাশিতে। মাঠ হয়ে গেল ছোট্ট পুকুরের মতো। বৃষ্টির টুপটাপ শব্দে এক অন্যরকম সুর বেজে উঠল। শিক্ষকরা তখন পাঠ বন্ধ রেখে আমাদের সঙ্গে বর্ষার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।
স্কুল ছুটি হলে দেখি, চারিদিকে জল জমে গেছে। রাস্তার কোথাও হাঁটু সমান, কোথাও কোমর সমান পানি। আমি বন্ধুদের সঙ্গে মিলে জল পেরিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলাম। পাড়ার বাচ্চারা তখন বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দ করছে। কোথাও কাগজের নৌকা ভাসছে, কোথাও বৃষ্টির জলে ছিটাছিটি চলছে। ভিজতে ভিজতে আমিও যেন এক অদ্ভুত আনন্দ খুঁজে পেলাম।
যদিও সেই ভেজা অবস্থায় বাড়ি পৌঁছে একটু সর্দি-কাশির কষ্ট হয়েছিল, তবুও সেই দিনের অভিজ্ঞতা সত্যিই স্মরণীয়। বৃষ্টি আমাদের শুধু ভিজিয়ে দেয়নি, দিয়েছে এক অনন্য আনন্দ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপভোগ।
উপসংহার : বর্ষণমুখর দিনের অভিজ্ঞতা যেমন কষ্টকর, তেমনি আনন্দদায়কও বটে। এই দিনের স্মৃতি আমার হৃদয়ে আজও জীবন্ত হয়ে আছে।
১১.৩ বইমেলা।
উত্তর: বইমেলা
মানুষের মানসিক উন্নতি ও জ্ঞানার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হলো বই। বই শুধু শিক্ষার হাতিয়ার নয়, এটি মানুষের চিন্তাভাবনাকে প্রসারিত করে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করে। এই বইয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণকেই কেন্দ্র করে প্রতিবছর বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় বইমেলা। বইমেলা আমাদের সমাজে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।
বইমেলায় বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা তাদের নতুন ও পুরনো বই প্রদর্শনের জন্য স্টল বসায়। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, জীবনী, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনি—এমন নানা বিষয়ের বই মেলায় পাওয়া যায়। পাঠকরা সহজেই নিজেদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করতে পারেন। শুধু বই কেনাবেচার ক্ষেত্রেই নয়, বইমেলা হলো সাহিত্যিক, পাঠক ও প্রকাশকের এক মিলনক্ষেত্র। এখানে লেখকদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করার সুযোগ হয়, সাহিত্য-আলোচনা, কবিতা পাঠ, বই প্রকাশনা অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে মেলা এক প্রাণবন্ত রূপ লাভ করে।
বইমেলার পরিবেশ সত্যিই আনন্দমুখর। রঙিন পোস্টার, আলোকসজ্জা, নানা থিমে সাজানো স্টল এবং মানুষের ভিড় মেলাকে এক উৎসবের আবহ দেয়। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে প্রবীণ পাঠক পর্যন্ত সকলেই বইমেলায় আসেন। অনেক পরিবার শিশুদের নিয়ে মেলায় আসে, ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যেও বইয়ের প্রতি আগ্রহ জাগে। বইয়ের পাশাপাশি মেলায় ছোটখাটো হস্তশিল্প, খাবারের দোকান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকে, যা দর্শনার্থীদের আনন্দ বাড়ায়।
আজকের যুগে প্রযুক্তি ও মোবাইলের প্রভাবে অনেকেই বই পড়ার অভ্যাস হারাচ্ছেন। এই অবস্থায় বইমেলা মানুষকে বইয়ের কাছে টেনে আনে এবং পাঠাভ্যাসে নতুন করে উজ্জীবিত করে। বইমেলা শুধু জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে না, এটি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিরও এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
উপসংহার : বইমেলা আমাদের সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখে। তাই প্রত্যেকের উচিত বইমেলায় অংশগ্রহণ করা এবং বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। বইই পারে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয়, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের পথে নিয়ে যেতে।
১১.৪ সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা।
সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা
মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে তার চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা। এই সৃজনশীলতার বিকাশে সাহিত্য পাঠের ভূমিকা অপরিসীম। সাহিত্য শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভব করার ক্ষমতা এবং সমাজ সম্পর্কে সচেতনতার অন্যতম উৎস।
প্রথমত, সাহিত্য পাঠ আমাদের জ্ঞানকে বিস্তৃত করে। ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে আমরা অতীত সম্পর্কে জানতে পারি। উপন্যাস, গল্প কিংবা প্রবন্ধে লুকিয়ে থাকে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। ফলে সাহিত্য আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে এবং বাস্তব জীবনের নানা দিক সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।
দ্বিতীয়ত, সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের গভীর আবেগকে জাগ্রত করে। কবিতা, নাটক কিংবা উপন্যাস আমাদের মনে সহমর্মিতা, প্রেম, দুঃখ ও আনন্দের অনুভূতি জাগায়। অন্যের সুখ-দুঃখকে উপলব্ধি করতে শিখি আমরা সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে। সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের কষ্টের কথাও সাহিত্য আমাদের সামনে তুলে ধরে, যা আমাদের মানবিক হতে সাহায্য করে।
তৃতীয়ত, সাহিত্য আমাদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করে। শিশুসাহিত্য কিংবা কাব্য পাঠ করলে আমাদের মনে নতুন স্বপ্ন ও চিন্তার জগৎ তৈরি হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতিও অনেকাংশে মানুষের কল্পনাশক্তির ফল, আর সাহিত্য সেই কল্পনাশক্তিকে ডানা মেলতে সাহায্য করে।
চতুর্থত, সাহিত্য সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার। অনেক সাহিত্যকর্ম মানুষের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি জুগিয়েছে। জাতীয়তাবাদী সাহিত্য স্বাধীনতার আন্দোলনে মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়েছে। সাহিত্য মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতার বোধ তৈরি করে।
পঞ্চমত, সাহিত্য আমাদের ভাষাজ্ঞান ও রুচিবোধ উন্নত করে। ভালো সাহিত্য পাঠ করলে ভাষা ব্যবহারে শুদ্ধতা আসে এবং সৃজনশীল প্রকাশভঙ্গি গড়ে ওঠে।
উপসংহার : সর্বোপরি, সাহিত্য পাঠ মানুষের মনকে উদার, চিন্তাকে প্রসারিত এবং জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। যে জাতি সাহিত্যকে ভালোবাসে, সে জাতি সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয় এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তাই আমাদের সকলের উচিত নিয়মিত সাহিত্য পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।