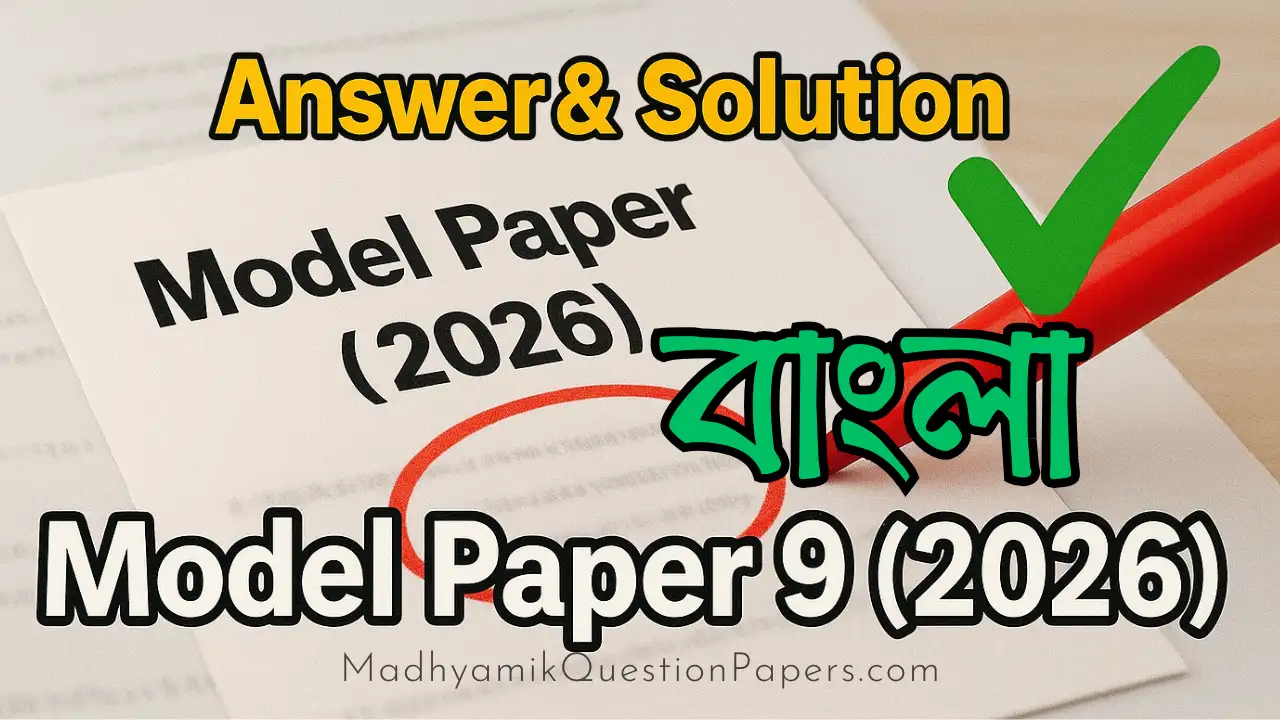আপনি কি মাধ্যমিকের বাংলা Model Question Paper 9 প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন? দেখে নিন 2026 WBBSE বাংলা Model Question Paper 9-এর সঠিক উত্তর ও বিশ্লেষণ। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 9- এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৬ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ ছোটোমাসি তপনের থেকে কত বছরের বড়ো?
(ক) বছর পাঁচেকের
(খ) বছর আস্টেকের
(গ) বছর দশেকের
(ঘ) বছর বারোর
উত্তর: (খ) বছর আস্টেকের
১.২ ‘খুব হয়েছে হরি, এই বার সরে পড়ো। অন্যদিকে যাও।’- একথা বলেছে-
(ক) ভবতোষ
(খ) অনাদি
(গ) কাশীনাথ
(ঘ) জনৈক বাসযাত্রী
উত্তর: (গ) কাশীনাথ
১.৩ মূল ‘অদল বদল’ গল্পটি কোন্ ভাষায় লেখা?
(ক) মারাঠি
(খ) গুজরাতি
(গ) পাঞ্জাবি
(ঘ) অসমিয়া
উত্তর: (খ) গুজরাতি
১.৪ “সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।।”- ‘সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী’-
(ক) বিদ্বেষ ত্যাগ করো
(খ) ক্ষমা করো
(গ) ভালোবাসো
(ঘ) মঙ্গল করো
উত্তর: (খ) ক্ষমা করো
১.৫ ইন্দ্রজিতের স্ত্রীর নাম–
(ক) ইন্দিরা
(খ) সরমা
(গ) নিকষা
(ঘ) প্রমীলা
উত্তর: (ঘ) প্রমীলা
১.৬ “ভাঙ্গিল প্রবল বাও” ‘বাও’ শব্দের অর্থ হল –
(ক) বাতাস
(খ) বান
(গ) জল
(ঘ) ঝড়
উত্তর: (ক) বাতাস
১.৭ কানে কলম গুঁজে দুনিয়া খোঁজেন–
(ক) প্রাবন্ধিক
(খ) দার্শনিক
(গ) গল্পকার
(ঘ) নাট্যকার
উত্তর: (খ) দার্শনিক
১.৮ “ফাউন্টেন পেনের এক বিপদ,” ‘বিপদ’-টা হল –
(ক) চুরি যাওয়া
(খ) পেনের বল নষ্ট হওয়া
(গ) কালি শুকিয়ে যাওয়া
(ঘ) লেখককে নেশাগ্রস্ত করা
উত্তর: (ঘ) লেখককে নেশাগ্রস্ত করা
১.৯ আমাদের দেশে তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সুসাধ্য হবে, যখন এদেশে–
(ক) বাংলায় প্রচুর পারিভাষিক শব্দ তৈরি হবে
(খ) বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ঘটবে
(গ) মাতৃভাষার প্রতি মানুষের প্রীতির মনোভাব গড়ে উঠবে
(ঘ) লেখকেরা অনুবাদের আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন
উত্তর: (খ) বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ঘটবে
১.১০ “ছেলেরা ফুটবল খেলে।” ‘ফুটবল’ কোন কারকের উদাহরণ?
(ক) কর্তৃ
(খ) কর্ম
(গ) করণ
(ঘ) অধিকরণ
উত্তর: (গ) করণ
১.১১ যে কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করায়, সে হল–
(ক) প্রযোজ্য কর্তা
(খ) প্রযোজক কর্তা
(গ) উহ্য কর্তা
(ঘ) অনুক্ত কর্তা
উত্তর: (খ) প্রযোজক কর্তা
১.১২ ‘জ্ঞানহীন’ পদটি কোন্ সমাসের উদাহরণ?
(ক) ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
(খ) দ্বিগু সমাস
(গ) কর্মধারয় সমাস
(ঘ) করণ তৎপুরুষ সমাস
উত্তর: (ঘ) করণ তৎপুরুষ সমাস
১.১৩ পূর্বপদ প্রাধান্য পায় –
(ক) অব্যয়ীভাব সমাসে
(খ) দ্বন্দু সমাসে
(গ) কর্মধারয় সমাসে
(ঘ) বহুব্রীহি সমাসে
উত্তর: (ক) অব্যয়ীভাব সমাসে
১.১৪ ‘আমার সঙ্গে এসো।’ কোন্ শ্রেণির বাক্য?
(ক) নির্দেশক
(খ) প্রার্থনাসূচক
(গ) শর্তসাপেক্ষ
(ঘ) অনুজ্ঞাসূচক
উত্তর: (ঘ) অনুজ্ঞাসূচক
১.১৫ ‘আমাদের মধ্যে যারা ওস্তাদ তারা ওই কালো জলে হরতকী ঘষত।’ বাক্যটি কোন্ শ্রেণির?
(ক) সরল বাক্য
(খ) জটিল বাক্য
(গ) মিশ্রবাক্য
(ঘ) যৌগিক বাক্য
উত্তর: (খ) জটিল বাক্য
১.১৬ ‘মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে।’ বাক্যটি কোন্ বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্তৃবাচ্য
(খ) কর্মবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
১.১৭ ‘বাচ্য’ কথাটির অর্থ হল-
(ক) বচন
(খ) বিরুদ্ধ
(গ) বক্তব্য
(ঘ) বাচন ক্ষমতা
উত্তর: (গ) বক্তব্য
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ ‘নতুন মেসোকে দেখে জানল সেটা।’ নতুন মেসোকে দেখে তপন কী জানল?
উত্তর: নতুন মেসোকে দেখে তপন উপলব্ধি করেছিল যে, সাধারণ মানুষও সহজেই চমৎকার গল্প লিখতে পারে। লেখালেখির জগৎ কেবল বড় কিংবা বিখ্যাত লেখকদের জন্য সংরক্ষিত নয়, বরং তা সবার জন্য উন্মুক্ত।
২.১.২ জগদীশবাবু তীর্থ ভ্রমণের জন্য কত টাকা বিরাগীকে দিতে চেয়েছিলেন?
উত্তর: সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পে জগদীশবাবু তীর্থযাত্রার খরচ হিসেবে বিরাগীকে একশো এক টাকা দিতে চেয়েছিলেন।
২.১.৩ ‘মিথ্যেবাদী কোথাকার।’ উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কেন মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে?
উত্তর: থানায় গিরিশ মহাপাত্রের পকেট তল্লাশি করে গাঁজার অংশ পাওয়ার পর নিমাইবাবু তাকে গাঁজা সেবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে গিরিশ জানায় যে সে গাঁজা খায় না, কিন্তু বন্ধুদের জন্য তা তৈরি করে দেয়। এই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত জগদীশবাবু তাকে ‘দয়ার সাগর’ বলে বিদ্রূপ করেন এবং তার মধ্যে গাঁজা সেবনের সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট থাকায় তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেন।
২.১.৪ ‘ইসাবের মনে পড়ল,’ ইসাবের কী মনে পড়ল?
উত্তর: ইসাবের মনে পড়ে গেল, সে দেখেছে অমৃতের বাবা যখনই অমৃতকে মারতে যায়, তখনই তার মা এসে আগলে দাঁড়ান।
২.১.৫ “বড়ো ভয় করিতে লাগিল নদেরচাঁদের।” নদেরচাঁদের ভয় করার কারণ কী?
উত্তর: নদীর রূপ ছিল ভয়ানক; রাগ ও ক্ষোভে সে যেন পাগলপ্রায়। নদেরচাঁদ নদীর পাড় থেকে মাত্র এক হাত উঁচুতে ছিল তার আবাস। তাই, বর্ষার জলে স্ফীত সেই নদী যে কোনও মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কিছু করে বসবে এই আশঙ্কায় নদেরচাঁদ ভয় পেয়েছিল।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ ‘অসুখী একজন’ কবিতাটি কে বাংলায় তরজমা করেছেন?
উত্তর: নবারুণ ভট্টাচার্য আমাদের পাঠ্য ‘অসুখী একজন’ কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন।
২.২.২ ‘অভিষেক করিলা কুমারে।’ রাবণ কীভাবে কুমারকে অভিষিক্ত করলেন?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘অভিষেক’ কবিতায় রাবণ কুমারকে অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎকে গঙ্গাজল দিয়ে নিয়মমতো অভিষেক করান এবং নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করে পরদিন সকালে যুদ্ধযাত্রা করতে বলেন।
২.২.৩ “ওরে ওই স্তব্ধ চরাচর।” ‘চরাচর’ স্তব্ধ কেন?
উত্তর: “প্রলয়োল্লাস” কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কল্পনা করেছেন যে ধ্বংসের দেবতা প্রলয়ংকর শিবের অট্টহাসির প্রচণ্ড শব্দে সমগ্র চরাচর অর্থাৎ গোটা বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।
২.২.৪ ‘মধ্যেতে যে কন্যাখানি’ মধ্যের কন্যাটির পরিচয় দাও।
উত্তর: কবি সৈয়দ আলাওল রচিত পদ্মাবতী কাব্যের ‘পদ্মা-সমুদ্রখণ্ড’ অংশ থেকে সংগৃহীত ‘সিন্ধুতীরে’ শীর্ষক কবিতাংশে উল্লিখিত ‘কন্যা’ হলেন সিংহলরাজ গন্ধর্বসেনের কন্যা, যিনি পরবর্তীতে চিতোররাজ রত্নসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী পদ্মাবতী হিসেবে পরিচিত হন।
২.২.৫ “তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান” গান কোথায় বেড়াবে?
উত্তর: জয় গোস্বামীর লেখা ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় কবি উল্লেখ করেছেন নদীতে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শ্রোতারা গানের তালে তালে ভ্রমণ করেন।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘দোয়াত যে কত রকমের হতে পারে,’ প্রবন্ধে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার দোয়াতের নাম লেখো।
উত্তর: শ্রীপান্থ তাঁর ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ রচনায় বিভিন্ন ধরনের দোয়াতের কথা বলেছেন। যেমন — কাচ, কাঠ-গ্লাস, পোর্সেলিন, সাদা পাথর, জেড পাথর, পিতল, ব্রোঞ্জ, ভেড়ার শিং, এমনকি সোনার দোয়াতও।
২.৩.২ ‘জন্ম নিল ফাউন্টেন পেন।’ ফাউন্টেন পেনের জন্ম-বৃত্তান্তটি উল্লেখ করো।
উত্তর: লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যান একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। অন্যদের মতো তিনিও তার কাজের জন্য দোয়াত ও কলম সঙ্গে নিয়ে বেরোতেন। একদিন এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে গিয়ে তার কলম থেকে গুরুত্বপূর্ণ দলিলের ওপর কালি পড়ে যায়। ফলে তাকে কালি ভরতে বাড়ি ফিরতে হয়। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন, অন্য একজন ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। এই ঘটনায় ওয়াটারম্যান খুবই হতাশ ও বিরক্ত হন এবং তখনই সিদ্ধান্ত নেন এমন একটি কলম তৈরি করবেন, যাতে আলাদা করে দোয়াত নিয়ে ঘুরতে না হয়। আর এভাবেই ফাউন্টেন পেনের উদ্ভব ঘটে।
২.৩.৩ ‘অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী’ কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী’ প্রবাদটির মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো বিষয়ে অর্ধ-সত্য বা অসম্পূর্ণ জ্ঞান রাখা সম্পূর্ণ অজ্ঞতার চেয়েও বেশি বিপদজনক।
২.৩.৪ বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত পরিভাষা সমিতি নবাগত রাসায়নিক বস্তুর ইংরেজি নাম সম্বন্ধে কী বিধান দিয়েছিলেন?
উত্তর: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত পরিভাষা কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, নতুন কোনো রাসায়নিক পদার্থের নাম তার ইংরেজি নামেই বাংলায় ব্যবহার করা হবে।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ বিভক্তি ও নির্দেশকের দুটি প্রধান পার্থক্য লেখো।
উত্তর:
| বিভক্তি | নির্দেশক |
| বিভক্তি হলো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ এর সাথে যুক্ত হয়ে বাক্যে তাদের কার্য-সম্পর্ক (কর্তা, কর্ম, সম্প্রদান ইত্যাদি) নির্দেশ করে। যেমন – ‘ছাত্র-টি বই-টি পড়েছে। | নির্দেশক হলো বিশেষ্য পদ এর আগে বসে সেই বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করে বোঝায়। এটি আলাদা শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন – ‘সেই লোকটি’, ‘ঐ গাছটি’। |
২.৪.২ অ-কারক সম্পর্ক বলতে কী বোঝো?
উত্তর: “অ-কারক সম্পর্ক” বলতে বাংলা ব্যাকরণে সেই সমস্ত বাক্যকে বোঝায় যেখানে ক্রিয়ার সাথে নামপদের (শব্দের) কোনো কারক সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, বাক্যটিতে ব্যবহৃত নামপদগুলি (কর্তা, কর্ম, করণ ইত্যাদি) সরাসরি মূল ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে না বা ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয় না।
২.৪.৩ করণে বীপ্সার একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: করণে বীপ্সার একটি উদাহরণ হল – বারবার মনে হয়, ওই শৈশবে ফিরতে চাই।”
২.৪.৪ ব্যাসবাক্যটি সমাসবদ্ধ করে তার শ্রেণি নির্ণয় করো ‘অন্ধ করে যে’।
উত্তর: ‘অন্ধ করে যে’ শব্দটির ব্যাসবাক্য হল – অন্ধ কারে যেন এবং সমাস হল – উপপদ তৎপুরুষ সমাস।
২.৪.৫ সংজ্ঞাসহ ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়েরই অর্থ সমান গুরুত্বপূর্ণ থাকে এবং উভয় পদ মিলে ‘অমুক-তমুক’ বা ‘একটি-অন্য একটি সম্পর্ক প্রকাশ করে, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। এখানে সমস্ত পদ দুটির কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু বোঝায় না, বরং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, আদান-প্রদান বা বিনিময় সম্পর্ক সূচিত করে। ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের একটি উদাহরণ হল – হাতাহাতি।
২.৪.৬ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো ‘উপকথা’।
উত্তর: ‘উপকথা’ শব্দটির ব্যাসবাক্য হল – কথার সদৃশ্য এবং সমাস হল – অব্যয়ীভাব সমাস।
২.৪.৭ আকাঙ্ক্ষা কী? উদাহরণ দাও।
উত্তর: কোনো কিছু অর্জনের জন্য অন্তরের যে গভীর ও তীব্র বাসনা, তাই আকাঙ্ক্ষা। এটি ব্যক্তিগত বা সামাজিক যেকোনো প্রকারের হতে পারে এবং প্রায়শই জীবনের প্রতি এক ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেই ফুটিয়ে তোলে।আকাঙ্ক্ষার একটি উদাহরণ হল – ছোটবেলা থেকেই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল একজন ডাক্তার হওয়ার।
২.৪.৮ “রামচন্দ্র চোদ্দো বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন।” এই বাক্যটির উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ করো।
উত্তর: পিতার আজ্ঞা পালন ও সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন।”
২.৪.৯ ভাববাচ্যে কর্তা লুপ্ত অবস্থায় আছে (লুপ্ত কর্তা ভাববাচ্য), এরকম একটি বাক্য লেখো।
উত্তর: ভাববাচ্যে কর্তা লুপ্ত অবস্থায় আছে এরকম একটি বাক্য হল – বইটি পড়া হয়েছে। এই বাক্যটিতে কে বইটি পড়েছে সেই কর্তা (ব্যক্তি) উল্লেখ নেই, শুধু কাজটি (পড়া) হয়েছে বোঝানো হয়েছে। এটিই লুপ্ত কর্তাবাচক ভাববাচ্য।
২.৪.১০ “তাকে বাঘে খেয়েছে।” বাক্যটিকে কর্মবাচ্যে পরিণত করো।
উত্তর: “তাকে বাঘে খেয়েছে।” বাক্যটিকে কর্মবাচ্যে পরিণত করলে হবে – বাঘ তাকে খেয়েছে।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ “অথচ আপনি একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মতো সব তুচ্ছ করে সরে পড়লেন?” হরিদা কীভাবে খাঁটি সন্ন্যাসীর মতো ব্যবহার করেছিলেন, তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।
উত্তর: হরিদা বিরাগীর বেশ ধরে জগদীশবাবুর বাড়ি গেলেও, তীর্থভ্রমণের জন্য জগদীশবাবু যে একশো এক টাকা দিয়েছিলেন, সে টাকা তিনি নেননি। কথক ও তাঁর বন্ধুরা যখন হরিদার টাকা না নেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন যে, যেহেতু তিনি বিরাগী সেজেছিলেন, টাকা নিলে তাঁর ঢং নষ্ট হয়ে যেত।, তাই বিরাগীর নিয়মই রক্ষা করেছেন। বিরাগী সন্ন্যাসীরা কখনও টাকা স্পর্শ করেন না। সেই জন্যই, অভাবগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও হরিদা সেই টাকা গ্রহণ করতে চাননি।
৩.১.২ “নিজের এই পাগলামিতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।” কার কথা বলা হয়েছে? তার ‘পাগলামি’-টি কী?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পের উল্লিখিত অংশে নদেরচাঁদের কথা বলা হয়েছে।
নদেরচাঁদের পাগলামির পরিচয় – নদেরচাঁদের পাগলামির পরিচয় হলো এই যে, শৈশব থেকেই নদীর সাথে তার গভীর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। কর্মজীবনে প্রবেশ করেও নদীর প্রতি তার সেই আকর্ষণ কমেনি। তাই, টানা পাঁচ দিন প্রবল বৃষ্টির কারণে নদীকে দেখতে না পেয়ে সে ‘ছেলেমানুষের মতো’ অস্থির হয়ে উঠেছিল। বৃষ্টি কিছুটা থামামাত্রই সে নদীর দিকে ছুটে যায়। নদীর প্রতি এই অস্থিরতা, এই আকুলতাই ছিল তার পাগলামি।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ ‘ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?’ কেন ধ্বংস সাধিত হচ্ছে ? ধ্বংসকে ভয় না পেতে বলেছেন কেন কবি?
উত্তর: রুদ্ররূপে শিবের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই আবির্ভাব প্রকৃতপক্ষে অসুন্দরকে ধ্বংস করার জন্যই। একইভাবে ধ্বংসের বার্তা বহন করে, প্রলয়ের মাদকতায় উন্মত্ত বিপ্লবী যুবাদের উদ্ভব হয়। ধ্বংসের সেই তীব্রতায় মানুষ শিহরিত বোধ করে। কিন্তু কবির মতে, এই প্রলয় আসলে সৃষ্টিরই যন্ত্রণা। সমাজে যত কিছু প্রাণহীন ও কুৎসিত, তার পরিসমাপ্তি ঘটাতেই এই বিপ্লবী শক্তির আগমন। তাই কবির ধারণা, ধ্বংসকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।
৩.২.২ “গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে”- কবির এই মন্তব্যের তাৎপর্য আলোচনা করো।
উত্তর: কবি বলেন— “গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে।” এই মন্তব্যের মধ্যে কবির গভীর মানবিক ও প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। অস্ত্রের ভয় ও হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে কবি যুদ্ধের পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন সংগীতকে তাঁর প্রতিরক্ষার প্রতীক হিসেবে। গানের বর্ম মানে শুধু সুর ও ছন্দ নয়, বরং মানবতার, সত্যের ও ন্যায়ের শক্তিতে সজ্জিত হওয়া। গান মানুষের অন্তরকে জাগিয়ে তোলে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সাহস জোগায়। তাই কবি বুঝিয়েছেন— রক্তপাত নয়, বরং সংগীত, শুভবোধ ও সৃজনশীলতার মাধ্যমেই অশুভ শক্তির মোকাবিলা করা যায়।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ ‘মনে হলে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।’ বক্তা কে? লজ্জাকর ঘটনাটির উল্লেখ করো।
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ গল্পাংশ থেকে উদ্ধৃত এই উক্তিটির বক্তা হলেন অপূর্ব। অপূর্বকে কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও একদল ফিরিঙ্গি যুবক লাথি মেরে তাকে প্ল্যাটফর্ম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। অপূর্ব যখন এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করল, সাহেব স্টেশনমাস্টার তাকে শুধুমাত্র ‘দেশি লোক’ এই অজুহাতে কুকুরের মতো তড়িয়ে দিল। এই অপমাণ ঘটনা পরাধীন দেশে প্রতিদিনই ঘটে চলেছে। এই ঘটনায় অপূর্ব খুব ব্যাথা পেল; তার প্রচন্ড রাগও হলো। তার ‘মনে হলে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।’ কিন্তু সে দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে, দেশের মা-ভাই-বোনদের যারা সব অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে চায়, তারাই তার সত্যিকারের আপনজন। আর সেই মানুষগুলোকে নিজের কাছের মানুষ হিসেবে পাওয়ার পথের সমস্ত কষ্ট ও বাধা সে বুক পেতে গ্রহণ করতে চায়।
৪.২ গল্প প্রকাশিত হওয়ার পরেও ছোটোমেসোর প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল, তা করে না তপন। প্রকাশিত গল্পটি পড়ে তার কেন মনে অভিমান জাগে, তা বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের “জ্ঞানচক্ষু” গল্পে, তপনের লেখা গল্পটি তার ছোটোমেসোমশায়ের উদ্যোগে ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মেসোমশায় গল্পটিকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার জন্য যে সংশোধন করেছেন, সেই কথাটিই তিনি সুকৌশলে সকলের সামনে প্রচার করে দেন। ফলে, তপনের নিজের লেখার চেয়ে মেসোমশায়ের সংশোধনের কথাই বেশি আলোচিত হতে থাকে। এতে করে, গল্পটি ছাপার আনন্দ তপন একদমই উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু এর চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয় তখন, যখন তার মা তপনকে নিজের মুখে গল্পটা পড়ে শোনাতে বলেন। লজ্জা কাটিয়ে গল্পটা পড়তে গিয়ে তপন দেখে, তার প্রতিটি লাইনই যেন “নতুন, আনকোরা, তপনের একদম অপরিচিত”। সংশোধনের নামে ছোটোমেসোমশায় আসলে তপনের গল্পটিকেই নতুন করে লিখে ফেলেছেন তাঁর “পাকা হাতের কলমে”। নিজের সৃষ্টির এমন রদবদল তপনকে একদম বিহ্বল করে দেয়। সে আর পড়তে পারে না, বোবা ও স্তব্ধের মতো বসে থাকে। এই ঘটনা থেকেই তপনের মনে গভীর অভিমান জন্মায় এবং সে দৃঢ় সংকল্প করে যে, ভবিষ্যতে যদি কখনো লেখা ছাপাতে হয়, তবে সে নিজেই গিয়ে তা ছাপাতে দেবে।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ “আমরাও তবে এইভাবে/ এ-মুহূর্তে মরে যাব না কি?” এমনটা মনে হচ্ছে কেন?
উত্তর: শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায় সমাজ ও সভ্যতার অস্থির চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। যুদ্ধ, বিভেদ, আর আদর্শহীনতা সভ্যতার পথরুদ্ধ করেছে। ‘ডান পাশে ধ্বস’ আর ‘বাঁয়ে গিরিখাদ’—এই দুইয়ের মাঝখানে এগোনোর পথ হয়ে উঠেছে সঙ্কটময়। মাথার ওপর যুদ্ধবিমান ধ্বংস ও মৃত্যুর ছায়া দীর্ঘ করে তোলে। ঠিক যেমন বরফ পথকে দুর্গম করে, তেমনই যুদ্ধ, আদর্শের অভাব আর স্বার্থপরতা এগিয়ে চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের তাণ্ডবে মানুষ গৃহহারা হয়। শিশুমৃত্যু ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে—”আমাদের ঘর গেছে উড়ে/আমাদের শিশুদের শব-/ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে।” এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সাধারণ মানুষকেও শিহরিত করে। সর্বনাশের এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুধু জীবনের অগ্রগতি থেমে যায় না, বিপন্ন হয়ে পড়ে তার অস্তিত্বই। মৃত্যুভয় স্পর্শ করে সকলকে। তখনই আশঙ্কাগ্রস্ত মানুষদের মনে হয়—”আমরাও তবে এইভাবে/এই মুহূর্তে মরে যাব না কি?”
৫.২ “দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে; কাকে, কেন ‘মানহারা মানবী’ বলা হয়েছে? কবির এমন আহ্বানের কারণ ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘আফ্রিকা’ কবিতায় আফ্রিকাকে ‘মানহারা মানবী’ বলে উল্লেখ করেছেন। এর পেছনের কারণ হলো, উন্নত ইউরোপীয় সভ্যতা আফ্রিকাকে শোষণ করলেও সেখানকার জীবনধারা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে কখনো স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে আফ্রিকাকে উপেক্ষা ও অপমানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে হয়েছে। দাসব্যবসা থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক শোষণ—বঞ্চনার এক দীর্ঘ ইতিহাস আফ্রিকাকে বেষ্টন করে রয়েছে। ‘মানহারা মানবী’ শব্দবন্ধটি দিয়ে এই বঞ্চনাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।
কবির এমন আহ্বানের কারণ – আফ্রিকা লাঞ্ছিত হয়েছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের হাতে। লুন্ঠিত পায়ের ক্ষত-বিক্ষত জুতার তলায় বিদীর্ণ হয়েছে সেই মহাদেশের বুক। নিরীহ আফ্রিকাবাসী নতমুখে সহ্য করেছে অবর্ণনীয় অপমান। তথাকথিত সভ্য মানুষ কখনো ফিরেও তাকায়নি এই অসম্মানিত আফ্রিকার দিকে। যুগসন্ধির কবি সভ্য মানুষেরই প্রতিনিধি। তাই এই মর্যাদাহারা আফ্রিকার দুয়ারে দাঁড়িয়ে সমগ্র সভ্য মানবতার পক্ষ থেকে তাকে ক্ষমা চেতেই হবে। এই কারণেই কবি তাকে ডেকেছেন।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ “আশ্চর্য, সবই আজ অবলুপ্তির পথে।” ‘সবই’-র পরিচয় দাও। উল্লিখিত বিষয়টি কীভাবে আজ ‘অবলুপ্তির পথে’ আলোচনা করো।
উত্তর: “হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” রচনায় লেখক শ্রীপান্থর মতে, কলম আজ বিলুপ্তির পথে।শৈশব থেকেই লেখকের শিক্ষাজীবনের সাথী ছিল বাঁশের কলম, খাগের কলম, পালকের কলম ইত্যাদি। পরবর্তীতে বাজারে ফাউন্টেন পেনের আবির্ভাব ঘটে। কলমের বাজারে এটি একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করে। কিন্তু ফাউন্টেন পেনকেও পিছনে ফেলে বল-পেন এসে যায় বাজারে। কলম হয়ে ওঠে সহজলভ্য ও সস্তা। সবার কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথেই কলম তার নিজস্ব মর্যাদা হারাতে থাকে। একদিন যে দোয়াতকলম দিয়ে লিখে দেশ-বিদেশের সাহিত্যিকরা অমর সব সৃষ্টি করে গেছেন, সেই দোয়াতকলম এখন শুধু ইতিহাসের পাতায় সীমিত। বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কার হিসেবে কম্পিউটার দখল করে নেয় কলমের স্থান। সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত লেখকের ছিল কলমের প্রতি এক গভীর টান। বাঁশের কলম, খাগের কলম ছেড়ে বল-পেনের কাছে আত্মসমর্পণ করতেও তিনি মনে কষ্ট পেয়েছেন। “যদি চিরতরে হারিয়ে যায় হাতের লেখা”— এই চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলত। কম্পিউটারের প্রভাবে সব ধরনের কলম আজ বিলুপ্তির পথে।
৬.২ “বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় এখনও নানা রকম বাধা আছে।” প্রাবন্ধিক কোন্ ধরনের বাধার কথা বলেছেন?
উত্তর: প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ রচনা প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করেছেন। যেমন –
প্রথম সমস্যা: পারিভাষিক শব্দের অভাব – পারিভাষিক শব্দের অভাব হিসেবে তিনি বাংলায় বিজ্ঞান চর্চায় প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দের স্বল্পতার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ সত্ত্বেও এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়নি।
দ্বিতীয় সমস্যা: বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার- পাশ্চাত্যের তুলনায় এদেশের সাধারণ মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার সীমিত। বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকলে বৈজ্ঞানিক রচনা বুঝতে অসুবিধা হয়। বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে এই সমস্যা অনেকাংশে কাটানো সম্ভব।
তৃতীয়ত সমস্যা: রচনাশৈলীর অনুশীলন – বিজ্ঞান রচনার জন্য উপযুক্ত রচনাশৈলী আমাদের অনেক লেখক এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি। ফলে লেখায় প্রায়ই কৃত্রিমতা ও জড়তা থেকে যায় এবং সেগুলো অনেকক্ষেত্রে ইংরেজি বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদে পরিণত হয়। এ থেকে মুক্তি পেতে বাংলা ভাষার নিজস্ব গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী লেখার রীতি রপ্ত করা জরুরি।
চতুর্থ সমস্যা: লেখকের অপর্যাপ্ত জ্ঞান –লেখকের নিজস্ব অপর্যাপ্ত জ্ঞান। বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখকের জ্ঞান যদি অগভীর হয়, তাহলে তাঁর রচনায় ভুল বা অস্পষ্ট তথ্য সাধারণ পাঠকের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই রাজশেখর বসুর পরামর্শ হলো, কোনো বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের আগে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে তা যাচাই করে নেওয়া উচিত।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “বাংলায় আমি এমন আগুন জ্বালাইব, যাহা গঙ্গার সমস্ত জল দিয়াও নিভানো যাইবে না।” বক্তার এই উক্তির তাৎপর্য কী? কে বাংলায় আগুন জ্বালাতে চেয়েছেন?
উত্তর: প্রশ্নে উদ্ধৃত বক্তব্যটি “বাংলায় আমি এমন আগুন জ্বালাইব, যাহা গঙ্গার সমস্ত জল দিয়াও নিভানো যাইবে না” – এটি একটি চিঠির অংশ, যা নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারে ওয়াটস নামক একজন ইংরেজ প্রতিনিধির কাছে ধরা পড়ে। এটি ছিল বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর হুমকি। “আগুন” শব্দটি দিয়ে এখানে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, হানাহানি ও সর্বনাশ সৃষ্টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গঙ্গার জল দিয়ে নিভানো যাবে না বলতে বোঝানো হয়েছে যে এই সংঘর্ষ ও ধ্বংস এতটাই ভয়াবহ হবে যে বাংলার প্রাকৃতিক বা প্রচলিত কোনো শক্তি একে থামাতে পারবে না। ই হুমকিটি দিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে অ্যাডমিরাল ওয়াটস। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে আলোচনার সময় ওয়াটসের লেখা একটি গোপন চিঠি নবাবের হস্তগত হয়, যাতে এই বক্তব্য ছিল। অর্থাৎ, ইংরেজ কর্তৃপক্ষই বাংলায় এই ‘আগুন’ জ্বালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। এই ঘটনাটি নাটক বা ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায়, যেখানে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের এই গুপ্তচরবৃত্তি ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করেন এবং ওয়াটসকে দরবার থেকে বহিষ্কার করেন। এটি ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পূর্ববর্তী উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিরই ইঙ্গিতবাহী। বাংলায় আগুন জ্বালাতে চেয়েছেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অ্যাডমিরাল ওয়াটস।
৭.২ “ওকে ওর প্রাসাদে পাঠিয়ে দিন জাঁহাপনা। ওর সঙ্গে থাকতে আমার ভয় হয়।” বক্তা কে? তার এরকম ভয় হওয়ার কারণ কী?
উত্তর: এখানে বক্তা হলেন ঘসেটি বেগম, যিনি সিরাজউদ্দৌলার পিসি।
ঘসেটি বেগমের এরকম ভয় হওয়ার কারণ হলো— তিনি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন এবং তাঁর ক্ষমতালাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাইতেন। ঘসেটি বেগমের এমন মন্তব্যের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন একজন সাহসী ও শক্তিশালী শাসক। ঘসেটি বেগম আশঙ্কা করতেন যে, সিরাজ যদি তাঁর বিরুদ্ধে চলমান ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন, তবে তাঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ঘসেটি বেগম নিজেও সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্তে জড়িত ছিলেন। মীরজাফর ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার পরিকল্পনা করছিলেন। ঘসেটি বেগম চাইছিলেন না যে সিরাজ তাঁর কাছাকাছি অবস্থান করুক বা তাঁর উপর সন্দেহ প্রকাশ করুক, কারণ তা তাঁর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে পারে। তাই তিনি সিরাজকে প্রাসাদে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর এই ভীতির মূলে ছিল ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এবং সিরাজের প্রতি তাঁর গভীর অসন্তুষ্টি ও বিদ্বেষ থেকেই তিনি বলেন— “ওর সঙ্গে থাকতে আমার ভয় হয়।”
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ “কোনি তুমি আনস্পোরটিং।”- কোন্ প্রসঙ্গে, কার এই উক্তি? কোনিকে ‘আনস্পোরটিং’ বলার কারণ কী? এরপর কী ঘটেছিল?
উত্তর: ‘কোনি তুমি আনস্পোরটিং।’ — এই কথা জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার একজন বিচারক বা কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন। এটি বলা হয় যখন জাতীয় পর্যায়ের মেয়েদের সাঁতার প্রতিযোগিতায় কোনিকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার দিন কোনির দল থেকে অন্য একজন মেয়েকে নির্বাচিত করা হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার যোগ্যতা কোনিরই ছিল। বিষয়টি হয়তো অনিচ্ছাকৃত ছিল, কিন্তু এটি পক্ষপাতমূলক ও অন্যায় ছিল।
কোনিকে ‘আনস্পোরটিং’ বলার কারণ – জাতীয় পর্যায়ের মেয়েদের সাঁতার প্রতিযোগিতায় কোনিকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয় এবং প্রতিযোগিতার দিন কোনির দল থেকে কোনির পরিবর্তে অন্য একজন মেয়েকে নির্বাচিত করা হয়। এই ঘটনার পর কনি ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং প্রতিযোগিতার অন্য একটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাকে ‘আনস্পোরটিং’ বা খেলোয়াড়সুলভ আচরণবিহীন বলে অভিযুক্ত করা হয়। এটি মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করার কৌশল ছিল, যাতে কনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।
কিন্তু এরপরই গল্পে আসে এক নাটকীয় ও গৌরবময় মুহূর্ত। খিদ্দা উপযুক্ত যুক্তি ও দৃঢ়তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত হন এবং কোনিকে আরেকটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেন। সেখানে কোনি অংশ নিয়ে অর্জন করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। সে প্রমাণ করে দেয় নিজের ক্ষমতা, আরও প্রতিষ্ঠা করে যে অন্যায়ের মুখে কখনো মাথা নত না করে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সঠিক পথ। এই ঘটনাই যেন উপন্যাসের মূল বার্তা – “Fight, কোনি, fight!” – এর জীবন্ত প্রতীক, যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণের সাহসী বার্তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
৮.২ “একটা মেয়ে পেয়েছি, তাকে শেখাবার সুযোগটুকু দিও তা হলেই হবে।” বক্তার এমন আকুতির কারণ কী? এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বক্তার কোন্ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?
উত্তর: জুপিটারে কোনিকে ভর্তি করতে নেওয়ার সময় ক্ষিতীশকে চূড়ান্তভাবে অপমানিত হতে হয়। তাকে বলা হয় যে কোনিকে ট্রায়াল দিতে হবে। কিন্তু ট্রায়ালে পাস করেও ‘জলে আর জায়গা নেই’ – এই অযুহাতে কোনির ভর্তি হয় না। শেষ পর্যন্ত ক্ষিতীশ তার সমস্ত ধৈর্য হারিয়ে পৌঁছে যান চিরশত্রু ক্লাব অ্যাপোলোর গেটে। সেখানকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট নকুল মুখুজ্জেকে জুপিটারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তিনি উদ্ধৃত মন্তব্যটি করেন।
বক্তার মনোভাবের পরিচয় – ক্ষিতীশের কাছে কোনিকে সাঁতার শেখানো এবং একজন সফল সাঁতারু হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। জুপিটারের প্রশিক্ষকের পদ ছাড়তে বাধ্য হওয়ার পরও ক্ষিদ্দা যে ভেবেছিলেন, “কতগুলো স্বার্থপর, লোভী মূর্খ আমাকে দল বেঁধে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই বলে কি শত্রুশিবিরে গিয়ে উঠব?”তিনি সেই একই মানুষ হয়েও পরিস্থিতির পরিবর্তনে কোনিকে গড়ে তুলতে অ্যাপোলোর দ্বারস্থ হন। এখানে ক্ষিদ্দার মধ্যে এক ধরনের আদর্শ প্রশিক্ষকের ছবি ফুটে ওঠে যিনি চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু তৈরি করলেও তাদের সাফল্যকে নিজের কৃতিত্ব বলে দাবি করেন না, বরং মেধা খুঁজে বের করে তাকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার স্বপ্নই যাঁর প্রধান প্রেরণা। আর এই পুরো প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি ক্ষিতীশের কাছে ছিল এক ধরনের সাধনা।
৮.৩ “রমা যোশির সোনা কুড়োনো বন্ধ করা ছাড়া আমার আর কোনো স্বার্থ নেই।” বক্তা কে? কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে বক্তা এরূপ মন্তব্য করেছেন লেখো।
উত্তর: “রমা যোশির সোনা কুড়োনো বন্ধ করা ছাড়া আমার আর কোনো স্বার্থ নেই।” উক্ত লাইনটির বক্তা হলেন প্রণবেন্দু।
উদ্ধৃতিটি একটি সাঁতার প্রতিযোগিতা (সম্ভবত জাতীয় স্তরের) সম্পর্কিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে। প্রণবেন্দু পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সাঁতার দলের কোচ বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তিনি চান বাংলার দলটি সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করুক, এবং তার মতে, মহারাষ্ট্রের রমা যোশি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। রমা যোশি ফ্রি স্টাইল ইভেন্টে প্রায় অপরাজেয়, এবং প্রণবেন্দু বিশ্বাস করেন যে কেবল কনকচাঁপা পালই তার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। কনকচাঁপা পালকে দলে নেওয়া নিয়ে ধীরেন ঘোষ এবং অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে প্রণবেন্দুর তর্ক হয়। ধীরেন ঘোষ কনকচাঁপার সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং প্রণবেন্দুকে “ব্ল্যাকমেল” করার অভিযোগ তোলেন। ধীরেনের এই মন্তব্যের জবাবেই প্রণবেন্দু ঘোষণা করেন যে, “রমা যোশির সোনা কুড়োনো বন্ধ করা ছাড়া আমার আর কোনো স্বার্থ নেই।” অর্থাৎ, তিনি শুধু বাংলার দলকে চ্যাম্পিয়ন বানানোর এবং রমা যোশির জয়যাত্রা থামানোর লক্ষ্যেই কনকচাঁপাকে দলে নিতে চাইছেন; এর বাইরে তার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই।
৯। চলিত বাংলায় অনুবাদ করো:
No country can progress depending on other. Borrower becomes weak day by day and loses its own strength. A country lacking in strength is surely a sing of his disease. A diseased country cannot grow.
উত্তর: কোনো দেশই অন্যের উপর নির্ভর করে উন্নতি করতে পারে না। ধারকারী দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নিজের শক্তি হারায়। যে দেশ নিজস্ব শক্তিহীন, তা অবশ্যই তার অসুস্থতার লক্ষণ। অসুস্থ দেশ কখনও উন্নতি করতে পারে না।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ অরণ্য সপ্তাহ উদ্যাপনে তৎপর দুই ছাত্রের কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
বিষয়ঃ
অরণ্য সপ্তাহ উদ্যাপনে তৎপর দুই ছাত্রের সংলাপ
সুমন : সোহম, শুনেছিস? আগামী সপ্তাহে আমাদের স্কুলে “অরণ্য সপ্তাহ” উদযাপন করা হবে।
সোহম: হ্যাঁ রে! আমি তো খুব উৎসাহী। গাছ লাগানোর কর্মসূচি হবে শুনেছি।
সুমন : ঠিক তাই। আমি ভাবছি অন্তত তিনটা চারাগাছ রোপণ করব। তোকে সঙ্গে পাব তো?
সোহম: অবশ্যই! গাছ লাগানো মানে আমাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করা।
সুমন : ঠিক বলেছিস। এখনকার পরিবেশ দূষণ আর বনধ্বংস আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে।
সোহম: তাই তো। অরণ্য সপ্তাহে সবাই যদি একটাও গাছ লাগায়, দেশটা সবুজে ভরে যাবে।
সুমন : শুধু লাগানোই নয়, গাছগুলোর যত্নও নিতে হবে।
সোহম: হ্যাঁ, গাছই তো আমাদের অক্সিজেন দেয়, ছায়া দেয়, বৃষ্টি আনে।
সুমন : তাহলে ঠিক কর, কালই চারা কিনে আনব।
সোহম: ঠিক আছে, চল একসাথে প্রকৃতিকে রক্ষা করি।
উপসংহার: গাছ আমাদের জীবনসাথী, তাই অরণ্য রক্ষাই আমাদের কর্তব্য।
১০.২ ‘পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে পথ দেখাল ছাত্রছাত্রীরা’ এই বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে পথ দেখাল ছাত্রছাত্রীরা
নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫শে সেপ্টেম্বর: আজ শহরের বিভিন্ন স্থানে পালিত হলো “পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ”। পথচারী ও যানবাহন চালকদের সচেতন করতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় এই কর্মসূচিতে। সকালে বিদ্যালয়ের সামনে ব্যানার ও পোস্টার হাতে ছাত্রছাত্রীরা র্যালি বের করে। র্যালির মাধ্যমে তারা জানায়—“ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলুন, জীবনকে সুরক্ষিত রাখুন।”
পথে চলা মানুষদের ট্রাফিক সিগন্যাল, জেব্রা ক্রসিং ও হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝানো হয়। অনেক চালককে ফুল ও লিফলেট দিয়ে সচেতন করা হয়। ট্রাফিক পুলিশও তাদের পাশে থেকে সহযোগিতা করে।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, “ছাত্রছাত্রীদের এমন উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।”
এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষ ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন হয় এবং দুর্ঘটনা রোধে সতর্ক হওয়ার বার্তা পায়।
ছাত্রছাত্রীদের এই উদ্যোগ সমাজে নিরাপদ চলাচলের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।
১১। কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো:
১১.১ বঙ্গে বর্ষা
বিষয়ঃ
বঙ্গে বর্ষা
ভারতের প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলা অন্যতম। এই বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে যেন বর্ষার এক অটুট বন্ধন। বঙ্গদেশে বর্ষা আসে আশ্বিন মাসের আগে, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। আকাশে জমে কালো মেঘ, চারিদিক ঢেকে যায় অন্ধকারে। গরমে ক্লান্ত ভূমি বর্ষার প্রথম ফোঁটায় যেন নতুন প্রাণ ফিরে পায়।
বর্ষার সময় বাংলার প্রকৃতি হয়ে ওঠে অপরূপা। মাঠে-ঘাটে জল জমে, নদী-নালা উপচে পড়ে। কাঁঠাল, আম, জাম, লিচু, সব ফুরিয়ে গেলে বর্ষা নিয়ে আসে নতুন ফসলের আশীর্বাদ। চাষিরা নবান্নের আশায় ধান রোপণ করে। বাংলার কবিরা বর্ষার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—
“মেঘে মেঘে আকাশ ঢেকে, আছে তোর বরষার ছোঁয়া।”
এই বর্ষাই যেন বাংলার প্রাণের সুর।
বর্ষা শুধু সৌন্দর্যের নয়, জীবনের জন্যও অপরিহার্য। মাঠের ফসল, নদীর জল, মাছের প্রাচুর্য—সবই বর্ষার দান। প্রকৃতির তৃষ্ণা মেটাতে যেমন বর্ষার দরকার, তেমনি মানুষের মনও এই সময় সতেজ হয়। বর্ষার দিনে গ্রামবাংলার পথ ধরে হাঁটলে দেখা যায়—পাল তোলা নৌকা, কাদায় মাখা ধানের চারা, আর দূরে মেঘে ঢাকা পাহাড়।
তবে বর্ষার কিছু অসুবিধাও আছে। অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, অনেক সময় নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যা দেখা দেয়। ফলে ঘরবাড়ি, ফসল, গবাদিপশু—সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রামীণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তবুও এই কষ্টের মাঝেও বাংলার মানুষ বর্ষাকে ভালোবাসে, কারণ সে জীবন ও আশার প্রতীক।
সবশেষে বলা যায়, বঙ্গে বর্ষা মানেই নবজীবনের আগমন। সে যেমন সৌন্দর্য ও সজীবতা আনে, তেমনি জীবনের জন্য অপরিহার্য সম্পদও দেয়। তাই বর্ষা বাংলার হৃদয়ে অমর হয়ে আছে।
১১.২ একটি নদীর আত্মকথা।
রচনা:
একটি নদীর আত্মকথা
আমি এক নদী। আমার জন্ম হয়েছে পর্বতের কোলে, ঝরনার কোলাহলে। প্রথমে আমি ছিলাম একটুখানি জলধারা—নির্মল, পবিত্র ও শান্ত। ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে নামতে আমি পেয়েছি নতুন রূপ, নতুন শক্তি। পথ চলার শুরুতেই কত বাঁক, কত পাথরের বাধা পেরিয়ে আমি ছুটে চলেছি অজানার পথে।
আমার তীরে তীরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য গ্রাম ও জনপদ। কৃষকেরা আমার জল দিয়ে চাষ করে, জেলেরা আমার বুকে নৌকা ভাসিয়ে মাছ ধরে। আমার জলে স্নান করে মানুষ শরীর ও মনকে করে পবিত্র। আমি তাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠেছি। আমার জলেই অনেক শিশুর হাসি, নারীর কলস, আর মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি প্রতিফলিত হয়।
কিন্তু আমার জীবন সবসময় এমন আনন্দময় নয়। বর্ষাকালে আমি কখনও কখনও রুদ্রমূর্তি ধারণ করি। অতিবৃষ্টিতে আমার বুক ফুলে ওঠে, বাঁধ ভেঙে আমি গ্রাম ডুবিয়ে দিই। তখন মানুষ আমাকে অভিশাপ দেয়। অথচ আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে কষ্ট দিতে চাই না; প্রকৃতির নিয়মেই আমার সেই রূপ ধারণ করতে হয়।
শুকনো মরশুমে আমার বুক ফেটে যায়। তখন আমি দেখি আমার জলে ফাটল ধরা বালুচর, খরস্রোত হারিয়ে নিঃস্ব আমি। মানুষ তখনও আমার বুক থেকে জল তুলে নেয়, মাটি কেটে নেয়, ময়লা ফেলে দেয়। আমার জল দূষিত হয়, প্রাণীরা মরতে থাকে। আমি কষ্ট পাই, কারণ আমি তো সকলের মঙ্গল চাই।
একদিন আমার বুক দিয়ে নৌকা চলত, গাছের ছায়া পড়ত, পাখিরা গান গাইত। আজ সেই দিন অনেক বদলে গেছে। নদীর তীর দখল করে মানুষ গড়ছে বাড়িঘর, ফেলে দিচ্ছে প্লাস্টিক ও বর্জ্য। আমি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছি।
তবুও আমি আশাবাদী। যদি মানুষ আবার আমাকে ভালোবাসে, আমার বুকের ময়লা পরিষ্কার করে, আমার জল রক্ষা করে, তবে আমি আবার ফিরে পাব আমার পুরনো সজীব রূপ। আমি তখন আবার বইব আনন্দে, দান করব জীবন, উর্বর করব মাটি।
আমি নদী—প্রকৃতির প্রাণ। আমাকে রক্ষা করা মানে নিজের জীবনকেই রক্ষা করা। তাই বলি, “আমাকে ভালোবাসো, আমিই তোমাদের বাঁচিয়ে রাখব।”
নৈতিক শিক্ষা: নদী আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তার সংরক্ষণ আমাদের কর্তব্য।
১১.৩ একজন মহাপুরুষের কথা।
একজন মহাপুরুষের কথা
ভূমিকা:
বিশ্বের ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাঁদের জীবন, আদর্শ ও কর্ম মানবসমাজকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করে। তাঁরা শুধু তাঁদের যুগেই নন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও হয়ে ওঠেন পথপ্রদর্শক। এমনই এক মহাপুরুষ হলেন মহাত্মা গান্ধী।
মহাত্মা গান্ধীর জীবন পরিচয়:
মহাত্মা গান্ধীর আসল নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর ভারতের গুজরাট রাজ্যের পোরবন্দর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। লন্ডনে আইন পড়া শেষ করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে তিনি ধীরে ধীরে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হয়ে ওঠেন।
তাঁর আদর্শ ও কর্ম:
গান্ধীজির জীবনের মূলমন্ত্র ছিল সত্য ও অহিংসা। তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অস্ত্র নয়, সত্য ও ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ‘অসহযোগ আন্দোলন’, ‘নমক সত্যাগ্রহ’ প্রভৃতি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার জন্য একত্রিত হয়।
তাঁর অবদান:
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজির অবদান অনন্য। তিনি কেবল রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, একজন সমাজসংস্কারকও ছিলেন। অস্পৃশ্যতা দূর করা, গ্রামীণ উন্নয়ন, নারীশিক্ষা ও আত্মনির্ভরতার ওপর তিনি জোর দেন। তাঁর ‘চরকা’ আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক হয়ে ওঠে।
তাঁর আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা:
আজও গান্ধীজির সত্য ও অহিংসার আদর্শ বিশ্বের নানা প্রান্তে মানুষের অনুপ্রেরণা। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বা নেলসন ম্যান্ডেলা—অনেকে তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করেছেন। আধুনিক সমাজে যখন সহিংসতা ও ঘৃণার বিস্তার ঘটছে, তখন গান্ধীর আদর্শ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।
উপসংহার:
মহাত্মা গান্ধী কেবল ভারতের নয়, বিশ্বের একজন মহাপুরুষ। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়—সত্যের পথে চললে, ধৈর্য ও সাহস থাকলে অসম্ভবও সম্ভব। তাই গান্ধীজির মতো মহাপুরুষদের জীবন ও আদর্শ আমাদের চিরকাল অনুসরণীয়।
১১.৪ একটি ভয়াবহ রোগ: ডেঙ্গি।
একটি ভয়াবহ রোগ – ডেঙ্গি
ভূমিকা:
বর্তমান যুগে নানা ধরনের সংক্রামক রোগের মধ্যে ডেঙ্গি একটি ভয়াবহ রোগ। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা মশার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি বছর বর্ষাকাল আসলেই ডেঙ্গি আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দেয় এবং অনেক সময় প্রাণহানিরও আশঙ্কা থাকে।
রোগের কারণ:
ডেঙ্গি রোগের মূল বাহক হলো এডিস মশা। এই মশা সাধারণত পরিষ্কার ও স্থির জলে ডিম পাড়ে। বাড়ির আশপাশে, ফুলের টব, পুরনো টায়ার, ছাদের ট্যাঙ্ক, কৌটো ইত্যাদিতে জমে থাকা জলে এই মশার বংশবিস্তার ঘটে। ডেঙ্গি ভাইরাস সংক্রমিত কোনো ব্যক্তিকে কামড়ানোর পর, সেই মশা আরেকজন মানুষকে কামড়ালে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে।
রোগের লক্ষণ:
ডেঙ্গি আক্রান্ত হলে প্রথমে জ্বর আসে, যা হঠাৎ করেই শুরু হয় এবং খুব তীব্র হয়। এরপর দেখা দেয় তীব্র মাথাব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা, শরীর ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা এবং চামড়ায় ফুসকুড়ি। অনেক ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণও হতে পারে, যা “ডেঙ্গি হেমোরেজিক ফিভার” নামে পরিচিত। রক্তক্ষরণজনিত ডেঙ্গি হলে অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে ওঠে।
প্রতিকার ও চিকিৎসা:
ডেঙ্গির নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ বা টিকা নেই। তাই প্রতিরোধই এর সবচেয়ে ভালো উপায়। রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচুর জল পান করা, বিশ্রাম নেওয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করা জরুরি। কখনোই নিজের মতো করে ওষুধ খাওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে ব্যথানাশক ওষুধ।
প্রতিরোধের উপায়:
১. আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে।
২. কোথাও জল জমে থাকতে দেওয়া যাবে না।
৩. ফুলের টব, ড্রাম, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
৪. শরীর ঢেকে রাখে এমন পোশাক পরতে হবে।
৫. মশারি ব্যবহার ও মশা প্রতিরোধক স্প্রে ব্যবহার করতে হবে।
৬. সরকার পরিচালিত সচেতনতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা উচিত।
উপসংহার:
ডেঙ্গি রোগ এক ভয়ঙ্কর জনস্বাস্থ্য সমস্যা। একটু অসাবধানতা প্রাণঘাতী হতে পারে। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ পরিষ্কার রাখা, মশার বংশবিস্তার রোধ করা এবং প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই পারে ডেঙ্গির ভয়াবহতা কমাতে। সচেতনতা ও সতর্কতাই আমাদের একমাত্র অস্ত্র।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।