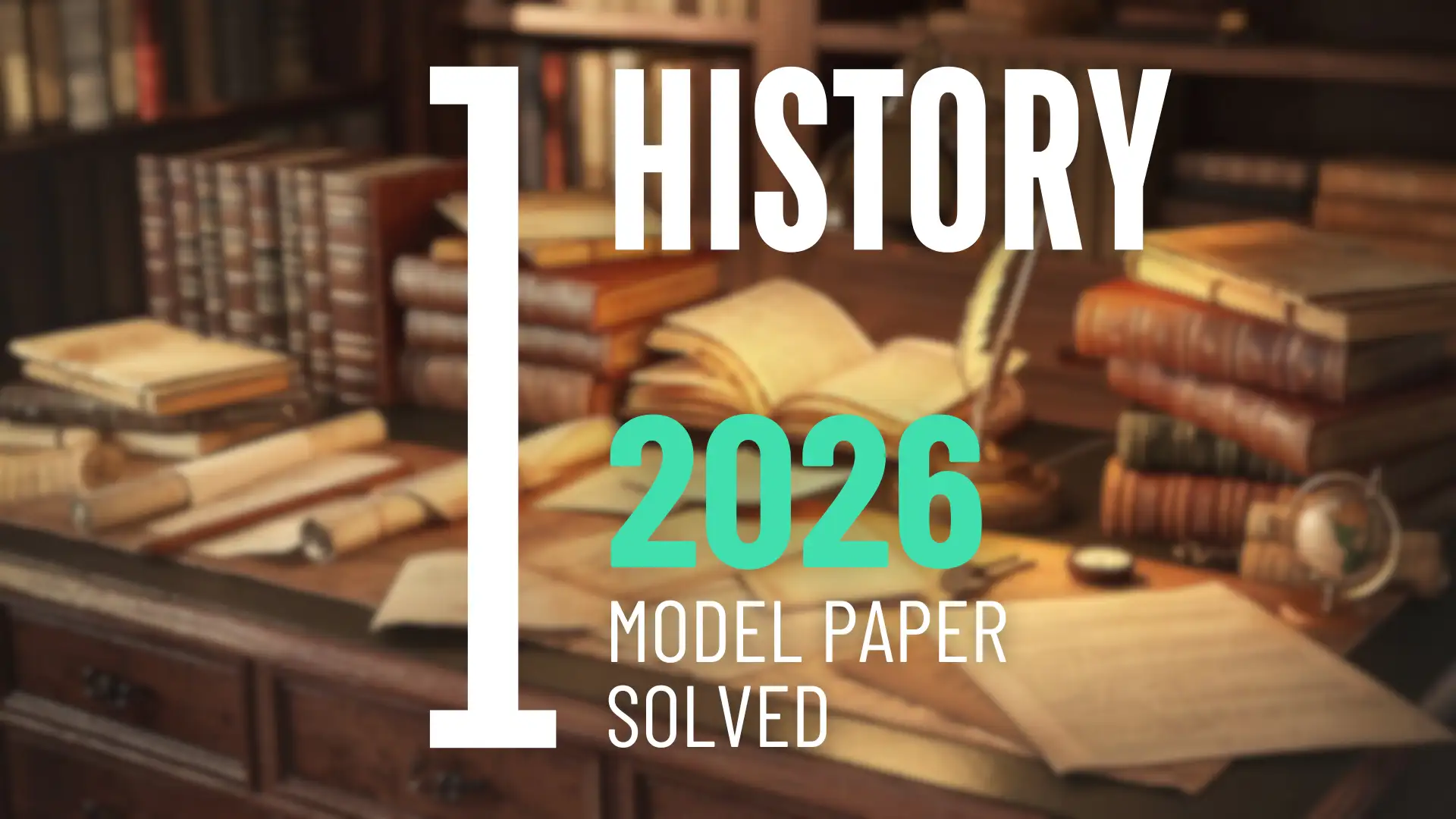আপনি কি মাধ্যমিকের ইতিহাস Model Question Paper 1 প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন? দেখে নিন 2026 WBBSE ইতিহাস Model Paper 1-এর সঠিক উত্তর ও বিশ্লেষণ। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর ইতিহাস ২০২৬ মাধ্যমিক Model Question Paper 1-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। ইতিহাস মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৬ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggleবিভাগ-ক
১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:
১.১ ভারতে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার জনক-
(ক) রণজিৎ গুহ
(খ) অমলেশ ত্রিপাঠী
(গ) রামচন্দ্র গুহ
(ঘ) সুমিত সরকার
উত্তর: (ক) রণজিৎ গুহ
১.২ ভারতীয়রা আলুর ব্যবহার শিখেছিল যাদের কাছ থেকে-
(ক) পোর্তুগিজ
(খ) ইংরেজ
(গ) মোগল
(ঘ) ওলন্দাজ
উত্তর: (ক) পোর্তুগিজ
১.৩ ‘নীলদর্পণ’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক ছিলেন –
(ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ
(খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(গ) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(ঘ) রেভাঃ জেমস লঙ
উত্তর: (ঘ) রেভাঃ জেমস লঙ
১.৪ ‘হুতোম প্যাঁচা’ কার ছদ্মনাম?-
(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র
(খ) কালীপ্রসন্ন সিংহ
(গ) শিবনাথ শাস্ত্রী
(ঘ) কেশবচন্দ্র সেন
উত্তর: (খ) কালীপ্রসন্ন সিংহ
১.৫ বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন-
(ক) উমেশচন্দ্র দত্ত
(খ) শিশিরকুমার ঘোষ
(গ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
(ঘ) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
উত্তর: (ক) উমেশচন্দ্র দত্ত
১.৬ ভারতে প্রথম অরণ্য আইন পাস হয়-
(ক) ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে
(খ) ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে
(ঘ) ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে
উত্তর: (গ) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে
১.৭ ‘ওয়াহাবি’ শব্দের অর্থ হল
(ক) নবজাগরণ
(খ) কর্তব্য
(গ) নির্দেশ
(ঘ) বিদ্রোহ
উত্তর: (ক) নবজাগরণ
১.৮ ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল
(ক) ভারতসভা
(খ) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা
(গ) ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি
(ঘ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস
উত্তর: (খ) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা
১.৯ ‘বাংলার মুকুটহীন রাজা’ বলা হয়
(ক) রাজা রামমোহন রায়কে
(খ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
(গ) কেশবচন্দ্র সেনকে
(ঘ) সৈয়দ আহমদ খানকে
উত্তর: (খ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
১.১০ ‘বন্দেমাতরম’ সংগীতে প্রথম সুর দেন-
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) যদুভট্ট
(ঘ) মধুসূদন দত্ত
উত্তর: (গ) যদুভট্ট
১.১১ ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেন-
(ক) জগদীশচন্দ্র বসু
(খ) সত্যেন্দ্রনাথ বসু
(গ) চন্দ্রমুখী বসু
(ঘ) আনন্দমোহন বসু
উত্তর: (ক) জগদীশচন্দ্র বসু
১.১২ ভারতে সর্বপ্রথম ছাপাখানা গড়ে তোলে-
(ক) ব্রিটিশরা
(খ) ফরাসিরা
(গ) পোর্তুগিজরা
(ঘ) জার্মানরা
উত্তর: (গ) পোর্তুগিজরা
১.১৩ সর্বভারতীয় কিষানসভার প্রথম সভাপতি ছিলেন-
(ক) বাবা রামচন্দ্র
(খ) এন জি রঙ্গ
(গ) স্বামী সহজানন্দ
(ঘ) ফজলুল হক
উত্তর: (গ) স্বামী সহজানন্দ
১.১৪ রম্পা উপজাতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন-
(ক) বাবা রামচন্দ্র
(খ) মাদারি পাসি
(গ) স্বামী বিদ্যানন্দ
(ঘ) আল্লুরি সীতারাম রাজু
উত্তর: (ঘ) আল্লুরি সীতারাম রাজু
১.১৫ ‘মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা’ (১৯২৯) হয়েছিল-
(ক) জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে
(খ) বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে
(গ) শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে
(ঘ) কৃষক নেতাদের বিরুদ্ধে
উত্তর: (গ) শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে
১.১৬ বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টা করেন-
(ক) বীণা দাস
(খ) কল্পনা দত্ত
(গ) প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
(ঘ) সুনীতি চৌধুরি
উত্তর: (ক) বীণা দাস
১.১৭ অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন-
(ক) সতীশচন্দ্র বসু
(খ) সতীশচন্দ্র দত্ত
(গ) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(ঘ) সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত
উত্তর: (ক) সতীশচন্দ্র বসু
১.১৮ দক্ষিণ ভারতের বিদ্যাসাগর বলা হয়-
(ক) জ্যোতিবা ফুলে-কে
(খ) গোপালহরি দেশমুখ-কে
(গ) বীরেশলিঙ্গম পাণ্ডুলু-কে
(ঘ) মহাদেব গোবিন্দ রানাডে-কে
উত্তর: (গ) বীরেশলিঙ্গম পাণ্ডুলু-কে
১.১৯ ভাষাভিত্তিক পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল-
(ক) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে
(খ) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে
(ঘ) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে
উত্তর: (গ) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে
১.২০ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তৈরি করা হয়েছিল
(ক) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে
(খ) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে
(ঘ) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে
উত্তর: (গ) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে
বিভাগ-খ
২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও)
উপবিভাগ ২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও:
২.১.১ গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হরিনাথ মজুমদার।
২.১.২ ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় অঙ্কিত?
উত্তর: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতমাতা চিত্রটি ১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় অঙ্কিত হয়েছিল।
২.১.৩ U Ray & Sons কবে স্থাপিত হয়?
উত্তর: U Ray & Sons প্রকাশনা সংস্থাটি ১৮৯৫ সালে কলকাতায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেন।
২.১.৪ মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর হলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।
উপবিভাগ ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো:
২.২.১ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
উত্তর: ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। (ভুল)
২.২.২ মোপালা আন্দোলন একটি শ্রমিক আন্দোলন ছিল।
উত্তর: মোপালা আন্দোলন একটি শ্রমিক আন্দোলন ছিল। (ভুল)
২.২.৩ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগান ক্লাব আইএফএ শিল্ড জয় করেছিল।
উত্তর: ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগান ক্লাব আইএফএ শিল্ড জয় করেছিল। (ঠিক)
২.২.৪ গান্ধিজি ও ড. আম্বেদকর যৌথভাবে দলিত আন্দোলন করেছিলেন।
উত্তর: গান্ধিজি ও ড. আম্বেদকর যৌথভাবে দলিত আন্দোলন করেছিলেন। (ভুল)
উপবিভাগ ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও:
| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |
| ২.৩.১ জওহরলাল নেহরু | (১) ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ME-20 |
| ২.৩.২ অরণ্যের অধিকার | (২) সত্যশোধক সমাজ |
| ২.৩.৩ রাজা রাধাকান্ত দেব | (৩) লেটারস ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার ΜΕ -18 |
| ২.৩.৪ জ্যোতিরাও ফুলে | (৪) মহাশ্বেতা দেবী |
উত্তর:
| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |
| ২.৩.১ জওহরলাল নেহরু | (৩) লেটারস ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার |
| ২.৩.২ অরণ্যের অধিকার | (৪) মহাশ্বেতা দেবী |
| ২.৩.৩ রাজা রাধাকান্ত দেব | (১) ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি |
| ২.৩.৪ জ্যোতিরাও ফুলে | (২) সত্যশোধক সমাজ |
উপবিভাগ ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নামাঙ্কিত করো:
২.৪.১ পন্ডিচেরি,
২.৪.২ মুন্ডা বিদ্রোহের এলাকা,
২.৪.৩ মোপালা বিদ্রোহের স্থান,
২.৪.৪ দেশীয় রাজ্য মহীশূর। পর্ষদ নমুনা প্রশ্ন
উপবিভাগ ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো:
২.৫.১ বিবৃতি: ঔপনিবেশিক সরকার উপজাতিদের জন্য ‘দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি’ নামে একটি পৃথক অঞ্চল গঠন করেছিলেন।
ব্যাখ্যা ১: এটি গঠিত হয়েছিল চুয়াড় বিদ্রোহের পর।
ব্যাখ্যা ২: এটি গঠিত হয়েছিল কোল বিদ্রোহের পর।
ব্যাখ্যা ৩: এটি গঠিত হয়েছিল মুন্ডা বিদ্রোহের পর।
উত্তর: ব্যাখ্যা ২: এটি গঠিত হয়েছিল কোল বিদ্রোহের পর।
২.৫.২ বিবৃতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘গোরা’ উপন্যাস লিখেছিলেন।
ব্যাখ্যা ১: পাশ্চাত্য শিক্ষার সমালোচনা করার জন্য।
ব্যাখ্যা ২: ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে সমালোচনা করার জন্য।
ব্যাখ্যা ৩: সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে সমালোচনা করার জন্য।
উত্তর: ব্যাখ্যা ১: পাশ্চাত্য শিক্ষার সমালোচনা করার জন্য।
২.৫.৩ বিবৃতি: ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়।
ব্যাখ্যা ১: বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির জন্য।
ব্যাখ্যা ২: কারিগরি শিক্ষার উন্নতির জন্য।
ব্যাখ্যা ৩: জাতীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য।
উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: জাতীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য।
২.৫.৪ বিবৃতি: ভারত সরকার ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। ME-17
ব্যাখ্যা ১: এর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের দমন করা।
ব্যাখ্যা ২: এর উদ্দেশ্য ছিল আইন অমান্য আন্দোলন দমন করা।
ব্যাখ্যা ৩: এর উদ্দেশ্য ছিল দেশব্যাপী সাম্যবাদী কার্যকলাপ দমন করা।
উত্তর: ব্যাখ্যা ১: এর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের দমন করা।
বিভাগ-গ
৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে-কোনো ১১টি)
৩.১ নতুন সামাজিক ইতিহাস কী?
উত্তর: নতুন সামাজিক ইতিহাস বলতে বোঝায় গতানুগতিক শাসককেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চার বাইরে মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি নিয়ে নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চা আবর্তিত হওয়া।
৩.২ আধুনিক ভারত ইতিহাসের উপাদানরূপে আত্মজীবনীর গুরুত্ব কী? ΜΕ -’24
উত্তর: আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় আত্মজীবনীর মূল গুরুত্ব হলো এর প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ এবং স্মৃতিচারণার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার জীবন্ত উপস্থাপনা।
৩.৩ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ΜΕ – ’15, ’13
উত্তর: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও আইন-কানুন শিক্ষাদানের জন্য, যাতে তারা স্থানীয় জনগণকে অধিক দক্ষতা ও সহানুভূতির সাথে শাসন করতে পারেন। এই কলেজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসকদের ভারতের ভাষা ও প্রথায় শিক্ষিত করে তোলা, যাতে তাদের শাসনকার্য আরও কার্যকর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।
৩.৪ উডের নির্দেশনামা কী?
উত্তর: বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই ভারতে পশ্চিমা শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি নির্দেশনামা জারি করেন, যা “উডের ডেসপ্যাচ” বা “চার্লস উডের প্রতিবেদন” নামে পরিচিতি লাভ করে।
৩.৫ সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হল কেন? ΜΕ -’19
উত্তর: সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি হল –
- ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সন্ন্যাসী-ফকিরদের মধ্যে আত্মকলহের ফলে বিদ্রোহীরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।
- মজনু শাহ, ভবানী পাঠকদের মতো নেতারা পরাজিত ও নিহত হলে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এই বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।
- উন্নত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাংগঠনিক শক্তির অভাবে তারা ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে না পারলে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।
৩.৬ খুৎকাঠি প্রথা কী?
উত্তর: ঔপনিবেশিক শাসন শুরুর আগে থেকেই ভারতের আদিবাসী মুন্ডা জনগোষ্ঠীর মধ্যে জমির মালিকানাসংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুসারে, মুন্ডারা বহু প্রজন্ম ধরে সমষ্টিগতভাবে তাদের পৈতৃক জমির যৌথ মালিকানা ভোগ করে আসছিল। এই প্রথাটি ‘খুৎকাঠি প্রথা’ নামে পরিচিত।
৩.৭ ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি কীভাবে জাতীয়তাবাদ উন্মেষে সাহায্য করেছিল? ΜΕ -’24
উত্তর:
বর্তমান ভারত ও জাতীয়তাবাদ – এই গ্রন্থে স্বামীজি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিলেন –
জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার – তিনি প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের আমল থেকে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস বর্ণনা করে জাতীয় গৌরব জাগ্রত করেন। তিনি দেখান যে পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়ে নিজস্ব জাতীয় ঐতিহ্যেই প্রকৃত জাতীয়তাবোধের উৎস নিহিত।
সামাজিক মূল্যবোধের জাগরণ – বিবেকানন্দ বলেছেন যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শোষিত শ্রেণী একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, দেশ শাসন করবে এবং এর মধ্য দিয়েই সমাজের প্রকৃত মূল্যবোধের বিকাশ ও মানুষের জাগরণ ঘটবে।
দেশপ্রেমের মন্ত্র – তিনি ভারতভূমিকে “আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী” বলে বর্ণনা করে একটি গভীর ও আবেগময় দেশপ্রেমের ভিত্তিতে সমগ্র জাতিকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।
জাতীয়তাবাদের বাণী – তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে দেশমাতৃকার মুক্তির ডাক দেন। তিনি “বর্তমান ভারত”-এ উল্লেখ করেন যে, মানুষ জন্ম থেকেই মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গপ্রাপ্ত।
জাতীয় ঐক্যের ডাক – বিবেকানন্দ উপলব্ধি করতেন যে পরাধীন ভারতের মুক্তির একমাত্র পথ হল ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তিনি বর্ণবৈষম্য ও দরিদ্রদের প্রতি বঞ্চনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সকল ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার কথা বলেন।
নারীর মর্যাদা ও জাতি গঠন – বিবেকানন্দ জাতীয় পুনর্জাগরণে নারীর ভূমিকাকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। তিনি সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীকে ভারতীয় নারীর আদর্শ রূপে উপস্থাপন করে নারীর মর্যাদা পুনঃস্থাপনের উপর জোর দেন।
৩.৮ হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার দুটি উদ্দেশ্য লেখো।
উত্তর: হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার দুটি উদ্দেশ্য হল –
- হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা। 2. প্রত্যেককে আত্মনির্ভর করে তোলা।
৩.৯ ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার স্মরণীয় কেন? ΜΕ – ’23
উত্তর: ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানচর্চার জন্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।
৩.১০ বিদ্যাবণিক কাকে, কেন বলা হয়?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ‘বিদ্যাবনিক’ নামে পরিচিত। ১৮৫৬ সালে সংস্কৃত প্রেসের মালিকানা গ্রহণের পর তিনি নিজ রচিত ও অন্যান্য লেখকদের বই মুদ্রণ শুরু করেন। এছাড়া তিনি সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি ও কলকাতা পুস্তকালয় নামে বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় আধুনিক বই বাণিজ্যের পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর এই ভূমিকার কারণেই তিনি ‘বিদ্যাবনিক’ অভিধায় ভূষিত হন।”
৩.১১ সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়? ΜΕ -’24, ’17
উত্তর:
৩.১২ একা আন্দোলনের প্রধান দাবিগুলি কী ছিল?
উত্তর: একা আন্দোলনের মূল দাবিগুলি ছিল উচ্চ ভাড়া, জমিদারদের অত্যাচার এবং শোষণমূলক ভূমি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এছাড়াও কৃষকরা আরোপিত উচ্চ কর ও অন্যায্য ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে।
৩.১৩ দলিত কাদের বলা হয়? ΜΕ -’19, ’15
উত্তর: “দলিত” শব্দটির উদ্ভব মারাঠি “দলন” শব্দ থেকে, যার প্রকৃত অর্থ “পদদলিত” বা “অবহেলিত”। ভারতের বর্ণভিত্তিক সমাজে যারা সবচেয়ে নিচু স্তরে অবস্থান করে, যারা শোষিত, বঞ্চিত ও অচ্ছুৎ বলে বিবেচিত, তারাই “দলিত” নামে পরিচিত ছিল।
৩.১৪ অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি কী?
উত্তর: ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, ছাত্রসভায় উপস্থিতি ও ‘বন্দেমাতরম’ slogan দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার কার্লাইল সার্কুলার জারি করে। বাংলা সরকারের তৎকালীন মুখ্যসচিব কার্লাইলের এই দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ছাত্র ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসারী ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু (১৮৮৩-১৯৪১) ছাত্রদের একত্রিত করে কলকাতায় ‘অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি’ গঠন করেন।
৩.১৫ কী পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন? ΜΕ -’18
উত্তর: ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর পাকিস্তান-প্রশিক্ষিত হানাদার বাহিনী ও সেনারা কাশ্মীরে প্রবেশ করে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালালে মহারাজা হরি সিং সপরিবারে শ্রীনগর ত্যাগ করে ভারত সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সংকটময় মুহূর্তে তৎকালীন ভারতীয় গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত ছাড়া কোনো সহায়তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। ফলে বাধ্য হয়ে ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর মহারাজা হরি সিং কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
৩.১৬ সদ্য স্বাধীন ভারতের সামনে প্রধান দুটি সমস্যা কী ছিল?
উত্তর: সদ্য স্বাধীন ভারতের প্রধান দুটি সমস্যা হল –
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা – দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে, যাতে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়।
ভারতভুক্তির সংকট – স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করলেও হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীরের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য প্রাথমিকভাবে ভারতের সাথে যুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানায়।
বিভাগ-ঘ
৪. সাত বা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)
উপবিভাগ ঘ.১
৪.১ আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় সরকারি নথিপত্রের গুরুত্ব লেখো।
উত্তর: ইতিহাসের মূল লক্ষ্যই হলো সত্যের অনুসন্ধান। আর এই ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে সরকারি নথিপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা নতুন দিল্লিতে অবস্থিত হলেও কলকাতা, মাদ্রাজ, মুম্বাইয়ের মতো শহরের আঞ্চলিক আর্কাইভেও অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষিত আছে।
বিভিন্ন ধরনের সরকারি নথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো –
সরকারি প্রতিবেদন – ব্রিটিশ আমলে সরকার শিক্ষা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইত্যাদি নানা বিষয়ে একাধিক কমিশন গঠন করেছিল। সেই কমিশনগুলির প্রতিবেদন থেকে ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। যেমন: নীল কমিশন (১৮৬০) ও হান্টার কমিশন (১৮৮২) -এর প্রতিবেদন।
পুলিশ ও গোয়েন্দা রিপোর্ট – ব্রিটিশবিরোধী গণআন্দোলন, জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ, গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের তৎপরতা কিংবা নেতাদের চলাফেরার ওপর পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা সরকারের কাছে নিয়মিত প্রতিবেদন জমা দিতেন। পরবর্তীতে এসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে ঐতিহাসিক গবেষণায় নতুন দিক যুক্ত হয়।
কর্মচারীদের বিবরণ – বিভিন্ন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে পরবর্তীকালে সেগুলির বিবরণ লিখে রেখেছেন। আধুনিক ইতিহাসচর্চায় এগুলি এক অনন্য উপাদান। স্যার সৈয়দ আহমদের ‘দ্য কজেস অফ ইন্ডিয়ান রিভোল্ট’ (১৮৫৭ -এর মহাবিদ্রোহ প্রসঙ্গে রচিত) তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
সীমাবদ্ধতা – সরকারি নথি ব্যবহার করে ইতিহাস রচনা করতে গেলে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। সরকারের কাছে অপ্রিয় বা বিব্রতকর অনেক সত্য ঘটনা এই নথিগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়তে পারে। আবার, অনেক সময় এগুলো সরকারি প্রচারের কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ঐতিহাসিককে এগুলো ব্যবহারে থাকতে হয় বিশেষ সজাগ।
উপসংহার – কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সরকারি নথিপত্র আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি ইতিহাসচর্চায় এনেছে নতুন গতিধারা ও সম্ভাবনা।
৪.২ বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনে নব্যবঙ্গ দলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনে নব্যবঙ্গ দলের ভূমিকা –
বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনে নব্যবঙ্গ বা ইয়ংবেঙ্গল দলের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদিও কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান ছিল। নিম্নে এই ভূমিকা বিশ্লেষণাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হলো –
নব্যবঙ্গ দলের উৎপত্তি ও আদর্শ –
পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যে উগ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন তা ইয়ংবেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ)। তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছাত্ররা যুক্তিবাদ, মুক্তচিন্তা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ করেছিলেন।
সমাজসংস্কারে নব্যবঙ্গের অবদান –
সাংগঠনিক ও বৌদ্ধিক ভূমিকা – ডিরোজিওর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছাত্ররা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সভা-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে প্রগতিশীল ধ্যানধারণা প্রচার করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।
সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম – ইয়ংবেঙ্গল দলের সদস্যরা তাদের পত্রপত্রিকার মাধ্যমে হিন্দু সমাজের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তারা নারী শিক্ষার পক্ষে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেন।
যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রসার – তারা ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাদের রচনাবলীতে ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মানবতাবাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
নব্যবঙ্গ দলের সীমাবদ্ধতা –
সমাজের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগের অভাব – সমাজের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র না থাকায় সমাজজীবনে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। তাদের আন্দোলন মূলত উচ্চশিক্ষিত এক শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ – সমালোচকদের মতে, দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতে আগ্রহী ছিলেন। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীকে ‘নকলনবিশের দল’ বলে মন্তব্য করেছেন। ডেভিড কফ এদের ‘ভান্ত পুঁথি পড়া বুদ্ধিজীবী’ বলে অভিহিত করেছেন।
প্রজন্মগত সংকট – ইতিহাসবিদ সুমিত সরকারের মতে, “তারা ছিল পিতা ও সন্তানহীন একটি প্রজন্ম” – অর্থাৎ তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতি থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।
উপবিভাগ ঘ.২
৪.৩ ঔপনিবেশিক সরকার কী উদ্দেশ্যে অরণ্য আইন প্রণয়ন করেছিল? ΜΕ – 22, 18
উত্তর: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বনাঞ্চলের ওপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ঔপনিবেশিক বন আইন প্রণয়ন করে। ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৫ সালে ‘বন সনদ’, ১৮৬৫ সালে প্রথম ‘ভারতীয় বন আইন’ এবং ১৮৭৮ সালে দ্বিতীয় ‘ভারতীয় বন আইন’ পাস করে।
অরণ্যের শ্রেণিবিভাগ – ১৮৭৮ সালের আইন অনুযায়ী বনাঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—সংরক্ষিত বন, সুরক্ষিত বন এবং অশ্রেণীবদ্ধ বন। সংরক্ষিত বনে বনাঞ্চলের পরিচালনা ও বনসম্পদের ওপর সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে সুরক্ষিত বনে কিছু নির্দিষ্ট গাছ কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের জ্বালানিকাঠ সংগ্রহ, পশুচারণাসহ কিছু প্রথাগত অধিকার বজায় রাখা হয়।
আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য – ঔপনিবেশিক বন আইন প্রণয়নের পেছনে কাজ করেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা এবং প্রয়োজনীয়তা।
অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য – ঔপনিবেশিক বন আইন প্রণয়নের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক। ভারতের বিশাল ও সম্পদশালী বনাঞ্চলকে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে এনে ব্রিটিশ অর্থনীতির স্বার্থে কাজে লাগানোই ছিল এই আইনের মূল লক্ষ্য।
সামরিক উদ্দেশ্য – এই আইন প্রণয়নের পেছনে সামরিক কারণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্রিটেনের রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের একটি বড় সরবরাহস্থল ছিল ভারতের বন।
রেলপথের প্রসার – ভারতে রেলপথ সম্প্রসারণ বন আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্যারান্টি প্রথার মাধ্যমে ভারতে রেলপথ বসানো রেলওয়ে কোম্পানিগুলোর রেললাইনের স্লিপার ও অন্যান্য অংশ তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন ছিল। বন আইনের মাধ্যমেই এই চাহিদা পূরণ করা হয়।
বিনোদনের উদ্দেশ্য – ব্রিটিশ রাজপরিবার, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং তাদের সহযোগী দেশীয় রাজন্যবর্গের একটি প্রধান বিনোদন ছিল শিকার। সে জন্যই বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত করে শিকারক্ষেত্র নির্বিঘ্ন করাও বন আইন প্রণয়নের একটি উদ্দেশ্য ছিল।
উপসংহার – সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বনাঞ্চলের ওপর ব্যাপক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী দাবি করত যে, অজ্ঞান কৃষক ও আদিবাসীদের হাত থেকে বনসম্পদ রক্ষার জন্যই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ইতিহাসবিদ এই যুক্তি মেনে নেন না। তাদের মতে, বন সংরক্ষণের পেছনে ব্রিটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি।
৪.৪ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব কীরূপ ছিল? ΜΕ – 20, 17
উত্তর: উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এক নতুন শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণি যুক্তিবাদী, বাস্তববাদী ও ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুগত ছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় তারা বিদ্রোহের প্রতি দ্বিধান্বিত মনোভাব পোষণ করেছিল। কলকাতার ধনী শ্রেণি ও জমিদার সমাজ মনে করত ইংরেজ শাসন ভারতের জন্য কল্যাণকর, কারণ এতে শিক্ষা, আইন ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা এসেছে। তাই তারা বিদ্রোহের বিরোধিতা করে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষেই অবস্থান নেয়।
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহীদের “বর্বর ও দুষ্ট” বলেছেন, রাজনারায়ণ বসু বিদ্রোহকে “নৈরাজ্যবাদী” বলেছেন। অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের দুর্দশা উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষিত সমাজের সমর্থনের অভাবে বাংলায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েনি।
সব মিলিয়ে দেখা যায়, শিক্ষিত বাঙালি সমাজ বিদ্রোহের প্রতি সন্দিহান ও সংযত ছিল। তবে বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকেই পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, যা পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে।
উপবিভাগ ঘ.৩
৪.৫ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কীভাবে একটি অগ্রণী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল?
উত্তর: বাংলায় ছাপাখানা ব্যবস্থার বিকাশে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ডেনিশ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরি, তাঁর সহকর্মী জশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড-এর সহযোগিতায় এই মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও মুদ্রণ।
প্রথম দিকে অভিজ্ঞ মুদ্রাকর উইলিয়াম ওয়ার্ড ও দেশীয় হরফ নির্মাতা পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় প্রেসের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে এই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় আটশোরও অধিক পৃষ্ঠার ‘ধর্ম্মপুস্তক’ বা বাংলা বাইবেল। এটি ছিল বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ মুদ্রণ।
পরবর্তীকালে এখানে রামরাম বসুর ‘হরকরা’ ও ‘জ্ঞানোদয়’, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ‘বত্রিশ সিংহাসন’, কাশীরাম দাসের ‘মহাভারত’, ও কীর্তিবাসের ‘রামায়ণ’ সহ বহু সাহিত্যগ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এছাড়া কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকও এই প্রেসে ছাপা হত।
১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে প্রায় ৪০টি ভাষায় ২,১২,০০০ কপি বই প্রকাশিত হয়, যা সেই সময়ের জন্য এক বিস্ময়কর সাফল্য।
ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য, শিক্ষা ও মুদ্রণ সংস্কৃতির নবজাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আধুনিক প্রযুক্তি, বহুভাষিক প্রকাশনা ও শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে এটি ভারতের এক অগ্রণী ও ঐতিহাসিক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।
৪.৬ ভারতে বামপন্থী ভাবধারার প্রসারে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অবদান কী?
উত্তর:
ভূমিকা – ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সাফল্য সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যার প্রভাব ভারতেও পড়ে। ১৯২০ -এর দশক থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থী ও সাম্যবাদী আদর্শের প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম. এন. রায়ের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।
বামপন্থী মতাদর্শ – ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা হলেও, জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারাও বামপন্থী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।
মানবেন্দ্রনাথ রায় – নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে বেশি পরিচিত, তাকে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ বিবেচনা করা হয়। প্রথমে তিনি পূর্ববঙ্গের অনুশীলন দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ সালে অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জার্মানি যাওয়ার জন্য তিনি ভারত ত্যাগ করেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান এবং সেখানে গ্রেফতার হন। সেখানেই তিনি ‘মানবেন্দ্রনাথ’ নাম ধারণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে মেক্সিকো যান এবং সেখানেই মার্কসবাদের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। মেক্সিকোতেই ১৯১৯ সালে মিখাইল বোরোদিনের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ১৯২০ সালে লেনিনের আমন্ত্রণে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে তিনি রাশিয়া যান। এই সম্মেলনে উপনিবেশগুলোতে বিপ্লবের কৌশল নিয়ে লেনিনের সাথে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। লেনিন তাঁর ‘ঔপনিবেশিক তত্ত্ব’-এ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বকে সমর্থন করলেও, মানবেন্দ্রনাথ রায় এর বিরোধিতা করে একটি বিকল্প তত্ত্ব পেশ করেন। শেষ পর্যন্ত লেনিন কিছুটা সংশোধনী এনেছিলেন।
রাশিয়ায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা – ১৯২০ সালের অক্টোবরে মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখার্জি এবং খিলাফত নেতা মহম্মদ আলি ও মহম্মদ সাফিক তাসখন্দে মিলিত হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ১৯২১ সালের শুরুতে আফগানিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশের তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর ১৯২২ সালে মানবেন্দ্রনাথ রায় বার্লিনে ‘ভ্যানগার্ড অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত বই ‘ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন’ প্রকাশিত হয়। এই সময় বিদেশে থাকা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বরকতউল্লাহর মতো বিপ্লবীরাও মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হন।
বামপন্থায় এম. এন. রায়ের প্রভাব – ভারতের বাইরে শুরু হলেও, দেশের ভেতরে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে মানবেন্দ্রনাথ রায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি নলিনী গুপ্ত ও শওকত উসমানিকে ভারতে পাঠান বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। ১৯২১ সালে কলকাতায় মুজফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে এবং বোম্বাইতে এস. এ. ডাঙ্গে, নিম্বকার প্রমুখের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ডাঙ্গে ১৯২১ সালে ‘গান্ধি বনাম লেনিন’ নামে একটি পুস্তিকা লিখে গান্ধীবাদী পদ্ধতির সমালোচনা করেন এবং ১৯২২ সালে ‘সোশ্যালিস্ট’ পত্রিকা চালু করেন। তাঁর মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।
এম. এন. রায়ের সংযোগ ও কৌশল – ১৯২২ সালের নভেম্বরে ডাঙ্গেকে লেখা একটি চিঠিতে মানবেন্দ্রনাথ রায় একটি দ্বি-স্তরীয় কৌশলের প্রস্তাব দেন একটি ছিল জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী খোলা আন্দোলন, অন্যটি ছিল গোপনে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ। ১৯২২ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের সমালোচনা করলেও জাতীয় আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেনি। এম. এন. রায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বিতরণের জন্য ইস্তাহার লিখতেন। ডাঙ্গে, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার প্রমুখের জওহরলাল নেহেরুর সাথে সুসম্পর্ক ছিল।
বামপন্থার প্রসার ও দমন – কমিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ব্রিটিশ সরকার মেনে নেয়নি। মানবেন্দ্রনাথ রায় যাদের ভারতে পাঠিয়েছিলেন, তাদের অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয় এবং পেশাওয়ার ও কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়। ১৯২৪ সালে মুজফ্ফর আহমেদ, ডাঙ্গে, শওকত উসমানি ও নলিনী গুপ্তকে কানপুর মামলায় কারারুদ্ধ করা হয়।
কানপুরে কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক সূচনা – ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে কানপুরে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় বলে ধরা হয়। এই সময় বাংলায় মুজফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে ‘পেজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি’ গঠিত হয়, যার সাথে কাজী নজরুল ইসলাম, কুতুবউদ্দিন আহমেদ ও হেমন্তকুমার সরকার যুক্ত ছিলেন।
মূল্যায়ন – নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কংগ্রেসের সাথে মতবিরোধের পর তিনি র্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠন করেন। ভারতের কমিউনিস্ট আদর্শের প্রচার এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এর নীতি-কৌশল নির্ধারণে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে তাই তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।
উপবিভাগ ঘ.৪
৪.৭ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ME – 24
উত্তর:
ভূমিকা – ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় এবং একই বছরের ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। বাংলাকে বিভক্ত করার এই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলা ও ভারতজুড়ে যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনে ছাত্রসমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশিষ্ট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ছাত্ররাই ছিল এই আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচারক।
‘স্বদেশি’ ও ‘বয়কট’ আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ –
বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনেরই দুটি প্রধান দিক ছিল ‘স্বদেশি’ ও ‘বয়কট’ আন্দোলন।
স্বদেশি আন্দোলন – ‘স্বদেশি’ বলতে বোঝায় দেশে তৈরি জিনিস ব্যবহার, দেশীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচলন। ছাত্ররা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। তারা ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই’— এই গান গেয়ে জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশি চেতনা ছড়িয়ে দেয়।
বয়কট আন্দোলন – ‘বয়কট’ হলো বিদেশি পণ্য, বিদেশি রীতি-নীতি ও বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করা। ছাত্রদের উদ্যোগে এই আন্দোলন একটি সক্রিয় সংগ্রামে রূপ নেয়। তারা বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেয়, বিদেশি কাগজ-কলম ব্যবহার না করার শপথ নেয়, বিদেশি দোকানের সামনে পিকেটিং করে এবং বিদেশি পণ্য পুড়িয়ে ‘বহ্নি উৎসব’ পালন করে। ১৯০৫ সালের জুলাই মাস থেকেই কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সভা-সমাবেশ করতে শুরু করে। ৩১ জুলাই সমস্ত কলেজের ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ৭ আগস্ট টাউন হলে একটি ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে অংশগ্রহণ করে।
সরকারি দমননীতি – ছাত্রদের এই সক্রিয়তা রোধ করতে ব্রিটিশ সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেয়। তারা কার্লাইল সার্কুলার (১২ অক্টোবর, ১৯০৫) এবং পেডলার সার্কুলার (২১ অক্টোবর, ১৯০৫) জারি করে। এতে বলা হয়, যে সব ছাত্র স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে যোগ দেবে বা ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দেবে, তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হবে।
অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি – সরকারের এই ছাত্র-বিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ‘অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল আন্দোলনের কারণে বহিষ্কৃত ছাত্রদের জন্য বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ – জাতীয়তাবাদী নেতাদের উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ১১ মার্চ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে একটি ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ গঠন করা হয়। স্বদেশি আন্দোলনে জড়িত ছাত্রদের সহায়তাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য।
মূল্যায়ন – বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাদের এই সংগ্রাম পরবর্তীকালের বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের জন্য অনুপ্রেরণা ও পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে।
৪.৮ হায়দরাবাদ রাজ্যটি কীভাবে ভারতভুক্ত হয়েছিল? ΜΕ – 18
উত্তর:
ভূমিকা – ৮২ হাজার বর্গমাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ও ভারত ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত হায়দরাবাদ রাজ্যটি ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্যের ৮৭ শতাংশ মানুষ ছিলেন হিন্দু, কিন্তু শাসক নিজাম ছিলেন মুসলিম। স্বাধীনতা লাভের পর, নিজাম ওসমান আলি খানের অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ভারত সরকার নিজামের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু নিজাম হায়দরাবাদের জনগণ ও ভারত সরকারের কথা না শুনে স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তবে ভারতের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতার কারণে হায়দরাবাদের স্বাধীনতা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।
নিজামের কার্যকলাপ – এই সময় নিজাম ‘মজলিস-ইত্তিহাদ-উল-মুসলিমিন’ নামের একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ও ভারতবিরোধী সংগঠনের নেতা কাশিম রিজভির কুপরামর্শে প্রভাবিত হন। নিজাম রিজভির নেতৃত্বে এবং নিজ সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ‘রাজাকার’ নামে একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র দাঙ্গাবাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনী ভারতের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে। এসময় পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আসতে থাকে এবং রিজভি মুসলিম জনগণকে জিহাদের ডাক দেন।
হায়দরাবাদে বিদ্রোহ – ১৯৪৬ সালে হায়দরাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকরা নিজামের অত্যাচার ও কুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৯৪৭ সালের ৭ আগস্ট হায়দরাবাদ স্টেট কংগ্রেস প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণের দাবিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে। নিজাম ২০ হাজার সত্যাগ্রহীকে গ্রেফতার করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।
হায়দরাবাদের ভারতভুক্তি – পরিস্থিতি সংকটময় হয়ে উঠলে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার নিজামকে একটি চরমপত্র দেয়। ভারত সরকার অন্যান্য দাবির পাশাপাশি অত্যাচারী রাজাকার বাহিনী ভেঙে দেওয়ার দাবি জানায়। নিজাম ভারতের দাবি উপেক্ষা করলে ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী হায়দরাবাদে প্রবেশ করে। ১৮ সেপ্টেম্বর ভারত হায়দরাবাদ রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নেয়। ১৯৪৯ সালে নিজাম ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি হায়দরাবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।
মূল্যায়ন – হায়দরাবাদের ভারতভুক্তি ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময় হায়দরাবাদ রাজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করে অন্ধ্র, বোম্বাই ও মহীশূর রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। হায়দরাবাদের ভারতভুক্তি প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র বলেছেন, ‘হায়দরাবাদের ঘটনা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয়কে চিহ্নিত করে।’ কারণ হায়দরাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানরা নিজামের শাসনের বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে সমর্থন করেছিলেন।
বিভাগ – ঙ
৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ উনিশ শতকের বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজগুলির কীরূপ ভূমিকা ছিল? ME – 18
উত্তর:
ভূমিকা – উনিশ শতকে বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত ছিল ব্রাহ্ম সমাজ। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা পরবর্তীতে ব্রাহ্ম সমাজ নামে পরিচিতি লাভ করে।
ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন শাখা – রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ কালক্রমে বিবর্তিত ও বিভক্ত হয়। যেমন-
১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে আদি ব্রাহ্ম সমাজ।
২. কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ও নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ।
৩. শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে গঠিত হয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।
সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা –
ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার আন্দোলন – ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে, গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে ১৭ নম্বর রেগুলেশন জারি করে সতীদাহ প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করেন।
নারী অধিকারের আন্দোলন – রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজ স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করে, যাতে স্বামীর মৃত্যুর পর নারীরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে।
বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন – রাজা রামমোহন রায় পুরুষদের বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন।
কৌলীন্য প্রথা ও বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন – ব্রাহ্ম সমাজ তখনকার হিন্দু সমাজে প্রচলিত কৌলীন্য প্রথা ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলন চালায়।
জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা – সমাজে গভরভাবে প্রোথিত জাতিভেদ প্রথার ভ্রান্তি দূর করতেও রাজা রামমোহন রায় আন্দোলন করেছিলেন।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার – রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজের হাল ধরেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচার করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের কঠোর বিরোধী এবং বিধবা বিবাহের পক্ষসমর্থক ছিলেন।
কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার – কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার আন্দোলন নতুন গতি পায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ১৮৬৬ সালে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৮৮০ সালে তিনি নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে তোলেন। কেশবচন্দ্র সেন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করেন। পাশাপাশি তিনি বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য কাজ করেন।
তিন আইন – কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনের ফলেই সরকার ১৮৭২ সালে তিনটি আইন পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় এবং অসবর্ণ বিবাহকে আইনসিদ্ধ করা হয়।
উপসংহার – কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তাদের সমাজ সংস্কার কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু ১৮৮০ সালের পর থেকে ব্রাহ্ম সমাজ ধীরে ধীরে তার প্রভাব হারায়। তবুও, উনিশ শতকের বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্ম সমাজগুলির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।
৫.২ সংক্ষেপে মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) চরিত্র বিশ্লেষণ করো। ΜΕ – 17
উত্তর:
প্রস্তাবনা – ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে সিপাহিদের পাশাপাশি কৃষক, সাধারণ মানুষ, জমিদার, অভিজাত ও রাজা-রানিরাও অংশ নিয়েছিলেন। তাই এই ঘটনাকে কেউ ‘সিপাহি বিদ্রোহ’, কেউ ‘সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া’, আবার কেউ কেউ ‘জাতীয় সংগ্রাম’ বলে অভিহিত করেছেন। ভারতের ইতিহাসে এই বিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি নির্ণয় তাই একটি বিতর্কিত বিষয়।
বিদ্রোহের স্বরূপ –
কেবলমাত্র সিপাহি বিদ্রোহ – চার্লস রেইক, হোমস, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যালেসন, সৈয়দ আহমদ, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে শুধুমাত্র একটি সিপাহি বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছেন। তাদের যুক্তি ছিল-
১. এই বিদ্রোহের মূল চালিকাশক্তি ছিল সিপাহিরা। তাদের অসন্তোষ থেকেই বিদ্রোহের সূত্রপাত।
২. এই বিদ্রোহে ভারতীয় জাতীয় চেতনার অগ্রদূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি অংশগ্রহণ করেনি।
৩. দেশের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ এই বিদ্রোহকে সমর্থন করলেও অনেকেই কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এতে যোগ দেয়।
সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া – কিছু ঐতিহাসিকের মতে, ১৮৫৭ সালের ঘটনা ছিল একটি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বা সনাতনপন্থীদের বিদ্রোহ। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, রজনী পাম দত্ত প্রমুখ এই মত পোষণ করেন। লর্ড ডালহৌসির ‘স্বত্ববিলোপ নীতি’র ফলে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব প্রমুখ তাদের রাজ্য হারান। অযোধ্যা ব্রিটিশরা দখল করে নেয়। নতুন ভূমিনীতি তালুকদারদের জমি কেড়ে নেয়। ফলে রাজ্য ও জমি হারানো রাজা-রানি, তালুকদার, কৃষক এবং চাকরিচ্যুত সৈনিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহে শামিল হয়। রজনী পাম দত্ত, পি. সি. যোশি ও ইবনে খালদুনের মতে, এটি ছিল জমি হস্তান্তর ও শ্রেণি-সংঘাতের প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, লক্ষ্মীবাঈ বা নানাসাহেব তাদের পূর্বতন মর্যাদা ফিরে পেতেই বিদ্রোহে যোগ দেন। ড. মজুমদারের মতে, এটি ছিল ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত ও মৃতপ্রায় সামন্তদের ‘মরণকালীন আর্তনাদ’।
গণবিদ্রোহ – উত্তর ও মধ্য ভারতে সিপাহিদের সঙ্গে স্থানীয় সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়ে এই বিদ্রোহকে গণবিদ্রোহের রূপ দেয়। মজফফরনগর, সাহারানপুর, অযোধ্যা, কানপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক গণঅংশগ্রহণ ঘটে। বিহারের পশ্চিমাঞ্চল ও পাটনার বহু জেলায় সাধারণ মানুষ সিপাহিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। জন কে ও সি. এ. বেইলি প্রমুখ ঐতিহাসিক এটিকে ‘গণবিদ্রোহ’ বলে চিহ্নিত করেছেন।
জাতীয় সংগ্রাম – ইংল্যান্ডের টোরি দলের নেতা ডিজরেইলি এবং সমকালীন ইংরেজ ঐতিহাসিক নর্টন, ডাফ, আউট্রাম, হোমস, চার্লস বল প্রমুখ এই বিদ্রোহকে ‘জাতীয় সংগ্রাম’ বলে অভিহিত করেছেন। তাদের যুক্তি হলো –
১. ভারতীয় সিপাহিদের শুরু করা এই বিদ্রোহে পরে অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড ও বিহারের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।
২. লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, কুয়ের সিং প্রমুখ নেতৃবর্গ ও বহু জমিদার-তালুকদার এতে যোগ দেন।
৩. বিদ্রোহীরা দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ‘ভারতের সম্রাট’ ঘোষণা করে একটি দেশীয় শাসনব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা করে। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসও এটিকে ‘জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম’ বলে মন্তব্য করেছেন।
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম – স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এই মত স্বীকার করেননি। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এটি ‘না ছিল প্রথম, না ছিল জাতীয়, আর না ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ’। কারণ –
১. সমগ্র ভারতবাসী এতে অংশ নেয়নি; বরং অনেক ভারতীয় রাজা ও শিখ-গোর্খা সৈন্য সরকারকে সাহায্য করে।
২. বিদ্রোহীদের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা পরিকল্পনা ছিল না।
৩. ১৮৫৭ সালে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনারই জন্ম হয়নি।
৪. একে স্বাধীনতা সংগ্রাম বললে পূর্ববর্তী সব বিদ্রোহকেও তাই বলতে হয়।
অন্যদিকে, শশীভূষণ রায়চৌধুরী একে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় যুদ্ধ ও গণসংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন।
কৃষক বিদ্রোহ – অনেকের মতে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল একটি কৃষক বিদ্রোহ। অনেক ইংরেজ কর্মচারীও মানেন যে, ব্রিটিশ সরকারের জমিনীতি বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছিল। ইবনে খালদুনের মতে, কৃষকেরা এতে মরণপণ লড়াই করেছিল, আর জমিদাররা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থে ইংরেজদের পক্ষ নেয়।
মুসলমান চক্রান্ত – কিছু ঐতিহাসিক, বিশেষ করে পাকিস্তানি ঐতিহাসিক আই. এইচ. কুরেশি ও সৈয়দ মইনুল হক, এই বিদ্রোহকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। মুঘল সম্রাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান বিদ্রোহীদের তৎপরতা দেখে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তবে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয়, কারণ এতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে।
মূল্যায়ন – ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পেছনে শুধু সিপাহিদের অসন্তোষই নয়, বরং বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের গভীর ক্ষোভ ও হতাশা কাজ করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি। ঐতিহাসিকদের মতে, এই বিদ্রোহ ছিল অপরিহার্য, কারণ কোনো পরাধীন জাতি চিরকাল বিদেশি শাসন মেনে নিতে পারে না। অধ্যাপক রণজিৎ গুহ ও গৌতম ভদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই আন্দোলনের গণচরিত্রের ওপর জোর দিয়েছেন। মোটকথা, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বিদ্রোহীদের দেশপ্রেমে কোনো খাদ ছিল না এবং বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এই আন্দোলনে একত্রিত হয়েছিল।
৫.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের কৃষক আন্দোলনের পরিচয় দাও।
উত্তর:
ভূমিকা – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক আন্দোলনের সূচনা ঘটে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলমান জাতীয় আন্দোলনের মূলধারায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি, নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনেও বিপুল সংখ্যক কৃষক যুক্ত হয়। এসব আন্দোলন কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি জাতীয় আন্দোলনকেও শক্তিশালী করে তোলে।
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা –
বাংলা – ১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের তমলুক ও কাঁথি অঞ্চলে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে কৃষকরা ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন করে এবং চৌকিদারি কর প্রদান বন্ধ করে দেয়। পাবনা, বগুড়া ও বীরভূমে জমি জরিপ ও খাজনা নির্ধারণের কাজে কৃষকরা বাধার সৃষ্টি করে। কুমিল্লা, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরের কৃষকরা অসহযোগ আন্দোলনে শরিক হয়। ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে বাঁকুড়ায় খাজনা বন্ধের আন্দোলন তীব্রতা পায়। বাংলায় এই আন্দোলনগুলোকে নেতৃত্ব দেয় বেঙ্গল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি এবং ফজলুল হক ও আক্রম খাঁ প্রতিষ্ঠিত কৃষক প্রজা পার্টি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের কৃষকরা জমিদারদের খাজনা দেওয়া স্থগিত রাখে। ১৯৪২ সালের ১৭ ডিসেম্বর তমলুকে এক স্বাধীন বা সমান্তরাল সরকার গঠিত হয়, যার নামকরণ করা হয় ‘তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’।
বিহার – বিহারেও একের পর এক কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়। স্বামী বিদ্যানন্দের নেতৃত্বে দ্বারভাঙা, মুজফ্ফরপুর, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও মুঙ্গেরের কৃষকরা কর প্রদান বন্ধ করে দেন। বিহার কিষান সভা ও অখিল ভারত কিষান সভার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী বিহারে একাধিক কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। তার নেতৃত্বে ১৯৩৮-৩৯ সালে ‘বখাস্ত ভূমি আন্দোলন’ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। আগস্ট আন্দোলনের সময় মধুবনি এলাকায় প্রায় পাঁচ হাজার কৃষক সশস্ত্রভাবে থানায় হামলা চালায়।
যুক্তপ্রদেশ – বাবা রামচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৯২০ সালে প্রতাপগড়, রায়বেরেলি, সুলতানপুর ও ফৈজাবাদের কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে খাজনা প্রদান বন্ধ করে। জওহরলাল নেহেরু এই কৃষকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে যুক্তপ্রদেশ কিষান সভা গঠন করেন।
একা আন্দোলন – ১৯২১ সালের শেষদিকে যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর, বারাবাঁকি, হরদই ও বরাইচ জেলায় এই আন্দোলনের সূচনা। তালুকদারদের স্বেচ্ছাচারী শাসন ও খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও কিষান সভার কর্মীরা একত্রিত হয়ে এই আন্দোলন গড়ে তোলেন। ঐক্য বা ‘একতা’ থেকে এই আন্দোলন ‘একা আন্দোলন’ নামে পরিচিতি পায়। শুরুতে কংগ্রেস ও খিলাফত নেতারা এগিয়ে নিলেও, আন্দোলনের হিংসাত্মক রূপ নেওয়ায় তারা সরে দাঁড়ান। পরবর্তীতে মাদারি পাসির নেতৃত্বে কৃষকরা সংঘবদ্ধ থাকার শপথ নেয়। তবে পুলিশি দমন-পীড়নের মুখে আন্দোলন ভেঙে পড়ে। ঐতিহাসিক এরিক হবসবম এই হিংসাত্মক আন্দোলনকে ‘সামাজিক ডাকাতি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ – অসহযোগ আন্দোলনের সময় মালাবার অঞ্চলে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহ। অস্পষ্ট প্রজাস্বত্ব আইন ও জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে মোপলা কৃষকরা বিদ্রোহ সংগঠিত করে। ১৯২১ সালে মোপলা নেতা ইয়াকুব হাসানের গ্রেপ্তারের পর এই বিদ্রোহ তীব্রতর হয়। তারা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস ও থানায় হামলা চালায়। প্রায় দশ হাজার মোপলা গেরিলা কৌশলে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। শেষদিকে এই বিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক রূপ নিলে সরকার সামরিক আইন জারি করে তা দমন করে।
অন্ধ্রপ্রদেশের রাম্পা বিদ্রোহ – অসহযোগ আন্দোলনের সময় কৃষ্ণা, গুন্টুর ও গোদাবরী জেলার কৃষক ও আদিবাসীদের আন্দোলন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো আল্লুরি সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে উত্তর গোদাবরীতে সংঘটিত রাম্পা বিদ্রোহ (১৯২২-২৪)। মহাজনদের শোষণ, জমিদারদের অত্যাচার এবং অরণ্য আইন ও বেগার প্রথার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কৃষকরা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে। ১৯২৪ সালের ৬ মে আল্লুরি সীতারাম রাজু ধরা পড়লে বিদ্রোহের অবসান ঘটে।
গুজরাটের বারদোলি সত্যাগ্রহ – ১৯২৮ সালে সুরাট জেলার বারদোলির কৃষকরা জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে, যা বারদোলি সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কৃষকরা সরকারের ৩০% রাজস্ব বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্যাটেল হিন্দু ও মুসলিম কৃষকদের ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে খাজনা না দেওয়ার শপথ করান। আন্দোলনের চাপে সরকার তদন্ত কমিশন গঠন করতে ও সমঝোতায় বসতে বাধ্য হয় এবং আন্দোলন সফল হয়।
মূল্যায়ন – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা বিচ্ছিন্ন কৃষক আন্দোলনগুলোকে সংহত ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কিষান সভা গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক দল ও কমিউনিস্টরা মিলে ১৯৩৬ সালে ‘অখিল ভারত কিষান সভা’ প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মূলত কংগ্রেস ও বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতৃত্ব কৃষক আন্দোলনের নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয়।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি আরও বিভিন্ন বছরের প্রশ্নপত্রের উত্তরও পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথেই থাকুন।