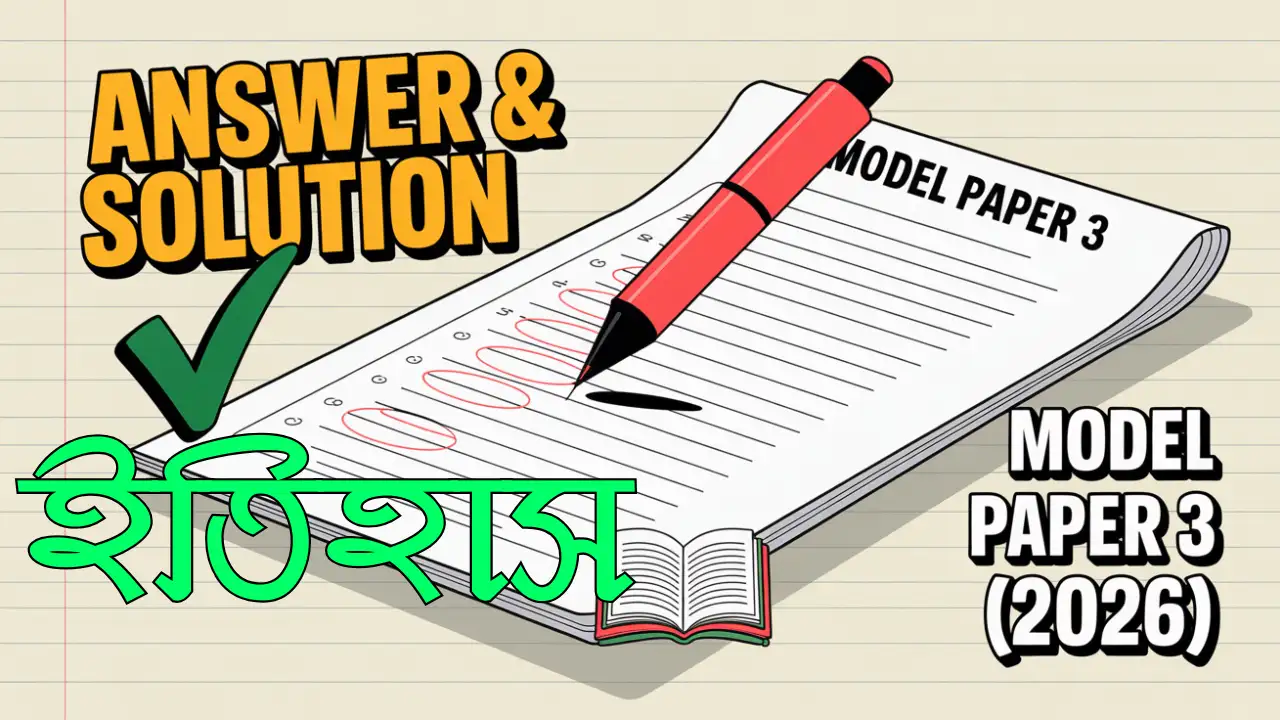আপনি কি ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ইতিহাস Model Question Paper 3 এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর ইতিহাস ২০২৬ মাধ্যমিক ইতিহাস Model Question Paper 3-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। ইতিহাস মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৬ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggleবিভাগ-ক
১.১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:
১.১ ‘জীবনের ঝরাপাতা’ রচনা করেছিলেন। –
(ক) সরলাদেবী চৌধুরানি,
(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
(গ) স্বামী বিবেকানন্দ,
(ঘ) লীলা নাগ
উত্তর: (ক) সরলাদেবী চৌধুরানি
১.২ ইন্দিরা গান্ধিকে লেখা জওহরলাল নেহরুর চিঠিগুলির হিন্দি অনুবাদ করেছেন-
(ক) মুনসি প্রেমচাঁদ,
(খ) কৃয়ন চন্দ্র,
(গ) খুশবন্ত সিং,
(ঘ) সাদাত হাসান মান্টো
উত্তর: (ক) মুনসি প্রেমচাঁদ
১.৩ ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন-
(ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
(খ) রাধাকান্ত দেব,
(গ) কেশবচন্দ্র সেন,
(ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী
উত্তর: (গ) কেশবচন্দ্র সেন,
১.৪ সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি গঠিত হয়-
(ক) ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে,
(খ) ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে,
(গ) ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে,
(ঘ) ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে
উত্তর: (ঘ) ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে
১.৫ কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন –
(ক) ওয়ারেন হেস্টিংস,
(খ) লর্ড হেস্টিংস,
(গ) লর্ড ক্যানিং,
(ঘ) লর্ড আমহার্স্ট
উত্তর: (ক) ওয়ারেন হেস্টিংস
১.৬ ‘হুল’ কথাটির অর্থ হল –
(ক) ঈশ্বর,
(খ) স্বাধীনতা,
(গ) অস্ত্র,
(ঘ) বিদ্রোহ
উত্তর: (ঘ) বিদ্রোহ
১.৭ ভারতে প্রথম নীলকর ছিলেন –
(ক) জেমস লঙ,
(খ) লুই বোনার্ড,
(গ) জোনাথন ডানকান,
(ঘ) মেকলে
উত্তর: (খ) লুই বোনার্ড
১.৮ নবগোপাল মিত্র ছিলেন হিন্দুমেলার –
(ক) সভাপতি,
(খ) সহ-সভাপতি,
(গ) সম্পাদক,
(ঘ) সহ-সম্পাদক
উত্তর: (ঘ) সহ-সম্পাদক
১.৯. আধুনিক ভারতে প্রথম ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল-
(ক) সোমপ্রকাশ পত্রিকায়,
(খ) অমৃতবাজার পত্রিকায়,
(গ) বামাবোধিনী পত্রিকায়,
(ঘ) দেশ পত্রিকায়
উত্তর: (খ) অমৃতবাজার পত্রিকায়
১.১০ ‘Eighteen Fifty Seven’ নামক গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন-
(ক) রমেশচন্দ্র মজুমদার,
(খ) সুরেন্দ্রনাথ সেন,
(গ) আনন্দমোহন বসু,
(ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী
উত্তর: (খ) সুরেন্দ্রনাথ সেন
১.১১ ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স’-এর যে বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন-
(ক) জগদীশচন্দ্র বসু,
(খ) সি ভি রমন,
(গ) প্রফুল্লচন্দ্র রায়,
(ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ বসু
উত্তর: (খ) সি ভি রমন
১.১২ লাইনোটাইপ তৈরি করেন –
(ক) পঞ্চানন কর্মকার,
(খ) সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
(গ) চার্লস উইলকিনস,
(ঘ) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
উত্তর: (খ) সুরেশচন্দ্র মজুমদার
১.১৩ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-
(ক) ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে,
(খ) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে,
(গ) ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে,
(ঘ) ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে
উত্তর: (খ) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে
১.১৪ ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের জনক ছিলেন –
(ক) লালা লাজপত রায়,
(খ) রাসবিহারী বসু,
(গ) জয়প্রকাশ নারায়ণ,
(ঘ) মানবেন্দ্রনাথ রায়
উত্তর: (ঘ) মানবেন্দ্রনাথ রায়
১.১৫ একা আন্দোলনের নেতা ছিলেন –
(ক) মাদারি পাসি,
(খ) ড. আম্বেদকর,
(গ) মহাত্মা গান্ধি,
(ঘ) বাবা রামচন্দ্র
উত্তর: (ক) মাদারি পাসি
১.১৬ দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-
(ক) কল্পনা দত্ত,
(খ) লীলা নাগ (রায়),
(গ) বাসন্তী দেবী,
(ঘ) বীণা দাস
উত্তর: (খ) লীলা নাগ (রায়),
১.১৭ অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন –
(ক) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
(খ) শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু,
(গ) আনন্দমোহন বসু,
(ঘ) চিত্তরঞ্জন দাশ
উত্তর: (খ) শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু
১.১৮ কল্পনা দত্ত রচিত গ্রন্থটি হল –
(ক) শৃঙ্খল ঝঙ্কার,
(খ) চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান,
(গ) সত্তর বৎসর,
(ঘ) জীবনের ঝরাপাতা
উত্তর: (খ) চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান
১.১৯ ভাষাভিত্তিক গুজরাট রাজ্যটি গঠিত হয় –
(ক) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে,
(খ) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে,
(গ) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে,
(ঘ) ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে
উত্তর: (গ) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে
১.২০ স্বাধীন ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্যটি হল –
(ক) অন্ধ্রপ্রদেশ,
(খ) তামিলনাড়ু,
(গ) গুজরাট,
(ঘ) কেরল
উত্তর: (ক) অন্ধ্রপ্রদেশ
বিভাগ-খ
২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও)
উপবিভাগ ২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও:
২.১.১ ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের নাম কী?
উত্তর: ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের নাম হল আলম আরা (Alam Ara)।
২.১.২ ‘উলগুলান’ বলতে কী বোঝায়? ME-’17
উত্তর: “উলগুলান” একটি শব্দ যা মূলত ‘বিদ্রোহ’, ‘বিপ্লব’ বা ‘জনগণের অভ্যুত্থান’ এর অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।
২.১.৩ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট -এর প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন? ME-23, ’20
উত্তর: বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট -এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন প্রমথনাথ বসু।
২.১.৪ কোন্ বিপ্লবী ‘বাংলার অগ্নিকন্যা’ নামে পরিচিত?
উত্তর: কল্পনা দত্ত এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এই দুজন বিপ্লবী ‘বাংলার অগ্নিকন্যা’ নামে পরিচিত।
উপবিভাগ ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো:
২.২.১ ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
উত্তর: ভুল।
২.২.২ ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপীয় সমাজকে সমর্থন করেছিলেন। ME-17
উত্তর: ভুল।
২.২.৩ চট্টগ্রামে মাস্টারদা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’ প্রতিষ্ঠা করেন।
উত্তর: ঠিক।
২.২.৪ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং -এর ফাঁসি হয়।
উত্তর: ঠিক।
উপবিভাগ ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও:
| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |
| ২.৩.১ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন | (১) কৃষক আন্দোলন |
| ২.৩.২ সেওয়ারাম (শিউরাম) | (২) রাধাকান্ত দেব |
| ২.৩.৩ জমিদার সভা | (৩) ভিল বিদ্রোহ |
| ২.৩.৪ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল | (৪) ডিরোজিও |
উত্তর:
| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |
| ২.৩.১ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন | (৪) ডিরোজিও |
| ২.৩.২ সেওয়ারাম (শিউরাম) | (৩) ভিল বিদ্রোহ |
| ২.৩.৩ জমিদার সভা | (২) রাধাকান্ত দেব |
| ২.৩.৪ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল | (১) কৃষক আন্দোলন |
উপবিভাগ ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নামাঙ্কিত করো:
২.৪.১ বাউল সম্রাট লালন ফকিরের জন্মস্থান কুষ্টিয়া
২.৪.২ মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) একটি কেন্দ্র – দিল্লি ME-24, ’22
২.৪.৩ কোহিমা ME-’15, ’12
২.৪.৪ দেশীয় রাজ্য কাশ্মীর।
উপবিভাগ ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো:
২.৫.১ বিবৃতি: উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ‘একটি প্রতারণা মাত্র’।
ব্যাখ্যা ১: সাংস্কৃতিক জাগরণ হয়নি।
ব্যাখ্যা ২: প্রকৃত জাগরণ হয়নি।
ব্যাখ্যা ৩: পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষ প্রতারণা করে।
উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষ প্রতারণা করে।
২.৫.২ বিবৃতি: কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২ খ্রি) মূলত উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম ছিল।
ব্যাখ্যা ১: কোল জনগণ ব্রিটিশ কোম্পানির হাত থেকে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল।
ব্যাখ্যা ২: ছোটোনাগপুর অঞ্চলে কোম্পানি শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোল জনগণ সংঘবদ্ধ হয়েছিল।
ব্যাখ্যা ৩: কোল বিদ্রোহে দেশীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নেতৃত্ব দিয়েছিল।
উত্তর: ব্যাখ্যা ২: ছোটোনাগপুর অঞ্চলে কোম্পানি শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোল জনগণ সংঘবদ্ধ হয়েছিল।
২.৫.৩ বিবৃতি: রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা পছন্দ করতেন না।
ব্যাখ্যা ১: কারণ, এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ব্যয়সাপেক্ষ।
ব্যাখ্যা ২: কারণ, এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা।
ব্যাখ্যা ৩: কারণ, এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মনের বিকাশ ঘটাত না।
উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: কারণ, এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মনের বিকাশ ঘটাত না।
২.৫.৪ বিবৃতি: স্বদেশি আন্দোলনে কৃষকরা যোগদান করেনি। ΜΕ -’18
ব্যাখ্যা ১: কৃষকরা বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিল।
ব্যাখ্যা ২: কৃষকরা এই আন্দোলনকে ভালো মনে করেনি।
ব্যাখ্যা ৩: আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কৃষক স্বার্থ নিয়ে উদাসীন ছিল।
উত্তর: ব্যাখ্যা ৩: আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কৃষক স্বার্থ নিয়ে উদাসীন ছিল।
বিভাগ-গ
৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (যে-কোনো ১১টি)
৩.১ আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ME-’19
উত্তর: আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় ব্যক্তি, ঘটনা বা বিষয়ভিত্তিক ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এটি জাতীয় ইতিহাসের বৃহত্তর পরিসর ও আঞ্চলিক ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে সহায়তা করে। ফলে জাতীয় ইতিহাসের পটভূমি স্থানীয় প্রেক্ষাপটে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্থানীয় ইতিহাস আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস রচনার জন্য মৌলিক উপাদান ও তথ্যসূত্রের যোগান দেয়। এটি ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং গবেষণাকে প্রামাণিক ও সমৃদ্ধ করে। ইতিহাসের বৃহত্তর আলোচনায় অনেক স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায়। আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে এই শূন্যতা পূরণ হয় এবং ইতিহাসের পূর্ণরূপটি জনসমক্ষে প্রকাশ পায়। এর ফলে “Total History” বা সামগ্রিক ইতিহাসের ধারণা আরও বাস্তব ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
৩.২ সত্যজিৎ রায় স্মরণীয় কেন?
উত্তর: সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র “পথের পাঁচালী” (১৯৫৫) -র মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন। এই চলচ্চিত্রটি কান চলচ্চিত্র উৎসব-এ “শ্রেষ্ঠ মানব দলিল” (Best Human Documentary) পুরস্কারসহ মোট ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। “পথের পাঁচালী”, “অপরাজিত” ও “অপুর সংসার” – এই তিনটি চলচ্চিত্র নিয়ে গঠিত অপু ত্রয়ী বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। তিনি শুধু চলচ্চিত্রকারই নন; চিত্রনাট্যকার, শিল্প নির্দেশক, সঙ্গীত পরিচালক এবং জনপ্রিয় লেখক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি একমাত্র ভারতীয় হিসেবে অস্কার সম্মানে ভূষিত হন (১৯৯২) এবং ভারতরত্ন (১৯৯২) -ও লাভ করেন। সুতরাং, সত্যজিৎ রায় তাঁর শৈল্পিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বেই স্মরণীয় হয়ে আছেন।
৩.৩. বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে রাজা রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ME-’17
উত্তর: রাজা রাধাকান্ত দেব নারীশিক্ষার প্রতি তাঁর প্রত্যক্ষ সমর্থন জানান। তিনি কলকাতার শোভাবাজারে নিজ বাড়িতে বালিকাদের জন্য পড়াশোনা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া, মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে তিনি পারিতোষিক বা পুরস্কারের ব্যবস্থাও চালু করেন। তিনি শুধু ব্যবহারিক পদক্ষেপই নেননি, নারীশিক্ষার পক্ষে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও মতাদর্শগত ভিত্তিও তৈরি করেন। তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুল বুক সোসাইটির প্রধান পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৮২২ সালে ‘স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক’ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করেন। এই বইটিতে প্রমাণ করা হয় যে নারীদের শিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় এবং প্রাচীন ভারতে নারীরা সুশিক্ষিত হতেন। এটি নারীশিক্ষার বিরোধী রক্ষণশীল মতবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী যুক্তি ছিল। রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রেরণা ও সমর্থনে একাধিক নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লেডিস অ্যাসোসিয়েশন, মিস কুক ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি স্কুল, উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় এবং বারাসত কালিকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়। তাঁর এই প্রচেষ্টা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাধাকান্ত দেব নারীদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতির আয়োজন করতেন এবং সেগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে সক্ষম হন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাংলায় নারীশিক্ষা আন্দোলনের একজন অগ্রদূত ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিয়ে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা নেন, অন্যদিকে তেমনই নারীশিক্ষার পক্ষে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে এর ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর এই বহুমুখী প্রচেষ্টা বাংলার নারী সমাজের জাগরণের পথ প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৩.৪ নব্য বেদান্তবাদ কী?
উত্তর: স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো নব্য-বেদান্ত। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব “যত মত, তত পথ” এই বাণীর মাধ্যমে জীবসেবাকেই শিবসেবার মতবাদ প্রচার করেছিলেন। বিবেকানন্দ তার গুরুদেবের এই বাণীকে বাস্তবায়িত করার জন্য বলেছেন, “বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে হবে”। এর অর্থ হলো ভারতের আধ্যাত্মিকতার সাথে পাশ্চাত্যের কর্মযোগের সমন্বয় সাধন করা। এভাবেই বিবেকানন্দ বেদান্তের সাথে মানবসেবার আদর্শ যুক্ত করে একটি নতুন বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা দেন। আর এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনকে “নব্য-বেদান্ত” নামে অভিহিত করা হয়।
৩.৫ নীল বিদ্রোহে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা কীরূপ ছিল? ΜΕ-’18
উত্তর: নীল বিদ্রোহে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভূমিকা নিম্নরূপ ছিল –
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার মাধ্যমে সংগ্রাম – তিনি তাঁর সম্পাদিত ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকাকে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করেন। একদিকে তিনি নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে সরব হয়েছিলেন, অন্যদিকে নীলকর-বিরোধী জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেন।
তথ্য সংগ্রহ ও আর্থিক সহায়তা – তিনি নিজে এবং তাঁর নিযুক্ত সাংবাদিকদের মাধ্যমে নীলকরদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের দুর্দশার তথ্য সংগ্রহ করতেন। এই সব খবর তিনি তাঁর পত্রিকায় “নীল জেলা” নামক একটি বিশেষ কলামে নিয়মিত প্রকাশ করতেন। তদুপরি, তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকা সত্ত্বেও তিনি নীলচাষীদের মামলা পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য করতেন।
মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সংগঠিত করা – তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নীলকরদের দাদন প্রথা, উর্বর জমিতে জবরদস্তি করে নীলচাষ করানো এবং কৃষকদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনিগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। এভাবে তিনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং শহুরে জনগণকে নীল বিদ্রোহের পক্ষে সংগঠিত করতে সক্ষম হন।
সংক্ষেপে, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকতার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নীল বিদ্রোহকে একটি জাতীয় আন্দোলনের রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
৩.৬ পাইকান জমি বলতে কী বোঝো?
উত্তর: স্থানীয় জমিদারদের সশস্ত্র রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও ধলভূমে নগদ বেতন পেতেন না; বরং তারা খাজনামুক্ত একখণ্ড জমি ভোগ করার অধিকার লাভ করতেন। এই বিশেষ ধরনের জমিই পরিচিত ছিল ‘পাইকান জমি’ নামে।
৩.৭ ভারতসভা কবে, কোথায় গড়ে উঠেছিল?
উত্তর: ভারতসভা কলকাতায়, ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই গড়ে উঠেছিল।
৩.৮ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা করেছিলেন?
উত্তর: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্যঙ্গচিত্র (ক্যারিকেচার) ও কার্টুনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সমাজের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর শিল্পকর্মে ব্রিটিশ শাসন, ঔপনিবেশিক মানসিকতা এবং সেই ব্যবস্থায় বিকৃত ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ধারালো ব্যঙ্গের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।
তাঁর সমালোচনার মূল দিকগুলো ছিল নিম্নরূপ –
ব্রিটিশ শাসকের ব্যঙ্গ – তিনি ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও শাসকদের অহংকার, অদক্ষতা এবং ভারতবাসীর প্রতি তাদের অবহেলামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যঙ্গচিত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিলেন।
‘বাবু’ সংস্কৃতির মুখোশ উন্মোচন – ঔপনিবেশিক শাসন দ্বারা সৃষ্ট একটি বিকৃত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা অন্ধভাবে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করত এবং দেশীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, গগনেন্দ্রনাথ তাদের ‘বাবু’ চরিত্রে চিত্রিত করে কঠোর সমালোচনা করেন।
ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শোষণ – তাঁর চিত্রগুলোর মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতের অর্থনৈতিক শোষণের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন।
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ – তিনি ছিলেন গভীরভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। তাঁর শিল্পকর্মে সাম্রাজ্যবাদের অমানবিকতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট প্রতিবাদী সুর রয়েছে।
সারসংক্ষেপ – গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবলমাত্র একজন শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সমাজসচেতন ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যঙ্গচিত্র ছিল ঔপনিবেশিক সমাজের অসঙ্গতি, বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী শিল্পীসুলভ অস্ত্র।
৩.৯ চার্লস উইলকিনস কে ছিলেন? ΜΕ -’19
উত্তর: চার্লস উইলকিন্স ছিলেন বাংলা মুদ্রণশিল্পের জনক। তিনি সর্বপ্রথম ধাতু নির্মিত সচল বাংলা হরফের সৃষ্টিকর্তা। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় তৈরি বাংলা হরফ ব্যবহার করে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের ‘A Grammar of the Bengal Language’ বইটি মুদ্রণ করেন। বাংলায় প্রথম ছাপা বই প্রকাশের জন্য তাঁকে ‘বাংলার গুটেনবার্গ’ বা ‘বাংলার ক্যাক্সটন’ বলা হয়।
৩.১০ ‘গোলদিঘির গোলামখানা’ কাকে, কেন বলা হয়?
উত্তর: ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের সময় স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যঙ্গ করে “গোলদিঘির গোলামখানা” বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি এই অভিধাটি ব্যবহার করেছিলেন কারণ, কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে গোলদিঘির পাশে অবস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির কেন্দ্রস্থল। তাঁর মতে, এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও দেশপ্রেমের বিকাশ ঘটানো নয়; বরং সরকারি চাকুরির জন্য কেরানি বা দাসসুলভ মানসিকতাসম্পন্ন কর্মী তৈরি করা। এই ‘কেরানিবৃত্তি’ ছিল তাঁর চোখে গোলামিরই প্রতীক। তাই, গোলদিঘির পাশের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তাঁর কাছে একটি ‘গোলাম’ বা দাস তৈরির কারখানা (“গোলামখানা”) বলে গণ্য হয়েছিল।
৩.১১ তেভাগা আন্দোলনের প্রধান দাবিগুলি কী? ΜΕ -’16, ’14
উত্তর: তেভাগা আন্দোলনের প্রধান দাবিগুলি ছিল নিম্নরূপ –
ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দাবি – এই আন্দোলনের মুখ্য ও কেন্দ্রীয় দাবি ছিল যে জমিতে উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ (তেভাগা) ভাগচাষী বা কৃষকের প্রাপ্য হবে। এর আগে প্রচলিত ব্যবস্থায় জমির মালিকদের ভাগ ছিল অর্ধেক বা তারও বেশি।
জমিদার ও মহাজনদের শোষণের বিরোধিতা – আন্দোলনটি জমিদার, মহাজন এবং নীলকরদের শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল। কৃষকরা এই শোষণ থেকে মুক্তি চেয়েছিল।
কৃষকের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা – আন্দোলনের একটি অন্যতম দাবি ছিল ভাগচাষী কৃষকদের জমির উপর স্থায়ী অধিকার প্রদান করা।
খাজনা ও কর মওকুফ – অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা খাজনা ও বিভিন্ন কর মওকুফেরও দাবি জানায়।
৩.১২ চৌরিচৌরা ঘটনা বলতে কী বোঝো?
উত্তর: চৌরিচৌরা ঘটনা বলতে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি সংঘটিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে বোঝায়। এই ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে ঘটে। ঘটনার পটভূমি ছিল অসহযোগ আন্দোলন। সেদিন এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের সময় পুলিশ ভগবান আহির নামে এক স্বেচ্ছাসেবকের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। এরপর পুলিশ বিনা প্ররোচনায় সাধারণ জনতার উপর গুলি চালালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত জনতা প্রতিবাদস্বরূপ চৌরিচৌরা থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এই অগ্নিকাণ্ডে থানার ভিতরে থাকা ২২ জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়।
৩.১৩ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১৯৩২) কী? ME-’11
উত্তর: সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১৯৩২) ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃক ঘোষিত একটি আইন বা সিদ্ধান্ত, যা ১৯৩২ সালে প্রণয়ন করা হয়। এতে মুসলমান, শিখ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়। অর্থাৎ, মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কেবল মুসলমানরাই ভোট দিতে পারবেন এবং শিখদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কেবল শিখরাই ভোট দিতে পারবেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ঐক্য ভঙ্গ করার জন্য এই কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেয়। এটি ‘কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড’ নামেও পরিচিত।
৩.১৪ কোমাগাতামারু ঘটনা কী?
উত্তর: কোমাগাতামারু ঘটনা ছিল ১৯১৪ সালে সংঘটিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যেখানে কোমাগাতামারু নামক একটি জাপানি জাহাজে করে ৩৭৬ জন ভারতীয় (শিখ, হিন্দু ও মুসলিম) কানাডায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে বিদেশে ভালো জীবন গড়ার লক্ষ্যেই তাদের এই যাত্রা। কিন্তু কানাডার তখনকার বর্ণবাদী এবং কঠোর অভিবাসন আইনের কারণে, জাহাজটি ভ্যানকুভার বন্দরে পৌঁছালে তাদের মধ্যে মাত্র ২৪ জনকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। বাকি সবাইকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। জাহাজটি যখন ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের) হুগলি নদীর বজবজ বন্দরে ফিরে আসে, তখন ব্রিটিশ পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। এই অসম সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় শহীদ হন এবং অনেকেই আহত হন। এই ঘটনা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে রয়েছে।
৩.১৫ পোত্তি শ্রীরামালু কে ছিলেন?
উত্তর: পত্তি শ্রীরামালু ছিলেন একজন গান্ধীবাদী নেতা এবং সমাজসেবী। তিনি তেলুগু ভাষাভাষীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য (অন্ধ্রপ্রদেশ) গঠনের দাবিতে ১৯৫২ সালের ১৯ অক্টোবর আমরণ অনশন শুরু করেন। ৫৮ দিন অনশন চালানোর পর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ ভারত সরকার একটি স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হয়। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের আন্দোলনে তাঁর এই অবিস্মরণীয় ত্যাগের জন্য তাঁকে ‘অমরজীবী’ উপাধি দেওয়া হয়।
৩.১৬ অপারেশন পোলো কী?
উত্তর: অপারেশন পোলো ছিল ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরিচালিত একটি সামরিক অভিযান। এটি ‘অপারেশন পুলিশ অ্যাকশন’ নামেও পরিচিত।
বিভাগ-ঘ
৪. সাত বা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)
উপবিভাগ ঘ.১
৪.১ টীকা লেখো: এ দেশে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদী-পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক। ME-12
উত্তর:
ভূমিকা – অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে, শিক্ষানীতি নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচ্য (ওরিয়েন্টাল) না পাশ্চাত্য (অ্যাংলিসিস্ট) পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত – তা নিয়ে একটি তীব্র বিতর্কের সূচনা ঘটে, যা ইতিহাসে “প্রাচ্যবাদী-পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক” নামে পরিচিত।
বিতর্কের সূত্রপাত ও প্রকৃতি – ১৮১৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু এই অর্থ প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান নাকি পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যয় হবে, তা নিয়ে দ্বন্দ্বের শুরু। ১৮২৩ সালে রাজা রামমোহন রায় সরকারের কাছে একটি পত্র লিখে পাশ্চাত্য শিক্ষা, অর্থাৎ ইংরেজি ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য এই তহবিল ব্যবহারের আহ্বান জানান। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন (১৮২৮-১৮৩৫) জনশিক্ষা কমিটিতে এই দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং কমিটির সদস্যরা দুটি ভাগে বিভক্ত হন – প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী।
প্রাচ্যবাদীদের অবস্থান – প্রাচ্যবাদী বা ওরিয়েন্টালিস্ট গোষ্ঠী ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি ও ভাষা (সংস্কৃত, আরবি, ফারসি) ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাদের মতে, এতে ভারতীয়দের মধ্যে স্বকীয়তা ও আত্মবিশ্বাস বজায় থাকবে। এই গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সমর্থক ছিলেন এইচ. টি. প্রিন্সেপ, হেনরি থমাস কোলব্রুক, ও হোরেস হেম্যান উইলসন।
পাশ্চাত্যবাদীদের অবস্থান – পাশ্চাত্যবাদী বা অ্যাংলিসিস্ট গোষ্ঠী ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিশেষত ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের প্রসারের দাবি তুলে ধরেন। তাদের যুক্তি ছিল যে এতে একটি শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠবে, যা ব্রিটিশ শাসনের জন্য সহায়ক হবে এবং দেশে “সভ্যতার আলো” ছড়িয়ে পড়বে। লর্ড মেকলে, আলেকজান্ডার ডাফ, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, সন্ডার্স ও কলভিন ছিলেন এই মতের প্রধান প্রবক্তা।
মেকলের মিনিট ও পাশ্চাত্যবাদীদের বিজয় – ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, লর্ড টমাস ব্যাবিংটন মেকলে তার বিখ্যাত “মিনিটস অন এডুকেশন” বা “মেকলে মিনিট”-এ প্রাচ্য শিক্ষাকে “অপূর্ণ ও ভ্রান্তিজনক” আখ্যা দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি দাবি করেন যে সমস্ত ইউরোপীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার ইংরেজি ভাষায় সঞ্চিত রয়েছে। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক মেকলের এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করেন এবং সরকারি নীতি হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।
বিতর্কের ফলাফল ও তাৎপর্য – এই বিতর্কে পাশ্চাত্যবাদীদের বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে সরকারি উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের পথ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয়। এর ফলশ্রুতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, যা একটি নতুন শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটায়। একদিকে যেমন আধুনিক চিন্তাভাবনা, বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে। এই সিদ্ধান্ত ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাববিশিষ্ট Turning Point (বিবর্তন বিন্দু) হিসেবে চিহ্নিত।
৪.২ স্বামীজির নব্য বেদান্তবাদের মূল বক্তব্য কী ছিল?
উত্তর: স্বামী বিবেকানন্দের নব্য বেদান্তবাদের মূল বক্তব্য ছিল –
সকলের জন্য বেদান্ত – তিনি বেদান্ত দর্শনকে তপোবন বা সন্ন্যাসীদের সীমিত গণ্ডি থেকে মুক্ত করে গৃহস্থ ও সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে যুক্ত করেন। তাঁর মতে, ব্রহ্মলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করা আবশ্যক নয়।
জীবসেবাই ব্রহ্মসেবা – তাঁর মতে, প্রতিটি জীবই ব্রহ্মের অংশ। তাই মানুষের সেবার মাধ্যমেই ব্রহ্মের সেবা করা যায় এবং জীবাত্মার মুক্তি সম্ভব।
সমষ্টিগত মুক্তি – ব্যক্তিগত মুক্তির পরিবর্তে তিনি সমষ্টির মুক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, “জগতের কল্যাণই নিজের মোক্ষলাভ।”
সমন্বয়বাদী দর্শন – তিনি বেদান্তের শাশ্বত আধ্যাত্মবাদ ও আদর্শবাদের সাথে যুক্তিবাদ ও কর্মযোগের সমন্বয় ঘটান, যা সাধারণ মানুষের মনে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।
সংক্ষেপে, বিবেকানন্দের নব্য বেদান্ত হল একটি কর্মকেন্দ্রিক, মানবসেবামূলক ও সমন্বয়বাদী দর্শন যা আধ্যাত্মিকতাকে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবসেবার সাথে অঙ্গীভূত করে।
উপবিভাগ ঘ.২
৪.৩ মহারানির ঘোষণাপত্রের (১৮৫৮) ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী?
উত্তর: মহারানির ঘোষণাপত্র (১৮৫৮) এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিম্নরূপ –
ভূমিকা – ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনের কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আনে। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর ভারতের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদে মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রটি প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ভারতের শাসনভার সরাসরি ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের হাতে ন্যস্ত হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে।
মহারানির ঘোষণাপত্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য –
শাসনক্ষেত্রে পরিবর্তন – এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ভারতের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের হাতে স্থানান্তরিত হয়। গভর্নর জেনারেল ‘ভাইসরয়’ উপাধি ধারণ করেন এবং একজন ভারত সচিব নিযুক্ত হন।
দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি নীতি – লর্ড ডালহৌসির ‘স্বত্ববিলোপ নীতি’ আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করা হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি ও সন্ধি মেনে নেওয়ার এবং দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজাদের সমর্থন আদায় করা।
ধর্মীয় নীতি ঘোষণা – ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের একটি প্রধান কারণ ছিল ধর্মীয় হস্তক্ষেপের ভয়, তাই ব্রিটিশ সরকার এই নীতি গ্রহণ করে।
চাকরির ক্ষেত্রে সমতার প্রতিশ্রুতি – জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল যোগ্য ভারতবাসীকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের অধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। যদিও বাস্তবে এর প্রয়োগ খুবই সীমিত ছিল।
ক্ষমা ঘোষণা – বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের ক্ষমা করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল উত্তেজনা প্রশমিত করা।
সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির পরিত্যাগ – ব্রিটিশ সরকার আর ভারতীয় রাজ্যগুলির (ভূখণ্ড) দখল করার নীতি পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করে।
মূল্যায়ন – মহারানির ঘোষণাপত্র ছিল একটি কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দলিল, যার মূল লক্ষ্য ছিল ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ-পরবর্তী অস্থিরতা দূর করে ভারতীয়দের, বিশেষত দেশীয় রাজাদের মন জয় করা এবং ব্রিটিশ শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা। ঘোষণাপত্রে দেওয়া অনেক প্রতিশ্রুতিই পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়নি, তাই এই সময়কালকে অনেক ইতিহাসবিদ ‘প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অধ্যায়’ বলে অভিহিত করেন। তবুও, এটি ভারতের শাসন কাঠামোতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন চিহ্নিত করে এবং ব্রিটিশ রাজের সরাসরি শাসনের সূচনা করে।
৪.৪ উনিশ শতকের সভাসমিতিগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
উত্তর: উনিশ শতকের সভাসমিতিগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ –
বাংলায় সূচনা ও বিস্তার – এই সভাসমিতিগুলির বিকাশ সর্বপ্রথম বাংলায় শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তা ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।
শিক্ষিত উচ্চবিত্তের নেতৃত্ব – সাধারণত সমাজের ইংরেজি-জানা শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরাই এই সভাসমিতিগুলির নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।
সীমিত জনসংযোগ – এই সংগঠনগুলির প্রভাব মূলত শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের ওপর এগুলির তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি।
জাতীয়তাবাদী চেতনার ফল – জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সভাসমিতিগুলির উদ্ভব ঘটে।
রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিবর্তন – প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলির রাজনৈতিক কার্যকলাপ মন্থর গতিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এগুলির রাজনৈতিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।
জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ-বিরোধিতার প্রসার – সর্বোপরি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে এই সভাসমিতিগুলি অত্যন্ত সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
উপবিভাগ ঘ.৩
৪.৫ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা কীরূপ ছিল? ME-’20
উত্তর: বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলন কেবল মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শ্রমিকদের মাঝেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে, যা নিম্নলিখিত দিকগুলোতে প্রতিফলিত হয় –
সংগঠিত ধর্মঘট ও প্রতিবাদ – বাংলায় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের দিনই সারাদেশে কলকারখানায় ব্যাপক ধর্মঘট পালিত হয়। হাওড়ার বার্ন কোম্পানির ১২,৫০০ শ্রমিক এবং ফোর্ট গ্লস্টার পাটকলের শ্রমিকরা ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি ও রাখিবন্ধন পালন করে ধর্মঘট করে। বাংলার ৩৭টি পাটকলের মধ্যে ১৮টিতেই ধর্মঘট সংঘটিত হয়। কলকাতা ও খিদিরপুর বন্দরের শ্রমিক, সরকারি ছাপাখানার কর্মী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে রেলকর্মীরাও ধর্মঘটে যোগ দেন।
জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া – শ্রমিকদের এই আন্দোলন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা উপলব্ধি করে যে জাতীয় আন্দোলনের সাফল্যের সাথে তাদের নিজেদের মুক্তিও জড়িত। শ্রমিকরা বুঝতে পারে যে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান না ঘটলে তাদের উন্নতি সম্ভব নয়। তারা জাতীয় রাজনীতির একটি অংশীদারে পরিণত হয়।
নেতৃত্ব ও সংগঠন – প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, অপূর্ব কুমার ঘোষ, অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা শ্রমিকদের সংগঠিত করেন। তারা সরকারি ছাপাখানা, রেল ও পাটকলের শ্রমিকদের একত্রিত করে ধর্মঘটে উৎসাহিত করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রিন্টার্স অ্যান্ড কম্পোজিটার্স লিগ গড়ে তোলেন।
বাংলার বাইরে প্রভাব – এই আন্দোলন বাংলার সীমানা অতিক্রম করে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তুতিকোরিনের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক, পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডির অস্ত্র কারখানার শ্রমিক, বিহারের জামালপুর রেল কারখানার শ্রমিক এবং বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরাও ধর্মঘট ও বিক্ষোভে অংশ নেয়।
রাজনৈতিক সচেতনতা ও সীমাবদ্ধতা – এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলন একটি অসংগঠিত অবস্থা থেকে জাতীয়তাবাদীদের সমর্থনে একটি সংগঠিত ও ব্যাপকতর রাজনৈতিক রূপ লাভ করে।
তবে ১৯০৮ সালের পর জাতীয় আন্দোলন যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন শ্রমিক আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে আসে।
সারসংক্ষেপে, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণি কেবল অংশগ্রহণই করেনি, বরং তাদের সংগঠিত ধর্মঘট ও জাতীয়তাবাদী চেতনা আন্দোলনকে একটি গণআন্দোলনের রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৪.৬ একা আন্দোলনকে কীভাবে বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়?
উত্তর: একা আন্দোলন (1921–22) মূলত অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে কৃষকদের ওপর জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল। তবে এটি শুধু স্থানীয় কৃষকের প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ থাকেনি; আন্দোলনটিকে বৃহত্তর গণআন্দোলনের রূপ দেওয়ার সচেতন প্রচেষ্টা দেখা যায়। প্রথমত, একা আন্দোলনের নেতা কেদারী নাথ মজুমদার, গঙ্গারাম, সুরাজ মণ্ডল প্রমুখ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি তাদের সংগঠিত করতে প্রচার, সভা ও গণআন্দোলনের কৌশল ব্যবহার করেন।
দ্বিতীয়ত, গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে একা আন্দোলনের নেতৃত্ব অহিংস উপায়ে খাজনা না দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করে, যাতে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয়। তৃতীয়ত, আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে প্রচার করে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলেন এবং জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্য গঠনের চেষ্টা করেন।
চতুর্থত, এই আন্দোলন নারী, শ্রমজীবী মানুষ ও নিম্নবর্গের বৃহৎ অংশকে যুক্ত করতে চেষ্টা করে যাতে আন্দোলনটি কেবল জমিদারি বিরোধ নয়, বরং সামাজিক সমতার দাবি হয়ে ওঠে। পঞ্চমত, কংগ্রেসের অনেক স্থানীয় কর্মী একা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এটি জাতীয় আন্দোলনের অংশ হিসেবে গুরুত্ব পায়।
ছয় নম্বর, আন্দোলনকারীরা দাবি তুলেছিলেন যে জমি যিনি চাষ করেন, জমির অধিকার তাঁরই হওয়া উচিত — যা একটি বৃহত্তর কৃষক আন্দোলনের রাজনৈতিক দাবি ছিল। সপ্তমত, গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্বদেশি কমিটি গঠন করে আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হয়।
সুতরাং, দেখা যায় যে একা আন্দোলন কেবল খাজনা না দেওয়ার প্রতিবাদে সীমিত ছিল না; বরং রাজনৈতিক সংগঠন, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃহত্তর কৃষক সমাজকে যুক্ত করার মাধ্যমে আন্দোলনটিকে সর্বভারতীয় গণআন্দোলনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।
উপবিভাগ ঘ.৪
৪.৭ সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো: দেশবিভাগ (১৯৪৭) জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা। ΜΕ -’18
উত্তর:
ভূমিকা – ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাজন ইতিহাসের এক ভয়াবহ মানবিক সংকট সৃষ্টি করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সহিংসতার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জন্মভূমি ছেড়ে সীমান্তের ওপারে শরণার্থীতে পরিণত হন।
উদ্বাস্তু সমস্যার কারণ ও বৈশিষ্ট্য –
ধর্মীয় বিভাজন ও দাঙ্গা – ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে শিখ ও হিন্দু; পূর্ব বাংলায় হিন্দু) নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সহিংসতা তাদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার প্রধান কারণ ছিল।
জনস্রোতের প্রকৃতি – আনুমানিক ২ কোটি মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। তারা পায়ে হেঁটে, ট্রেনে, গাড়িতে ও নৌকায় করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব, দিল্লি) আশ্রয় নেয়।
অবিলম্বিক চ্যালেঞ্জ –
আশ্রয় – লক্ষাধিক মানুষ রেলস্টেশন, খোলা জায়গায় আশ্রয় নেয়।
ত্রাণ – খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসার তীব্র সংকট দেখা দেয়।
পুনর্বাসন – সরকারি আশ্রয়শিবির স্থাপন ও পুনর্বাসন প্রকল্প চালু করা হয়।
দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব –
অর্থনৈতিক চাপ – বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্য, বাসস্থান ও কাজের সংস্থান করা ভারতের অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে।
সামাজিক সংঘাত – স্থানীয় জনগণের সাথে কর্মসংস্থান ও সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
রাজনৈতিক উদ্যোগ – এই সমস্যা মোকাবিলায় আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলন (১৯৪৮) এবং নেহরু-লিয়াকত চুক্তি (১৯৫০) স্বাক্ষরিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উদ্বাস্তু স্রোত কমিয়ে আনা।
উপসংহার – দেশবিভাগজনিত এই উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল এক গভীর মানবিক ট্র্যাজেডি, যা ভারত ও পাকিস্তানের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং যার রেশ আজও বিদ্যমান।
৪.৮ দেশভাগ ভারতে কী কী সমস্যার সৃষ্টি করেছিল লেখো।
উত্তর:
ভূমিকা – ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের ফলে ভারত উপমহাদেশে এক গভীর ও জটিল মানবিক সংকটের সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিশাল সংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুতিই ছিল এর সবচেয়ে তাৎক্ষণিক ও মর্মান্তিক পরিণতি। দেশভাগ ভারতের সামনে নিম্নলিখিত প্রধান সমস্যাগুলির সৃষ্টি করেছিল:
বিশাল উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি – ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের দুইপাশে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে অন্য দেশে শরণার্থী হিসেবে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। প্রায় ২ কোটিরও বেশি মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। তারা পায়ে হেঁটে, ট্রেনে, গাড়িতে ও নৌকায় সীমান্ত পার হয়ে আসেন। এই বিশাল জনস্রোত সামলাতে ভারতকে চরম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিংসা – দেশভাগের সময়ে এবং পরবর্তীকালে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে পাঞ্জাব ও বাংলায় এই দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নেয়। লাখো মানুষ নিহত হন এবং নারীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন হয়। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেসের এই পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়।
অর্থনৈতিক চাপ ও পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ – এত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুকে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও কাজের ব্যবস্থা করা ভারত সরকারের পক্ষে এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনীতির উপর এই অতিরিক্ত চাপ পড়ে। সরকারকে আশ্রয় শিবির তৈরি, খাদ্য সরবরাহ এবং পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ নীতি গ্রহণ করতে হয়।
সম্পত্তি ও আবাসনের সংকট – পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুরা তাদের সব স্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেন। ভারতে তাদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসনের ব্যবস্থা না থাকায় তারা রেলস্টেশন, খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। স্থানীয়দের সাথে আবাসন ও কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও বিরোধের সৃষ্টি হয়।
সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংঘাত – উদ্বাস্তু ও স্থানীয়দের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের পার্থক্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রে মেলবন্ধন ঘটেনি। উদ্বাস্তুরা স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রবেশ করায় এবং চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তৈরি করায় সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
আন্তঃসীমান্ত সম্পর্কের টানাপোড়েন – উদ্বাস্তু সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৮ সালে আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলন এবং ১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকত আলি খানের মধ্যে দিল্লি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সমস্যার মৌলিক সমাধান হয়নি।
উপসংহার – দেশভাগ কেবল ভূখণ্ডের বিভাজনই ঘটায়নি, এটি তৈরি করেছিল এক ভয়াবহ মানবিক ট্র্যাজেডি। উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক চাপ এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের গভীর ক্ষত ভারতের সমাজ ও রাজনীতিকে দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবিত করেছে।
বিভাগ-ঙ
৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও :
৫.১ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সতীদাহপ্রথাবিরোধী প্রচেষ্টাগুলির পরিচয় দাও। রামমোহন রায় কীভাবে সতীদাহপ্রথাবিরোধী আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করেন? ME – ’20
উত্তর:
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সতীদাহ প্রথা বিরোধী প্রচেষ্টাগুলির পরিচয় –
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা একটি বর্বর ও নারীবিদ্বেষী সামাজিক কুপ্রথা হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্তরে যে প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ –
প্রাথমিক সরকারি পদক্ষেপ (১৮১৩) – ১৮০৫ সালে নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এর প্রেক্ষিতে ১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার এই প্রথাকে আইনগত স্বীকৃতি দেয় বটে, কিন্তু কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি জারি করে। যেমন –
1. সতী হওয়ার জন্য নারীর স্বেচ্ছাসম্মতি বাধ্যতামূলক।
2. সতী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স ১৬ বছর।
3. গর্ভবতী নারী বা শিশুসন্তানের মাকে সতী হতে দেওয়া যাবে না।
4. সতীদাহ অনুষ্ঠানের আগে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হবে।
বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ – কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার জন অনস্টুয়ার ১৮১৮ সালে কলকাতা শহরের মধ্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।
খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা – উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশনারিরা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। তারা ‘সমাচার দর্পণ’-এর মতো পত্রিকায় এই প্রথার বিরুদ্ধে লেখালেখি করেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে এটি হিন্দু শাস্ত্রসম্মত নয়। তারা গভর্নর জেনারেলের কাছে এই প্রথা নিষিদ্ধ করার আবেদনও জানান।
স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের আপত্তি – মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা সুপ্রিম কোর্টকে জানান যে সতীদাহ প্রথার সমর্থনে হিন্দু শাস্ত্রে কোনও নির্দেশ নেই।
রামমোহন রায় কীভাবে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করেন –
রাজা রামমোহন রায় ছিলেন সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ও সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাঁর কৌশলপূর্ণ ও বহুমুখী প্রচেষ্টাই এই আন্দোলনকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। তাঁর ভূমিকা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে উল্লেখযোগ্য –
বৌদ্ধিক ও শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রদান – রামমোহন রায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যে সতীদাহ প্রথা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদিত নয়। তিনি মনুসংহিতা, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যে শাস্ত্রে বিধবাদের জন্য সংযমী জীবনযাপনের বিধান আছে, স্বামীর চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার কোনও নির্দেশ নেই। তিনি তাঁর বাংলা ও ইংরেজি রচনাবলীর মাধ্যমে এই যুক্তি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন।
জনমত গঠন – তিনি তাঁর সংবাদপত্র ‘সংবাদ কৌমুদী’ -কে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। পত্রিকায় নিয়মিতভাবে সতীদাহের নৃশংসতা, তার অশাস্ত্রীয়তা এবং নৈতিক অনৈতিকতার বিরুদ্ধে লেখা প্রকাশিত হত, যা শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।
প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ – রামমোহন রায় কেবল তত্ত্বীয় আলোচনায় সীমিত থাকেননি। কথিত আছে যে তিনি নিজে শ্মশানে যেতেন এবং স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতে ইচ্ছুক বিধবাদের ও তাদের পরিবারবর্গকে মানবিক আবেদন ও শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেন, যাতে তারা এই নৃশংস কাজ থেকে বিরত থাকে।
সরকারের কাছে আবেদন ও চাপ সৃষ্টি – যদিও রামমোহন রায় প্রথমদিকে আইনী হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন না, পরবর্তীতে তিনি বুঝতে পারেন যে সামাজিক সংস্কার ছাড়া এই প্রথা নির্মূল সম্ভব নয়। ১৮১৮ সালে তিনি একটি আবেদনপত্রে লেখেন যে সতীদাহ হল “নরহত্যা” এবং এটি মানবতাবোধ ও শাস্ত্র উভয় দিক থেকেই নিন্দনীয়। সর্বশেষে, ১৮২৯ সালে বাংলার প্রায় ৩০০ জন বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদনপত্র গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে পেশ করতে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।
ফলাফল – রামমোহন রায়ের এই সুপরিকল্পিত, যুক্তিপূর্ণ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা লর্ড বেন্টিঙ্ককে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করে। ফলস্বরূপ, ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ‘বিধান XVII’ (Regulation XVII) জারি করার মাধ্যমে সতীদাহ প্রথাকে চিরতরে বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই ঐতিহাসিক সাফল্যে রামমোহন রায়ের ভূমিকা ছিল নির্ধারক ও সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল।
৫.২ উনিশ শতকে লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশের পরিচয় দাও।
উত্তর:
ভূমিকা – ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশের যুগ। এই সময় সাহিত্য (লেখা) ও চিত্রকলা (রেখা) জাতীয় চেতনা গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সাহিত্যিক এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিল্পী তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতবাসীর মনে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেন।
লেখায় জাতীয়তাবোধের পরিচয় –
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) –
মাতৃভূমির দেবীরূপ – এই উপন্যাসে মাতৃভূমিকে দেবী দুর্গারূপে কল্পনা করে ‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের প্রবর্তন করা হয়। এটি ভারতবাসীর মনে মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি ও স্বদেশপ্রেমের ধারণা জাগিয়ে তোলে।
বন্দেমাতরম গান – ‘বন্দেমাতরম’ গানটি পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান স্লোগান ও অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা: উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসনের অন্যায়, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা’ (১৯১০) –
সমাজের বাস্তব চিত্র – ‘গোরা’ উপন্যাসে দেশের দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং ইংরেজি-শিক্ষিত ভদ্রসমাজের অবজ্ঞার চিত্র ফুটে উঠেছে।
বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা – গোরা চরিত্রের মাধ্যমে বর্ণবৈষম্যের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং স্বদেশবাসীর মধ্যে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে অবস্থান – রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী এবং জাতীয় ঐক্যের অন্তরায়।
স্বামী বিবেকানন্দের ‘বর্তমান ভারত’ (১৯০৫) –
সাংস্কৃতিক গৌরববোধ – স্বামীজি ভারতীয়দের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গৌরব সম্পর্কে সচেতন করেন, যা জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।
জাতীয় ঐক্য – হিন্দু ধর্মের উদার মানবিক দিক তুলে ধরে তিনি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আত্মনির্ভরশীলতা: তিনি শিক্ষা, আত্মনির্ভরশীলতা ও চরিত্র গঠনের ওপর জোর দেন, যা জাতীয় জাগরণের অপরিহার্য অঙ্গ।
রেখায় জাতীয়তাবোধের পরিচয় –
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতমাতা’ চিত্র (১৯০৫) –
দেবীরূপে দেশ – এই চিত্রে ভারতভূমিকে এক দেবীমূর্তিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, যা মানুষের মনে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের আবেগ সৃষ্টি করে।
জাতীয়তাবাদের প্রতীক – ‘ভারতমাতা’ চিত্র শুধু একটি শিল্পকর্ম নয়, এটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক শক্তিশালী ও আবেগপূর্ণ প্রতীকে পরিণত হয়। এটি সাধারণ মানুষ থেকে বিপ্লবীদের সকলের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র –
সমাজ ও শাসনের সমালোচনা – গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে সমকালীন সমাজের অসংগতি ও ব্রিটিশ শাসকদের রূপ তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন।
ঔপনিবেশিক সমালোচনা – ‘নবহুল্লোড়’, ‘জাতাসুর’, ‘অদ্ভুদলোক’, ‘বিরূপবজ্র’ প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্র ঔপনিবেশিক সমাজ ও শাসনের তীব্র সমালোচনার প্রতিফলন ছিল।
উপসংহার – ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক ও শিল্পীরা তাদের লেখা ও রেখার মাধ্যমে ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ বপন করেন। তাদের সৃষ্টিকর্ম ভারতীয়দের আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদা ও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি রচনা করে এবং পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করে। কলম ও তুলির এই শক্তিই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।
৫.৩ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ΜΕ -’17
উত্তর:
ভূমিকা – উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ভারতের বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করতে ভগিনী নিবেদিতা, যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও, “ভারতের বিপ্লববাদের জননী” মাদাম কামা (ভিকাজি রুস্তম কামা) ভারতের বাইরে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর অনেক তরুণী, বিশেষ করে দীপালি সংঘের সদস্যরা, সশস্ত্র পথে সংগ্রামে আকৃষ্ট হন।
সংগঠন গঠন ও প্রশিক্ষণ – ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নারীদের সংগঠিত করতে লীলা নাগ (রায়)-এর ভূমিকা অপরিসীম। ১৯২৩ সালে তিনি ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন ‘দীপালি সংঘ’। এই সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা। এখানে লাঠিখেলা, শরীরচর্চা, অস্ত্র চালনা প্রভৃতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। দীপালি সংঘ ছিল নারী বিপ্লববাদের একটি কার্যকরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
সশস্ত্র অভিযান ও আত্মবলিদান – সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীরা সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন এবং আত্মবলিদান দিয়েছেন।
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার – দীপালি সংঘের সদস্যা ও মাস্টারদা সূর্য সেনের দলের সদস্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন অভিযানসহ সশস্ত্র অপারেশনে অংশ নেন। ১৯৩২ সালে তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পাহাড়তলি ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ সফলভাবে কার্যকর হয়। পুলিশের হাতে ধরা পড়া এড়াতে তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহুতি দেন, এর ফলে তিনি হয়ে উঠছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের “প্রথম মহিলা শহীদ”।
কল্পনা দত্ত – ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সদস্যা কল্পনা দত্ত ডিনামাইট দিয়ে আদালত উড়িয়ে বন্দী বিপ্লবীদের মুক্ত করার (‘ডিনামাইট ষড়যন্ত্র’) পরিকল্পনা করেন। তিনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সাথে ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের দায়িত্বে ছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রেপ্তার হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন মামলায় তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী ও বীণা দাস – ১৯৩১ সালে কুমিল্লার স্কুলছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনকে গুলি করে হত্যা করেন। ১৯৩২ সালে বীণা দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন। এই ঘটনাগুলো নারীদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার তীব্রতার পরিচয় দেয়।
আজাদ হিন্দ ফৌজে ভূমিকা – নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ডাকে সাড়া দিয়ে ডা. লক্ষ্মী স্বামীনাথন (সায়গল) আজাদ হিন্দ ফৌজের ‘ঝাঁসি বাহিনী’র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় ১,৫০০ নারী এই বাহিনীতে যোগ দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নেন এবং দেশমুক্তির সংগ্রামে অংশ নেন। ১৯৪৫ সালে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন ব্রিটিশ সেনার হাতে বন্দি হন।
পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য – ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের বিশ্লেষণে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয় –
সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব – মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নারীরাই এই আন্দোলনে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন।
সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা – যদিও নারীরা সাহসিকতার সাথে অংশ নিয়েছিলেন, সামগ্রিকভাবে তাদের অংশগ্রহণ সীমিত ছিল এবং পুরুষ-কেন্দ্রিক বিপ্লবী দলগুলোতে তাদের উপর পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেকক্ষেত্রেই কম দেওয়া হত।
বাংলার নারীদের অগ্রণী ভূমিকা – সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে দেশের নারীদের মধ্যে বাংলার নারীসমাজই সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রীতিলতা, কল্পনা, বীণা, শান্তি-সুনীতি, লীলা নাগ – সকলেই বাংলার মাটি ও সমাজের সন্তান ছিলেন।
উপসংহার – সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীরা কেবল প্রেরণাদাত্রীই ছিলেন না, তারা সংগঠক, প্রশিক্ষক এবং অস্ত্র হাতে শত্রুর সাথে লড়াই করে জীবন উৎসর্গকারী যোদ্ধা হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের এই সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মবলিদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।