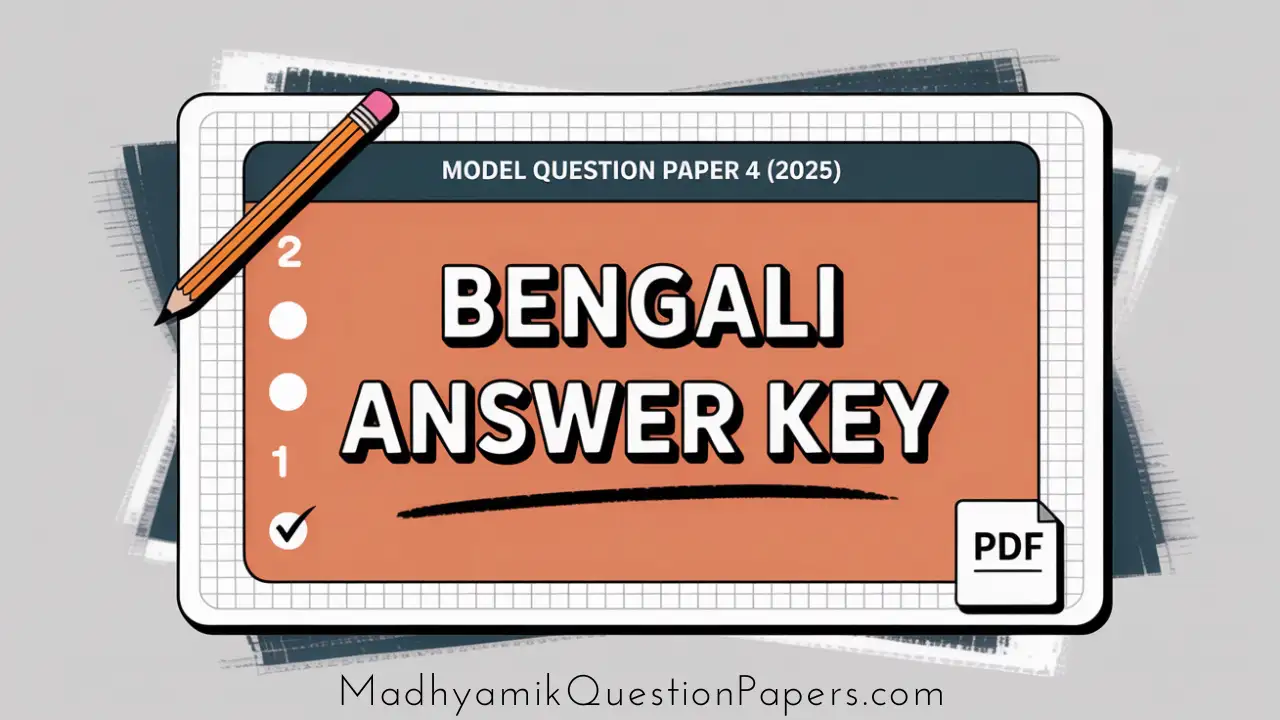আপনি কি ২০২৫ সালের মাধ্যমিক বাংলা Model Question Paper 4 (2025)-এর সঠিক উত্তর খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই প্রতিবেদনে আমরা WBBSE এর বাংলা Model Question Paper 4 (2025)-এর প্রতিটি প্রশ্নের নিখুঁত ও বিস্তারিত উত্তর তুলে ধরেছি।
নিচে প্রশ্নোত্তরগুলো পরপর সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং প্রস্তুতিতে কাজে লাগাতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার উত্তর মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ।
MadhyamikQuestionPapers.com ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তর একেবারে বিনামূল্যে সরবরাহ করে আসছে। ২০২৫ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান এখানেই সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে সম্পূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তরগুলো এখনই দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ ‘তুমি তো ইউরোপিয়ান নও।’ কে অপূর্বকে কথাটি বলেছিলেন?
(ক) বর্মার জেলাশাসক,
(খ) বর্মার সব-ইনস্পেক্টর,
(গ) রেঙ্গুনের সব-ইনস্পেকটর,
(ঘ) বড়োসাহেব।
উত্তর: (খ) বর্মার সব-ইনস্পেক্টর
১.২ রেললাইন থেকে ব্রিজের দূরত্ব
(ক) এক মাইল,
(খ) তিন মাইল,
(গ) চার মাইল,
(ঘ) পাঁচ মাইল।
উত্তর: (ক) এক মাইল
১.৩ ‘আমাকে বাঁচানোর জন্য তো আমার মা আছে।’ কথাটির বস্তা ছেলে।
(ক) অমৃত,
(খ) ইসাব,
(গ) কালিয়া,
(ঘ) দলের একটি
উত্তর: (ক) অমৃত
১.৪ “কৃপা কর…” পদ্মা যাঁর কৃপা চাইছেন, তিনি হলেন
(ক) ইন্দ্র
(খ) সমুদ্রনৃপতি,
(গ) মাগন গুণী,
(ঘ) নিরঞ্জন।
উত্তর: (ঘ) নিরঞ্জন
১.৫ ‘প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু’ আফ্রিকার মনে যা জাগাচ্ছিল, তা হল
(ক) বিভীষিকা,
(খ) অসন্তোষ,
(গ) মন্ত্র,
(ঘ) ক্রন্দন।
উত্তর: (গ) মন্ত্র
১.৬ ‘কৌশিক-ধ্বজ’ কথার অর্থ
(ক) সবুজ পতাকা,
(খ) রেশমি পতাকা,
(গ) সাদা পতাকা,
(ঘ) লাল পতাকা।
উত্তর: (খ) রেশমি পতাকা
১.৭ ফাউন্টেন পেন সংগ্রহ করতেন
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
(খ) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,
(গ) জীবনানন্দ দাশ,
(ঘ) সত্যজিৎ রায়।
উত্তর: (খ) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
১.৮ কোথায় পপুলার সায়েন্স লেখা সুসাধ্য?
(ক) ইতালি-ইওরোপ,
(খ) ইংল্যান্ড-আমেরিকায়,
(গ) ইওরোপ-আমেরিকায়,
(ঘ) ভারত-চিনে।
উত্তর: (গ) ইওরোপ-আমেরিকায়
১.৯ যারা ইংরেজিতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করেন, লেখকের মতে তাদের রচনা কীরূপ হয়?-
(ক) উৎকট,
(খ) উদ্ভট,
(গ) কিস্তৃত,
(ঘ) কিমাকার।
উত্তর: (ক) উৎকট
১.১০ ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।’ রেখাঙ্ক্ষিত পদটি কোন্ কারক?
(ক) নিমিত্ত,
(খ) কর্ম,
(গ) অপাদান,
(ঘ) অধিকরণ।
উত্তর: (গ) অপাদান
১.১১ ‘ক্রিয়ান্বয়ী কারকম্’ কথাটি বলেছিলেন
(ক) পাণিনি,
(খ) ভর্তৃহরি,
(গ) পতঞ্জলি,
(ঘ) কালিদাস।
উত্তর: (গ) পতঞ্জলি
১.১২ কোন্ কর্মধারয় সমাসে উপমেয়র উল্লেখ নেই?-
(ক) উপমান কর্মধারয়,
(খ) উপমিত কর্মধারয়,
(গ) রূপক কর্মধারয়,
(ঘ) কোনোটিই সত্য নয়।
উত্তর: (ক) উপমান কর্মধারয়
১.১৩ ‘আমরা’ এই সমাসবদ্ধ পদটি যে সমাসের দৃষ্টান্ত
(ক) একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস,
(খ) নিত্য সমাস,
(গ) অব্যয়ীভাব সমাস,
(ঘ) সমার্থক দ্বন্দু সমাস।
উত্তর: (ক) একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস
১.১৪ তোমার কথা শুনেই সে এ কাজ করেছে। বাক্যটি একটি
(ক) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য,
(খ) সন্দেহবাচক বাক্য,
(গ) শর্তসাপেক্ষ বাক্য,
(ঘ) আবেগসূচক বাক্য।
উত্তর: (গ) শর্তসাপেক্ষ বাক্য
১.১৫ অর্থবোধের জন্য বাক্যে পদসমূহের যথাযথভাবে সাজানোকেই বলে-
(ক) আকাঙ্ক্ষা,
(খ) আসত্তি,
(গ) যোগ্যতা,
(ঘ) কোনোটিই নয়।
উত্তর: (খ) আসত্তি
১.১৬ “পাঁচদিন নদীকে দেখা হয় নাই”-এটি কোন্ বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্তৃবাচ্য,
(খ) ভাববাচ্য,
(গ) কর্মবাচ্য,
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য।
উত্তর: (খ) ভাববাচ্য
১.১৭ কর্মবাচ্যের কর্তাকে বলা হয়
(ক) অনুক্ত কর্তা,
(খ) উক্ত কর্তা,
(গ) উহ্য কর্তা,
(ঘ) প্রযোজ্য কর্তা।
উত্তর: (ক) অনুক্ত কর্তা
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ ‘এ-সব কথা বলার দুঃখ আছে।’ কোন্ কথা বলার দুঃখ আছে?
উত্তর: ইংরেজ পুলিশ নিমাইবাবু অপূর্বর আত্মীয় হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মনিয়োগকারী সব্যসাচীই তার বেশি আপন এই কথা বলার দুঃখ আছে।
২.১.২ ‘নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে।’ নদীর বিদ্রোহের কারণ কী ছিল?
উত্তর: নদীর বিদ্রোহের কারণ শুকনো নদী পাঁচ দিনের বৃষ্টির জলে উন্মত্ত, তীব্র স্রোতযুক্ত জলধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মানুষের তৈরি নতুন ব্রীজ প্রযুক্তি প্রকৃতিকে বন্দি করে নিজেদেরই ক্ষতি করেছে । প্রকৃতির রুদ্ররোষ মানুষের সৃষ্ট গর্বের সৌধ ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে । সেই কারণে নদী প্রতিশোধ নিতে চায়।
২.১.৩ কোন্ সময় ইসাব আর অমৃত দুজনেরই ভয় কেটে গেল?
উত্তর: পান্নালাল প্যাটেলের “অদল-বদল” গল্পে ইসাব ও অমৃতের ভয় তখনই কেটে যায়
যখন ইসাবের বাবা একটি সূঁচ-সুতো দিয়ে অমৃতের ছেঁড়া জামাটি সেলাই করে দেন।ফলে তাদের জামা-কাপড় বদলানোর ভয় কেটে যায় ।
২.১.৪ গল্প ছাপা হলে যে ভয়ংকর আহ্লাদটা হবার কথা, সে আহ্লাদ খুঁজে পায় না।’- উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আহ্লাদিত হতে না পারার কারণ কী?
উত্তর: গল্প ছাপা হলে যে ভয়ংকর আহ্লাদ হওয়ার কথা, তপন তা অনুভব করতে পারে না। গল্প প্রকাশিত হওয়া এবং তার প্রশংসা শোনা সত্ত্বেও, সে নিজেকে উল্লাসিত বা আনন্দিত মনে করতে পারে না। এর প্রধান কারণ হল, তার চারপাশের মানুষের আলোচনার মধ্যে তপনের নিজের কোনো অবদান বা সাফল্য অনুভূত হয় না। বরং, গল্পের ‘কারেকশন’ বা ত্রুটি নিয়ে নানা মন্তব্য এবং মেসোর অবদান তার আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। তপন মনে করে যে তার লেখার গুরুত্ব সেভাবে উপলব্ধি করা হয়নি, ফলে সে আহ্লাদিত হতে পারে না।
২.১.৫ “আমার অপরাধ হয়েছে।” কে, কী অপরাধ করেছিল?
উত্তর: সুবোধ ঘোষের বহুরূপী গল্পে শহরের সম্পন্ন ব্যক্তি জগদীশবাবু উক্ত কথাটি বলেছেন।
‘বহুরূপী’ গল্পে জগদীশবাবুর বাড়ির বারান্দার নিচে এক বিরাগী সন্ন্যাসী আসেন। জগদীশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দা থেকেই তাঁকে আসার আমন্ত্রণ জানান। তখন সন্ন্যাসী বলেন, “আপনি বোধ হয় এগারো লক্ষ টাকার সম্পত্তির অহংকারে নিজেকে ভগবানের চেয়েও বড়ো বলে মনে করেন।” এই তীব্র মন্তব্য শুনে জগদীশবাবু নিজের আচরণকে অপরাধ বলে মনে করেন। এতে বোঝা যায়, তিনি অহংকার করেন ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে আত্মজ্ঞান ও অনুতাপবোধও রয়েছে।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ “দেহ আজ্ঞা মোরে;” কে, কীজন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করেছেন?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ‘অভিষেক’ কাব্যাংশের প্রশ্নোদ্ধৃত অংশে ‘রাক্ষস-কুল-ভরসা’ ইন্দ্রজিৎ, পিতা রাবণের কাছে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন।
২.২.২ ‘আফ্রিকা’ কবিতায় দিনের অন্তিমকাল কীভাবে ঘোষিত হয়েছিল?
উত্তর: ‘আফ্রিকা’ কবিতায় দিনের অশুভ ধ্বনিতে অন্তিমকাল ঘোষিত হয়েছিল।
২.২.৩ ‘তুরিত গমনে আসি’ তুরিত গমনে এসে পদ্মা কী দেখতে পেয়েছিলেন?
উত্তর: ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতানুসারে, তুরিত গমনে এসে ভোরবেলা পদ্মা ও সখীসহ বাগানে বেড়ানোর সময় দেখেছিলেন সমুদ্রতীরে একটি ভেলা সেখানে দ্রুত পৌঁছে দেখেন ভেলায় অচৈতন্য অবস্তায় পাঁচ কন্যাকে দেখতে পেয়েছিলো।
২.২.৪ “আঁকড়ে ধরে সে-খড়কুটো” এখানে ‘খড়কুটো’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: পতনশীল মানুষ যেমন সামান্যতম বস্তুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। তেমনি কবিও খুব অল্প গান জানেন বলেই তা তাঁর কাছে সামান্য বস্তু, যেটির মাধ্যমে তিনি অস্ত্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চান।
২.২.৫ ‘অসুখী একজন’ কবিতায় শিশু ও বাড়ির খুন হয়ে যাওয়া কোন্ প্রতীকী তাৎপর্যে প্রযুক্ত হয়েছে?
উত্তর: শিশুরা হলো পরবর্তী প্রজন্ম, স্বদেশের সম্পদ ও নিষ্পাপ মানবতার প্রতীক। অপরদিকে, বাড়ি শুধু একটি গৃহ নয়, বরং পরিবার, আশ্রয় ও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার প্রতীক।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘আগেকার দিনে গ্রামে কেউ দু-একটা পাশ দিতে পারলে’ বয়স্করা কী আশীর্বাদ করতেন?
উত্তর: হারিয়ে যাওয়া কালি কলম ‘ রচনা অনুসারে ‘আগেকার দিনে গ্রামে কেউ দু-একটা পাশ দিতে পারলে’ বয়স্করা আশীর্বাদ করে বলতেন , বেঁচে থাকো বাছা তোমার সোনার দোয়াত – কলম হোক ।
২.৩.২ “আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন” শব্দের ‘ত্রিবিধ কথা’ কী?
উত্তর: আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন” শব্দের ‘ত্রিবিধ কথা হলো অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা ।
২.৩.৩ ‘এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়।’ কোন্ ধারণার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: অনেকের মতে বিজ্ঞান আলোচনায় পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে সাধারণ শব্দ ব্যবহার করলে রচনা সহজ ও বোধগম্য হয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়।
২.৩.৪ “… তাতে লিখে আমার সুখ নেই।” কীরকম কলমে লিখে প্রাবন্ধিকের সুখ নেই?
উত্তর: “অফিসে কলম নিয়ে যেতে ভুলে গেলে, সহকর্মীদের কাছ থেকে একটি কলম পেলেও, সেটির শুকনো কালি ও ভোতা মুখের কারণে বক্তা স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন না। ফলে এমন কলমে লিখে তাঁর তৃপ্তি হয় না।” বক্তা তখন বলেন “তাতে লিখে আমার সুখ নেই”।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ করণে বীপ্সার সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।
উত্তর: সংজ্ঞা: বীপ্সা কথার অর্থ হল পুনরুক্তি বা পৌনঃপুনিকতা । একই কথাকে বার বার বললে তাকে বীপ্সা বলে। বাক্যের করণ কারকটি যদি পর পর দু বার ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে করণের বীপ্সা বলা হয়।
উদাহরণ: মেঘে মেঘে আকাশ ভরে গেছে।
২.৪.২ ঘাস জন্মালো রাস্তায় নিম্নরেখ শব্দটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
উত্তর: কর্তৃকারক —শূন্য বিভক্তি
২.৪.৩ উদাহরণসহ উপমান কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা লেখো।
উত্তর: সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।
উদাহরণ: তুষারের মতো শুভ্র = তুষারশুভ্র
২.৪.৪ ‘আপনারা সপরিবারে আসবেন।’ রেখাঙ্ক্ষিত পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: ব্যাসবাক্য: পরিবারসহ
সমাসের নাম: অব্যয়তৎপুরুষ সমাস
২.৪.৫ অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের সংজ্ঞার্থ লেখো।
উত্তর: অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের সংজ্ঞার্থ:
যে বাক্যের মাধ্যমে কারো প্রতি অনুমতি, নির্দেশ বা উপদেশ প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে।
২.৪.৬ জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরের দুটি নিয়ম লেখো।
উত্তর: জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরের দুটি প্রধান নিয়ম:
১. জটিল বাক্যের অধীনস্থ ধারাকে একটি স্বাধীন ধারায় রূপান্তর করতে হয়, যেটি সাধারণত অনুবর্তী সংযোজক (যেমন: যেহেতু, যদিও, যদি, যখন) ব্যবহার করে গঠিত হয়।
২. এই স্বাধীন ধারাটি সমন্বয়কারী যোজক (যেমন: এবং, কিন্তু, অথবা, তাই) ব্যবহার করে মূল ধারার সাথে যুক্ত করা হয়, ফলে একটি যৌগিক বাক্য গঠিত হয়।
২.৪.৭ “এমন কথা মুখে আনতে নেই।” কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন করো।
উত্তর: কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত বাক্য:
“এমন কথা কেউ মুখে আনে না।”
২.৪.৮ দ্বিগু সমাসের সঙ্গে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণসহ পার্থক্য লেখো।
উত্তর: দ্বিগু সমাস:
যে সমাসে পূর্বপদে সংখ্যা থাকে এবং সমাসবদ্ধ শব্দটি নিজেই সেই সংখ্যার বিশেষ্য হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে।
উদাহরণ: পঞ্চপাণ্ডব (পাঁচজন পাণ্ডব)।
সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস:
যে সমাসে পূর্বপদে সংখ্যা থাকে এবং সমাসবদ্ধ পদ অন্য কাউকে বোঝায়, তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে।
উদাহরণ: চতুরানন (চার মুখবিশিষ্ট ব্যক্তি – ব্রহ্মা)।
২.৪.৯ কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের অন্তত একটি পদ্ধতি উল্লেখ করো।
উত্তর: কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি হলো:
কর্তাকে “দ্বারা” যোগে কারক রূপে প্রকাশ করা এবং কর্মকে কর্তা রূপে স্থাপন করা।
উদাহরণ: কর্তৃবাচ্য: রবি বইটি পড়ে।
কর্মবাচ্য: বইটি রবির দ্বারা পড়া হয়।
এই পদ্ধতিতে কর্ম (বইটি) কে কর্তা করা হয় এবং মূল কর্তা (রবি) কে “দ্বারা” যোগে যুক্ত করে বাক্য রূপান্তর করা হয়।
২.৪.১০ নৌকা পার হতে পারলে তবে বিপদ থেকে মুক্তি। (বাক্যটিকে নঞর্থক বাক্যে পরিণত করো।
উত্তর: নঞর্থক বাক্য:
নৌকা পার হতে না পারলে তবে বিপদ থেকে মুক্তি নেই।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ “পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?”-কোন্ ঘটনাটিকে ‘অলৌকিক’ বলা হয়েছে? কেন সেই ঘটনা অলৌকিক?’
উত্তর: ছোটোমাসি আর মেসো একদিন বেড়াতে এলেন, সঙ্গে আনলেন একটি ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকা।
বুকের রক্ত যেন ছলকে উঠল তপনের।
তপন মনে করল, আজই বুঝি তার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন।
কিন্তু সত্যিই কি তা সম্ভব?
ছাপার অক্ষরে তপন কুমার রায়ের লেখা গল্প, যা হাজার-হাজার ছেলের হাতে হাতে ঘুরবে—
এই ঘটনাকে যেন পৃথিবীর এক অলৌকিক ঘটনা বলেছে।
৩.১.২ “নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে।” কে বুঝতে পেরেছে? নদীর বিদ্রোহ বলতে সে কী বোঝাতে চেয়েছে?
উত্তর:নদেরচাঁদের বুঝতে পেরেছিলো , শুকনো নদী পাঁচ দিনের বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। উন্মত্ত নদীর তীব্র স্রোতযুক্ত জলধারা দেখে নদেরচাঁদ নদীর বিদ্রোহের কারণ বুঝতে পারল।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “সব চূর্ণ হয়ে গেল, জ্বলে গেল আগুনে।” কোন্ কোন্ জিনিসের কথা বলা হয়েছে? এই পরিণতির কারণ কী?
উত্তর: যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড়ের মতো যুদ্ধ শুরু হয়।
এই যুদ্ধের ফলে শিশু ও বাড়িরা খুন হয়।
শান্ত হলুদ দেবতারা, যারা হাজার বছর ধরে ধ্যানে ডুবে ছিলেন,
তারা মন্দির থেকে উল্টে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যান।
সেই মিষ্টি বাড়ি, সেই বারান্দা যেখানে কবি ঝুলন্ত বিছানায় ঘুমাতেন,
গোলাপি গাছ, ছড়ানো করতলের মতো পাতা, চিমনি, প্রাচীন জলতরঙ্গ—
সবকিছু চূর্ণ হয়ে গেল, জ্বলে গেল আগুনে।
৩.২.২ “জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া; কাকে ‘মহাবাহু’ বলা হয়েছে? তার বিস্ময়ের কারণ কী?
উত্তর: ‘মহাবাহু’ বলা হয়েছে রাবণপুত্র বীর মেঘনাদ ওরফে ইন্দ্রজিৎকে। তিনি ধাত্রী মা প্রভাষা রাক্ষসীর ছদ্মবেশে আসা রক্ষঃকুললক্ষ্মীর কাছ থেকে জানতে পারেন যে, রাঘবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র তাঁর প্রিয় ভ্রাতা বীরবাহুকে হত্যা করেছেন। এ সংবাদে শোকাহত ও ক্রুদ্ধ রাজা রাবণ নিজেই সৈন্যসহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ বিস্মিত হন, কারণ তাঁর স্মরণে আছে তিনি নিশারণে রাঘবদের পরাজিত করে খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তাই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, নিহত রামচন্দ্র কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে বীরবাহুকে হত্যা করতে পারে—এই আশ্চর্য ঘটনাই ‘মহাবাহু’ ইন্দ্রজিতের বিস্ময়ের কারণ।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ ‘লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল।’ লোকটি কে? তার চেহারা, পোশাক, আসবাব ও জিনিসপত্রের যে পরিচয় পেয়েছ, পাঠ্যাংশ অনুসরণে লেখো।
উত্তর: লোকটি হল ‘পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট’ গিরীশ মহাপাত্র।
তার চেহারা, পোশাক, আসবাব ও জিনিসপত্রের যে পরিচয় : লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। অত্যন্ত ফরসা রং রৌদ্রে পুড়িয়া যেন তামাটে হইয়াছে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু ভারী রোগা। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। সহসা আশঙ্কা হয়, সংসারের মিয়াদ বোধ হয় বেশি দিন নাই। ভিতরের কী একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোটো কি বড়ো, টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন।অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মতো কী যে তাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহারই কোন অতল তলে তার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করতে সাহস করে না। কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচে আছে।
৪.২ “হাঁড়িতে অনেক সময় শুধু জল ফোটে, ভাত ফোটে না।”- এখানে কার কথা বলা হয়েছে? একথা বলার কারণ কী?
উত্তর: এখানে ‘বহুরূপী’ গল্পে হরিদার কথা বলা হয়েছে।
হাঁড়িতে অনেক সময় শুধু জল ফোটে, ভাত ফোটে না– একথা বলার কারণ–
‘বহুরূপী’ গল্পে হরিদা একদিন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। তাঁর বেশভূষা, আচরণ ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে জগদীশবাবু তাঁকে সত্যিকারের সন্ন্যাসী ভেবে সম্মান জানাতে চান এবং বিদায়ের সময় একশো টাকার প্রণামী দিতে চান। কিন্তু সন্ন্যাসীর রূপে হরিদা সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেন।
তিনি উদাসীন ভঙ্গিতে বলেন — “আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মাড়িয়ে চলে যেতে পারি, তেমনিই অনায়াসে সোনাও মাড়িয়ে চলে যেতে পারি।” অর্থাৎ, তিনি নিজ চরিত্রে এতটাই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে, টাকা নিলে তাঁর সন্ন্যাসীর চরিত্রের পরিপন্থী হত বলে তা গ্রহণ করেননি।
কারণ হরিদা অভাবী হয়েও নিজের আদর্শের কারণে ভাগ্যের দেওয়া সুযোগ ফিরিয়ে দিয়েছেন।
তাঁর এই সততা ও আদর্শবোধ নিশ্চিত করে দেয় যে ভবিষ্যতেও তাঁর অভাব মোচন হবে না- তাঁর হাঁড়িতে মাঝে মাঝে শুধু জল ফুটবে, কিন্তু চাল থাকবে না।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ ‘কন্যারে ফেলিল যথা’ কন্যার পরিচয় দাও। সে সর্বক্ষণ কোথায় অবস্থান করে?
উত্তর: ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতার ‘কন্যা’ হচ্ছেন রাণা রত্নসেনের প্রিয়া, রূপসী পদ্মাবতী। তিনি একজন রাজকুমারী এবং এই কবিতায় তাঁকে প্রেমিকা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যিনি তাঁর স্বামীর বা প্রেমিকের জন্য গভীরভাবে অপেক্ষমাণ। সৈয়দ আলাওল ‘পদ্মাবতী’ কাব্য অনুবাদের মাধ্যমে এই চরিত্রকে প্রেম, বিরহ ও নারীসত্তার প্রতীক করে তুলেছেন।
এই কন্যা সর্বক্ষণ সিন্ধুতীরে অবস্থান করে। এখানে ‘সিন্ধু’ বলতে বোঝানো হয়েছে সমুদ্র বা নদীর তীর, যা রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে—প্রেমিকের প্রতীক্ষাস্থল হিসেবে। পদ্মাবতী সেই স্থানেই বসে আছেন, প্রিয়জনের আগমনের আশায়। তাঁর অবস্থান কেবল শারীরিক নয়, মানসিক দিক থেকেও প্রতীক্ষায় পূর্ণ। তাঁর চোখ বারবার সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে, তিনি দিনরাত বিরহে কাতর হয়ে সেখানে অবস্থান করেন।
এইভাবে, কন্যা পদ্মাবতী হচ্ছে প্রেম ও অপেক্ষার প্রতীক, যিনি প্রেমিকের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকেন সেই ‘সিন্ধুতীরে’।
৫.২ ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় একদিকে ধ্বংসের চিত্র অন্যদিকে নতুন আশার বাণী কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা কবিতা অবলম্বনে লেখো।
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় ধ্বংস ও সৃষ্টির এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। কবি এখানে প্রলয়ঙ্কর রূপে ধ্বংসের মাধ্যমে একটি নতুন সমাজের সূচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।
কবিতায় কবি বলেন:
“ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? – প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!”
এই পঙ্ক্তিতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ধ্বংস আসলে নতুন সৃষ্টির বেদনা। পুরাতন, জীর্ণ, অন্যায় সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন, সুন্দর, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলাই প্রলয়ের উদ্দেশ্য।
আরও একটি পঙ্ক্তিতে কবি বলেন:
“ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!”
এখানে ‘চির-সুন্দর’ বলতে কবি সেই প্রলয়ঙ্কর শক্তিকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা ধ্বংসের মাধ্যমে নতুন সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে।
এইভাবে, ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় ধ্বংসের চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আশার বাণীও ফুটে উঠেছে। কবি বিশ্বাস করেন, ধ্বংসের মধ্য দিয়েই নতুন সমাজের জন্ম হয়, এবং সেই সমাজ হবে শোষণমুক্ত ও সাম্যবাদী।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ কালি কলমের প্রতি ভালোবাসা ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করো।
উত্তর: শ্রীপান্থের ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে লেখকের কালি কলমের প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। লেখক গ্রামবাংলার ছেলে, যার শৈশব কেটেছে বাঁশের কঞ্চি কেটে কলম বানিয়ে, মাটির দোয়াতে ঘরে তৈরি কালি দিয়ে কলাপাতায় লিখে। লেখার প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা ও কল্পনা এতটাই প্রগাঢ় ছিল যে, তিনি ভাবতেন—যদি যিশুর আগে প্রাচীন মিশরে জন্মাতেন, তবে নীলনদের তীর থেকে নলখাগড়া এনে কলম বানাতেন কিংবা হাড় কুড়িয়ে তৈরি করতেন লেখার উপকরণ। জীবনের প্রথম ফাউন্টেন পেন, একটি সস্তা জাপানি পাইলট পেন, তাঁর কাছে ছিল এক ‘জাদু কলম’। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একসময় এই কালি কলম হারিয়ে যেতে থাকে এবং কম্পিউটার তার জায়গা দখল করে। এইভাবেই প্রবন্ধটিতে লেখকের কালি কলমের প্রতি সুগভীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়।
৬.২ “তাতে পাঠকের অসুবিধা হয়” কীসে পাঠকের অসুবিধা হয়? অসুবিধা দূর করার জন্য কী কী করা দরকার?
উত্তর: রাজশেখর বসু তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, বারবার কোনো বিষয়ে বর্ণনা দিতে গেলে অকারণে কথার পুনরাবৃত্তি ঘটে, যা পাঠকের অসুবিধা সৃষ্টি করে।
এই অসুবিধা দূর করার উপায় হল—
1. পরিভাষার ব্যবহার: পরিভাষা ভাষাকে সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট করে। এগুলি বাদ দিলে ভাষা সবসময় সুন্দর হয় না এবং বর্ণনা অতিরিক্ত বড়ো হয়ে যায়।
2. পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা: অল্পশিক্ষিত বা বিজ্ঞান না-পড়া পাঠকের জন্য প্রথমবার ব্যবহারের সময় পারিভাষার ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। পরবর্তীতে শুধু শব্দটি দিলেই যথেষ্ট।
3. সরল ও স্পষ্ট ভাষা: বিজ্ঞান রচনার ভাষা অলংকারহীন, সরল ও স্পষ্ট হওয়া উচিত।
4. সঠিক তথ্য: প্রবন্ধে ভুল তথ্য থাকা চলবে না, কারণ তা পাঠকের কাছে বিভ্রান্তিকর হতে পারে। তাই লেখকদের সতর্ক থাকা জরুরি।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “দরবার ত্যাগ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি জাঁহাপনা।” বস্তা কে? তাঁরা কেন দরবার ত্যাগ করতে চান?
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশে “দরবার ত্যাগ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি জাঁহপনা” বস্তা হলেন মীরজাফর।
ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্ররোচনায় সিরাজের সভাসদদের একাংশ রাজদ্রোহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। সেই দলে লিপ্ত ছিলেন মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগতশেঠ প্রমুখ। আলোচ্য অংশে ‘আমরা’ বলতে এই সভাসদদের কথা বোঝানো হয়েছে। তারা নবাবের দরবার ত্যাগ করতে চেয়েছেন।
নবাব-বিরোধী সভাসদদের প্রধান মন্ত্রনাদাতা ছিলেন জনৈক ইংরেজ কর্মচারি ওয়াটস। এই ওয়াটস ছিল নবাবের দরবারে নিযুক্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন প্রতিনিধি। রাজদ্রোহে লিপ্ত থাকার অপরাধে সিরাজ তাকে দরবার থেকে বিতাড়িত করেন। রাজা রাজবল্লভ এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে নবাব রাজদ্রোহী সভাসদদের সতর্ক করে বলেন সকলের সব কুকীর্তির খবর তিনি রাখেন। এই প্রসঙ্গে নবাব-অনুগামী মীরমদন এবং মোহনলাল নবাবের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথাটি জানায়। তারা বলেন, “আমরা নবাবের নিমক বৃথাই খাই না”।
তাদের কথায় নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর অপমানিত বোধ করেন। সেই কারণে তিনি স্বপক্ষীয় সভাসদদের সঙ্গে দরবার ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন।
৭.২ “এই প্রতিহিংসা আমার পূর্ণ হবে সেইদিন-“- বস্তা কে? বক্তার প্রতিহিংসার পরিচয় দাও।
উত্তর: এই প্রতিহিংসা আমার পূর্ণ হবে সেইদিন উক্তিটি বলেছেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।
এই উক্তিটি নাটকের সেই মুহূর্তে বলা হয়েছে, যখন সিরাজউদ্দৌলা উপলব্ধি করেন যে তাঁর বিশ্বাসভাজন সেনাপতিরা, বিশেষ করে মীরজাফর, ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তিনি মনে করেন, এই বিশ্বাসঘাতকতা শুধু তাঁর নয়, বরং বাংলার স্বাধীনতার ওপর আঘাত। এই প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, সেদিনই তাঁর প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ হবে যেদিন এই সব কুচক্রী ও বিশ্বাসঘাতকদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাবে।
প্রতিহিংসার পরিচয়:
সিরাজউদ্দৌলার প্রতিহিংসা ছিল ব্যক্তিগত নয়, বরং তা ছিল স্বদেশ ও স্বাধীনতার পক্ষে এক ন্যায়সংগত প্রতিক্রিয়া। তিনি দেশের স্বার্থে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি এবং ঘরের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিহিংসা ছিল দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ এবং শোষণ-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক। এই উক্তির মাধ্যমে সিরাজউদ্দৌলার দৃঢ়চেতা, সাহসী, আত্মমর্যাদাপূর্ণ ও সংগ্রামী মনোভাব প্রকাশ পায়।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ “জীবনসংগ্রামের অপর নাম কোনি” চরিত্র বিশ্লেষণপূর্বক, উক্তিটির যথার্থতা আলোচনা করো।
উত্তর: “কোনি” উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কোনি। সে এক দরিদ্র পরিবার থেকে আসে এবং তার জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। কোনি যে যাত্রা শুরু করেছিল, তার সংগ্রাম ছিল শুধুমাত্র নিজেকে প্রমাণ করার, দেশের বড় মঞ্চে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার এবং তার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার।
কোনির জীবনসংগ্রাম শুরু হয় যখন তার প্রশিক্ষক খিদ্দা তাকে খুঁজে বের করেন। কোনির মধ্যে যে বিশেষ প্রতিভা ছিল তা তিনি দ্রুত বুঝতে পারেন। খিদ্দা কোনির প্রতি এক অদ্ভুত বিশ্বাস ও আশা রাখেন। তিনি কোনিকে তাঁর কঠোর প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন, যদিও কোনির পরিবারে অর্থের সংকট ছিল। কোনির প্রয়োজনীয় পোশাক, খাবার, জীবনের প্রাথমিক সুবিধা ছিল না, কিন্তু খিদ্দা তাকে সাহস জোগান। খিদ্দা জানতেন, কোনি দারিদ্র্যকে অতিক্রম করতে পারলে তার কাছে সাফল্য অটুট থাকবে।
কোনির সংগ্রাম শুধু প্রশিক্ষণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, সে প্রচণ্ড অবহেলা, তাচ্ছিল্য এবং অসম্মানও সহ্য করেছে। ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা তার দরিদ্রতা এবং অবস্থা নিয়ে হাস্যরস করত, তবে কোনি এগুলোর প্রতিবাদ করতে না পারলেও, সে কখনও হাল ছাড়েনি। জাতীয় দলে নির্বাচিত হলেও প্রতিযোগিতায় অপ্রত্যাশিত কারণে বাদ পড়ে, তাও তাকে ভেঙে দেয়নি। তার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল, “লড়তে লড়তে শিখে যাবি”, যা তাকে সব বাধা অতিক্রম করার জন্য প্রেরণা জোগাত।
তবে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও হতাশা কাটিয়ে কোনি একদিন বড় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং তার দক্ষতা প্রমাণ করে। খিদ্দার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল অপরিসীম, এবং খিদ্দা নিজের পিতৃতুল্য হয়ে কোনিকে প্রতিটি পদক্ষেপে সমর্থন করেছেন।
উক্তির যথার্থতা:
“জীবনসংগ্রামের অপর নাম কোনি” — এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে সঠিক, কারণ কোনির জীবন ছিল এক বিশাল সংগ্রামের প্রতিফলন। সে সব সময়ই সঠিক পথ অনুসরণ করেছে এবং নিজের পরিশ্রম, সাহস ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করেছে। কোনির সংগ্রাম শুধু একটি খেলার প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি ছিল তার আত্মবিশ্বাস, লক্ষ্য এবং জীবনের প্রতি তার অপরিসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ফলস্বরূপ। তার জীবনের সমস্ত পদক্ষেপ ছিল সংগ্রাম, তার হতাশা কাটানো এবং নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতীক।
“জীবনসংগ্রামের অপর নাম কোনি” এই উক্তি যে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি পুরো একটি জীবনধারা এবং সংগ্রামের ধারক। এই উক্তি দ্বারা কোনির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, কারণ তার সংগ্রাম এক নতুন অর্থ নিয়ে উঠে আসে।
৮.২ “জুপিটারে আর সে যায় না।” ‘সে’ কে? তার জুপিটারে না যাওয়ার কারণ বিবৃত করো।
উত্তর: “জুপিটারে আর সে যায় না”—এই বাক্যে ‘সে’ বলতে বোঝানো হয়েছে কোনিকে, যে মতি নন্দী রচিত ‘কোনি’ গল্পের প্রধান চরিত্র। কোনি একজন দরিদ্র ঘরের মেয়ে, যাকে তার কোচ খিদ্দা কৃত্রিম সুইমিং পুল ‘জুপিটার’-এ সাঁতারের প্রশিক্ষণ দিতেন।
কিন্তু কিছুদিন পর থেকে কোনি আর জুপিটারে যেতে পারত না, কারণ তার দাদা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারে উপার্জনের একমাত্র উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে পৌঁছায়। এমন সংকটে পড়ে কোনিকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়—সে একটি কারখানায় চাকরি করে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য হয়। ফলে নিয়মিত সাঁতার প্রশিক্ষণে যাওয়ার সুযোগ তার আর থাকে না।
এই পরিস্থিতিতে জুপিটারে যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। এটি শুধু একটি জায়গায় না যাওয়ার ঘটনা নয়—এর মাধ্যমে লেখক গরিব অথচ প্রতিভাবান মানুষদের জীবনে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কষ্ট ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন।
৮.৩ “চার বছরের মধ্যেই ‘প্রজাপতি’ ডানা মেলে দিয়েছে।” ‘প্রজাপতি’ কী? কার তত্ত্বাবধানে, কীভাবে ‘প্রজাপতি’ ডানা মেলে দিয়েছে?
উত্তর: উক্তি “চার বছরের মধ্যেই ‘প্রজাপতি’ ডানা মেলে দিয়েছে” মতি নন্দীর ‘কোনি’ গল্পে ব্যবহৃত একটি রূপক। এখানে ‘প্রজাপতি’ বলতে বোঝানো হয়েছে কোনিকে—একটি সাধারণ, দরিদ্র পরিবারের মেয়ে, যে কোচ খিদ্দার প্রশিক্ষণ ও নিজের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে একজন জাতীয় মানের সাঁতারুতে পরিণত করেছে।
খিদ্দার তত্ত্বাবধানে কোনি শুধুমাত্র সাঁতারের কৌশল শিখে ওঠেনি, বরং মানসিকভাবে দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী ও লড়াকু হয়ে উঠেছে। খিদ্দা তাকে ‘Fight, Koni, Fight’—এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাণিত করে তিলে তিলে গড়ে তোলেন। চার বছরের কঠোর অনুশীলন, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের ফলে কোনি নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়।
এই রূপক ‘প্রজাপতি’ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, যেমন করে একটি সাধারণ শুঁয়োপোকা রঙিন ও উড়ন্ত প্রজাপতিতে পরিণত হয়, তেমনই কোনি অভাবের অন্ধকার থেকে উঠে এসে সাফল্যের আকাশে উড়ে বেড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করে। এটি শুধুই ক্রীড়া জয় নয়, একটি মানবিক ও সামাজিক বিজয়ের প্রতীক।
৯। চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো:
Man is the maker of his fortune. We cannot prosper in our life if we are afraid of labour. Some people think that success in life depends on luck or chance. Nothing can be further from truth. Hard labour is needed success in every walk of life.
উত্তর: মানুষ তার নিজের ভাগ্যের স্রষ্টা। যদি আমরা পরিশ্রম করতে ভয় পাই, তবে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারব না। কিছু মানুষ মনে করেন যে জীবনে সাফল্য কাকতালীয় বা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। এর চেয়ে ভুল কিছু হতে পারে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
মানিক: হায়, আজকাল বাজারের দাম তো খুবই বেড়ে গেছে! সবকিছুই যেন আগের থেকে অনেক বেশি দামি হয়ে গেছে।
বকুল: হ্যাঁ, আমি নিজেও সেটা অনুভব করছি। একে তো রোজকার খরচ বেড়েছে, তাতে আবার সব কিছুই প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।
মানিক: সঠিক বলেছো। চাল, ডাল, তেল—সবই এখন আকাশ ছুঁইছুঁই। আগে যা কিছু কিনতাম, এখন সেটাও কিনতে খুব কষ্ট হয়।
বকুল: হ্যাঁ, আর সবজির দাম তো অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। আগে একটাকা দিয়ে এক মুঠো শাক কিনতাম, এখন সেটাও পাঁচটাকা হয়ে গেছে।
মনিক: এটা সত্যি, কিন্তু কি করা যাবে? সরকারের উচিত বিষয়টা নিয়ে কিছু পদক্ষেপ নেয়া।
বকুল: অবশ্যই, সরকারের উচিত এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে সাধারণ মানুষের জীবনে আরও চাপ না আসে।
১০.২ কোনো গ্রামীণ এলাকায় একটি সরকারি হাসপাতাল উদ্বোধন হল এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
দার্জিলিংয়ে গ্রামীণ হাসপাতালে নতুন দিগন্ত
লীলাবতী সানি, দার্জিলিং, ২২ মে: দার্জিলিং জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে সম্প্রতি একটি সরকারি হাসপাতালের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল, সকাল ১১টায় ‘স্টারডাস্ট রেস্টুরেন্ট’-এর পাশে নবনির্মিত এই হাসপাতালের ফিতে কাটেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক, পঞ্চায়েত সদস্য ও স্থানীয় মানুষজন।
এই হাসপাতালটিতে ৩০টি শয্যা, একটি ছোট অপারেশন থিয়েটার, শিশু ও মাতৃসেবা কেন্দ্র এবং ২৪ ঘণ্টার এমার্জেন্সি পরিষেবা চালু হয়েছে। এতে স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের চিকিৎসা সমস্যার অবসান ঘটবে।
মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, “স্বাস্থ্যই সম্পদ। এই হাসপাতাল গ্রামের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।” এলাকার মানুষ খুব খুশি এবং কৃতজ্ঞ। তাঁরা আশা করছেন, এই হাসপাতাল তাঁদের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করবে।
১১। যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লেখো: (কমবেশি ৪০০ শব্দে)
১১.১ প্রাকৃতিক বিপর্যয়: সমস্যা ও প্রতিকার।
উত্তর:
প্রাকৃতিক বিপর্যয়: সমস্যা ও প্রতিকার
ভূমিকা:
মানবজীবন প্রকৃতির ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃতি মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে যা আমাদের জীবনে দুর্যোগ ডেকে আনে। এ ধরনের ভয়ংকর পরিস্থিতিকেই বলা হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধস ইত্যাদি সবই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হঠাৎ করে ঘটে এবং মানুষকে চরম ভোগান্তিতে ফেলে।
বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়:
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নানা রকম রূপ রয়েছে।
ভূমিকম্প: মাটির নিচে টেকটনিক প্লেট সরে গেলে ভূমিকম্প হয়। এতে ভবন ধসে পড়ে, প্রাণহানি ঘটে।
ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে, ফসল ও গবাদিপশুর ক্ষতি হয়।
বন্যা: অতিবৃষ্টির কারণে নদীর জল উপচে পড়ে বন্যা হয়। এতে চাষাবাদ নষ্ট হয় ও পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে।
খরা: দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে খরা দেখা দেয়। এতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় ও খাদ্য সংকট দেখা দেয়।
ভূমিধস: বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় ভূমির উপরিভাগ ধসে পড়ে ভূমিধস হয়। এতে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে।
সমস্যাসমূহ:
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানুষের জান-মালের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। অনেকে গৃহহীন হয়ে পড়ে, ফসলের ক্ষতি হয়, খাদ্য ও পানির অভাব দেখা দেয়। তাছাড়া এসব দুর্যোগের পর নানান রোগবালাই ছড়িয়ে পড়ে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, অর্থনৈতিক ক্ষতিও হয় বিপুল পরিমাণে।
প্রতিকার ও করণীয়:
প্রাকৃতিক বিপর্যয় পুরোপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও প্রস্তুতি ও সচেতনতা বাড়িয়ে এর ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।
- দুর্যোগ পূর্বাভাস ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে।
- দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে।
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় টেকসই ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে হবে।
- সচেতনতা বাড়ানোর জন্য স্কুল-কলেজে নিয়মিত মহড়া ও শিক্ষা দিতে হবে।
- সরকার ও বেসরকারি সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকতে হবে।
উপসংহার:
প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানব সভ্যতার জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। তবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সচেতনতাকে কাজে লাগিয়ে এই বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আমাদের সকলের দায়িত্ব — পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকা। সচেতনতাই পারে বড় বিপদকে রুখে দিতে।
১১.২ ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ।
উত্তর:
ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ
ভূমিকা:
শিক্ষা শুধু বইপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা। এ কারণেই বলা হয় — “ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ”। ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ নানা জাতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল ও জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করে। তাই পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি ভ্রমণও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ।
ভ্রমণের গুরুত্ব:
ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বইয়ে পড়া বিষয়গুলো চোখে দেখে উপলব্ধি করতে পারে। যেমন, ইতিহাসের কোন রাজপ্রাসাদ বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বইয়ে পড়ে যতটা বোঝা যায়, বাস্তবে দেখলে তা আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভ্রমণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে, মনকে উদার করে, এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। এটি ক্লান্ত মনকে সতেজ করে তোলে এবং পড়াশোনার প্রতি নতুন আগ্রহ তৈরি করে।
ভ্রমণ ও শিক্ষা:
ভ্রমণের সময় মানুষ বিভিন্ন স্থান, পরিবেশ, জলবায়ু, জীবনধারা, পোশাক, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়। এটি ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বাস্তব শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহনশীলতা, দলবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতা ও আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাসফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শিক্ষাসফরের আয়োজন করা উচিত। ভ্রমণের সময় নিরাপত্তা, সঠিক নির্দেশনা ও শিক্ষকদের তত্ত্বাবধান থাকা আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন লেখার সুযোগ দিলে লেখার দক্ষতাও বাড়বে।
উপসংহার:
ভ্রমণ সত্যিই শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটি শুধু মনের খোরাক দেয় না, জীবনের নানা দিক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে। তাই বইয়ের পঠনের পাশাপাশি ভ্রমণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা একজন শিক্ষার্থীর জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
১১.৩ তোমার প্রিয় খেলা।
উত্তর:
তোমার প্রিয় খেলা
আমার প্রিয় খেলা হল ক্রিকেট। ক্রিকেট একটি জনপ্রিয় এবং উত্তেজনাপূর্ণ খেলা যা সারা বিশ্বে খেলা হয়। আমি ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট খেলা এবং দেখার প্রতি একটি গভীর ভালোবাসা অনুভব করি। আমার জন্য ক্রিকেট শুধু একটি খেলা নয়, এটি একটি আবেগ, একটি নেশা। বিশেষ করে দেশের জাতীয় দল যখন আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলে, তখন আমি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খেলা উপভোগ করি।
ক্রিকেটের প্রতি আমার ভালোবাসা শুরু হয়েছিলো যখন আমি প্রথমবার আমার বন্ধুদের সাথে মাঠে খেলতে যাই। তখনই আমি বুঝতে পারি, ক্রিকেট একটি এমন খেলা যেখানে শারীরিক কসরত, মানসিক প্রস্তুতি, দলগত কর্ম এবং কৌশল সবকিছু একত্রে প্রয়োজন। এটি খেলোয়াড়দের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা এবং মেধার পরিচয় দেয়। আমি সাধারণত ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলি, তবে বোলিংও মাঝে মাঝে করি।
খেলার মধ্যে যে আনন্দ এবং উত্তেজনা আছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। বিশেষ করে যখন আমি কোনো বড় টুর্নামেন্টে আমার দলের সঙ্গে অংশগ্রহণ করি, তখন সেই মুহূর্তগুলো সত্যিই অসাধারণ হয়। খেলার মধ্যে প্রতিটি রান, উইকেট, ক্যাচ, এবং ম্যাচের শেষ মুহূর্তগুলো অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হয়। আমি মনে করি, ক্রিকেট কেবল একটি খেলা নয়, এটি একটি জীবনধারা। এটি বন্ধুত্ব, কৌশল, এবং একত্রে কাজ করার এক অনন্য মাধ্যম।
আমি ক্রিকেটের মাধ্যমে শিখেছি কীভাবে একটি দলের অংশ হয়ে কাজ করতে হয়। দলগতভাবে একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য একে অপরের সাথে সহযোগিতা এবং সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, খেলার মধ্যে যে শ্রদ্ধা এবং আদর্শিক মূল্য রয়েছে, তা আমাকে জীবনেও অনেক কিছু শিখিয়েছে। শৃঙ্খলা, সময়ের প্রতি সচেতনতা, পরিশ্রম, এবং প্রতিটি মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা আমার ব্যক্তিগত জীবনে কাজে এসেছে।
ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের জন্যই নয়, এটি দর্শকদের জন্যও বিশেষ একটি উৎসাহের বিষয়। বিশ্বকাপের সময়, স্টেডিয়ামে হাজার হাজার দর্শক খেলা দেখতে আসেন, এবং দেশজুড়ে মানুষ একসাথে এই খেলা উপভোগ করে। আমার কাছে, ক্রিকেট একটি অনুভূতি, যা আমাকে আনন্দ দেয় এবং জীবনের একটি বিশেষ অংশ হয়ে উঠেছে।
সর্বোপরি, ক্রিকেট আমার প্রিয় খেলা, যা আমাকে শিখিয়েছে পরিশ্রমের মাধ্যমে কিভাবে সফলতা অর্জন করতে হয়, এবং যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য শক্তি ও সাহস প্রয়োজন।
১১.৪ তোমার প্রিয় দেশনায়ক।
উত্তর:
তোমার প্রিয় দেশনায়ক
আমার প্রিয় দেশনায়ক হলেন সুভাস চন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক, অগ্নিস্বরূপ নেতা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। তাঁর ত্যাগ, সংগ্রাম এবং নেতৃত্বের কারণে তিনি আজও লাখো মানুষের হৃদয়ে বেঁচে আছেন। সুভাস চন্দ্র বসুর জীবনে ছিল অসীম সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যা তাকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে এক অনন্য স্থান দিয়েছে।
সুভাস চন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি, কটকে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সুভাস চন্দ্র বসু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে প্রথমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। তবে তার কার্যক্রমের মাঝে ছিলেন দেশের জন্য একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে শুধুমাত্র জনগণের ঐক্য ও সংগ্রামের মাধ্যমে, আর এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া তার দায়িত্ব।
তবে সুভাস চন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবনটি অনেকটা বৈপ্লবিক ছিল। তিনি গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের প্রতি সম্মান রেখেও, অধিকাংশ সময় যুদ্ধকালীন কৌশল এবং প্রয়োজনে বিপ্লবী পথ বেছে নিতেন। ১৯৪০ সালের মধ্যে, তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করার পথ অনুসরণ করতে শুরু করেন। তিনি ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে একটি নতুন গতি দেয়। “জয় হিন্দ” এবং “दिल्ली चलो” এই দুটি মন্ত্র তাঁর নেতৃত্বের শক্তি ছিল।
সুভাস চন্দ্র বসুর দৃঢ় মনোবল এবং অসীম দেশপ্রেম স্বাধীনতার জন্য তাঁর সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম জনগণের সংগ্রাম, আর এ সংগ্রামে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োজন। তিনি নিজের জীবনকে অর্পণ করে, দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই চালিয়ে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
তাঁর জীবন ও সংগ্রাম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, দেশপ্রেম, সাহস, দৃঢ়তা এবং সংগ্রামের মাধ্যমে কোনো জাতি তার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। সুভাস চন্দ্র বসু শুধুমাত্র একজন মহান নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয় জনগণের এক অমূল্য রত্ন, যিনি আজও আমাদের স্মরণে চিরকালীন ভাবে বেঁচে আছেন।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।