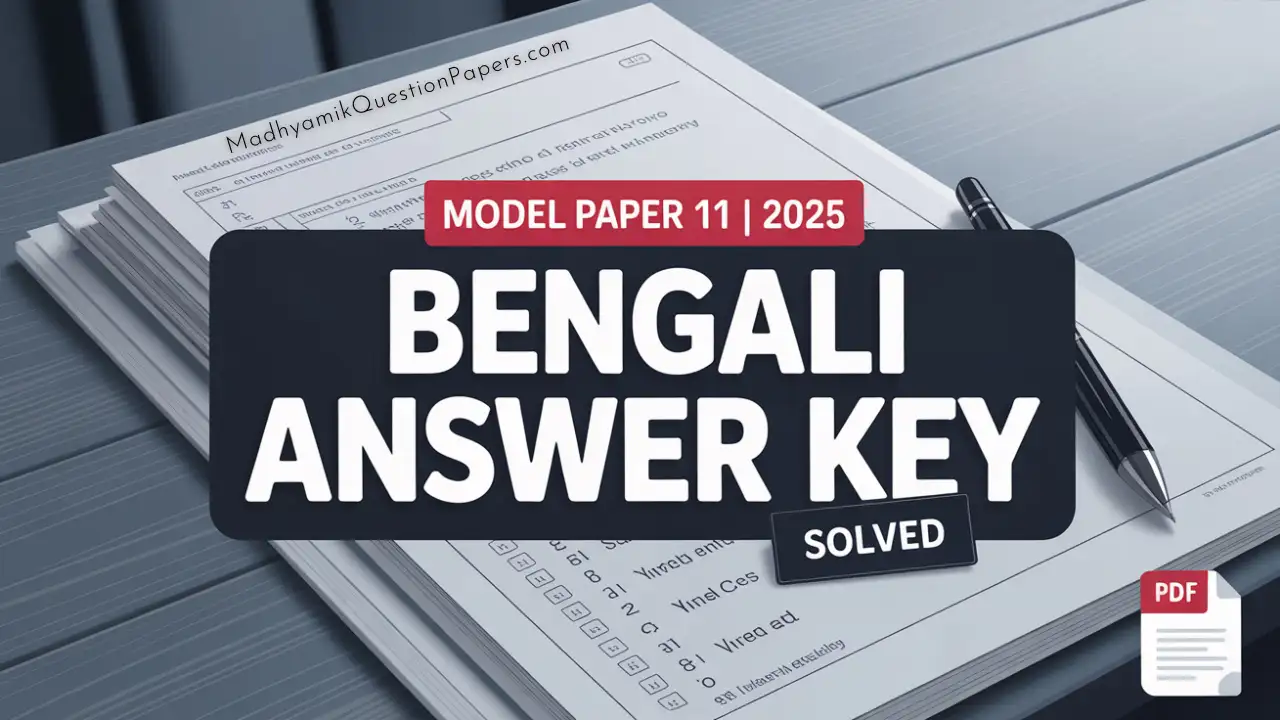আপনি কি ২০২৫ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 11 (2025) এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা Model Question Paper 11 (2025)-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com, ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৫ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ গিরীশ মহাপাত্রের চুলে মাখানো তেল থেকে যে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল
(ক) নারকেলের
(খ) জুঁইফুলের
(গ) জবা ফুলের
(ঘ) লেবুর
উত্তর: (ঘ) লেবুর
১.২ “ওসব হলো সুন্দর সুন্দর এক-একটি বঞ্চনা।” এখানে ‘ওসব’ হল ঘর,
(ক) ধন জন যৌবন
(খ) সংসারের মায়া
(গ) বাড়ি
(ঘ) টাকার থলি
উত্তর: (ক) ধন জন যৌবন
১.৩ গ্রাম-প্রধান ইসাবের নাম দিয়েছিল
(ক) অদল
(খ) বদল
(গ) প্রকৃত বন্ধু
(ঘ) কোনোটিই নয়
উত্তর: (খ) বদল
১.৪ পাবলো নেরুদার লেখা ‘অসুখী একজন’ কবিতাটি যে মূল কবিতার অনুবাদ, সেটি হল-
(ক) The Unhappy one’
(খ) ‘Extravagaria’
(গ) ‘Extravaganza’
(ঘ) ‘La Desdichada’
উত্তর: (ঘ) ‘La Desdichada’
১.৫ ‘ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায়’
(ক) নীল গগনে
(খ) নীল আকাশে
(গ) নীল খিলানে
(ঘ) নীল সাগরে।
উত্তর: (গ) নীল খিলানে
১.৬ ‘হৈমবতীসূত’ যাকে বধ করেছিলেন, তিনি হলেন
(ক) মহিষাসুর
(খ) তারকাসুর
(গ) বৃত্রাসুর
(ঘ) ভস্মাসুর
উত্তর: (খ) তারকাসুর
১.৭ নিজের হাতে কলমের আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল যে লেখকের, তার নাম
(ক) বনফুল
(খ) পরশুরাম
(গ) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
(ঘ) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
উত্তর: (গ) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
১.৮ শ্রীপান্থ প্রথম যে ফাউন্টেন পেনটি কিনেছিলেন তার নাম
(ক) জাপানি পাইলট
(খ) জাপানি পার্কার
(গ) জাপানি সোয়ান
(ঘ) জাপানি শেফার্ড
উত্তর: (ক) জাপানি পাইলট
১.৯ ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে উল্লিখিত নবাগত রাসায়নিক বস্তু-
(ক) টাইফয়েড
(খ) জিওমেট্রিক
(গ) প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন
(ঘ) ম্যালভাসি
উত্তর: (গ) প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন
১.১০ ধাতু বিভক্তির আরেকটি নাম হল
(ক) শব্দ বিভক্তি
(খ) নির্দেশক
(গ) অনুসর্গ
(ঘ) ক্রিয়া বিভক্তি
উত্তর: (ঘ) ক্রিয়া বিভক্তি
১.১১ বাক্যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সঙ্গে ক্রিয়া ভিন্ন অন্য পদের সম্পর্ককে বলা হয়
(ক) সম্বোধন পদ
(খ) কারক
(গ) বিভক্তি
(ঘ) সম্বন্ধপদ
উত্তর: (ঘ) সম্বন্ধপদ
১.১২ ইসাবের সঙ্গে কুস্তি লড়তে তো একেবারেই গররাজি নিম্নরেখ পদটি কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) অব্যয়ীভাব
(খ) নঞতৎপুরুষ
(গ) বহুব্রীহি
(ঘ) কর্মধারয়
উত্তর: (খ) নঞতৎপুরুষ
১.১৩ যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না তাকে বলে-
(ক) অলোপ সমাস
(খ) অব্যয়ীভাব সমাস
(গ) নিত্যসমাস
(ঘ) দ্বন্দু সমাস
উত্তর: (গ) নিত্যসমাস
১.১৪ ‘বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না।’এটি কী ধরনের বাক্য?
(ক) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য
(খ) নির্দেশক বাক্য
(গ) বিস্ময়সূচক বাক্য
(ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্য
উত্তর: (ক) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য
১.১৫ বাক্যের গঠন ও অর্থ অনুসারে রূপান্তরের সময় মূলবাক্যের ভাষারীতিটি
(ক) সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়
(খ) আংশিক পরিবর্তিত হয়
(গ) অপরিবর্তিত থাকে
(ঘ) কেবল ক্রিয়াখণ্ড পরিবর্তিত হয়
উত্তর: (ক) সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়
১.১৬ “দেখে আশ্চর্য বোধ হল” এটি হল
(ক) কর্তৃবাচ্য
(খ) কর্মবাচ্য
(গ) ভাববাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (ক) কর্তৃবাচ্য
১.১৭ ‘বাচ্য’ শব্দের অর্থ হল
(ক) বচন
(খ) বিরুদ্ধ
(গ) বক্তব্য
(ঘ) বাচন ক্ষমতা
উত্তর: (গ) বক্তব্য
২। কমবেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উভয় দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ “ইহা যে কতবড়ো ভ্রম তাহা কয়েকটা স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল।” ‘ভ্রমটি’ কী?
উত্তর: পথের দাবী’ রচনায় অপূর্বর ‘ভ্রম ছিল যে প্রভাতকাল পর্যন্ত ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটবেনা ।
২.১.২ ‘চিঠি পকেটেই ছিল।’ কোন্ চিঠি?
উত্তর: নদেরচাঁদ’ গল্পে উল্লেখ আছে যে, নদেরচাঁদ তার স্ত্রীকে পাঁচ পৃষ্ঠার একটি বিরহ-বেদনাপূর্ণ চিঠি লিখেছিল। গল্পে সেই চিঠিরই কথা বলা হয়েছে।
২.১.৩ ‘এসো, আমরা কুস্তি লড়ি।’ কে, কাকে বলেছে?
উত্তর: কালিয়া, অমৃত-এর সঙ্গে কুস্তি লড়তে চেয়েছিল।
২.১.৪ ‘পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?’ কোন অলৌকিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: এখানে যে অলৌকিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা হলো— তপনের লেখা একটি গল্প ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে এবং তা ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় ছাপা হয়ে হাজার-হাজার ছেলের হাতে হাতে ঘুরবে। ছোটোমাসি ও মেসো বেড়াতে এসে সেই পত্রিকা তপনকে দেন। নিজের নাম ও লেখা গল্প ছাপা হয়েছে দেখে তপনের বুকের রক্ত যেন ছলকে ওঠে। সে মনে করে আজই তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। এই ঘটনাকে তপন পৃথিবীর এক অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করে।
২.১.৫ “কী অদ্ভুত কথা বললেন হরিদা।” অদ্ভুত কথাটি কী?
উত্তর: ‘বহুরূপী’ গল্প অনুসারে, বিরাগী-রূপে আসা হরিদা জগদীশবাবুর কাছ থেকে টাকা নিতে অস্বীকার করে। কারণ, তার মতে, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে যদি সে টাকা নেয়, তবে তার ঢং নষ্ট হয়ে যাবে। গল্পে এই কথাটিকেই ‘অদ্ভূত’ বলা হয়েছে।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ “আমাদের পথ নেই আর” তাহলে আমাদের করণীয় কী?
উত্তর: এই পরিস্থিতিতে কবি আমাদের আরো বেঁধে বেঁধে থাকার বা সঙ্ঘবদ্ধ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।
২.২.২ কে, কার বুকের থেকে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল?
উত্তর: ‘আফ্রিকা’ কবিতায় কবি উল্লেখ করেছেন যে, ভয়ংকর সমুদ্রের তাণ্ডবে প্রাচ্য ধরিত্রীর বুক থেকে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়েছে।
২.২.৩ ‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশটি কোন্ কাব্যগ্রন্থের, কোন্ খন্ড থেকে নেওয়া হয়েছে?
উত্তর: পাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত ‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশটি সৈয়দ আলাওল রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের ৩৫তম খণ্ড ‘পদ্মা সমুদ্র’ থেকে নেওয়া হয়েছে।
২.২.৪ ‘তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান / নদীতে, দেশগাঁয়ে’ কীভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে তুমি মনে করো।
উত্তর: যদি মানুষ অস্ত্র ফেলে দিয়ে গানের পায়ে অস্ত্র অর্পণ করে মানবিকতা ও প্রেমবোধকে আশ্রয় করে একাত্ম হতে পারে, তবে গানের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে দেশ-গাঁয়ে, নদীতে নিয়ে বেড়ানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।
২.২.৫ “আমি চলে গেলাম দূর… দূরে।” ‘দূর’ শব্দটি কেন দু’বার ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর: পাবলো নেরুদার ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতা থেকে গৃহীত অংশে কথক তাঁর প্রিয় নারীকে অপেক্ষায় রেখে নিজ বাসভূমি ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিলেন । স্বদেশ ছেড়ে দূর থেকে দূরতর কোনো স্থানে চলে যাওয়াই ‘দূর’ শব্দটি দু’বার ব্যবহৃত হয়েছে।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘অবাক হয়ে সেদিন মনে মনে ভাবছিলাম,’ লেখক অবাক হয়ে কী ভাবছিলেন?
উত্তর: লেখক শ্রীপান্থ সুভো ঠাকুরের বিখ্যাত দোয়াতের সংগ্রহ দেখে ভাবেন, শেক্সপিয়র থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রের মতো মহান সাহিত্যিকেরা এই ধরনের দোয়াত ব্যবহার করেই অমর সাহিত্য রচনা করেছেন।
২.৩.২ The atomic engine has not even reached the blue print stage,’ এর সঠিক পরিভাষা কী?
উত্তর: The atomic engine has not even reached the blue print stage,’ এর সঠিক পরিভাষা “পরমাণু এঞ্জিনের নকশা পর্যন্ত এখনও প্রস্তুত হয়নি” লিখলে ভালো হয়।
২.৩.৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে পরিভাষাসমিতি নিযুক্ত করেছিলেন?
উত্তর: ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত হয়।
২.৩.৪ বিদেশে উন্নত ধরনের নিব কী দিয়ে তৈরি হত?
উত্তর: বিদেশে উন্নত ধরনের নিব তৈরি হত কচ্ছপের খোল কেটে।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে। রেখাঙ্কিত পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
উত্তর: “জাহাজের ধকলে” —
কারক: অপাদান কারক
বিভক্তি: “লে” (সপ্তমী / অপাদানবাচক বিভক্তি)
২.৪.২ অনুসর্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: অনুসর্গ কাকে বলে?
যেসব অব্যয় শব্দ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসে এবং কারক-সম্পর্ক নির্ধারণ করে, তাদের অনুসর্গ বলে।
উদাহরণ:
ছাত্রটির জন্য উপহার এনেছি।
২.৪.৩ সমস্যমান পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যেসব পদ বাক্যে একাধিক পদ বা বাক্যাংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে বা তাদের সংযুক্ত করে, তাদের সমস্যমান পদ বলে।
উদাহরণ: ও সে বন্ধু।
২.৪.৪ সে হাত বাড়াইয়া বন্ধুর করমর্দন করিল। রেখাঙ্ক্ষিত পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো।
উত্তর: ব্যাসবাক্য:
হাতের মর্দন = করমর্দন
সমাস নির্ণয়:
করমর্দন শব্দটি তৎপুরুষ সমাস, বিশেষত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।
২.৪.৫ যোগ্যতাহীন বাক্যের একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: যোগ্যতাহীন বাক্যের একটি উদাহরণ— “বৃষ্টির জলে আগুন জ্বলে”।
২.৪.৬ সরল বাক্যের একটি বৈশিষ্ট্য লেখো। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করতে একটি কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকাই যথেষ্ট।
উদাহরণস্বরূপ, “ছেলেটি বই পড়ছে” একটি সরল বাক্য।
এখানে —
“ছেলেটি” কর্তা (যে কাজটি করছে),
“বই” পাঠ্যের উদ্দেশ্য,
এবং “পড়ছে” হলো সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয়।
২.৪.৭ “পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল।” কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন করো।
উত্তর: কেউ (বা কর্তৃপক্ষ) পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করল।
২.৪.৮ উপায়াত্মক করণের একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: “সে পরিশ্রম করে সফলতা অর্জন করেছে” – এটি একটি উপায়াত্মক করণের উদাহরণ।
২.৪.৯ কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায়?
উত্তর: কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের মূল পার্থক্য হলো বাক্যে কর্তা ও কর্মের প্রাধান্য। কর্তৃবাচ্যে কর্তা প্রধান এবং কর্মবাচ্যে কর্ম প্রধান হয়।
২.৪.১০ একটি বাক্যে দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখাও।
উত্তর: একটি বাক্যে দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রয়োগের উদাহরণ:
আমি তাকে একটি বই দিলাম।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ ‘গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তপনের,” কী কারণে তপনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল?
উত্তর: তপনের নিজের লেখা গল্পটি ছোটো মেসো কারেকশন করে এতটাই পরিবর্তিত করে দিয়েছিল যে, তা পাঠ করে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।
৩.১.২ ‘নদীকে এভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত নদেরচাঁদ দিতে পারে।’ নদেরচাঁদের কৈফিয়তটি নিজের ভাষায় লেখো।
উত্তর: নদীকে এভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত সে দিতে পারে। নদেরচাঁদের কৈফিয়ত হলো—
নদেরচাঁদের নদীর ধারে জন্ম হয়েছে, নদীর ধারে সে মানুষ হয়েছে এবং চিরদিন নদীকে সে ভালোবেসেছে। যদিও তার দেশের নদীটি হয়তো এত বড়ো ছিল না, তবুও শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে বড়ো বা ছোটো নদীর হিসাব কেউ করে না।
দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা, নির্জীব নদীটি তার কাছে অসুস্থ দুর্বল কোনো আত্মীয়ার মতোই মমতা পেয়েছিল। একবার অনাবৃষ্টির বছরে সেই নদীটি যখন প্রায় শুকিয়ে যেতে বসেছিল, তখন নদেরচাঁদ দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল— যেমন কেউ কোনো পরম আত্মীয়ার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে কাঁদে। এই ছিল ‘নদীকে এভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।” ‘তারা’ কারা? কেন স্বপ্ন দেখতে পারল না?
উত্তর: পাবলো নেরুদা রচিত ‘অসুখী একজন’ কবিতায় দেবতাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে। কবি বলেছেন তারা (অর্থাৎ, দেবতারা) আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।
শান্ত, হলুদ দেবতারা হাজার হাজার বছর ধরে ধ্যানে ডুবে ছিল। মানুষে মানুষে বিবাদ বাঁধলেও দেবতারা সবসময় নির্বিরোধ প্রকৃতির হয়। তাই সারাক্ষণ তারা স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত। তারপর হঠাৎ একদিন শহরজুড়ে যুদ্ধের ঘন্টা বেজে উঠে। বহু মানুষের মৃত্যু হল সেই সর্বগ্রাসী যুদ্ধের আগুনে। ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ল এবং দেবতারাও ভূপতিত হল। এইজন্য তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।
৩.২.২ “এবার মহানিশার শেষে / আসবে ঊষা অরুণ হেসে” ‘মহানিশা’ কী? এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কবি কীসের ইঙ্গিত দিয়েছেন?
উত্তর: “মহানিশা” বলতে রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরের মধ্যবর্তী সময়, অর্থাৎ মধ্যরাত্রিকালকে বোঝানো হয়। এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কবি বুঝিয়েছেন,এই মহানিশার অবসানেই ঊষার আগমন ঘটবে এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী পরাধীনতার কালিমা মুছে স্বাধীনতার আলো লাভ করবে।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ “রামদাস চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল।” রামদাস কে? তার চোখ জলে ভরার কারণ কী?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ রচনাংশ অনুসারে অপূর্বর রেঙ্গুনের অফিসের সহকর্মী ছিলেন রামদাস তলওয়ারকর। একদিন অপূর্ব তাঁকে তাঁর জীবনের একটি বেদনাদায়ক ঘটনার কথা বলেন— কয়েকজন ফিরিঙ্গি ছোঁড়া অকারণে তাকে লাথি মেরে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে ফেলে দেয়। যখন অপূর্ব এর প্রতিবাদ করতে যান, সাহেব স্টেশন মাস্টারও তাকে তাড়িয়ে দেয়। সেই রেল স্টেশনে উপস্থিত কোনও ভারতীয় প্রতিবাদ তো করেই না, বরং কেউ এগিয়েও আসে না। এই ঘটনাটি শুনে সহমর্মী রামদাস দুঃখ ও লজ্জায় অব্যক্ত অপমানে দুচোখ ছলছল করে উঠেছিল
৪.২ ‘হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে।’ হরিদার জীবনে নাটকীয় বৈচিত্র্যের পরিচয় দাও।
উত্তর: হরিদার জীবনে সত্যিই এক নাটকীয় বৈচিত্র্য রয়েছে। সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পে কথক হরিদার সেই নাটকীয় বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিচয় দিয়েছেন।
সপ্তাহে বড়জোর একদিন হরিদা বহুরূপী সেজে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করতেন। অধিকাংশ দিন তাকে শূন্য হাড়ি উনুনে চাপিয়ে বসে থাকতে হতো। তবু তিনি বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে পেশাকে বেছে নেননি। কারণ, হরিদার জীবন নিজেই ছিল নাটকের মতো নানা রঙিন ঘটনার সমাহার।
এই নাটকীয় বৈচিত্র্যের কিছু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল:
চকের বাসস্ট্যান্ডে পাগলের বেশে আবির্ভাব: একদিন দুপুরে হরিদা উন্মাদ পাগলের সাজে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। মুখে লালা, হাতে ইট তুলে যাত্রীদের দিকে তেড়ে যান, ফলে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।
বাইজির সাজে রাস্তায় আগমন: এক সন্ধ্যায় ঠোঁটে রং, পায়ে ঘুঙুর পরে বাইজির বেশে হরিদা শহরের রাজপথে উপস্থিত হন। তাঁর নৃত্যভঙ্গি দেখে পথচারীরা মুগ্ধ হয়ে যায়।
নকল পুলিশ হয়ে লিচু চুরির শাস্তি: একবার পুলিশ সেজে হরিদা লিচু চুরি করা চারজন স্কুলছাত্রকে আটক করেন। পরে এক শিক্ষক ঘুষ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনেন।
সন্ন্যাসীর বেশে দার্শনিক উপদেশ: একবার বিরাগী সন্ন্যাসীর বেশে হরিদা জগদীশবাবুর বাড়ি গিয়ে তাঁকে দার্শনিক বাণী শুনিয়ে মুগ্ধ করেন।
নানান সাজে রূপ ধারণ: তিনি কখনও কাপালিক, কখনও ফিরিঙ্গি সাহেব, আবার কখনও বাউল, কাবুলিওয়ালা প্রভৃতি সেজে পথের মানুষকে চমকে দিতেন।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখো।
উত্তর: বিষয়বস্তু (সংক্ষেপে):
শঙ্খ ঘোষ রচিত ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায় কবি মানুষের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভালোবাসা ও মানবিক বন্ধনের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, বিভেদের প্রাচীর ভেঙে মানুষ যদি হাতে হাত রেখে একত্রে বসবাস করে, তবে পৃথিবী হবে শান্তিময়।
কবিতায় ইতিহাস বা গৌরবের অহংকার নয়, বরং মানুষের আন্তরিক সম্পর্ককেই জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। কবি চান, আমরা যেন একে অপরের পাশে দাঁড়াই, দুঃখে-সুখে পাশে থাকি। হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধা এই সম্পর্কই জীবনের প্রকৃত আশ্রয়।
এইভাবে কবি মানবতার জয়গান গেয়ে আহ্বান করেছেন —
“আয়, আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।”
৫.২ ‘আফ্রিকা’ কবিতা অবলম্বনে আফ্রিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের শোষণের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা নিজের ভাষায় লেখো।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আফ্রিকা’ কবিতায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের শোষণের চিত্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আফ্রিকা’ কবিতায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতা ও শোষণের ভয়াবহ চিত্র গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, একসময় আফ্রিকা ছিল শান্তি ও সভ্যতার প্রতীক। কিন্তু ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা লোভ, হিংসা ও দম্ভ নিয়ে এই শান্ত মহাদেশকে রক্তাক্ত করেছে।
তারা আফ্রিকার মানুষদের নিঃস্ব করে দাসে পরিণত করেছে। নারী, শিশু ও পুরুষদের উপর চালিয়েছে অমানবিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন। সভ্যতার নামে বর্বরতা চালিয়ে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা কালো মানুষদের শিকলে বেঁধে, চাবুকের আঘাতে ও বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাদের সংস্কৃতি, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা হরণ করেছে।
এই করুণ অবস্থাকে কবি বলেছেন—‘ধূলায় লুটানো দেবী’ ও ‘বিকৃতির কল্পনায় রাঙানো’। তবে কবি বিশ্বাস করেন, আফ্রিকা আবার জেগে উঠবে। তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও গর্ব একদিন তাকে পুনর্জীবিত করবে।
এইভাবে, কবিতাটি শুধু শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই নয়, বরং এক আশাবাদী পুনর্জাগরণের আহ্বানও।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ “তাই কেটে কাগজের মতো সাইজ করে নিয়ে আমরা তাতে ‘হোম-টাস্ক’ করতাম।” কীসে ‘হোম টাস্ক’ করা হত। ‘হোম-টাস্ক’ করার সম্পূর্ণ বিবরণ দাও।
উত্তর: “তাই কেটে কাগজের মতো সাইজ করে নিয়ে আমরা তাতে ‘হোম-টাস্ক’ করতাম— শৈশবে কলাপাতায় ‘হোম-টাস্ক’ করতেন। কলাপাতা কেটে কাগজের আকারে তৈরি করতেন এবং তাতে লেখার জন্য রোগা বাঁশের কঞ্চি কেটে কলম বানাতেন। কঞ্চির মুখ ছুঁচালো করার পাশাপাশি সেটিতে সামান্য চির ধরানো হত,। ঘরোয়া উপায়ে তৈরি কালি ব্যবহার করে এই কলমে কলাপাতার উপর লেখা হত।
ছাত্ররা নিজেদের লেখা কলাপাতা বান্ডিল করে বেঁধে স্কুলে নিয়ে যেত। শিক্ষকরা সেগুলি দেখে প্রমাণ হিসেবে আড়াআড়ি টেনে ছিঁড়ে দিতেন। পরে ছাত্ররা সেই ছেঁড়া কলাপাতাগুলি পুকুরে ফেলে দিত। কারণ, যদি অন্য কোথাও ফেলা হত, তবে গোরু তা খেয়ে ফেলতে পারত। তখনকার বিশ্বাস ছিল, গোরুকে অক্ষর খাওয়ানো পাপ এবং তা অমঙ্গল ডেকে আনে।
এইভাবেই শ্রীপান্থ তাঁর শৈশবের শিক্ষাজীবনের এক বিশেষ দিক তুলে ধরেছেন।
৬.২ ‘এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না।’ কোন্ দোষের কথা বলা হয়েছে? কীভাবে এই দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে?
উত্তর: ‘এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না।’দোষের কথা ও করণীয়—
প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসুর মতে, বাংলায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য লেখার জন্য যে রীতি অবলম্বন করা উচিত, তা বহু লেখকই রপ্ত করতে পারেননি। তাঁদের ভাষায় প্রায়ই আড়ষ্টতা দেখা যায় এবং অনেক সময়ই তা ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদের দোষে দুষ্ট। প্রশ্নে সেই দোষের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।
বাংলা পরিভাষার বিষয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন, বাংলা ভাষায় বহু ইংরেজি শব্দের যথাযথ পারিভাষিক শব্দ নেই। তিনি আরও বলেন, পরিভাষা রচনা কোনো একজনের পক্ষে সম্ভব নয়; এটি সমবেতভাবে না করলে নানা ত্রুটি দেখা দিতে পারে।
সহজ ভাষায় লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রাবন্ধিক বলেন, পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের জনগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কম। তাই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার সময় লেখকের উচিত প্রাথমিক বিজ্ঞানের মতো গোড়া থেকে শুরু করে সহজভাবে লেখা, যাতে সকল স্তরের পাঠক সেটি বুঝতে পারেন।
প্রাঞ্জল রচনা পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লক্ষ্য করেছেন, বিজ্ঞানের আলোচনায় যে সহজ রচনা পদ্ধতি প্রয়োজন, তা বহুক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হয় না। তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় আড়ষ্ট ভাষা ও ইংরেজির অনুবাদসুলভ প্রকাশভঙ্গি। প্রাবন্ধিক মনে করেন, এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না।
অলঙ্কার বর্জন সম্পর্কে তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে উপমার ব্যবহার থাকলেও অন্যান্য অলঙ্কার বর্জন করা উচিত।
ভুল তথ্য পরিহার করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন। তাঁর মতে, প্রবন্ধের তথ্য যদি সম্পূর্ণ নির্ভুল না হয়, তবে তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনিষ্টকর হতে পারে। তাই প্রাবন্ধিকের পরামর্শ, কোনো অবিখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে তা যাচাই করে নেওয়া উচিত।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “মুন্সিজি এই পত্রের মর্ম সভাসদদের বুঝিয়ে দিন।” কে, কাকে পত্র লিখেছিলেন? এই পত্রে কী লেখা ছিল
উত্তর: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত সিরাজউদ্দৌলা নাটকে এই প্রশ্নে উদ্ধৃত অংশটি রয়েছে ।
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত সিরাজউদ্দৌলা নাটকে ইংরেজ অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের একটি পত্র উদ্ধৃত হয়েছে, যা তিনি মুর্শিদাবাদের ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটসনকে পাঠান। পত্রে লেখা ছিল— “কর্নেল ক্লাইভ যে সৈন্যের কথা বলেছেন, তা দ্রুত কলকাতায় পৌঁছাবে। আমি আর একটি জাহাজ মাদ্রাজে পাঠিয়ে জানাব, বাংলায় আরও সৈন্য ও জাহাজ প্রয়োজন। আমি এমন আগুন জ্বালাব, যা গঙ্গার জল দিয়েও নেভানো যাবে না।”
এই পত্র থেকেই স্পষ্ট হয়, কলকাতা জয়ের পর ব্রিটিশদের লক্ষ্য ছিল সমগ্র ভারত দখল করা। নবাব সিরাজউদ্দৌলা এ পত্রের খবর পেয়ে ওয়াটসনকে রাজদরবার ত্যাগের নির্দেশ দেন এবং কঠোর ভাষায় বলেন— “আমরা চাইলে তোপের মুখে তোমাকে উড়িয়ে দিতে পারি, জেনে রেখো।”
৭.২ ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ অবলম্বনে মীরজাফরের চরিত্র্ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করো।
উত্তর: সিকান্দার আবু জাফরের সিরাজউদ্দৌলা নাটকে মীর জাফর এক জটিল চরিত্র। তিনি ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারী, লোভী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হিসেবে চিহ্নিত। নবাবের প্রতি তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, পলাশীর যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনায় বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ইংরেজদের সহায়তায় দেশ বিক্রি করে দেন, যদিও ক্লাইভের পরামর্শে জনসাধারণের মনে ভীতি সৃষ্টিতে তিনি দ্বিধান্বিত হন এবং ইংরেজদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। নাটকে তার চরিত্রে মানবীয় গুণাবলীও দেখা যায়—যেমন ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে সাময়িক দ্বিধা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ। তিনি মর্যাদা সচেতন ছিলেন এবং অপমান বোধে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন। নাট্যকার এই চরিত্রকে শুধুই বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখাননি; বরং কিছু মানবিক দিক তুলে ধরে চরিত্রটিকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। এজন্য মীর জাফরের প্রতি ঘৃণার পাশাপাশি কিছুটা সহানুভূতিও জাগে।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ ‘মেয়েদের টিম চ্যামপিয়নশিপ নির্ধারিত হবে এই রিলে সাঁতারেই। সেই সাঁতারে কোনির অতুলনীয় সাফল্যের যে ছবি উপন্যাসে রয়েছে, তার বিবরণ দাও।
উত্তর: রিলে সাঁতারে কোনির অসাধারণ সাফল্য
মতি নন্দীর কোনি উপন্যাসে সাঁতার প্রতিযোগিতার রিলে দৌড়ে কোনির অসাধারণ সাফল্যের চিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রভাবশালী। চ্যাম্পিয়নশিপের ভাগ্য নির্ভর করছিল এই রিলে সাঁতারের উপর। কোনি তার দল ও প্রশিক্ষকের সম্মান রক্ষার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে।
দৃঢ় সংকল্প
কোনি জানত এই সাঁতারেই তার এবং তার দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সে ছিল অবিচল ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।
অসাধারণ গতি
প্রতিযোগিতায় কোনি ছিল দ্রুততম সাঁতারু। তার গতি ছিল এতটাই চমৎকার যে সে প্রতিপক্ষদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিল।
অদম্য সাহস
প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং প্রবল চাপ সত্ত্বেও কোনি ভয় পায়নি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে সাঁতার কেটেছে এবং দলকে জয় এনে দিতে সচেষ্ট হয়েছে।
শেষ মুহূর্তের প্রচেষ্টা
শেষ ল্যাপে কোনি নিজের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দেয়। তার প্রচেষ্টায় দল জয়লাভ করে।
দলীয় জয়
কোনির এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের ফলে তার দল রিলে সাঁতারে জয়লাভ করে এবং চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নেয়।
এই দৃশ্যটি কোনির অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম ও দলের প্রতি তার দায়বদ্ধতার উজ্জ্বল উদাহরণ।
৮.২ “আমার ভবিষ্যৎ।” কার, কোন্ প্রশ্নের উত্তরে, কে কথাটি বলেছে? একথা বলার কারণ কী? কথাটির তাৎপর্য লেখো।
উত্তর: উক্ত মন্তব্যটি মতি নন্দী রচিত “কোনি” উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে ক্ষিতীশ সিংহ, কোনিকে নিয়ে বিষ্টুচরণ ধরের উদ্দেশ্যে করেন।
বক্তার মনোভাব:
এই মন্তব্যের মাধ্যমে বক্তা ক্ষিতীশ সিংহের গভীর আবেগ, ক্ষোভ, প্রত্যয় ও স্বপ্ন জড়িত রয়েছে।
কোনিকে নিয়ে বিষ্টুচরণ ধরের
প্রকৃত লক্ষ্য:
দীর্ঘদিন ক্ষিতীশ জুপিটার ক্লাবের সাঁতার প্রশিক্ষক ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে সাঁতারু তৈরি করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। এর জন্য তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ক্লাবের কিছু স্বার্থপর মানুষের ষড়যন্ত্রে তিনি সেই পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হন।
কিন্তু তিনি হার মানেননি। কোনির মধ্যে প্রতিভার সম্ভাবনা দেখে ক্ষিতীশ তাঁকে কেন্দ্র করেই নিজের স্বপ্নপূরণের পথ খুঁজে পান। সংগ্রাম, লড়াই আর কষ্টের মধ্য দিয়ে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্পই এই মন্তব্যে প্রতিফলিত হয়।
যাঁরা তাঁকে অপমান ও ব্যঙ্গ করেছে, সেই সকলের জবাব দিতে কোনিকেই হাতিয়ার করেন তিনি। সাঁতারই যার কাছে জীবনের সব, সে ক্ষিতীশ কোনির মধ্য দিয়ে নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এই মনোভাব থেকেই তিনি উক্ত মন্তব্য করেন।
৮.৩ “ঘুমের মধ্যেই কোনির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।” কোনি কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছিল? কোন্ স্বপ্ন দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল?
উত্তর: আলোচ্য অংশটি মতি নন্দী রচিত “কোনি” উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে।
একদিন ক্ষিতীশ সিংহ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলেন, দিনভর পরিশ্রমে ক্লান্ত কোনি মেঝেয় অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বালিশ না থাকায় সে নিজের দুটো হাত জড়ো করে মাথার নিচে রেখেছে। ক্ষিতীশ সিংহ তার পাশে বসে স্নেহভরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। একটু পরেই কোনি নড়ে উঠে আরো গুটিশুটি হয়ে সরে এল ক্ষিতীশ সিংহের দিকে। আর বিড়বিড় করে কী যেন বলল।
তিনি শুনতে পেলেন, ঘুমের মধ্যে কোনি আপনমনে কিছু বলছে।
তিনি ঝুঁকে পড়ল শোনার জন্য ।
কোনি বললো “দাদা”
ক্ষিতীশ বললেন “হ্যাঁ”
কোনির মুখে একটি পাতলা হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।
ঘুমের ঘোরেই কোনি বলছিল, “আমায় কুমির দেখাবে বলেছিলে।” ক্ষিতীশ ফিসফিস করে উত্তরে বলেন, “দেখাব, তোকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব।” এরপর তিনি বলেন, “আরো অনেক জায়গায় আমরা যাব— বেলুড় মণ, ব্যান্ডেল চার্চ, ডায়মন্ড হারবার, জাদুঘর, অনেক অনেক জায়গায়। তারপর তুই যাবি দিল্লি, মুন্বাই, মাদ্রাজ; আরো দূরে টোকিও, লন্ডন, বার্লিন, মস্কো, নিউইয়র্ক।”
ঘুমের আবেশ তখনও কাটেনি কোনির। ঘুমের মধ্যে সে যেন ভাবছে, তার দাদার সঙ্গেই কথা বলছে। ক্ষিতীশের কণ্ঠস্বর ও কথাগুলো সে তার দাদার কণ্ঠ বলেই মনে করে। তাই এত জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার কথা শুনে তার মুখ ঘুমের মধ্যেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
জেগে থাকা অবস্থায় যে অনুভূতি বা ইচ্ছা প্রকাশ করতে সে সংকুচিত হয়, সেই অবদমিত আবেগ ঘুমের মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়। এই অংশে ফুটে উঠেছে কোনির শিশুসুলভ আনন্দ, স্বপ্ন ও এক আন্তরিক মানবিক মুহূর্ত।
৯। চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো:
Words have lot of power. They can help or hurt, bless or curse. Unkind words do a lot of harm, kind words do lot of good. We can spoil a friend’s happiness by an unkind word, but cheer up a sad heart with a kind word which costs nothing. A kind word offers more welcome than costly present.
উত্তর: শব্দের অনেক শক্তি আছে। এগুলি সাহায্যও করতে পারে, আবার আঘাতও দিতে পারে; আশীর্বাদ দিতেও পারে, আবার অভিশাপও। অমার্জিত কথা অনেক ক্ষতি করতে পারে, আর মধুর কথা অনেক ভালো করে দিতে পারে। একটা রুক্ষ কথা বলে আমরা বন্ধুর আনন্দ নষ্ট করতে পারি, আবার বিনামূল্যের একটা স্নেহভরা কথা বলে মন খারাপ মানুষের মন ভালো করে দিতে পারি। একটা সদয় কথা দামি উপহারের চেয়েও অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ সাহিত্য পাঠের উপযোগিতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
সাহিত্য পাঠের উপযোগিতা নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ
রাহুল: অর্ণব, তুই প্রতিদিন সাহিত্য পড়ে! এতে কী লাভ বল তো?
অর্ণব: লাভই তো রাহুল! সাহিত্য মানুষকে ভাবতে শেখায়, অনুভব করতে শেখায়। এতে আমাদের মনের প্রসার ঘটে।
রাহুল: কিন্তু গল্প-কবিতা পড়ে সময় নষ্ট নয়?
অর্ণব: একদমই নয়। সাহিত্য শুধু আনন্দ দেয় না, জীবনের নানা দিক সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যেমন—মানবিকতা, সহানুভূতি, সততা—এসব গুণ তৈরি হয়।
রাহুল: আচ্ছা! এটা কি পরীক্ষার জন্যও উপকারী?
অর্ণব: অবশ্যই। সাহিত্য পাঠে ভাষাজ্ঞান বাড়ে, শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়, লেখার ক্ষমতা উন্নত হয়। ফলে পরীক্ষার উপকার হয়।
রাহুল: তাহলে তো সাহিত্য শুধু মনের খোরাকই নয়, জীবনের দিশাও দেয়!
অর্ণব: একদম ঠিক বলেছিস। সাহিত্য আমাদের পরিপূর্ণ মানুষ হতে শেখায়।
রাহুল: ঠিক আছে, আজ থেকে আমিও সাহিত্য পড়া শুরু করব!
১০.২ ‘বালকের উপস্থিত বুদ্ধিতে এড়ানো গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা’ এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
বালকের উপস্থিত বুদ্ধিতে এড়ানো গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা
নিজেস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, জুন ২৪: গতকাল শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা বালকের উপস্থিত বুদ্ধিতে এড়ানো সম্ভব হলো। স্থানীয় একটি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রোহিত পাল রেললাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখতে পায়, একটি গোটা গাছ ঝড়ে উপড়ে গিয়ে রেললাইনের উপর পড়ে আছে।
সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যায়, যে-কোনো সময় একটি ট্রেন আসতে পারে এবং বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। রোহিত দেরি না করে নিজের গায়ে থাকা লাল রঙের শার্টটি খুলে লাইনের দিকে দৌড়ে গিয়ে ওড়াতে থাকে।
চালক দূর থেকে সংকেত দেখে ট্রেন থামিয়ে দেন এবং বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। রোহিতের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার জন্য স্থানীয় মানুষজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রেল কর্তৃপক্ষ তাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
১১। যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লেখো: (কমবেশি ৪০০ শব্দে)
১১.১ বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও মানুষের ভবিষ্যৎ।
উত্তর:
বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও মানুষের ভবিষ্যৎ
বিজ্ঞান মানবজীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধির বলে প্রকৃতিকে জানার, বুঝার এবং নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। বিজ্ঞানের ধারাবাহিক অগ্রগতির ফলেই আজ মানবসভ্যতা এই উচ্চতর অবস্থানে এসে পৌঁছেছে।
বিশেষত বিংশ ও একবিংশ শতকে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি মানুষের জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। যোগাযোগ, চিকিৎসা, কৃষি, শিক্ষা, নির্মাণশিল্প, পরিবহন, এমনকি বিনোদন— প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান অসামান্য অবদান রেখেছে। আজ মানুষ ঘরে বসে মুহূর্তে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে খবর পাঠাতে পারে, হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানো প্রযুক্তি, মহাকাশ অভিযান ইত্যাদি আজ আর কল্পনা নয়— বাস্তবতা।
চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সবচেয়ে বেশি চমকপ্রদ। একসময় যেসব রোগকে মৃত্যুদণ্ড মনে করা হতো, আজ সেগুলির চিকিৎসা সহজলভ্য হয়েছে। ক্যানসার, এইডস, করোনাভাইরাস ইত্যাদি রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধে বিজ্ঞান কাজ করে চলেছে। অঙ্গপ্রতিস্থাপন, টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড আজ মানুষের আয়ু ও জীবনের গুণগত মান বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে।
তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। পরমাণু অস্ত্র, রাসায়নিক যুদ্ধ, পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ইত্যাদি বিজ্ঞানচর্চার ভুল প্রয়োগের ফল। এ ছাড়া প্রযুক্তিনির্ভর জীবনে মানুষের মধ্যে একাকিত্ব, মানসিক চাপ এবং সামাজিক সম্পর্কের অবক্ষয়ও দেখা দিচ্ছে।
তবুও বলা যায়, বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি, মহাকাশে বসবাস, চিকিৎসার আরও উন্নত পদ্ধতি— সবই আমাদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।
তবে মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান যেন কেবল যন্ত্রসভ্যতার রূপ না নেয়। মানুষের কল্যাণই হোক এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। নৈতিকতা, মানবতা ও পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ নিয়ে যদি আমরা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে পরিচালিত করতে পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে হবে সুন্দর, নিরাপদ ও সম্ভাবনাময়।
১১.২ নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রছাত্রীদের সমাজ উপযোগী ভূমিকা।
উত্তর:
নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রছাত্রীদের সমাজ উপযোগী ভূমিকা
নিরক্ষরতা একটি সমাজের সার্বিক অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। একজন ব্যক্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞান অর্জন করছেন, ততক্ষণ তিনি আধুনিক সমাজব্যবস্থায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন না। আমাদের দেশে এখনো বহু মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্রছাত্রীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সময় এসেছে।
ছাত্রছাত্রীরা হল ভবিষ্যতের দেশনির্মাতা। তাদের প্রাণশক্তি, উদ্যম এবং সমাজসচেতন মানসিকতা সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কাজে লাগানো যেতে পারে। বিশেষত গ্রামাঞ্চল বা অনুন্নত এলাকায় তারা স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরক্ষরদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। সন্ধ্যার সময় বা ছুটির দিনে তারা স্থানীয় স্কুলঘর বা খালি জায়গায় অক্ষরজ্ঞান শিবির চালাতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, পরিবেশ সচেতনতা ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কেও তারা নিরক্ষর মানুষদের অবগত করতে পারে।
তাদের এ উদ্যোগে শুধু নিরক্ষর মানুষরাই উপকৃত হবেন না, ছাত্রছাত্রীরাও বাস্তব জীবনের নানা অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদেরকে আরও সমাজমনস্ক করে তুলতে পারবে। এমনকি এই কাজগুলিকে ‘সামাজিক পরিষেবা’ হিসেবে স্কুল বা কলেজ স্তরে অন্তর্ভুক্ত করলে আরও বেশি ছাত্রছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে উৎসাহিত হবে।
তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজন যথাযথ দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা। শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় সমর্থন থাকলে এই আন্দোলন সফল হতে পারে। নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সরকারী দপ্তর থেকেও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
সংক্ষেপে বললে, সমাজে নিরক্ষরতা দূরীকরণ একটি বৃহৎ দায়িত্ব, যা শুধুমাত্র সরকার নয়, ছাত্রসমাজকেও ভাগ করে নিতে হবে। এ দায়িত্ব পালনে তারা একদিকে যেমন জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে অবদান রাখবে, তেমনি নিজেরাও হয়ে উঠবে প্রকৃত অর্থে দায়িত্বশীল নাগরিক। তাদের হাত ধরেই নির্মিত হতে পারে এক শিক্ষিত, স্বনির্ভর ও প্রগতিশীল সমাজ।
১১.৩ একটি বৃষ্টিমুখর দিনের অভিজ্ঞতা।
উত্তর:
একটি বৃষ্টিমুখর দিনের অভিজ্ঞতা
বৃষ্টি প্রকৃতির এক আশ্চর্য দান। কখনো তা উদ্দীপনা জাগায়, কখনো আবার সৃষ্টি করে ভোগান্তির। এক বৃষ্টিমুখর দিনের অভিজ্ঞতা আমার মনে আজও অমলিন হয়ে রয়েছে। সেই দিনের কথা ভাবলে আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক মনোরম অথচ কষ্টকর দিনের চিত্র।
সেদিন ছিল শ্রাবণের এক বৃহস্পতিবার। সকাল থেকে আকাশ ছিল মেঘলা, তবে বৃষ্টি শুরু হয়নি। আমি যথারীতি স্কুলে গিয়েছিলাম। প্রথম দুটি পিরিয়ড ভালোভাবে কাটলেও তৃতীয় পিরিয়ডে হঠাৎ করেই মেঘ গর্জে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। জানালার কাঁচ বেয়ে টুপটাপ জল পড়ার শব্দে মন ছুটে গেল ক্লাসরুমের বাইরের জগতে। বৃষ্টির শব্দে চারপাশ যেন এক অপার্থিব আবেশে ঢেকে গেল।
তবে এই রোমান্টিক আবহ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। স্কুল ছুটির পর বুঝলাম, বাইরে নেমে পড়া এই অঝোর বৃষ্টি আমাদের জন্য এক দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে ছাতা ছিল না, আর রিকশাও মেলেনি। বাধ্য হয়ে ভিজে ভিজেই বাড়ির পথ ধরলাম। পায়ে হেঁটে জল জমে থাকা রাস্তা পেরোতে গিয়ে কাদা ছিটে জামাকাপড় একেবারে নোংরা হয়ে গেল।
রাস্তায় দেখি ছোট ছোট খালবিল উপচে উঠেছে, ড্রেন উপচে জল রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ আবার এই পরিস্থিতিকে উপভোগ করছিল—কিছু শিশু রাস্তায় নেমে আনন্দে জল ছিটিয়ে খেলছিল। তাদের দেখে আমার মনের ক্লান্তিও কিছুটা দূর হলো।
শেষমেশ প্রায় আধঘণ্টা ভিজে আমি বাড়ি ফিরলাম। মা আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তোয়ালে ও গরম জল এনে দিলেন। গায়ে গরম জামা পরে, এক কাপ চা আর গরম লুচি খেয়ে আমি যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেলাম।
এই অভিজ্ঞতা আমাকে একদিকে যেমন প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও রূপের স্বাদ দিল, তেমনি শিখিয়ে গেল যে প্রকৃতির সামনে মানুষ কত অসহায়। তবে বৃষ্টির সেই দিনের স্মৃতি আজও আমার কাছে এক অমূল্য অনুভূতি হয়ে রয়ে গেছে। এমন বৃষ্টিমুখর দিনের রোমাঞ্চ আমি কখনও ভুলতে পারব না।
১১.৪ তোমার স্মরণীয় বাঙালি বৈজ্ঞানিক।
উত্তর:
আমার স্মরণীয় বাঙালি বৈজ্ঞানিক
আমার জীবনে যাঁর অবদান ও কীর্তি আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে, তিনি হলেন বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি শুধু একজন উদ্ভিদবিদ বা পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, দার্শনিক ও একজন মহান মনীষী। তাঁর বিজ্ঞানচর্চা ও মানবকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে আমার স্মরণীয় বিজ্ঞানীতে পরিণত করেছে।
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম হয় ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ফরসাগঞ্জে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বাংলাভাষায়, যা তাঁর মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচায়ক। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময়ও ছাত্রদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শেখানোর পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন।
জগদীশচন্দ্র বসু মূলত রেডিও তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ এবং উদ্ভিদ-চেতনা নিয়ে গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে উদ্ভিদেরও অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তিনি উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করার জন্য তৈরি করেন ‘ক্রেসকোগ্রাফ’ নামক যন্ত্র, যা বৈজ্ঞানিক জগতে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে।
এছাড়াও তিনি পদার্থবিজ্ঞানে রেডিও তরঙ্গের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। মারকনি যখন রেডিও-যোগাযোগের জন্য খ্যাতি পান, তখন বহু বিজ্ঞানী বলেন, জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা তার পূর্বসূরী ছিল। অথচ তিনি কখনো নিজের আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট নেননি। তাঁর মতে, জ্ঞানকে গোপন না রেখে তা মানবকল্যাণে কাজে লাগানো উচিত। এই মনোভাবই তাঁকে আরও শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে।
তিনি কখনো বিদেশি বিজ্ঞানীদের তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করেননি। ব্রিটিশ শাসনামলে তিনি বৈষম্যের শিকার হলেও মাথা নত করেননি। তাঁর আত্মমর্যাদা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস আজও আমাদের শিক্ষার অন্যতম দৃষ্টান্ত।
আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র বসুর কর্ম ও জীবনদর্শন আজও প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানকে যুক্ত করার যে প্রয়াস তিনি নিয়েছিলেন, তা সত্যিই অনন্য। তাই তিনি শুধু একজন বিজ্ঞানী নন, আমার কাছে একজন পথপ্রদর্শক। এই কারণেই তিনি আমার স্মরণীয় বাঙালি বৈজ্ঞানিক।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।