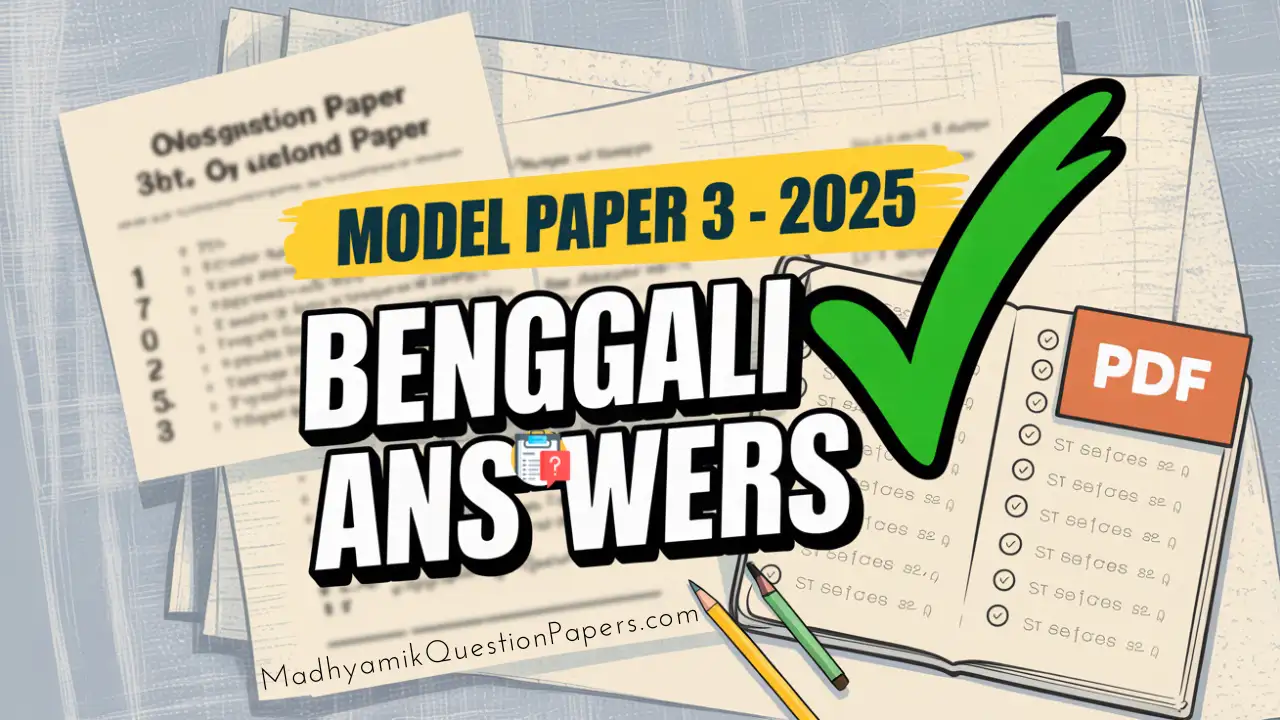আপনি কি ২০২৫ সালের মাধ্যমিক Model Question Paper 3 (2025) এর সমাধান খুঁজছেন? তাহলে আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE-এর বাংলা Model Question Paper 3 (2025)-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক ও বিস্তৃত সমাধান উপস্থাপন করেছি।
প্রশ্নোত্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সহজেই পড়ে বুঝতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে পারে। বাংলা মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও সহায়ক।
MadhyamikQuestionPapers.com ২০১৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত প্রশ্নপত্র ও সমাধান সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে আসছে। ২০২৫ সালের সমস্ত মডেল প্রশ্নপত্র ও তার সঠিক সমাধান এখানে সবার আগে আপডেট করা হয়েছে।
আপনার প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে এখনই পুরো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে নিন!
Download 2017 to 2024 All Subject’s Madhyamik Question Papers
View All Answers of Last Year Madhyamik Question Papers
যদি দ্রুত প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজতে চান, তাহলে নিচের Table of Contents এর পাশে থাকা [!!!] চিহ্নে ক্লিক করুন। এই পেজে থাকা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর Table of Contents-এ ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে। যে প্রশ্নে ক্লিক করবেন, সরাসরি তার উত্তরে পৌঁছে যাবেন।
Table of Contents
Toggle১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:
১.১ তপনের মেসোমশাই কোন্ পত্রিকার সম্পাদককে চিনতেন?
(ক) ‘শুকতারা’
(খ) ‘আনন্দমেলা’
(গ) ‘সন্ধ্যাতারা’
(ঘ) ‘দেশ’
উত্তর: (গ) ‘সন্ধ্যাতারা’
১.২ বিরাগীর ঝোলার ভেতরে যে বই ছিল, তা হল
(ক) গীতা
(খ) মহাভারত
(গ) কোরান
(ঘ) উপনিষদ
উত্তর: (ক) গীতা
১.৩ নদেরচাঁদ কত বছর স্টেশন মাস্টারি করেছে?
(ক) পাঁচ বছর
(খ) চার বছর
(গ) তিন বছর
(ঘ) এক বছর
উত্তর: (খ) চার বছর
১.৪ ‘তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।’- কারা স্বপ্ন দেখতে পারল না?
(ক) সেই মেয়েটি
(খ) গির্জার নান
(গ) কবিতার কথক
(ঘ) শান্ত হলুদ দেবতারা
উত্তর: (ঘ) শান্ত হলুদ দেবতারা
১.৫ “ওই নূতনের কেতন ওড়ে”-‘কেতন’ শব্দটির অর্থ-
(ক) শিখা
(খ) পতাকা
(গ) বাড়
(ঘ) জয়টিকা
উত্তর: (খ) পতাকা
১.৬ ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতাটির উৎস হল
(ক) ‘পাখি হুস’
(খ) ‘ভুতুমভগবান’
(গ) পাতার পোশাক’
(ঘ) ‘ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা’
উত্তর: (গ) পাতার পোশাক’
১.৭ ‘স্টাইলাস’ আসলে কী?-
(ক) তামার শলাকা
(খ) লৌহ শলাকা
(গ) ব্রোঞ্জের শলাকা
(ঘ)’প্ল্যাটিনাম শলাকা।
উত্তর: (গ) ব্রোঞ্জের শলাকা
১.৮ যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের প্রথম শ্রেণিটি
(ক) ইংরেজি ভাষায় দক্ষ
(খ) বাংলা ভাষায় দক্ষ
(গ) ইংরেজি জানে না বা অতি অল্প জানে
(ঘ) ইংরেজি জানে এবং ইংরেজি ভাষায় অম্লাধিক বিজ্ঞান পড়েছে
উত্তর: (গ) ইংরেজি জানে না বা অতি অল্প জানে
১.৯ ‘অনেক ধরে ধরে টাইপ-রাইটারে লিখে গেছেন মাত্র একজন।’ তিনি হলেন
(ক) সত্যজিৎ রায়
(খ) অন্নদাশঙ্কর রায়
(গ) রাজশেখর বসু
(ঘ) সুবোধ ঘোষ
উত্তর: (খ) অন্নদাশঙ্কর রায়
১.১০ অনুসর্গ প্রধান কারক হল
(ক) কর্তৃকারক
(খ) অপাদান কারক
(গ) সম্প্রদান কারক
(ঘ) করণ কারক
উত্তর: (ঘ) করণ কারক
১.১১ ‘পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী’ রেখাঙ্কিত পদটি হল
(ক) কর্মে বীপ্সার উদাহরণ
(খ) করণে বীপ্সার উদাহরণ
(গ) অসমাপিকা ক্রিয়ারূপী করণের উদাহরণ
(ঘ) একদেশসূচক অধিকরণের দৃষ্টান্ত
উত্তর: (খ) করণে বীপ্সার উদাহরণ
১.১২ যে সমাসে সমস্যমান পদ দুটির কোনোটিরই অর্থ প্রাধান্য থাকে না, অন্য অর্থ প্রকাশ পায় সেটি কী সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস
(খ) বহুব্রীহি সমাস
(গ) তৎপুরুষ সমাস
(ঘ) কর্মধারয় সমাস
উত্তর: (খ) বহুব্রীহি সমাস
১.১৩ ‘অস্তাচলগামী দিননাথ’ নিম্নরেখ পদটি যে সমাসের উদাহরণ, তা হল
(ক) কর্মধারয়
(খ) উপপদ তৎপুরুষ
(গ) দ্বিগু
(ঘ) বহুব্রীহি
উত্তর: (খ) উপপদ তৎপুরুষ
১.১৪ শর্তসাপেক্ষ বাক্য মাত্রই জটিল
(ক) মিশ্র
(খ) সরল
(গ) জটিল
(ঘ) কোনোটিই নয়
উত্তর:(গ) জটিল
১.১৫ ‘বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলোআনাই বজায় আছে’ এটি হল
(ক) সরল বাক্য
(খ) জটিল বাক্য
(গ) বিস্ময়সূচক বাক্য
(ঘ) যৌগিক বাকা
উত্তর: (ঘ) যৌগিক বাকা
১.১৬ ‘নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে’ এটি কোন্ বাচ্যের উদাহরণ?
(ক) কর্মবাচ্য
(খ) ভাববাচ্য
(গ) কর্তৃবাচ্য
(ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য
উত্তর: (খ) ভাববাচ্য
১.১৭ প্রদত্ত কোন্ ধরনের বাচ্য পরিবর্তনটি বাংলা ভাষায় অমিল?
(ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য
(খ) কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য
(গ) কর্মবাচ্য থেকে ভাববাচ্য
(ঘ) ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য
উত্তর: (গ) কর্মবাচ্য থেকে ভাববাচ্য
২। কমরেশি ২০টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
২.১ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.১.১ ‘পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল,’ কী দেখা গিয়েছিল?
উত্তর: পুলিশ স্টেশনে প্রবেশ করে দেখল, হলঘরের মধ্যে জনা-ছয়েক বাঙালি নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে বসে আছে। তারা ছিল বর্মা অয়েল কোম্পানির তেলের খনির কারখানায় কাজ করা মিস্ত্রি। সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় রেঙ্গুনে চলে এসেছিল। তাদের টিনের তোরঙ্গ ও পুটলি খুলে তদন্ত করা হচ্ছে । পলিটিকাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিক সন্দেহে অন্য আরেকটি ঘরে একজনকে আটকে রাখা হয়েছে। আর উপস্থিত যাত্রীদের নাম, ঠিকানা ও তাদের বিবরণ নিয়ে রেখে দেওয়া হচ্ছে।
২.১.২ “একটু মমতা বোধ করিল বটে, কোন্ ব্যাপারে ‘মমতা বোধ’ হয়েছিল?
উত্তর: অবিরাম বৃষ্টির সঙ্গে সুর মিলিয়ে নদেরচাঁদ দু-দিন ধরে তার স্ত্রীকে একটি পাঁচ পৃষ্ঠা বিরহবেদন-
পূর্ণ চিঠি লিখেছিল, সেই চিঠিটিকে নদীর স্রোতে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে একটু মমতাবোধ করছিল বটে।
২.১.৩ ‘ভয়ে অমৃতের বুক ঢিপঢিপ করছিল।’ অমৃতের ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছিল কেন?
উত্তর: কালিয়ার সঙ্গে লড়াই করে ইসাব বাবার কষ্ট করে কিনে দেওয়া জামাটা ছিঁড়ে ফেলে । ইসাবকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের ভালো জামার পরিবর্তে ইসাবের ছেঁড়া জামা গায়ে পরে অমৃত । ছেঁড়া জামা দেখে অমৃতের ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছিল এই ভয়ে যে মা থাকা সত্ত্বেও সে কি বাবার হাত থেকে রেহাই পাবে ?
২.১.৪ ‘তাই জানতো না।’ কে, কী জানত না?
উত্তর: জলজ্যান্ত একজন লেখককেও এতো কাছ থেকে দেখা যায়, তপন একথা জানত না।
২.১.৫ ‘একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল।’ কোথায়, কখন আতঙ্কের হল্লা বেজে ওঠে?
উত্তর: চকের বাসস্ট্যান্ডের কাছে ঠিক দুপুরবেলা একদিন একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল।
২.২ যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.২.১ ‘এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।’ বস্তা কোন্ কলঙ্কের কথা বলেছেন।
উত্তর: বক্তা অর্থাৎ ইন্দ্রজিতের মতে, তার মতো যোগ্য পুত্র থাকা সত্বেও যদি তার পিতা (রাবণ) যুদ্ধক্ষেত্রে যান, সেই ঘটনায় হবে কলঙ্কময়।
২.২.২ “আসছে নবীন-” ‘নবীন’ আসছে কেন?
উত্তর: নবীন জীবনহীন অসুন্দরকে চিরতরে ছেদ করতে আসছে।
২.২.৩ ‘পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন।’ পঞ্চকন্যা কীভাবে চেতনা ফিরে পেল?
উত্তর: সমুদ্রকন্যা পদ্মা ও তার সখীদের নিয়ে অচৈতন্য পঞ্চকন্যাদের বহু যত্নে ও সেবা করে চেতনা ফিরিয়ে এনেছিলো।
২.২.৪ ‘বর্ম খুলে দ্যাখো আদুড় গায়ে’ বর্ম খুলে কবি কী দেখতে বলেছেন?
উত্তর: অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান ‘ কবিতা থেকে গৃহীত আলোচ্য উদ্ধৃতাংশে কবি বর্ম বলতে ক্ষমতা বিদ্বেষ, , লোভ, অহংকার, মোহ প্রভৃতির ‘ ধর্ম ‘ খুলে দেখার কথা বলেছেন ।
২.২.৫ “সমস্ত সমতলে ধরে গেল আগুন” কেন এমন হল?
উত্তর: অসুখী একজন ‘ কবিতার অনুসারে আগ্নেয়পাহাড়ের মতো যুদ্ধ আসার ফলে সমস্ত সমতলে ধরে গেয়েছিলো আগুন।
২.৩ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৩.১ ‘বাংলায় একটা কথা চালু ছিল,’ কথাটি কী?
উত্তর: ‘বাংলায় একটা কথা চালু ছিল কথাটি হল, “কালি নেই, কলম নেই, বলে আমি মুনশি”।
২.৩.২ ‘এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত।’ রাজশেখর বসু কোন্ কথা সকল লেখককে মনে রাখতে বলেছেন?
উত্তর: সকল লেখককে মনে রাখতে বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা আত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।
২.৩.৩ “এতে রচনা উৎকট হয়।” রচনা ‘উৎকট’ হয় কীসে?
উত্তর: লেখক যদি ইংরেজিতে তার বক্তব্য ভাবেন এবং সেটিকে যথাযথ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চান, তাহলে তখন রচনা উৎকট হয়।
২.৩.৪ ‘বড়োরা শিখিয়ে দিয়েছিলেন,’ বড়োরা কী শিখিয়ে দিয়েছিলেন?
উত্তর: বড়োরা শিখিয়ে দিয়েছিলেন কলম শুধু সুঁচলো হলে চলবে না, কালি যাতে একসঙ্গে গড়িয়ে না পড়ে তার জন্য মুখটা চিরে দেওয়াটা জরুরি ।
২.৪ যে-কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
২.৪.১ “সেই নগরের নাম আমরা আলিনগর রাখি।” রেখাঙ্কিত পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
উত্তর: রেখাঙ্কিত পদ: আলিনগর
বাক্য: “সেই নগরের নাম আমরা আলিনগর রাখি।”
কারক: কর্তৃকারক
বিভক্তি: শূন্য বিভক্তি
২.৪.২ শব্দবিভক্তি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে বিভক্তি শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে শব্দকে পদে পরিণত করে, তাকে শব্দবিভক্তি বলে।
উদাহরণ- আমি বোনকে চিনি।
২.৪.৩ সমাস ও সন্ধির দুটি পার্থক্য নির্দেশ করো।
উত্তর: সন্ধি হলো দুটি বা ততোধিক শব্দের ধ্বনিগত মিলনের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন।
সমাস হলো দুটি বা ততোধিক শব্দের অর্থগত মিলনের মাধ্যমে একটি যৌগিক শব্দ গঠন।
২.৪.৪ “পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?” ‘অলৌকিক’ পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
উত্তর: ব্যাসবাক্য: যা লৌকিক নয়
সমাসের নাম: কর্মধারয় সমাস।
২.৪.৫ গঠনগত দিক থেকে বাক্য কয়প্রকার ও কী কী?
উত্তর: গঠনগত দিক থেকে বাক্য প্রধানত তিন প্রকার: সরল বাক্য, জটিল বাক্য, এবং যৌগিক বাক্য।
২.৪.৬ ‘তপন আর পড়তে পারে না।’ বাক্যটিতে বিশেষ্যখণ্ড চিহ্নিত করো।
উত্তর: বাক্য: ‘তপন আর পড়তে পারে না।’
এই বাক্যটিতে বিশেষ্যখণ্ড হল:
তপন — এটি একটি ব্যক্তি নাম এবং বিশেষ্য (নামবাচক বিশেষ্য)।
বিশেষ্যখণ্ড: তপন
২.৪.৭ ‘নদীর ধারে তার জন্ম হইয়াছে’ কর্তৃবাচ্যে পরিণত করো।
উত্তর: নদীর ধারে সে জন্মগ্রহণ করেছে।
২.৪.৮ কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে রূপান্তরের একটি নিয়ম লেখো।
উত্তর: কর্তৃবাচ্য বাক্যে কর্তা প্রধান থাকে, আর ভাববাচ্য বাক্যে ক্রিয়া প্রধান হয়। ভাববাচ্যে রূপান্তরের সময় কর্তা ‘দ্বারা’ অব্যয়সহ ব্যবহৃত হয়, এবং ক্রিয়াপদকে ‘হওয়া’ বা ‘যাওয়া’ প্রভৃতি সহকারে ব্যবহার করা হয়।
২.৪.৯ ‘বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।’ কর্মবাচ্যে পরিণত করো।
উত্তর: বুড়ো মানুষের কথাটা শোনা হোক।
২.৪.১০ সমধাতুজ কর্ম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যখন বাক্যে ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ উভয়ই একই ধাতু থেকে গঠিত হয়, তখন কর্মটিকে সমধাতুজ কর্ম বলে।
উদাহরণ: আমি একটা ভালো ঘুম ঘুমিয়েছি।
৩। প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কমবেশি ৬০ শব্দে উত্তর দাও:
৩.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.১.১ ‘এতকাল নদেরচাঁদ গর্ব অনুভব করিয়াছে।’ কী নিয়ে নদেরচাঁদ গর্ব অনুভব করত? তাঁর কোন্ উপলব্ধি সেই গর্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে, তা লেখো।
উত্তর: নতুন রং করা ব্রিজটির জন্য’ এতকাল নদেরচাঁদ গর্ব অনুভব করিয়াছে।’
যখন নদীর প্রচণ্ড রুদ্ররূপ বাঁধ ভেঙে ফেলে, তখন তার উপলব্ধি হয় -প্রকৃতির শক্তির সামনে মানুষের চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। এই উপলব্ধি তার সেই অহঙ্কারকে ভেঙে দেয় ও গর্বকে ক্ষুণ্ণ করে।
৩.১.২ ‘কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি।’ কার চোখের কথা বলা হয়েছে। চোখ দুটির বর্ণনা দাও।
উত্তর: উদ্ধৃতাংশে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচী ওরফে গিরীশ মহাপাত্রের চোখের কথা বলা হয়েছে। রুগ্ন ও অদ্ভুত বেশভূষাধারী গিরীশ মহাপাত্রের চেহারার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল তার চোখ দুটি। সে চোখ ছোটো না বড়ো, টানা না গোল, দীপ্ত না প্রভাহীন—এসব বিচার করা বৃথা। চোখ দুটি ছিল গভীর জলাশয়ের মতো, যেখানে কোনো খেলা চলবে না—সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই শ্রেয়। এই চোখই তার ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শক্তিমান ও বুদ্ধিদীপ্ত বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিকের পরিচয় প্রকাশ করে।
৩.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৩.২.১ “আঁকড়ে ধরে সে খড়কুটো” ‘খড়কুটো’ কাকে বলা হয়েছে? কেন বলা হয়েছে? আঁকড়ে ধরেছেন কেন?
উত্তর: আঁকড়ে ধরে সে খড়কুটো” ‘খড়কুটো’ বলা হয়েছে কবিতার ছোট ছোট শব্দগুলিকে। এই শব্দগুলি বাহ্যিকভাবে দুর্বল ও তুচ্ছ মনে হলেও তারা প্রতিবাদের এক নিঃশব্দ প্রতীক। কবি শব্দগুলিকে ‘খড়কুটো’ বলেছেন কারণ, যেমন ডুবে যাওয়া মানুষ বাঁচার আশায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, তেমনি কবি ও তাঁর আশ্রিত নারীরা এই শব্দগুলিকে আঁকড়ে ধরে রক্ষা পেতে চান দমন-পীড়নের হাত থেকে। তারা আশ্রয় নিয়েছেন কবিতার — কারণ কবিতা তাঁদের কাছে প্রতিরোধের শান্তিপূর্ণ অস্ত্র। তাই এঁরা এই শব্দগুলিকেই আঁকড়ে ধরে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন।
৩.২.২ “ আসছে নবীন – জীবনহারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন।” উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য লেখো।
উত্তর: প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটি কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে কবি পরাধীন ভারতের জীর্ণতা, দাসত্ব, জড়তা, বৈষম্য ও শোষণের অবসান সাধনের জন্য বৈপ্লবিক শক্তির আগমনী ধ্বনি শুনেছেন। প্রলয়রূপী যুগান্তরের পদসার কবিকে করেছে আত্মহারা। তাঁর বিশ্বাস, জীবনহারা ও অশুভের বিনাশ ঘটিয়ে নবীন শক্তির মধ্যেই রয়েছে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই নবীনই পারে সমাজের সমস্ত কুশ্রীতা ও জড়তাকে ধুয়ে-মুছে নতুন জীবনের সূচনা করতে। কবি এভাবেই পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন।
৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৪.১ “অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।” হরিদা কী ভুল করেছিলেন? অদৃষ্ট ক্ষমা না করার পরিণাম কী?
উত্তর: ‘বহুরূপী’ গল্পে হরিদা বিরাগীর ছদ্মবেশে জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁর বেশভূষা, আচরণ ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে জগদীশবাবু তাঁকে সত্যিকারের সন্ন্যাসী ভেবে সম্মান জানাতে চান এবং বিদায়ের সময় একশো টাকার প্রণামী দিতে চান। কিন্তু হরিদা সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেন।
তিনি উদাসীন ভঙ্গিতে বলেন — “আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মাড়িয়ে চলে যেতে পারি, তেমনিই অনায়াসে সোনাও মাড়িয়ে চলে যেতে পারি।” অর্থাৎ, তিনি নিজ চরিত্রে এতটাই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে, টাকা নিলে তাঁর সন্ন্যাসীর চরিত্রের পরিপন্থী হত বলে তা গ্রহণ করেননি।
এই ঘটনাকে গল্পের কথক ‘ভুল’ বলে মনে করেছেন, কারণ হরিদা অভাবী হয়েও নিজের আদর্শের কারণে ভাগ্যের দেওয়া সুযোগ ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই সততা ও আদর্শবোধ নিশ্চিত করে দেয় যে ভবিষ্যতেও তাঁর অভাব মোচন হবে না — তাঁর হাঁড়িতে মাঝে মাঝে শুধু জল ফুটবে, কিন্তু চাল থাকবে না। কথকের মতে, অদৃষ্ট হরিদার এই ‘ভুল’কে কখনও ক্ষমা করবে না।
৪.২ ‘অদল বদল’ গল্পে যে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, তা নিজের ভাষায় লেখো।
উত্তর: ‘অদল বদল’ গল্পে পান্নালাল প্যাটেল দুটি ভিন্ন জাতের চরিত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র – এক উচ্চবর্ণের ধনী ব্যক্তি ও এক নিম্নবর্ণের দরিদ্র ব্যক্তি, যাদের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবধান থাকলেও তাদের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। একে অপরের জীবনযাপন, দুঃখ-কষ্ট ও সামাজিক অবস্থান উপলব্ধি করার জন্য তারা অদলবদল করে। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে যে, মানুষ হিসেবে সবার মধ্যে সমান অনুভূতি, চাহিদা ও সম্মান পাওয়ার অধিকার আছে।
গল্পটি দেখায়, জাতপাত ও অর্থনৈতিক পার্থক্য সত্ত্বেও একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধা রেখে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা সম্ভব। এই বন্ধুত্ব কেবল ব্যক্তিগত নয়, সমাজের জন্যও এক আশাব্যঞ্জক বার্তা বহন করে—যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নয়, বরং সৌহার্দ্য ও সমবেদনার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
৫। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৫.১ ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।’ কোন্ পরিস্থিতিতে, কার এই আহ্বান? সেই আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা কবিতা অবলম্বনে লেখো।
উত্তর: যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে মানুষের বাসস্থান। প্রতিদিন কেউ না কেউ স্বজনহারা হয়েছে। ‘শিশুদের শব’ ‘কাছে দূরে’ ছড়িয়ে রয়েছে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি আজ বিধ্বস্তু। মানুষকে সাহায্য করার কেউ নেই। তাদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। এমন পরিস্থিতিতে কবিতার কথক আহ্বান করেছেন,।
প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের হাতে হাত মিলিয়ে এই প্রাণঘাতী বিপর্যয় থেকে মুক্ত হতে এগিয়ে আসে। ‘বেঁধে বেঁধে থাকি’ শব্দবন্ধটিতে একটি দৃঢ়, সংঘবদ্ধ ও গভীর বিশ্বাসের স্বর উদ্ভাসিত হয়েছে। ‘আরো’ অব্যয়টির প্রয়োগে সেই একতা ও শপথের সুর যেন দ্বিগুণিত হয়।
৫.২ “রূপে অতি রম্ভা জিনি” রস্তা কে? তার রূপের সঙ্গে কার, কেন তুলনা করা হয়েছে?
উত্তর: “রূপে অতি রম্ভা জিনি” পঙ্ক্তিতে উল্লিখিত রমণীটি হলেন কবির প্রেয়সী বা প্রিয়তমা। কবি তাঁর রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাকে দেবলোকের অপ্সরা রম্ভা-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। রম্ভা হিন্দু পুরাণে এক অনন্যসুন্দরী অপ্সরা হিসেবে পরিচিত, যিনি অসাধারণ রূপ ও নৃত্যকলার জন্য বিখ্যাত।
এই তুলনার মাধ্যমে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রেয়সীর রূপ এতটাই মোহনীয় ও আকর্ষণীয় যে তিনি স্বর্গীয় রমণীর থেকেও শ্রেষ্ঠ। কবির চোখে তার প্রেয়সী রূপের পরিপূর্ণতায় রম্ভাকেও হার মানায়। এভাবে কবি তার প্রেম ও বিরহের গভীরতাকে আরও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন।
মূলভাব: এই তুলনাটি প্রেমিকার প্রতি কবির অগাধ প্রেম, আকর্ষণ ও তার বিচ্ছেদজনিত বেদনার গভীরতাকে তুলে ধরে।
৬। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৬.১ ‘সব মিলিয়ে লেখালেখি রীতিমতো ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠান।’ কীভাবে লেখালেখি একটা অনুষ্ঠানের রূপ পেত, তা আলোচনা করো।
উত্তর: উদ্ধৃতাংশটির ব্যাখ্যা:
উদ্ধৃতাংশটি শ্রীপান্থ রচিত ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে লেখক তাঁর কিশোর বয়সের লেখাপড়া নিয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। লেখক গ্রামের ছেলে ছিলেন বলে লেখাপড়ার প্রথম জীবনে ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করতে পারেননি। তিনি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নিজেই কলম ও খালি তৈরি করতেন। কলমের মুখ সূঁচালো করে কেটে মাঝখানে চিরে দিতেন এবং দোয়াতের কালি ডুবিয়ে ডুবিয়ে লিখতেন।
কলমের কালি নিজেই তৈরি করতে হত। রান্নার কড়াই-এর তলার কালি লাউপাতা দিয়ে ঘষে তুলে পাথরের বাটিতে জলে গুলে নিতেন। কালি যেন স্থায়ী হয়, তার জন্য আতপ চাল ভেজে গুঁড়ো করে তাতে মেশাতেন এবং হরিতকী ঘষে পোড়া খন্তির ছ্যাঁকা দিতেন। দীর্ঘদিন ধরে লেখক এই দোয়াতের কালি ও বাঁশের কঞ্চির কলম ব্যবহার করতেন।
পরে শহরে এসে হাইস্কুলে ভর্তি হলে তিনি কঞ্চির কলম ছেড়ে দেন। প্রথমে কালির বড়ি দিয়ে লিখতেন, পরে বাজারে কাজল কালি ও সুলেখা কালি পাওয়া গেলে তা দিয়ে লেখালিখি করতেন। লেখা শুকাতে ব্লটিং পেপার বা বালির ব্যবহার করতেন। লেখাপড়া ও বিশেষত লেখালিখির জন্য যথাযথভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ত, যার জন্য অনেক আয়োজন করতে হত। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লেখক উপরিউক্ত মন্তব্যটি করেছেন।
৬.২ ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে পরিভাষা রচনা প্রসঙ্গে লেখক যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা আলোচনা করো।
উত্তর: রাজশেখর বসু ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার এক বড় বাধা হিসেবে পারিভাষিক শব্দের অভাবের কথা বলেছেন। এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী লেখক নানা বিষয়ে পরিভাষা রচনার কাজ করেছিলেন। যেহেতু তাঁরা এই কাজটি একত্রে করেননি, ফলে নতুন পরিভাষাগুলির মধ্যে কোনো রকম সমতা ছিল না এবং একই বিষয়ে একাধিক পরিভাষা তৈরি হয়েছিল। তবে ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত পরিভাষা সমিতি এই কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একত্রিতভাবে একটি পরিভাষা-সংকলন তৈরি করতে সক্ষম হয়। যদিও প্রাবন্ধিকের মতে, সেই সংকলনটি আরও পূর্ণাঙ্গ হওয়া প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, পারিভাষিক শব্দ ছাড়া বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা সম্ভব নয়। তবে পরিভাষা তৈরির সময় বিজ্ঞানচর্চার নিজস্ব রচনাশৈলীর প্রতিও লক্ষ্য রাখা জরুরি। সবশেষে, বিজ্ঞানচর্চার সুবিধার্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার মানুষদের সহযোগিতায় সম্মিলিতভাবে নতুন পরিভাষা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রাবন্ধিক।
৭। কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৭.১ “তোমাদের কাছে আমি লজ্জিত।” বক্তা কাদের কাছে, কেন লজ্জিত তা ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ অনুসরণে আলোচনা করো।
উত্তর: নবাব সিরাজদ্দৌলা ও ফরাসি বণিকদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা
উদ্ধৃত উক্তিটি নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের প্রধান চরিত্র নবাব সিরাজদ্দৌলার। এই উক্তিতে নবাব নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা ও সমস্ত ফরাসি বণিকদের কাছে লজ্জিত।
সুদূর ফ্রান্স থেকে বহুদিন আগে ফরাসিরা বাংলায় এসে বাণিজ্য শুরু করে। নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ফরাসিদের কোনো বিরোধ ছিল না। উভয়ের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ।
কিন্তু অনেক পরে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আসে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র বাণিজ্য নয়, বরং পুরো বাংলা দখল করে কায়েমি শাসন কায়েম করা। তাই ফরাসিদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করতে তারা নবাবের অনুমতি না নিয়েই চন্দননগরে আক্রমণ চালায় এবং তা দখল করে নেয়। এ ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ অন্যায়।
ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা নবাবের কাছে অনুরোধ জানান যে, ইংরেজরা যেন তাদের বাণিজ্যে কোনো বাধা না সৃষ্টি করে। নবাব ইংরেজদের নির্দেশ দেন শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু ইংরেজরা নবাবের আদেশ অমান্য করে চন্দননগর দখল করে নেয়।
এই অবস্থায় নবাব সিরাজদ্দৌলা ফরাসিদের কোনো সাহায্য করতে পারেননি। কারণ, কিছুদিন আগে তিনি ইংরেজ ও পূর্ণিয়ার শওকত জঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করে সৈন্য ও অর্থ দুই দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর মন্ত্রীমন্ডলিও যুদ্ধ করতে রাজি ছিলেন না।
এই সমস্ত কারণে তিনি নিজেকে অক্ষম মনে করে ফরাসিদের কাছে লজ্জিত বলে প্রকাশ করেন।
৭.২ ‘বলতে পার, ওই ঘসেটি বেগম মানবী না দানবী?’ কে, কাকে কথাটি জিজ্ঞাসা করেছেন? বক্তার কেন এরূপ মনে হয়েছে?
উত্তর: উক্ত উক্তিটি নবাব সিরাজউদ্দৌলা বলেছেন এবং তিনি কথাটি বলেছেন তাঁর স্ত্রী লুৎফা-কে উদ্দেশ করে।
সিরাজউদ্দৌলা এই প্রশ্নটি করেন ঘসেটি বেগমের নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হয়ে। নাটকে দেখা যায়, ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি মীরজাফর, জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভের সঙ্গে মিলে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন। এমনকি নিজ পরিবারের একজন সদস্য হয়েও তিনি সিরাজের প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। এসব বিশ্বাসঘাতক আচরণে সিরাজ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তার মানবিকতা নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেন।
তাই ক্ষোভ ও বেদনায় তিনি লুৎফার উদ্দেশে প্রশ্ন করেন — ঘসেটি বেগম আসলেই একজন মানুষ, না কি একজন দানব। এই প্রশ্নের মাধ্যমে সিরাজ তাঁর আত্মীয়ার নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন।
৮। কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
৮.১ ‘ক্ষিতীশের একটা হাত তোলা। চোয়াল শক্ত।” ক্ষিতীশ সিংহের এই রকম প্রতিক্রিয়ার কারণ কী?
উত্তর: প্রতিক্রিয়ার কারণ: মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসের সাঁতার
ট্রেনার ক্ষিতীশ সিংহ জুপিটার ক্লাব থেকে বিতাড়িত হলেও দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের নাড়ির টান থাকায় সে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব অ্যাপোলোতে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে মৃত্যুর আগে অন্তত একজন চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু তৈরি করার তাগিদে মনের বিরুদ্ধে গিয়েই তাকে সেই অপ্রিয় কাজ করতে হয়। অ্যাপোলোর ভাইস প্রেসিডেন্ট নকুল মুখুজ্জে তাকে দেখে সমাদরে আহ্বান জানায়। মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে ক্ষিতীশ তাকে কোনির বিষয়ে জানায় এবং শেষপর্যন্ত নিজের শর্তে তাকে রাজি করিয়ে কোনিকে অ্যাপোলোয় ভরতি করে। কিন্তু অ্যাপোলোয় ঢোকার মুহূর্তে জুপিটারের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে ক্ষিতীশ হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। তার চোখ চিক চিক করে ওঠে। হৃদয়-ছেঁড়ার সুতীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে-থাকা ক্ষিতীশ বাড়ি ফিরেও ঘুমোতে পারে না। ক্ষিতীশের মন যখন এমনভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বজড়িত, তখন সকালবেলাতেই ভেলো এসে বাহবা জানিয়ে বলে- “জুপিটারকে এবার শায়েস্তা করা দরকার। … নাড়ির সম্পর্ক-টম্পর্কগুলো একটু ভুলে যাও…।” নিজের এতদিনকার ক্লাবের প্রতি ভেলোর এই কথা তাকে আরও বেশি যন্ত্রণাকাতর করে তোলে বলেই ক্ষিতীশ হাত তুলে চোয়াল শক্ত করে এই প্রতিক্রিয়া জানায়।
৮.২ কোথায় জাতীয় সাঁতারের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ওই প্রতিযোগিতায় শেষ দিনের অবিস্মরণীয় ঘটনার বিবরণ দাও।
উত্তর: জাতীয় সাঁতারের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লির তলকাতোরা সুইমিং কমপ্লেক্সে। এই প্রতিযোগিতাই ছিল কোনির জীবনের বড় এক সুযোগ, যেখানে তার সাঁতারের দক্ষতা প্রমাণ করার মঞ্চ তৈরি হয়।
শেষ দিনের অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে রিলে সাঁতারে। কোনির দল চারজনের মধ্যে তিনজন সদস্যকে নিয়ে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু চতুর্থজন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন কোচ খিদ্দা কোনিকে দলে রাখার জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমে কিছু দ্বিধা থাকলেও শেষে কর্তৃপক্ষ কোনিকে দলে নিতে রাজি হয়।
রেস শুরু হলে কোনি শেষ সাঁতারু হিসেবে জলে নামে এবং অসাধারণ দক্ষতায় দলকে বিজয় এনে দেয়। তার এই সফলতা গোটা দলের গর্বে পরিণত হয়। উপস্থিত দর্শকদের কণ্ঠে উঠে আসে “Fight, কোনি, fight”—এই লাইনটি, যা পরিণত হয় একটি সংগ্রামী কিশোরীর জয়ের প্রতীক হিসেবে।
এই ঘটনা শুধু কোনির নয়, সমস্ত সংগ্রামী মানুষের প্রেরণা হয়ে ওঠে।
৮.৩ “খাওয়ায় আমার লোভ নেই। ডায়েটিং করি।” বক্তা কে? তার ডায়েটিং-এর পরিচয় দাও।
উত্তর: মতি নন্দীর ‘কোনি’ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে নেওয়া উক্তিটির বক্তা বিষ্টু ধর ওরফে বেষ্টাদা।
অদ্ভুত ডায়েটিং: বিষ্টু ধর অত্যন্ত বনেদি পরিবারের ধনী আইএ পাস করা মানুষ-পাড়ার সবার বেষ্টাদা। তার সাতখানা বাড়ি। একখানা গাড়ি। বড়োবাজারে ঝাড়াই মশলার বিশাল ব্যাবসা। কিন্তু তার ওজন সাংঘাতিক রকম বিপজ্জনক। সাড়ে তিন মন ওজনের বিষ্টুবাবু শরীর সুস্থ রাখতে ও স্বাভাবিক জীবন কাটাতে খাদ্যাভাস পালটে ডায়েটিং করছে। তার সেই ডায়েটিং বড়ো অদ্ভুত রকম। সে আগে রোজ আধ কিলো ক্ষীর খেত এখন ডায়েটিং-এর কারণে তিনশো গ্রাম খায়; একইভাবে জলখাবারে আগে যেখানে কুড়িখানা লুচি খেত এখন মাত্র পনেরোখানা। এ ছাড়া সে মেপে আড়াইশো গ্রাম চালের ভাত ও রাতে বারোখানা রুটি খায়। ঘি খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। তবে গরম ভাতের সঙ্গে মাত্র চার চামচ খায়; তার একবিন্দুও বেশি নয়। বিষ্টু ধর বিকেলবেলা দু-গ্লাস মিছরির শরবত আর চারটে কড়াপাকের মিষ্টি খায়। এই ডায়েটিং নিয়ে সে গর্বিত। একইসঙ্গে সে ঘোষণা করে-তার অত নোলা নেই, সংযম কেচ্ছাসাধন সেও পারে। হাটের ব্যামো-ফ্যামো আমার হবে না, বংশের কারও হয়নি। অর্থাৎ নিজের ভারিক্কি চেহারার কারণে এখন খুব কম খায়-ডায়েটিং করে। খাদ্যের ব্যাপারে নিজের নির্লোভ মানসিকতা ও ডায়েটিং-এর মাধ্যমে আপাত কম খাওয়া নিয়ে বিষ্টু ধর গর্বিত।
৯। চলিত গদ্যে শুঙ্গানুবাদ করো:
Work is another name of life. Idle person have no place on the earth. So do not waste time. Wastage of time means wastage of life. Time and tide wait for none. If you want to be happy, you have to do your duties regularly.
উত্তর: কাজই জীবনের আরেক নাম। অলস মানুষের এই পৃথিবীতে কোনো স্থান নেই। তাই সময় নষ্ট করো না। সময় নষ্ট মানেই জীবন নষ্ট। সময় এবং স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না। যদি সুখী হতে চাও, তাহলে নিয়মিত নিজের দায়িত্বগুলো পালন করতে হবে।
১০। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
১০.১ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রবর্তনের যৌক্তিকতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
উত্তর:
বিষয়: অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রবর্তনের যৌক্তিকতা
রানা: শুভ, তুমি জানো তো, এখন আবার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু করা হয়েছে। তুমি কি এতে সায় দিচ্ছ?
শুভ: হ্যাঁ রানা, আমি মনে করি এটা একটা ভালো পদক্ষেপ। আগে সবাই জানতো, ফেল করলেও পরের শ্রেণিতে উঠা যাবে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ কমে গিয়েছিল।
রানা: সেটা ঠিক, কিন্তু অনেকেই তো মানসিক চাপে ভেঙে পড়ে। ছোটদের ওপর এত চাপ দেওয়া কি ঠিক?
শুভ: চাপ নয়, বরং এটা একটা শৃঙ্খলার অংশ। যদি ছোটবেলা থেকেই পরিশ্রম করতে শেখানো যায়, তাহলে ভবিষ্যতে তারা আরও ভালো করবে।
রানা: ঠিক বলেছো। তবে শিক্ষকদেরও যত্ন নিয়ে পড়াতে হবে, যাতে সবাই বুঝে শিখতে পারে।
শুভ: একদম ঠিক। পাশ-ফেল থাকুক, তবে সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষাদানও জরুরি।
রানা: হ্যাঁ, তাহলে শিক্ষার মানও বাড়বে, আর শিক্ষার্থীরাও হবে দায়িত্বশীল।
১০.২ জলাজমি বা পুকুর ভরাট করে বহুতল বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
উত্তর:
নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ মে: বর্তমানে নগরায়নের চাপে জলাজমি ও পুকুর ভরাট করে বহুতল ভবন নির্মাণের প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই প্রবণতা পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। জলাধার ভরাটের ফলে এলাকার স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে এবং বৃষ্টির জল নিস্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে করে শহরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।
পুকুর এবং জলাজমি প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। এগুলির অস্তিত্ব জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু এখন অর্থলাভের আশায় এদের ধ্বংস করা হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।
সরকারের উচিত কঠোরভাবে এই ধরনের নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা এবং বিদ্যমান আইন বাস্তবায়ন করা। জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।
১১। যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লেখো: (কমবেশি ৪০০ শব্দে)
১১.১ বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ।
উত্তর:
বিষয়: বিজ্ঞান – আশীর্বাদ না অভিশাপ
ভূমিকা:
বিজ্ঞান মানুষের এক মহৎ অর্জন। সভ্যতার অগ্রগতির পেছনে বিজ্ঞানের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীন কালে মানুষ প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ প্রকৃতিকে অনেকাংশে জয় করেছে। তবে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি কখনো আশীর্বাদ, আবার কখনো অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়।
বিজ্ঞানের আশীর্বাদ:
আজকের দিনে আমরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছি, তার বেশিরভাগই বিজ্ঞানের দান। বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়নে বহু কঠিন রোগের নিরাময় সম্ভব হয়েছে। শিক্ষা, যোগাযোগ, কৃষি, পরিবহণ, মহাকাশযাত্রা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে।
বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে সহজ, আরামদায়ক ও গতিময় করে তুলেছে। দূরত্ব আজ আর সমস্যা নয়। কয়েক সেকেন্ডেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খবর পৌঁছে যায়।
বিজ্ঞানের অভিশাপ:
তবে বিজ্ঞান কেবল আশীর্বাদই নয়, তার কিছু ভয়াবহ দিকও রয়েছে। পরমাণু বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, রাসায়নিক অস্ত্র ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরি করে মানুষ নিজেই তার জীবন ও পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলেছে। শিল্পকারখানার বর্জ্য, যানবাহনের ধোঁয়া, প্রযুক্তির অতি ব্যবহার ইত্যাদির ফলে পরিবেশ দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হচ্ছে।
তরুণ প্রজন্ম স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়ছে, যার ফলে মানসিক চাপ, পড়াশোনায় অবহেলা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে।
উপসংহার:
সত্যি বলতে, বিজ্ঞান নিজে আশীর্বাদ বা অভিশাপ নয়। এটি নির্ভর করে আমাদের ব্যবহারের উপর। যদি বিজ্ঞানকে কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে আশীর্বাদ; আর যদি এর অপব্যবহার করা হয়, তবে তা হতে পারে মারাত্মক অভিশাপ।
তাই আমাদের উচিত বিজ্ঞানের সুফল গ্রহণ করে এর কুফল থেকে দূরে থাকা এবং পরিবেশবান্ধব, মানবকল্যাণমূলক কাজে বিজ্ঞানের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
১১.২ দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতি।
উত্তর:
বিষয়: দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতি
ভূমিকা:
মানুষের জীবনে দেশপ্রেম একটি শক্তিশালী ও আবেগঘন অনুভূতি। এই দেশাত্মবোধই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখে এবং জাতীয় সংহতির ভিত্তি গড়ে তোলে। কোনো জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি হলো তার নাগরিকদের দেশপ্রেম ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন।
দেশাত্মবোধের অর্থ ও গুরুত্ব:
দেশাত্মবোধ মানে শুধু নিজের দেশকে ভালোবাসা নয়, বরং দেশের কল্যাণে আত্মত্যাগের মনোভাব পোষণ করাও এর অংশ। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। তিনি দেশের সম্পদ রক্ষা করেন, দেশের আইন মেনে চলেন এবং দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদেরও উচিত দেশের ইতিহাস জানা, জাতীয় সংগীত শ্রদ্ধার সঙ্গে গাওয়া এবং সৎ ও দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে ওঠা।
জাতীয় সংহতি ও তার প্রয়োজনীয়তা:
জাতীয় সংহতি অর্থ হলো—জাতি, ধর্ম, ভাষা, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও ঐক্যের বন্ধন। একটি জাতি যতই বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক না কেন, জাতীয় সংহতির মাধ্যমেই তারা একসঙ্গে কাজ করতে পারে। ভেদাভেদ ভুলে সকলে এক হয়ে কাজ করলে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।
জাতীয় সংহতি না থাকলে সমাজে হিংসা, বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যা দেশকে পিছিয়ে দেয়।
দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতির সম্পর্ক:
দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় সংহতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দেশপ্রেম থেকেই জাতীয় ঐক্য জন্ম নেয়। যেমন, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে দেশমাতৃকার জন্য লড়াই করেছেন—এটাই ছিল দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতির বাস্তব দৃষ্টান্ত।
উপসংহার:
দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতি একটি শক্তিশালী জাতি গঠনের মূলভিত্তি। আজকের তরুণ প্রজন্মকে এই মূল্যবোধে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই আমরা একটি শান্তিপূর্ণ, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।
আমাদের সকলের উচিত নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশকে ভালোবাসা ও জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা।
১১.৩ বিদ্যালয় জীবনের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।
উত্তর:
বিষয়: বিদ্যালয় জীবনের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা
ভূমিকা:
বিদ্যালয় জীবন প্রতিটি মানুষের জীবনে স্মৃতিময় ও আনন্দঘন একটি অধ্যায়। এই জীবনের প্রতিটি দিনই কোনো না কোনোভাবে আমাদের মনে দাগ কাটে। তবে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা এতটাই গভীরভাবে হৃদয়ে স্থান করে নেয় যে তা চিরকাল অমলিন থেকে যায়। আমার বিদ্যালয় জীবনের তেমনই একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল—আমার প্রথম বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং পুরস্কারপ্রাপ্তি।
প্রসঙ্গ:
গত বছর আমাদের বিদ্যালয়ে আন্তঃশ্রেণি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল—“বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতা।” শিক্ষকরা উৎসাহ দিয়ে আমাদের অংশগ্রহণ করতে বলেন। আমি সাহস করে নিজের নাম লেখালাম। যদিও আগে কখনো জনসমক্ষে কথা বলিনি, তবুও নিজেকে তৈরি করতে থাকলাম। বিষয় সম্পর্কে নানা বই ও অনলাইন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনুশীলন করতাম।
প্রতিযোগিতার দিন:
অবশেষে প্রতিযোগিতার দিন এসে গেল। আমি মঞ্চে উঠার সময় প্রচণ্ড নার্ভাস ছিলাম। সবার দৃষ্টি আমার দিকে, বুক ধুকপুক করছে। কিন্তু একবার বক্তৃতা শুরু করার পর যেন সব ভয় কেটে গেল। আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পুরো বক্তৃতা উপস্থাপন করলাম। বক্তৃতা শেষে দর্শকদের করতালি আমার মনে সাহস যোগায়।
ফলাফল ও অনুভূতি:
শেষে ফলাফল ঘোষণার সময় আমার নাম প্রথম স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আমি অবিশ্বাস্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের মুহূর্তটি আমার জীবনের এক অনন্য অর্জন। শিক্ষক, বন্ধু ও অভিভাবকদের অভিনন্দন আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করে।
উপসংহার:
এই অভিজ্ঞতা আমাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বিদ্যালয় জীবনের অনেক দিন হয়তো ভুলে যাব, কিন্তু এই দিনটি আমার স্মৃতিতে চিরকাল অমলিন থাকবে। এটি শুধু একটি পুরস্কার ছিল না, ছিল নিজের সীমা অতিক্রম করার প্রথম সাফল্য।
১১.৪ বিজ্ঞান সাধনায় বাঙালি।
উত্তর:
বিষয়: বিজ্ঞান সাধনায় বাঙালি
ভূমিকা:
বিজ্ঞান মানব সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। বিশ্ববিখ্যাত অনেক বিজ্ঞানী তাদের গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্বকে দিয়েছেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। সেই ধারাবাহিকতায় বাঙালিও বিজ্ঞান সাধনায় পিছিয়ে নেই। জাতি হিসেবে বাঙালি যেমন আবেগপ্রবণ, তেমনি জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও তাদের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস।
বিজ্ঞান চর্চায় বাঙালির সূচনা:
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সময়টা ছিল বাঙালির জাগরণের যুগ। এই সময়েই বিজ্ঞানচর্চার পটভূমি তৈরি হয়। পশ্চিমা শিক্ষার ছোঁয়ায় বাঙালি তরুণেরা বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। সেই পথ ধরে অনেকেই পরিণত হন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীতে।
বিশিষ্ট বাঙালি বিজ্ঞানীরা:
বাঙালির বিজ্ঞান সাধনার কথা বললে প্রথমেই যাঁর নাম উঠে আসে, তিনি হলেন জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি রেডিও তরঙ্গ, উদ্ভিদের প্রাণবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য এবং বেতার প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করে সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেন।
সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে যৌথভাবে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান তৈরি করেন, বিশ্ববিজ্ঞানমঞ্চে বাঙালির অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন।
মেঘনাদ সাহা ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তার তৈরি সাহা আয়নীকরণ তত্ত্ব আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি মাইলফলক।
আধুনিক যুগে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, ড. জাফর ইকবাল, ড. ফিরোজ আহমেদ প্রমুখ বিজ্ঞান চর্চায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।
বর্তমান প্রেক্ষাপট:
বর্তমানে বাংলাদেশেও বিজ্ঞান চর্চা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তরুণ বিজ্ঞানীরা গবেষণায় এগিয়ে আসছেন। তবে এই অগ্রগতিকে টিকিয়ে রাখতে চাই পর্যাপ্ত গবেষণা তহবিল, সুযোগ-সুবিধা ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থা।
উপসংহার:
বিজ্ঞান সাধনায় বাঙালির অবদান বিশ্ব দরবারে আমাদের গৌরব এনে দিয়েছে। এই ধারাকে আরও এগিয়ে নিতে আমাদের বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আজকের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমুখী করে তুলতে হবে, যেন তারা আগামীর নতুন জগৎ নির্মাণে নেতৃত্ব দিতে পারে।
MadhyamikQuestionPapers.com এ আপনি অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্রের ও Model Question Paper-এর উত্তরও সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ কেমন লাগলো, তা আমাদের কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আরও পড়ার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য MadhyamikQuestionPapers.com এর সাথে যুক্ত থাকুন।